অন্যদিন-এর ‘শেকড়ের সন্ধানে’ বিভাগে তুলে ধরা হচ্ছে সাহিত্যস্রষ্টাদের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের তথ্যসহ তাঁদের জন্মভিটার পরিচিতি। আজ থাকছে আরজ আলী মাতুব্বরকে নিয়ে রচনা-
আরজ আলী মাতুব্বর। লৌকিক দার্শনিক হিসেবে খ্যাত। জীবন ঘঁষে তিনি আগুন জ্বেলেছেন। পৃথিবীর পাঠশালার ছাত্র তিনি। স্বশিক্ষিত। জনজীবনের চিন্তা-চেতনা তাঁর রচনার ভাববস্তু। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানামুখী জিজ্ঞাসার যে চিত্র তাঁর লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁর প্রজ্ঞা, মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় মেলে। এখানে তুলে ধরা হলো দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন ও জন্মভূমিকে।
পৃথিবীর পাঠশালায় স্বশিক্ষিত এক অসাধারণ দার্শনিক ভোলার জাতীয় মঙ্গলের কবি মোজাম্মেল হকের স্মৃতি বিজড়িত স্থান তালুকদার বাড়ি ঘুরে আবার আমরা এসেছি বরিশাল শহরে।
আমরা যাব লামচরি গ্রামে। আরজ আলী মাতুব্বরের পৈতৃক ভিটাতে— যা এখন ‘মাতুব্বর বাড়ি’ বলে পরিচিত। কিন্তু যাব কীভাবে? এক প্রবীণ ব্যক্তি পথের দিশা বাতলে দিলেন। জানালেন, প্রথমে আমাদের যেতে হবে তালতলী বাজারে।
একটি রিকশায় চড়ে আমি ও বিশ্বজিৎ তালতলী বাজারের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। শহরের অট্টালিকা, দোকানপাট আর জনারণ্য পেরিয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম তালতলী বাজারে। এখান থেকে লামচরির দূরত্ব পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। দূরত্বের কথা শুনেই ক্লান্ত আমাদের মন হেঁটে যেতে সায় জানাল না। এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা হলো— যাওয়া-আসায় তাকে আমরা ভাড়া দেব এক শ’ টাকা।
ইট বিছানো অসমতল পথে ঠোক্কর খেতে খেতে এক সময় পৌঁছে গেলাম, লামচরি গ্রামে, মাতুব্বর বাড়িতে।
প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল আরজ আলী মাতুব্বরের সমাধিটি—লাল রঙের সমাধিতে বড় পাথরে লেখা রয়েছে ‘আরজ’। সমাধির পেছনে লাইব্রেরি। লেখা রয়েছে ‘লামচরি আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি’। স্থাপিত: ১৩৮৬ বাংলা। প্রতিষ্ঠাতা আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে। লাইব্রেরির পেছনে পুকুর, অন্যদিকে মাতুব্বর বাড়ি।
কয়েক বিঘা জমির ওপর দণ্ডায়মান মাতুব্বর বাড়ি। চারদিকে নানা ধরনের গাছ। ফুলের গাছও রয়েছে। আমরা পাতা বাহারের গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে হাজির হলাম মাতুব্বর বাড়ির উঠোনে। এটি হলো আরজ আলীর ছোট ছেলে আ. বারেকের অংশ। আ. বারেক জীবিত নেই। জীবিত নেই আরজ আলী মাতুব্বরের মেজ ছেলে আ. খালেকও। তবে বড় ছেলে আ. মালেক জীবিত আছেন। তিনি থাকেন বরিশাল শহরে। পেশাগত জীবনে যিনি একসময় বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করতেন। সব মিলিয়ে মোট ১০ জন ছেলেমেয়ের জনক ছিলেন আরজ আলী। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে হয় এক ছেলে ও তিন মেয়ে— আবদুল মালেক, এশারণ নেছা, ছলেমান নেছা, ফয়জন্নেসা। অন্যদিকে দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে হয় ছয় ছেলেমেয়েÑ হাজেরা খাতুন, মনোয়ারা বেগম, নূরজাহান বেগম, বিয়াম্মা বেগম, আবদুল খালেক এবং আবদুল বারেক।
‘বাড়িতে কেউ আছেন?’ উঁচু কণ্ঠে কথাটি বলতেই এক চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের মহিলা বেরিয়ে এলেন। আমাদের আগমনের কারণ শুনে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন, সঙ্গে এক যুবক। আলাপচারিতায় জানা গেল, যুবকটির নাম ইউসুফ। মহিলাটির বড় মেয়ে রেখার স্বামী। আর মহিলাটি হলেন মরহুম আবদুল বারেকের স্ত্রী। আরও জানা গেল, আরজ আলী মাতুব্বরের ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল, বইপত্র সবই রয়েছে লাইব্রেরিতে। আর লাইব্রেরিটি দেখাশোনা করেন গোলাম রসুল মোল্লা নামে এক ভদ্রলোক। আমরা লাইব্রেরিটি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে ইউসুফ গোলাম রসুল মোল্লার বাড়ির দিকে রওনা হলো। আমার মনে পড়ল, কীর্তনখোলা নদীর ধারের এই লামচরি গ্রামটি একসময় জলাভূমি ছিল। পরে চর জেগে উঠলে আরজ আলীর দাদা তথা পিতামহ আমান উল্লা মাতুব্বর লামচরি গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। চর তখনো বিরান ও নির্জন। মানুষের বসবাস যেমন শুরু হয় নি, তেমনি খেত-খামারও হয় নি। সময়ের পরিক্রমায় মানুষেরা বসবাস করতে থাকে, চাষবাসও করতে থাকে। এমনি একজন মানুষ ছিলেন আরজের বাবা এন্তাজ আলী মাতুব্বর। ৩ ছেলে ও দুই মেয়ের জনক এই মানুষটি ১৩১১ সালে মারা যাবার সময় রেখে যান ৫ বিঘা জমি এবং বসতবাড়িটি। তখন আরজ আলীর মা লালমন্নেছা বিবি ছেলে আরজ আলী ও মেয়ে কুলসুমকে নিয়ে জীবন-সমুদ্রে পাড়ি জমান। বড় মেয়ের তখন বিয়ে হয়েছিল। আর অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল দুই ছেলে। কিন্তু পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হলে কী হবে—উপর্যুপরি কয়েক বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে খেতে ফসল মারা যায়। জমিদারদের খাজনা বাকি পড়ায় জমি বেদখল হলো, টিনের বসতবাড়িটাও নিলামে চড়ল। পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় আরজ আলীর মা ভিটাতে এক চিলতে ঘর তুললেন। ঘরখানি দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত আর প্রস্থে ছিল চার হাত। এই ঘরটির চারপাশে ছিল বালিশ, কাঁথা, চুলা, হাঁড়িপাতিল, পানির কলসি ইত্যাদি। এইসবের মাঝে, বলাই বাহুল্য, আরজ আলী এবং তাঁর মা-বোনকে শুতে হতো গুটিসুটি হয়ে। আর এই অবস্থায়ই আরজ আলী সমাজ, সংসার, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ভাবতে থাকেন। মনে উদয় হয় অসংখ্য প্রশ্ন। উত্তর মেলে না।
বিশ্বজিতের ডাকে সংবিত ফিরে। দেখতে পাই ইউসুফ লাইব্রেরিয়ান গোলাম রসুল মোল্লাকে ডেকে এনেছে। বিশ্বজিৎ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে লাইব্রেরির দিকে। গোলাম রসুল মোল্লা তালা খুলে আরজ আলী প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটির দরজা খোলেন। আমরা ভেতরে ঢুকি এবং হতবাক হয়ে যাই। ভেতরে ছোট দুটি কক্ষ। একটি তালাবদ্ধ। জানা যায়, চাবি হারিয়ে গেছে। অন্যটি বইতে ঠাসা। কিন্তু অধিকাংশ বই-ই পোকার খাদ্যে পরিণত হয়েছে। চেয়ার-টেবিলও ঘুণপোকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। জানালা ভেঙে গেছে। দেয়াল নোনা ধরা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির দিনে চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে। হায়, যে লাইব্রেরি ছিল আরজ আলীর স্বপ্নের ঠিকানা, তার কী দশা! সবচেয়ে দুঃখ হয়, আরজ আলীর প্রাণের জিনিস বইয়ের দশা দেখে। মনে পড়ল, আরজ আলী একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। ছোটবেলায় গ্রামের এক মক্তবে বছর খানেক পড়েছিলেন। বই-খাতা কেনার সামর্থ্য ছিল না। শুকনো তাল ও কলাপাতায় লিখতেন। জ্ঞাতি এক চাচা যেদিন দু’আনা দামের সীতারাম বসাক লিখিত ‘আদর্শলিপি’ বইটি কিনে দিলেন, সেদিন তার কী আনন্দ! সহপাঠীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বইটি দেখিয়েছেন। মামা বা খালার বাড়িতে বেড়াতে গেলে অমূল্য রতেœর মতোই বইটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।
মক্তব যখন বন্ধ হয় গেল, পৃথিবীর পাঠশালার ছাত্র হয়ে গেলেন আরজ আলী। বরিশাল শহরের পরিচিত ছাত্রদের কাছ থেকে বইপত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর অধিকাংশই ছিল পুথি সাহিত্য। বরিশাল শহরে বিদ্যোৎসাহী জনদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যেতেন প্রায় বারো কিলোমিটার হেঁটে। বাড়িতে ফিরতেন, তার সমপরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে। পরে বাড়িতেই বই নিয়ে আসতেন। বরিশালের শঙ্কর লাইব্রেরি, ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরি, ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরি থেকেও বই নিয়ে এসে পড়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির ধ্রুবতারার মতো আরজ আলীকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন জীবনের চলার পথে।
১৩৩০ সাল থেকে পাঠাগার গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন আরজ আলী। আঠারো বছরের চেষ্টায় সংগৃহীত হয় নয়শটি বই। কিন্তু ১৩৪৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠে এক প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আরজদের বৈঠক ঘর এবং তার সবটাই উড়িয়ে নিয়ে যায়। সেদিন এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, মাতৃ বিয়োগেও এমন যাতনা বোধ করেন নি। যা’ হোক, নবউদ্যমে আবার বই সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৭ বছরে তিনি ৪০০টি বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু এইসব বইও ১৩৬৫ সালের ৬ কার্তিকে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে হারিয়ে যায়। তখন আরজ আলী ঠিক করেন, বই সংগ্রহের আগে বই সংরক্ষণের জন্যে উপযুক্ত বাড়ি বানাবেন। দীর্ঘ একুশ বছর কায়িক শ্রম থেকে লব্ধ অর্থে তিনি এই লাইব্রেরির দালান ঘরটি গড়ে তোলেন, ১৩৮৬ সালে। কিন্তু হায়, এ কী দশা লাইব্রেরিটির!
আমি ভাবি, এই পশ্চাৎপদ গ্রামে দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে কী করে একজন আরজ আলী মাতুব্বর মহাবিশ্বকে দেখার দৃষ্টি অর্জন করেন? বিস্ফোরকের মতো প্রশ্নের উদয় হয় তার মনে? মনে পড়ে, আরজ আলীর নবচেতনার উন্মেষ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় একটি বিশেষ ঘটনায়। মা মারা যাবার পর বরিশাল শহর থেকে পেশাদার আলোকচিত্রীকে নিয়ে মৃতদেহের ছবি তোলার পর গ্রামের বেশিরভাগ সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি, তারা জানাজায় অংশগ্রহণ করে নি। সন্তাপ মনে আরজ সুহৃদ দু’ একজনকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের মৃতদেহ কবরস্থ করেন। তাঁর শোকাতুর মনে তখন প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, ছবি তোলা যদি সত্যিই হারাম হয়ে থাকে, সে জন্যে তো দায়ী তিনি। তাঁর মা নয়। তাহলে এ অন্যায়ের জন্যে তাঁর মাকে শাস্তি পেতে হলো কেন? এভাবেই আরজ আলীর ভেতরে নতুন চেতনার সঞ্চারিত হয়। তবে তাঁর আলোচনা, প্রশ্ন, দার্শনিক বিশ্লেষণ শুধুই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে নয়। গ্রন্থ বা ধর্ম জনগণের মধ্যে কীভাবে উপস্থিত তাকে নিয়েই আরজ আলী মাতুব্বরের বিশেষ মনোযোগ।
আরজ আলী যেসব বিষয় অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করেছেন সেগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ১. দৈনন্দিন দুর্ভোগ এবং তা পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা; ২. লোভ এবং ভয় কেন্দ্রিক ধর্ম-ডিসকোর্স; ৩. জগতের উদ্ভব এবং তার নিয়ম এবং ৪. ঈশ্বর, শয়তান, রাম, রাবণ, ফেরেশতা, দেবতা সম্পর্কিত মিথ পর্যালোচনা। এই চারটি ক্ষেত্রে আরজ আলীর চারটি প্রশ্ন উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, আরজ আলী বলেছেন যে, স্বামী ভুল করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তারপর যদি আবার তাকে গ্রহণ করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিধিসম্মত ব্যবস্থা হলো স্ত্রীকে ‘হিলা’ বিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। আরজ আলী প্রশ্ন ‘একের কারণে অন্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় কেন?’ পুরো ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে তিনি আরো প্রশ্ন করেন, ‘এই রূপ মিলন ব্যভিচারের নামান্তর নয় কি?’

দ্বিতীয় ক্ষেত্রের একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের দেহ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রসঙ্গে মানুষের সেই দেহ পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন আসে। আরজ আলীর সহজ প্রশ্ন, দেহ পুনরুদ্ধার কি সম্ভব? যদি তা সম্ভব না হয়, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ কি আধ্যাত্মিক?
তৃতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্য নিয়ে আরজ আলীর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যেমন, আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি সেই পৃথিবীর বয়স কত? কীভাবে এর উৎপত্তি? দিনরাত কীভাবে? কীভাবে মৌসুমের পরিবর্তন? কীভাবে প্রাণের উদ্ভব? কোন প্রাণ দিয়ে প্রাণীজগতের শুরু? এই পৃথিবীর সঙ্গে বাকি জগতের কী সম্পর্ক? এই জগতের শেষ কোথায়?
চতুর্থ ক্ষেত্রে দেখতে পাই, হিন্দুদের ‘রামায়ণ’-এ বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করে আরজ আলী মাতুব্বর রাবণকে পেয়েছেন এক অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ হিসেবে ও তবে অনার্য হেতু রামের বৈরী। হনুমান চরিত্রটিও তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হনুমান কোনো একক ব্যক্তি বা প্রাণী নয়, এটি আসলে গোত্রের নাম। ফেরাউন ইসলাম ধর্মে একটি খুবই খারাপ নাম, ঈশ্বরদ্রোহী, মানুষের শত্রু। আরজ আলী বলেছেন, ফেরাউন হচ্ছে মিশররাজাদের উপাধি। তিনি তৎকালীন সৃজনশীল কাজ ও বিশাল নির্মাণের নমুনা দেখে অনেক ফেরাউনের বিশাল অবদানের বিষয়টি সামনে এনেছেন।
জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল আরজ আলী মাতুব্বরের ৪টি বই—সত্যের সন্ধান, অনুমান, সৃষ্টির রহস্য, স্মরণিকা। আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত পা-ুলিপি ছিল। যেমন, সীজের ফুল (কবিতা), সরল ক্ষেত্রফল (গণিত), জীবনবাণী (আত্মজীবনী), ভিখারীর আত্মকাহিনী (আত্মজীবনী), কৃষকের ভাগ্য গ্রহ (প্রবন্ধ), বেদের অবদান (প্রবন্ধ), পরিচয়, আমার জীবন দর্শন, ডায়রি, জন্ম বংশাবলী, বংশ পরিচয় অধ্যয়ন সার ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এইসব রচনার অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে ‘আরজ আলী রচনাবলী-১ ও ২’তে।
গ্রামীণ মানুষের বৈঠকি কথোপকথনের সাদামাটা ভাষায় তাঁর রচনা নির্মিত। তাঁর জীবন যেমন সহজ-সরল অনাড়ম্বর ছিল, তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মও নিরেট সরল, আড়ম্বর আবরণহীন।
ইউসুফ এবং গোলাম রসুল মোল্লার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকশায় উঠি আমরা। রিকশা চলতে শুরু করে। চারপাশের সুন্দর প্রকৃতি, কীর্ত্তনখোলা নদী, মানুষজন দেখতে থাকি। দেখতে পাই একটি মাদ্রাসা—ঝকঝকে, সুন্দর; একটি স্কুল—জীর্ণ, হতশ্রী চেহারার। সামনে চেয়ে দেখি, চার নারী আসছে, বোরকা পরা। শুধু চোখ দুটি বাঙ্ময়। বাম দিকে তাকাই— বিশাল এক বাঁশবন। দিনেরবেলায়ও জমে আছে গুচ্ছগুচ্ছ অন্ধকার।
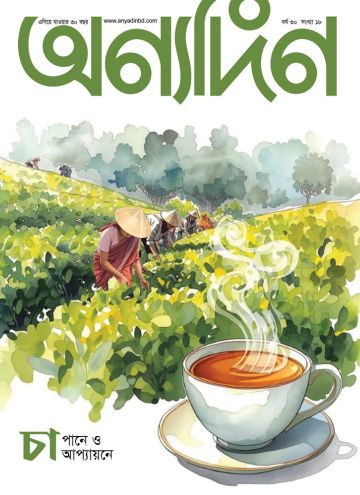




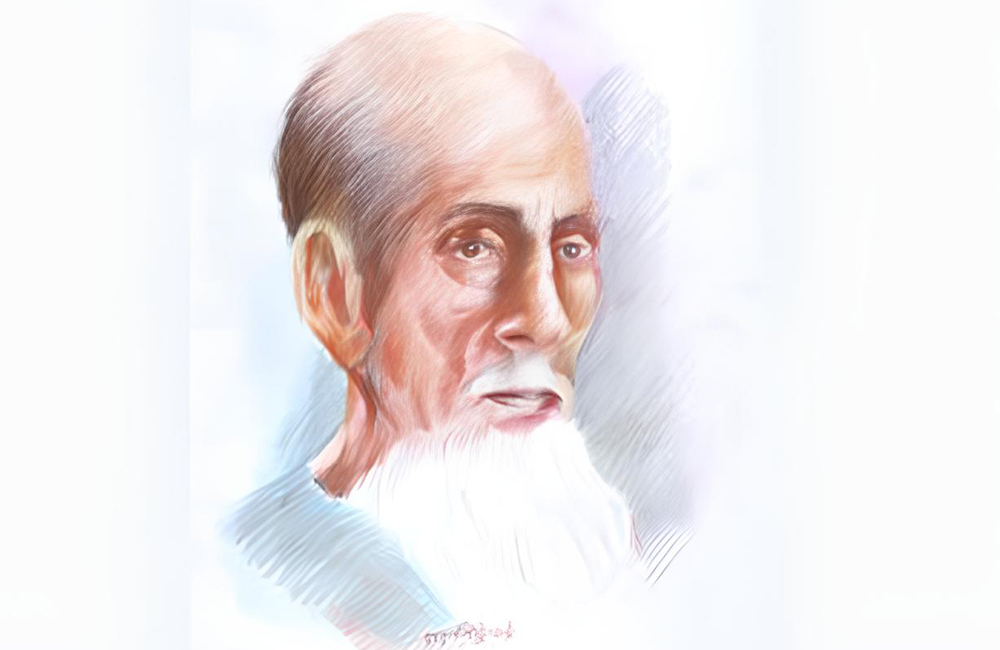

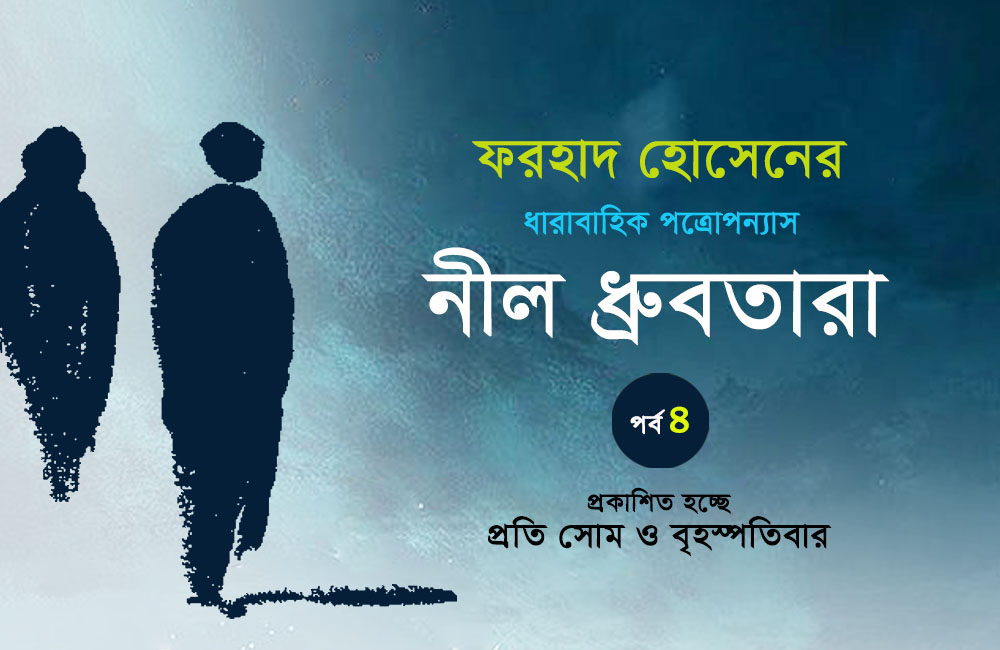







Leave a Reply
Your identity will not be published.