‘মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী’ হিসেবে খ্যাত ছিলেন আবুল ফজল। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার মূল কথা ছিল : ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’ তাই বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্র-আনুগত্য থেকে মুক্তিদানের প্রয়াসে আন্দোলন চালান তিনি। আন্দোলনের মুখপাত্র ছিল ত্রৈমাসিক ‘শিখা’। সজাগ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে তাই তিনি ছিলেন অকুতোভয়। জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিকালে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য তিনি ‘জাতির বিবেক’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।
আবুল ফজল সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য। আগামী ৪ মে আবুল ফজলের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে পুনমুর্দ্রিত হলো এই রচনাটি। লিখেছেন দীপংকর গৌতম।
আবুল ফজল কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং মননশীল চিন্তাবিদ। ভাবনা ও ভূমিকায় তিনি জাতীয় ব্যক্তিত্ব। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এ জাতির যে রূপান্তর তার পেছনে ভাবগত প্রেরণার জোগানদারদের অন্যতম ছিলেন আবুল ফজল। সেই ভাবাদর্শে সদ্যস্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন যেমন দেখেছেন তেমনি তার জন্যে প্রেরণা সঞ্চার ও পথনির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ বয়সেও। বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। পেয়েছেন একাধিক উল্লেখযোগ্য গণসংবর্ধনা। কিন্তু সেটা দিয়ে তাঁকে কল্পনা করা যাবে না। তিনি আরও বড় মাপের মানুষ ছিলেন। ছিলেন আলোক ব্রতচারী এক ঋষি।
শেকড়ের সন্ধানের এ পর্বে আমরা রাজধানী শহর থেকে চলে গিয়েছিলাম বন্দর নগরী চট্টগ্রামে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের সিদ্ধান্তে স্থির হয়েছিল আমাদের আটজন প্রয়াত কবি-সাহিত্যিকের ওপর লিখতে হবে। যাত্রী দুজন আমি ও আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সরকার। আমাদের হাতে শুধু সাদামাটা একটা ঠিকানা। এই ঠিকানা নিয়েই আমরা উঠে পড়লাম চট্টগ্রাম যাত্রার বিলাসবহুল নৈশকোচ গ্রিন লাইনে। রাত ১২টা বাজতেই ছুটে চলল গ্রিন লাইন। তারা সকাল ৭টায় আমাদের পৌঁছে দিল চট্টগ্রাম বিআরটিসি কাউন্টারের কাছে। ওখানে বসেই আমরা ঠিক করে নিলাম আমাদের যাত্রাপথ।
আমরা প্রথমে যাব সাতকানিয়া, ওখান থেকে আসব পটিয়া। পটিয়া থেকে বোয়ালখালী। সেখান থেকে চন্দনাইশ এসে যাত্রাবিরতি দেব। সেই সূত্র ধরে আমরা বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই সাউদিয়া পরিবহনে উঠে পড়লাম। আমাদের গন্তব্য সাতকানিয়ার কেঁওচিয়া গ্রাম। সাধারণত চট্টগ্রাম থেকে যে গাড়িগুলো কক্সবাজার যায়, সেই গাড়িগুলো সাতকানিয়ার কেরানিহাটে একটা স্টপিজ দেয়। সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে কেঁওচিয়া গ্রাম।
বাসস্ট্যান্ডে একজন শিক্ষককে ধরে আবুল ফজলের বাস্তুভিটার কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি তার আঞ্চলিক ভাষায় এক রিকশাওয়ালাকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কেঁওচিয়া গ্রামের আদ্যোপান্ত। তারপর ছুটে চলল রিকশা। আমাদের চোখ ভরা নির্ঘুম একরাত তার মধ্যে কখনো পিচঢালা কখনো মাটির সড়ক দিয়ে চলছি আমরা। গন্তব্য কেঁওচিয়া গ্রাম। যেতে যেতে আমাদের অভুক্ত পেট তেতে উঠছিল। তারমধ্যেও যাত্রা। আমরা যাচ্ছি মননশীল চিন্তাবিদ আবুল ফজলের গ্রামের বাড়িতে।
দূর থেকে অনেকেই চিনল বাড়িটা। সেই বাড়িতে এখন তার এক ভাগ্নে থাকেন। তিনিই সব দেখে-শুনে রাখেন। মাঝেমধ্যে সাংবাদিক আবুল মোমেন বাস্তুভিটা দেখতে যান বলে জানালেন আবুল ফজল সাহেবের অল্পশিক্ষিত ভাগ্নে।
এখানেই ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার কেঁউচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আবুল ফজল। তাঁর বাবা মৌলানা ফজলুর রহমান ছিলেন বিজ্ঞ আলেম। দীর্ঘ ৩০ বছর—১৮৯৯ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন। ধর্মচর্চাই ছিল তার মূল সাধনা। তাঁর দাদা মৌলানা হায়দার আলীরও আলেম হিসেবে খ্যাতি ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে আবুল ফজলের পারিবারিক আবহ যে কঠোরভাবে ধর্মনিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল তা বলাই বাহুল্য।
পারিবারিক এই ধর্মকেন্দ্রিক চেতনার প্রভাবে গ্রামের মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে বালক আবুল ফজল বাবার হাত ধরে শহরে আসেন মাদ্রাসায় পড়তে। এ সময় চলছে ইংরেজ শাসন। ইংরেজ তাদের শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে এদেশ থেকেই সহযোগী তৈরির বুদ্ধি আঁটে।
এছাড়াও একদল ইংরেজ অনুগত ইংরেজি শিক্ষিত তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু সেই সাথে আরেকদল এই ইংরেজি শিক্ষার সুবাদে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হয়ে যায়। এরা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ, সাম্যের স্বপ্নও দেখতে থাকে। এভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম ইংরেজি শিক্ষিতদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে।
আবুল ফজল যখন মাদ্রাসায় পড়তে গিয়েছেন তখন মুসলমানদেরও সরকারি-বেসরকারি চাকরি ও বিভিন্ন পেশার জন্যে তৈরি করতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ইংরেজি-বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোলসহ ধর্মীয় বিষয়ের বাইরের ধর্মনিরপেক্ষ নানা বিষয় সিলেবাসে রাখা হয়।
এভাবে মাদ্রাসায় পড়েও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে পরিচয় ঘটার সুযোগ হলো আবুল ফজলের। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম যুগের প্রায় সবাই মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা থেকেই এসেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ থেকে সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত অনেকেই এভাবে সাহিত্য সাধনায় এসেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কালজয়ী প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন।
কিছুদিনের মধ্যেই এর ফলাফল দেখা গেল। অচিরেই সাহিত্য সৃষ্টি করে ফেললেন আবুল ফজল। ছাপাও হলো তা। কিন্তু তারপর বাঁধল বিপত্তি। কে যেন তাঁর আলেম পিতার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়। পড়াশোনা করতে গিয়ে লেখালেখি তাও বাংলায়। স্বভাবতই ক্ষেপে গেলেন তিনি।
একদিন ঘটল ভিন্ন ঘটনা। ছেলেকে বাগে পেয়ে যান মৌলানা ফজলুর রহমান। আন্দরকিল্লার রাস্তায় নেমেছেন মসজিদ থেকে। তখন ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। আবুল ফজল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ক্লাস ছেড়ে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। মিছিলের সাথে চলে এসেছেন আন্দরকিল্লা আর পড়ে যান পিতার সামনে। সাথে সাথে পিতা লাঠি উঁচিয়ে ছেলেকে শাসন করতে উদ্যত হন। আবুল ফজল বুদ্ধির জোরে বাবার রাগকে প্রশমিত করতে সক্ষম হন।
১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আবুল ফজল ১৯২৫ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে সেখানে ভর্তি হন ১৯২৫ সালেই।
সেখানে বি.এ ক্লাশে ভর্তি হলেও ততদিনে আবুল ফজলের অন্তর আলোকিত ও বিকশিত হতে উন্মুখ। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ হলো ভিন্নমাত্রা। প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের ক্লাস, তরুণ অধ্যাপকদের মুক্তচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলসহ নানা মনীষীর সাক্ষাৎ¬—উদার প্রাণ চঞ্চল সহপাঠীদের সঙ্গ—সব মিলে আবুল ফজলের মনোজগৎ চমৎকার খোরাক পেয়ে গেল।
আবুল ফজল এ সময় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে তাঁরা গড়ে তুললেন দুটি ক্লাব। এর একটির নাম বধঃরহম পষঁন অন্যটি ষধঁমযরহম পষঁন। এর একটিতে চাঁদা দিয়ে খাওয়া হতো, অন্যটিতে আড্ডা। এ সময়ে মুসলিম সমাজের সংস্কারের চিন্তা মাথায় রেখে গড়ে উঠেছিল আরও দুটি সংগঠন। একটা আল মামুন ক্লাব অন্যটি এন্টি পর্দা লীগ বা পর্দাবিরোধী সংঘ। এসবে যাতায়াতের ফলেই হয়তো আবুল ফজল লিখেছিলেন তাঁর প্রথম সমাজ ভাবনামূলক প্রবন্ধ—পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা। তাঁর এই মনোভাব প্রায় দুঃসাহসিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যখন ১৯৩৯ সালে তিনি নববিবাহিত তরুণী ভার্যাকে বোরকা ও পালকির বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আবুল ফজল সাহিত্যচর্চায় সবচেয়ে বেশি নিবেদিত হয়ে পড়েন ‘শিখা’ গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্তির মাধ্যমে। তরুণ মুসলিম সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন তখন নিজেদের লেখালেখির পাশাপাশি মুসলমান সমাজকে তুলে আনার জন্যে সংস্কারমূলক চিন্তা করছিলেন। তাঁরা গঠন করেন ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’। আর এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করতে শুরু করেন ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র ‘শিখা’।
এই পত্রিকার নামেই ইতিহাসে এই গোষ্ঠী পরিচিতি পায় ‘শিখা গোষ্ঠী’ নামে। শিখা গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, প্রাণপুরুষ বলা যায় আবুল হুসেনকে, কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন অন্যতম সংগঠক। আবুল ফজল, কাজী আনোয়ারুল কাদির, মোতাহার হোসেন চৌধুরীসহ আরও অনেকে এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। শিখা গোষ্ঠীর মূল ব্যক্তিরা সকলেই নিজ নিজ ধর্ম ও সমাজকে ভালোবাসতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অহেতুক চাপাচাপি থেকে সমাজকে একটু মুক্তি দিতে। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ও জ্ঞানকে গ্রহণ করতে, অর্থনীতি ও সামাজিক পর্যায়ে আরও বাস্তব বুদ্ধির সাথে চলতে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকা এসেছিলেন। ততদিনে তিনি নোবেল বিজয়ী বিশ্বখ্যাত কবি।
তরুণ আবুল ফজলের মনে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, ভাষণ সবই গভীর দাগ কেটেছিল। আজীবন রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চৌচির’ (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠিয়েছিলেন। আবুল ফজলকে কবি যে উত্তর দেন তাতে যেমন ছিল তরুণ লেখকদের জন্য উৎসাহের দু’ছত্র তেমনি মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠারও প্রকাশ। ১৯২৮ সনে তিনি বি.এ পাশ করেন। বাবা তখন জীবনের সায়াহ্নে। একদিকে মাথায় সাহিত্য সাধনার পোকা অন্যদিকে জীবিকার তাগিদ। প্রথম চাকরি হলো সীতাকুণ্ড হাই মাদ্রাসার হেডমাস্টারের। কিছুদিন পর আবুল ফজল কলকাতায় গিয়ে আইন পড়তে ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। এসময় ১৯২৯ সালে তাঁর পিতা মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবুল ফজলকে আইনে পড়াশুনা বাদ দিতে এবং দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেন। আবুল ফজল তাঁর পিতার আদেশ রক্ষা করেছিলেন।
১৯৪০ সালে তিনি এম এ পড়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ করেন। যথাসময়ে বাংলায় পাশ করেন তিনি।
১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামে অধ্যাপনা করতে আসেন এবং বদলি হয়ে ১৯৫৯ সালে অবসর নেন চাকরি থেকে। ১৯৬৬-র ছয়দফা ঘোষণার পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় সরকারি দমন-পীড়ন যখন চরমে তখন তিনি স্বাধিকার ও উদারনৈতিক যুক্তিবিচারের মাধ্যমে মূল্যবোধকে সামনে এনে কথা বলেছেন বারবার।
১৯৬২ সালে কথাসাহিত্যের জন্যে তিনি বালা একাডেমি পুরস্কার পান। এমন বহু সম্মান-পুরস্কার তিনি পেয়েছেন সারা জীবনে। তিনি অবসর জীবনের পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা ১৪ বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।
আবুল ফজল আমৃত্যু স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে লিখে গেছেন নিরন্তর। মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য তিনি ছিলেন উৎসর্গকৃত প্রাণ। এই মহান ব্যক্তি ১৯৮৩-এর ৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।
এভাবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের রক্ষণশীল গাঁয়ের সংস্কারের আবহে জন্মে আবুল ফজল দেশজোড়া তাঁর পরিচয় বিস্তার করেছিলেন। সেই গ্রামের চরিত্র আছে। তাঁর স্মৃতিভরা ভিটা পড়ে আছে। সব ছবি তুলে ফেলে বিশ্বজিৎ। আমরা চলি নতুন পথের সন্ধানে।
(অন্যদিন, আগস্ট, ২০০৪)





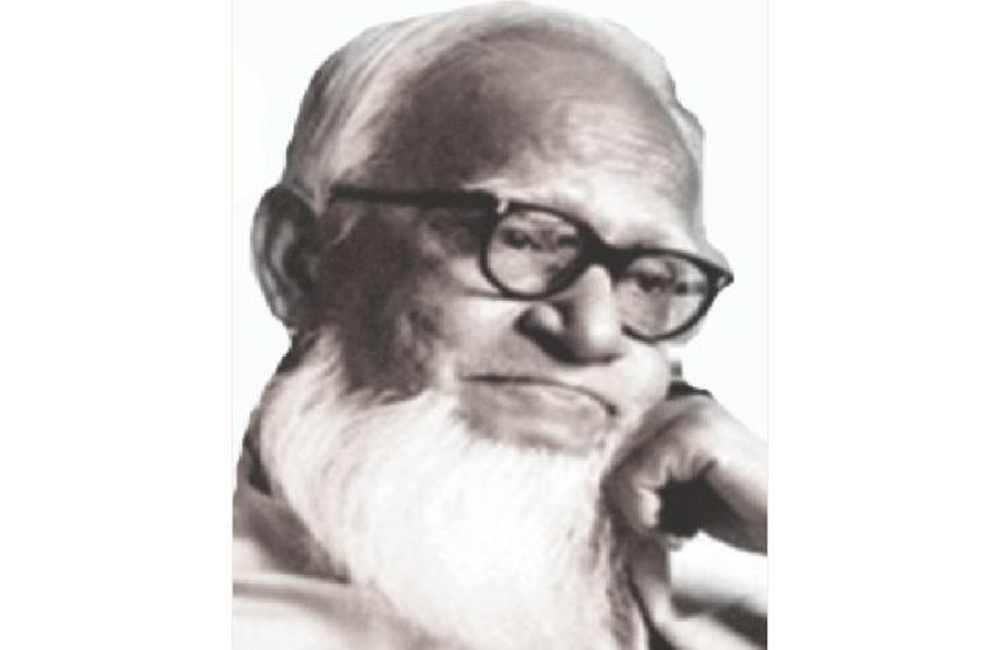
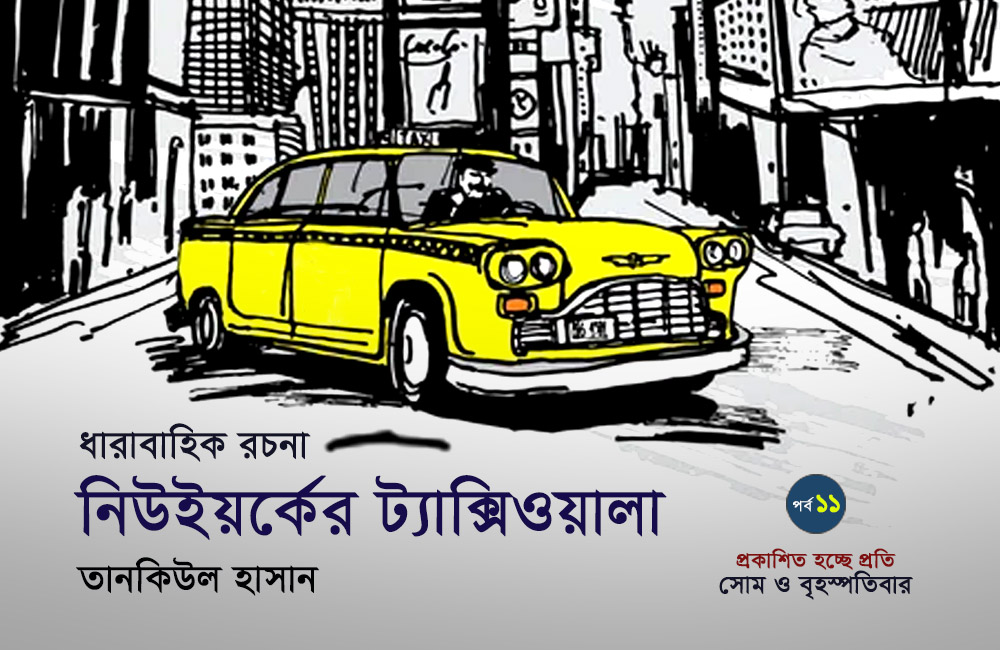



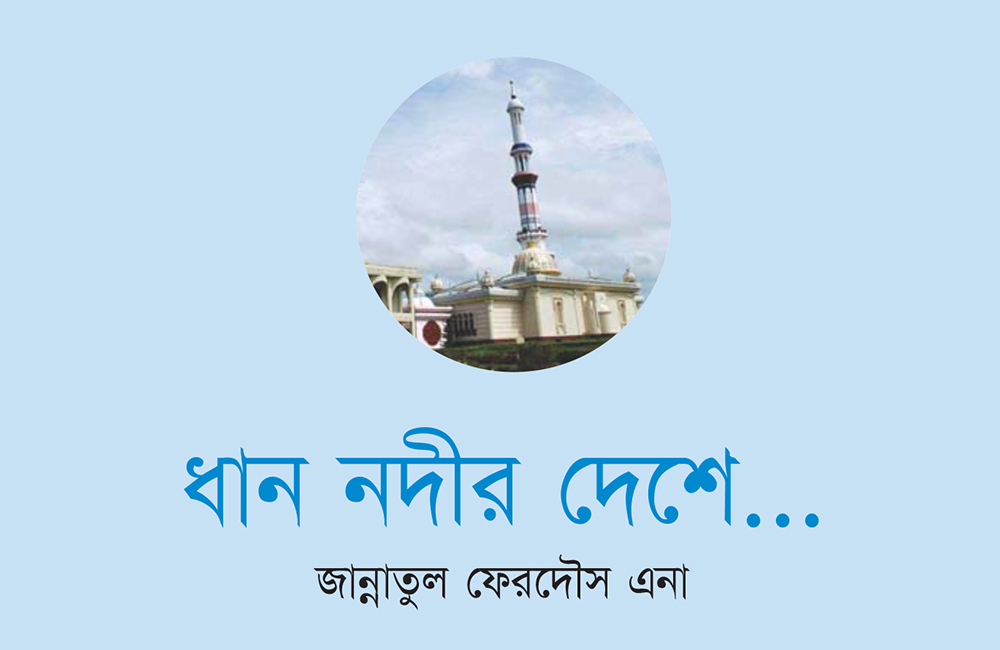




Leave a Reply
Your identity will not be published.