[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজি ছিলেন জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি বা দেবী বালা। খাজা হাবিবুল্লাহর বিয়ের অনুষ্ঠানে দেবী বাইজি ও অন্য এক বাইজি নাচ-গান করেছিলেন। দেবী বাইজি পরে প্রথম ঢাকায় নির্মিত পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র (নির্বাক) দ্য লাস্ট কিস-এ অভিনয় করেন। হরিমতি বাইজি ঢাকায় এসেছিলেন। তিনিও এই নির্বাক ছবিটিতে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় শেষে তাঁরা আবার নিজ পেশায় ফিরে যান। দেবী বাইজি ঢাকার বিভিন্ন সংগীতসভায় একা এবং কলকাতার হরিমতি বাইজির সঙ্গে গান করেন। কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর ছেলের বিয়েতে ঢাকা থেকে বাইজি আনতে পেরে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছিলেন। গান আর নাচে খুব দক্ষ না হলে সেকালে ভালো বাইজি হওয়া যেত না। তার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হতো সুরূপের মহিমা।
ঢাকার বাইজিদের সময় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকেই ফুরিয়ে যেতে থাকে। দেশভাগ ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ এঁদের পৃষ্ঠপোষকহীন করে ফেলে।
১৮৭৩ সালে কলকাতার মেয়েরা যখন রঙ্গমঞ্চে আসার অনুমতি পেলেন, তখন নিষিদ্ধপল্লীর সংগীতে পারদর্শীরাই প্রথম মঞ্চে এসেছিলেন। তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত সমস্ত অভিনেত্রীরাই সুগায়িকা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী থেকে বিংশ শতাব্দীর আঙুরবালা, ইন্দুবালা পর্যন্ত অনেকেরই নাম করা যায়। সুঅভিনেত্রী, সুগায়িকা কানন দেবী এখনো অনেকেরই প্রিয়।
মন্দিরে দেবদাসী বা সেবাদাসীরা মাতৃপ্রধান সমাজে সম্মানকর অবস্থায় ছিলেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি ‘গীতগোবিন্দ’ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর পত্নী অত্যন্ত সুন্দরী ও নাচেগানে পারদর্শী পদ্মাবতী ছিলেন একজন দেবদাসী। মা-বাবা পদ্মাবতীকে সেবাদাসী করতে চাইলেও পদ্মাবতী জয়দেবকে বিয়ে করে সংসারী হন। একসময় দেবীর উদ্দেশে নাচ ও সংগীত পরিবেশনের জন্যে বিয়ে বা সংসার না করে দেবতালয়েই সারাজীবন পড়ে থাকতেন এই সেবাদাসী এবং দেবদাসীরা। পরবর্তীকালে ধর্মালয়ে নারীর পরিবর্তে পুরুষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এই সেবাদাসীদের কাজ হয়, দেবতার বা মন্দিরের বদলে পুরুষ পুরোহিতদের এবং মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের নাচ-গান দিয়ে বিমোহিত করে তাঁদের যৌনাকাক্সক্ষা পূরণ করা। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অধিকাংশ শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার উৎস মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গকৃত নৃত্য। একদা মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৃত্য থেকেই বিভিন্ন ধারার নৃত্য চালু হয়েছে।
বাইজি-বারাঙ্গনারা সেই প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষদের আনন্দ সরবরাহ করার জন্যে নিজেদের ক্রমাগত বিভিন্ন কলায় প্রশিক্ষণ দান করে এসেছেন। সংস্কৃতিচর্চা ছাড়াও সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁরা, বিশেষ করে কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য বাইরের কুলটা নারীরা যখন ক্রমান্বয়ে এমন শিক্ষিত হয়ে উঠছেন এবং পুরুষদের মনোরঞ্জন করছেন, তাঁদের মননের চর্চার সঙ্গ হচ্ছেন, তখন অন্তঃপুরে অন্তরীন কুলবধূদের অধিকার আরও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তাঁদের কাছ থেকে বেদ-পাঠের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়।
বারবনিতা-বাইজিদের অসীম অবদান আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য নির্মাণে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় গানে, অভিনয়ে (নাটকে ও চলচ্চিত্রে) সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় এই নারীদের বহুমুখী ভূমিকা রয়ে গেছে, যা সংক্ষেপে নিচে বর্ণিত হলো :
সংগীত : সংগীতে বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রে বাইজি ও বারবনিতাদের অবদান অপরিসীম। নৃত্যগীত, বাজনা তখন কুলনারীদের জন্যে একরকম নিষিদ্ধ ছিল। গানে-নাচে-বাদ্যযন্ত্রে পুরুষদের মাতোয়ারা করার দায়িত্বে ছিলেন বাইজি-গণিকারা।
প্রথম রেকর্ড আবিষ্কার ও ভারতে তার প্রচার কাহিনির সঙ্গে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে নামটি হলো গওহরজান। দিনটা ছিল উপমহাদেশের গ্রামোফোন রেকর্ডিং ইতিহাসের তৃতীয় দিন, ১৯০২ সালের ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার। ত্রিশবছর বয়সী গওহরজান তিন হাজার টাকার অতি উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন ভাষায় নয়টি গান রেকর্ড করেন সেদিন। এ দিন রেকর্ডকৃত গওহরজানের একটি জনপ্রিয় গান ছিল: ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল, আর এল না। পরবর্তী সময়ে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ও টপ্পা আঙ্গিকের এ গানটি করেছেন। গওহরজান তাঁর অর্জিত প্রচুর অর্থ-ই বিভিন্ন সামাজিক কাজে দান করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডিংশিল্পে গওহরজান ছিলেন মধ্যমণি, যাঁর প্রতিটি রেকর্ডের অভাবনীয় সাফল্য তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। যেরাগসংগীত সে সময়ের শিল্পীদের পরিবেশন করতে হতো দীর্ঘ সময় ধরে, সেই পরিবেশনা মাত্র তিন মিনিটে সীমিত করে গেয়ে প্রথম রেকর্ড করেছেন গওহরজান—কোনোভাবে রাগের ধারা বা রসের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। তাঁর এই বৈপ্লবিক সাফল্য সেই সময়ের অন্য শিল্পীদেরও প্রেরণা দেয়। অনেক শিল্পীই তখন এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পান। উচ্চাঙ্গসংগীতকে এভাবে গওহরজান ও অন্যান্য বাইজিরা সাধারণ মানুষের কাছে উপভোগ্য করে তোলেন।
সংগীতশিল্পী হিসেবে শুধু তাঁর ঈর্ষর্ণীয় সুখ্যাতি ছিল, তাই নয়, শরীরে ককেশিয়ান রক্তধারী গওহর ছিলেন অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফ্যাশনদুরস্ত নারী। দামিদামি গহনা ও পাথর পরতে ভালোবাসতেন। কথিত আছে, ‘ঠাটে-ঠমকে চমক ছিল গওহরজানের।’
এ ছাড়াও তখনকার সময়ের কলের গানের অন্য নামকরা গায়িকারাও সবাই ছিলেন গণিকা পাড়া থেকে আগত। যেমন সুকুমারী দত্ত, নটী বিনোদিনী, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া বা এদের মতো প্রাথমিক যুগের বাংলা গানের গায়িকারা সবাই ছিল বাস্তবজীবনে পেশাদার গণিকা।
তিনরকম সংগীতের ধারা ছিল গণিকা-বাইজিদের : ১) চটুল বা হালকা কথার গান, ২) ভক্তিগীতি, ৩) উচ্চাঙ্গ সংগীত ও রাগরাগিনীভিত্তিক গান।
বিশ শতকের রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্তের গানে সুনাম অর্জন করেন হরিমতি, আনন্দময়ী দাস, নরসুন্দরী, বেদানাদাসী, মিস বটরাণী, মলিনাদেবী (যিনি বাইজি পেশা থেকে পরে সিনেমায় এসেছিলেন)। এঁরা সকলেই একই ধরনের পল্লীর বাসিন্দা। অনেক সংগীতজ্ঞ মনে করেন, রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় করার পেছনে গণিকা ও বাইজি গায়িকাদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। শোনা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের সুর পরিবর্তন করে তাঁরা তাঁদের মতো করে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছু মনে করতেন না। কোনো আপত্তি বা বারণও করতেন না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র গুপ্ত গণিকা-বাইজি শিল্পীদের সম্বন্ধে নিজে লিখেছেন, ‘সমাজের চোখে এরা যতই খারাপ হোক না কেন সাহিত্যে পেয়েছে তারা এক অদ্ভুত সম্মান।’
একসময় ভদ্রঘরের কন্যারা প্রকাশ্য সভায় গান পরিবেশনের কথা চিন্তা করতে না পারলেও, সুগায়িকা বারবনিতা ও বাইজিদের পরে আস্তে আস্তে বনেদি পরিবারের মেয়েরা সংগীতচর্চায় বেরিয়ে আসেন। এদের অনেকের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, ফিরোজা বেগম, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ এই নতুন ধারার পত্তন করেন।
মঞ্চনাটক : আমরা সবাই জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের আগে (১৮৭৩) মঞ্চে নারীরা অভিনয় করতে পারতেন না। পুরুষেরা নারী সেজে নারীর চরিত্র রূপায়িত করতেন। নারীদের মঞ্চে অভিনয় করার যখন ডাক এলো, বারবনিতা-বাইজিরাই প্রথম এগিয়ে এলেন। মঞ্চে অভিনয়ে প্রথমে এগিয়ে এলেন এলোকেশী, গঙ্গামণি, জগত্তারিনী, শ্যামা, বিনোদিনী, সুকুমারীদত্ত (গোলাপ সুন্দরী), তিনকড়িদাসী, তারাসুন্দরী, দুনিয়া (পূর্ববাংলায়)। কুসুম কুমারী এসে প্রথম নাচ পরিবেশন করেন এবং নাচ পরিচালনা করেন বাংলা মঞ্চনাটকে। তারাসুন্দরী সুলতানা রাজিয়ার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন।
কিন্তু অনেকেই যেটা জানেন না, তা হলো, ১৮৭৩ সালে নয়, ১৭৯৫ সালেই একজন বিদেশি পরিচালক বাঙালি নারীদের নিয়ে প্রথম মঞ্চনাটক পরিবেশন করেছিলেন। গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ তাঁর বেঙ্গলি থিয়েটারে ‘কাল্পনিক সংবদল’-এর জন্যে নারী চরিত্রে মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকে গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতিও আনতে হয়েছিল। তাঁর নাটকের জন্যে এই মেয়েদের সংগ্রহ করে এনেছিলেন গোলকনাথ দাস। কিন্তু কোথা থেকে তাঁদের জোগাড় করেছিলেন এই তথ্যটা তিনি দেন নি। খুব সম্ভবত কোনো পতিতালয় থেকে নয়, তাহলে রক্ষণশীলদের হাতে তাঁর রক্ষা থাকত না। তবে হতেও পারে, কোনো দূর-দূরান্তের নাম না-জানা পতিতালয় থেকে গোপনে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে কারও কারও ধারণা, কোনো লোকসংস্কৃতি দলের সদস্য হয়তো ছিলেন এই দুই অভিনেত্রী। সম্ভাব্য উৎস দলের তালিকায় মধ্যে থাকে গ্রামের ঝুমুর যাত্রা দল অথবা খোদ কলকাতার ঢপকীর্তনের দল। এই ধরনের লোকসংগীতের দলের মেয়েরা তখন বেশ সাবলীলভাবেই পুরুষদের সঙ্গে গান, নাচ করে এবং কথা বলে অভ্যস্ত ছিলেন। যেখান থেকেই তারা আসুক ‘কাল্পনিক সংবদল’-এর নায়িকা সুখময় ও সহচরী ভাগ্যবতীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাঁরা বাংলা থিয়েটারে একটা নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের আর কোথাও কখনো দেখা যায় নি, তাঁদের নামও কেউ আর শোনে নি।
এর পর মঞ্চ-থিয়েটারে মেয়েদের আবার স্বল্প সময়ের জন্যে আগমন ঘটেছিল ৪০ বছর পরে ১৮৩৫ সালে, যখন নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকটি প্রদর্শিত হয়। এই নাটকে অভিনেত্রীদের নামÑ রাধারাণী, জয়দুর্গা, রাজকুমারী ও বৌহরো ম্যাথরানী। এঁদের সকলকেই পতিতালয় থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, জানা গেল। এত সাবলীল তাঁদের অভিনয় যে সকলে অবাক হয়ে যায়। নবীনচন্দ্র বসুর পতিতা মেয়েদের জীবনকে আলোকিত করার এই চেষ্টার সরাসরি বিরোধিতা করে রক্ষণশীলরা। তখনকার সাধারণ বাঙালি মানসিকতায় থিয়েটারে নারীদের কোনো স্থান নেই। অন্তঃপুরের নারীদের বাইরে এসে মঞ্চে ওঠার প্রশ্নই আসে না। আর পতিতারা এলে তাদের সংস্পর্শে ভদ্দরলোকের থিয়েটার কলুষিত হয়ে যাবে। থিয়েটারপাগল অল্পবয়সী ভালো ঘরের ছেলেদের মাথা খাওয়া হবে। ফলে নবীন বসুর থিয়েটার বেশি দিন চলল না। থিয়েটারে অভিনেত্রী নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।
নবীনচন্দ্র বসুর সেই উদ্যোগের ৩৮ বছর পরে, ১৮৭৩ সালে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎ চন্দ্র ঘোষকে পরামর্শ দিলেন নারী চরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণ করার জন্যে। মাইকেলের নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হলো ১৮৭৩ সালে। তখনই মঞ্চে এলেন এলোকেশী, জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী ও শ্যামা। রক্ষণশীল সমাজ ক্ষেপে গেল। ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকায় নিন্দাবার্তা প্রকাশিত হলো : ‘সিমলার কতগুলি ভদ্রসন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া আর একটি থিয়েটার খুলিতেছে।... যে যেস্থানে পুরুষদের মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করতে হয়, সেই স্থানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়েমানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে—এই লোভে পড়িয়া তাঁহারা কতগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন।... মেয়েনটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টের হেতু হইবে।’
সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই ‘মন্দ’ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে সর্বসমক্ষে ভদ্রসন্তানদের অভিনয় করা সমর্থন করেন নি। বিস্ময়ের ব্যাপার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই বিতর্কে বেঙ্গল থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু এবার বেঙ্গল থিয়েটার রক্ষণশীলদের ভয়ে পিছিয়ে যায় নি। ইতিমধ্যে গণিকালয় থেকে আসা এক ঝাঁক তরুণীর নাট্যপ্রতিভার গুণে মঞ্চনাটক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছে। ততদিনে সেই কালের সেরা অভিনেত্রী বিনোদিনী মাত্র বারো বছর বয়সে গণিকালয় থেকে অভিনয় জগতে আসেন এবং পরবর্তী ১২ বছরে ৫০টি নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। বিনোদিনীর অভিনয় ক্ষমতায় অভিভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধায়সহ বহু জ্ঞানী-গুণীজন। নাট্যজগতের মহারথী গিরীশ চন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন। বিনোদিনী তাঁকে গুরু ও দেবতা বলে মানতেন। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার টাকা জোগাড় করতে বিনোদিনী জীবনের কঠিনতম স্বার্থত্যাগ করেন। নতুন থিয়েটারের নির্মাণের অর্থ জোগাতে তিনি নিজ প্রেমিককে, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন (যে প্রেমিক-ও তাকে খুবই ভালোবাসতেন), তাকে ছেড়ে আরেকজনের একক রক্ষিতা হতে রাজি হন, যে ‘আরেকজন’ বিনোদিনীকে এককভাবে পাওয়ার বিনিময়ে স্টার মঞ্চ তৈরির পুরো অর্থ জোগান দিতে রাজি হয়েছিলেন। প্রথমে কথা হয়েছিল, বিনোদিনীও আশা করেছিলেন, এই নতুন থিয়েটার তাঁর নামে বা তাঁর নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে হবে যেহেতু চরম স্বার্থ ত্যাগের বিনিময়ে বিনোদিনী এই থিয়েটার নির্মাণ করেছেন। প্রথম প্রথম উদ্যোক্তারা সেই মতে সায় দিলেও যখন দলিলপত্র, রেজিস্ট্রেশন সব শেষ হলো, দেখা গেল নামকরণ হয়েছে ‘স্টার থিয়েটার’। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে এইসব আশাভঙ্গ ও প্রতারণার কথা সবই খোলাখুলি লিখে গেছেন এবং বলেছেন তাঁর মতো পতিতা, বারবনিতারা ভদ্দরলোকের কাছ থেকে এরকম ব্যবহারই পেয়ে থাকে বরাবর।
বিনোদিনী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী (সুকুমারীর চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করার জন্যে পরবরর্তীকালে যিনি সুকুমারী নামেই অধিক পরিচিত হন) ও সমসাময়িক মেয়েরা মঞ্চে নারীর অভিনয়ের দুয়ার খুলে দেন।
এঁরা যখন প্রথমবারের মতো মঞ্চে অভিনয় করতে আসেন, প্রকাশ্য থিয়েটার মঞ্চে তখন অন্তঃপুরের নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় না করলেও প্রগতিশীল ঠাকুর পরিবারে মেয়ে ও বউরা কিন্তু পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সেই সময়েই ঘরোয়া পরিবেশে, পারিবারিক আবহে একসঙ্গে অভিনয় করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে জোঁড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে নারী-পুরুষ একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। নারীদের মধ্যে বিশেষ করে কাদম্বরী দেবী, মৃণালিনী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রমুখ। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে ঠাকুরবাড়িতে পারিবারিকভাবে নাটক মঞ্চায়ন হতো। তাতে পরিবারের সদস্যরা অভিনয় করতেন এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা ছিলেন সেই নাটকের দর্শক। এইসব নাটকে নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অগ্রজদের লেখা নাটকে অভিনয় করতে করতেই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রতিভা ছিল অসাধারণ। ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব নাটকের প্রায় সবগুলোতেই তিনি অভিনয় করেছেন। নিজের লেখা ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’, ‘বিসর্জন’, ‘রাজা-রানী’, ‘চিরকুমার সভা’য় যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি অভিনয় করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা নাটকেও। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিকাব্য ‘বাল্মিকীপ্রতিভা’ মঞ্চস্থ হয় ১৮৮১ সালে। এতে বাল্মিকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয় করেন আরও আগে, ১৮৭৭ সালে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকে। নাটকে তিনি অলীকবাবুর ভূমিকায় মঞ্চে উঠেছিলেন। তখন তার বয়স ১৬ বছর। তার অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।’ রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নারী ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কাদম্বরী দেবী। ফলে দেখাই যাচ্ছে, যখন রঙ্গমঞ্চে নারী শিল্পীদের অভিনয় করার অনুমতি মেলে কলকাতায় ১৮৭৩ সালে যখন বিনোদিনী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরীরা মঞ্চনাটকে প্রবেশ করে, প্রায় একই সময়ে ঠাকুর বাড়ির আঙিনাতে নারী-পুরুষ একত্রে নেচে, গেয়ে, সংলাপ বলে পূর্ণ নাটক করে গেছেন।
অনাথ শিশু ও বিধবাদের জন্যে স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত ‘সখী সমিতি’-র মতো সংগঠন পরিচালনা কেবলমাত্র সদস্যদের চাঁদায় সম্ভব নয় অনুভব করে স্বর্ণকুমারী দেবী বেথুন কলেজে একটি বার্ষিক মেলার আয়োজন করেন। এই মেলায় ঢাকা ও শান্তিপুরের শাড়ি, কৃষ্ণনগর ও বীরভূমের হস্তশিল্প এবং বহির্বঙ্গের কাশ্মীর, মোরাদাবাদ, বারানসি, আগ্রা, জয়পুর ও বোম্বাইয়ের হস্তশিল্প প্রদর্শিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একদিকে ‘সখী সমিতি’র জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে, অন্যদিকে ভারতের দেশজ পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে, যা স্বদেশী আন্দোলনের জন্যে অপরিহার্য। সেই যুগে এই মেলা কলকাতার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর [১৫ পৌষ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ], কলকাতার বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে এ মেলা বসে। ‘সখী সমিতি’ নামটি রবীন্দ্রনাথের-ই দেওয়া। দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠ কন্যা সরলা রায় (দাশ), যিনি তাঁর কর্মজীবন নারী-কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন সখী সমিতির অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন একটি গীতিনাট্য লিখে দেন। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ সালে ২৭ বছর বয়সে ‘মায়ার খেলা’ নৃত্যনাট্যটি লিখেছিলেন। কেবল নারী অভিনীত ‘মায়ার খেলা’ বেথুন কলেজে মঞ্চস্থ হয়েছিল ‘সখী সমিতি’র জন্যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ‘মায়ার খেলা’ গীতিনাট্যটি রচনা করেন ইউরোপীয় অপেরার ঢঙে। মূলত নৃত্যকেন্দ্রিক। পরে অবশ্য আরও অনেকগুলো গান সংযোজন করেন তিনি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নাট্য নয়, গীতই মুখ্য হয়ে দেখা দেয় ‘মায়ার খেলা’তে যখন তিনি তা পরিবর্তন করে বর্তমানের সংস্করণে উত্তরণ করেন। প্রথম সংস্করণ ‘মায়ার খেলা’ উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হইল এবং তাঁহাকেই সাদর উপহারস্বরূপে সমর্পণ করিলাম।’
চলচ্চিত্র : ঢাকার সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র (মূক) ‘দ্য লাস্ট কিস’-এর নায়িকা ছিলেন লোলিতা। তাঁকে বাদামতলীর নিষিদ্ধ পল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়। তাঁর আসল নাম ছিল বুড়ি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। ছবির কাজ শেষে বুড়ি আবার পুরোনো পেশায় ফিরে যান। এর বেশি কিছু লোলিতার সম্বন্ধে জানা যায় না। দ্যা লাস্ট কিসে’র সহ-নায়িকা চারুবালাকে আনা হয় কুমারটুলি পতিতালয় থেকে। জিন্দাবাহার লেন থেকে আনা হয় তখনকার দিনের ঢাকার সবচেয়ে খ্যাতিমান বাইজি দেবী বাইজি বা দেববালাকে। হরিমতি বাইজিও এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সিনেমায় তাঁদের অভিনয় করানোর জন্য অনেক পত্র-পত্রিকায় জোর প্রতিবাদ জানানো হয়। এঁরা সকলেই এই চলচ্চিত্রে অভিনয় শেষে আবার নিজেদের মূল পেশায় ফিরে যান।
পরবর্তীকালে কাননবালা বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে আবির্ভূত হন এক কিংবদন্তিসম নায়িকা হিসেবে। বারবনিতার কন্যা এবং সেখানেই বড় হওয়া, এঁদেরই একজন কাননবালা তাঁর অপরূপ রূপ, আশ্চর্য অভিনয়ক্ষমতা ও সংগীতে সমান পারদর্শিতা নিয়ে মঞ্চনাটকে অভিনয় শুরু করলেও সবাক চলচ্চিত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আরও পরে, পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে, এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আগত অপরূপা সুন্দরী ও অদ্বিতীয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন ব্যতিত বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে আজ পর্যন্ত কাননবালার চেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা সম্ভবত আর নেই। চলচ্চিত্রে সুচিত্রা সেনের আগমন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই প্রথম কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বউ চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করলেন। এর পর তাঁর পথ ধরে একে একে অনেকেই গর্বের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।
গওহরজানের খালা জদ্দান সেকালে কলকাতা ও ঢাকাসহ ভারতের সর্বত্র একজন অত্যন্ত নামকরা বাইজি বলে পরিচিত ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। জদ্দানের শেষ স্বামী উত্তম চাঁদ মোহন। জদ্দানকে বিয়ে করার জন্যে চাঁদ মোহন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মাওলান আবুল কালাম আজাদ এ বিয়েতে সাক্ষী হন। মুসলমান হয়ে মোহন নিজের নাম রাখেন আবদুর রশীদ। বিয়ের পর জদ্দান তাঁর বাইজি পেশা ছেড়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে আসেন। রশীদ আর জদ্দানের ঘরে জন্ম নেন নার্গিস। এই সেই নার্গিস ভারতের চিত্রজগতে যিনি শুধু চিরভাস্বর এক নায়িকা নন, কেবল অভিনেতা সুনীল দত্তের স্ত্রী ও আরেক অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের মা নন, জগতজোড়া যাঁর খ্যাতি, যিনি কিংবদন্তিসম জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা পেয়েছেন। ফলে দেখাই যাচ্ছে, সে যুগের এইসব বাইজিরাই মঞ্চে ও ছায়াছবিতে প্রথমে অভিনয় করতে এগিয়ে এসে শিক্ষিত নারীদের চলচ্চিত্রে আসার পথ খুলে দিয়েছিলেন। আরেকভাবে বলা যায় বাইজিদের ঘর থেকেই মেয়েরা প্রথম বেরিয়ে আসেন মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে।
সাহিত্য : এই গুণী বারবনিতা-বাইজি নারীরা নিজেরা সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন শুধু তাই নয়, তাঁরা উনিশ শতকের এবং বিংশ শতকের বড় বড় সব লেখক, কবি, নাট্যকারদের সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। সুকুমারী দত্ত নিজে নাটক লিখেছেন। তিনিই প্রথম নারী নাট্যকার, নাটকের নাম ‘অপূর্ব সতী। ১৮৭৫ সালে গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটার এটা মঞ্চস্থ করে প্রশংসা পেয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী নাটক ও সংগীত পরিবেশন ছাড়াও ‘আমার কথা’ বলে আত্মজীবনী ও ‘কনক’ এবং ‘বাসনা’ বলে দু’টি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন।
শাস্ত্রীয় সংগীতে ও নৃত্যে পারদর্শীতার জন্যে অনেক লেখক-শিল্পী এসে ভিড় করতেন বিখাত বাইজিদের দরজায়। তাঁরা তাঁদের গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ঠাকুরবাড়ির বেশ কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে এই জগতের খ্যাতনামা কয়েকজন বাইজি-বারবনিতার বিশেষ সখ্যতা ছিল।
বিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকদের রচনায়, গল্প-উপন্যাস-কবিতায়, মঞ্চস্থ নাটকে একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বারবনিতা-বাইজি চরিত্র অথবা এই সমাজ বা সংস্কৃতির খণ্ডাংশ। ঘুরেফিরে এই নারী চরিত্রগুলো খুব সহমর্মিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে সাহিত্যে। গৃহবধূ ও বারবনিতা যুক্তভাবে ঘরে-বাইরে পুরুষের মন জুগিয়ে একটি পূর্ণ নারীর আস্বাদ দিতে সমর্থ হতো। গণিকা-কন্যারা এসেছে সমাজে নির্যাতিতা অথবা মানব দরদি হিসেবে। তাঁদের প্রতি কটাক্ষ অথবা ঘৃণা কমই দেখা গিয়েছে। বারবনিতা-বাইজিদের চরিত্রগুলো সাধারণত অতি দরদ ও মমতা দিয়ে উপস্থাপন করতেন এই আধুনিকমনস্ক লেখকেরা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের ‘বাসবদত্তা’ কবিতা, ‘মানভঞ্জন’ গল্প (১৮৯৬), শেকসপিয়ার-এর ‘কমেডি অভ এররস্’ অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেখা ‘ভ্রান্তিবিলাস’, মাইকেল মধুসূদন দত্তের’ ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ‘সধবার একাদশী’ (১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘পরপারে’ (১৯১২) নাটক, শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ ও ‘শ্রীকান্ত’, ‘আঁধারে আলো’ (১৯১৫), শুভদা (১৯৩৮), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬)-এর ‘পিয়ারী’ উপন্যাস, রিজিয়া রহমানের উপন্যাস ‘রক্তের অক্ষর’, আল মাহমুদের উপন্যাস, ‘জলবেশ্যা’, মঈনুল আহসান সাবেরের ‘দুই বোন’, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘মধ্যাহ্ন’ ইত্যাদি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে গুরু পাপ জ্ঞানে এর থেকে পরিত্রাণে কেবল প্রায়শ্চিত্তের কথাই ভেবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) ও ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫)-এ গণিকা চরিত্র রয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বারাঙ্গনা কন্যাদের প্রতি সহমর্মিতায় ‘বারাঙ্গনা’ কবিতাটি লিখেছেন যা ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগ্রন্থে (১৯২৫) অন্তর্ভুক্ত। কবি লিখেছেন, ‘কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,/অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।’
বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাইজি-বারবনিতার অবদান আজ আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলা গান, নাচ, নাটক ও সিনেমার প্রাথমিক রূপ দিয়েছিল কলকাতা ও ঢাকার বারবনিতারাই। তারাই ছিলেন বর্তমানে প্রচলিত বাংলা গান, থিয়েটার ও সিনেমাশিল্পের জন্মদাত্রী, শাস্ত্রীয় সংগীতকে (সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতকেও) সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বড় বাহন। ফলে দেখা যায় সংগীতে, নাচে, মঞ্চ বা চলচ্চিত্রে অভিনয়ে, সাহিত্য রচনায় আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই নারীরা রয়েছে সক্রিয়, পুরুষের পাশাপাশি। পুরুষ তার পিতৃত্বের পবিত্রতায় সংশয়হীন হতে এবং স্ত্রীর একগামিতা (সতীত্ব) রক্ষার্থে স্ত্রীকে ঘরবন্দি করেছে কুলনারী হিসেবে। সেই সঙ্গে নিজের বিনোদন ও মননের চর্চা করতে ঘরের বাইরে রেখেছে আরেক ধরনের নারী মন্দ-নারী— কুলটা বা বারবনিতা কিংবা বাইজি বলে যারা সমাজে পরিচিত। রাত্রির অন্ধকারটুকু ছাড়া এই অর্থবান পুরুষেরা পড়ে থাকতেন বাইরের জগতে এই নারীদের দরবারেই। শিক্ষায়-দীক্ষায়-নাচেগানে-কবিতা-রসিকতায় এই শেষোক্ত নারীরা পুরুষের সাংস্কৃতিক মনকে, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করতে সমর্থ ছিল। ফলে তাঁদের সঙ্গ-কামনায় উন্মুখ হয়ে থাকত পুরুষকুল। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের সাজানো এই সামাজিক বিভাজনের কাঠামোতে পুরুষ-সম্রাট নির্বিচারে ভোগ অবাধ সুখ— ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই। পুরুষের খেলার পুতুল নারীও তার নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে থেকে তাঁর জন্যে নির্ধারিত ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন বরাবর। নিজদের সকল বঞ্চনা, সকল বিষাদ, সকল বৈষম্যের জ্বালা ভুলে বা গোপন করে পুরুষদের অকাতরে সেবা ও আনন্দ বিতরণ করে গিয়েছেন। বিশেষ করে বাইজি মেয়েদের হাসি, গান আর আনন্দের পেছনে প্রায় সব সময়েই লুকিয়ে থাকত অনেক ব্যক্তিগত কষ্ট, কান্না, বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ প্রেম, প্রতারণা এবং ঘর-সংসার-সন্তান কামনায় হোঁচট খেতে খেতে তারা অনেকেই যে ক্রমাগত অসীম মনোযন্ত্রণার শিকার হতেন, সে খবর কেউ রাখত না। এদিকে ঘরে আবদ্ধ কুলনারীও কেবল স্বামীর দেহরঞ্জন করে, সন্তানের জন্ম দিয়ে আর তাঁদের প্রতিপালন করতে করতে নিজেদের মননের চর্চার অবকাশ বা সুযোগ না পেয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় হাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তবু তাঁরা চেষ্টা করছিলেন তাঁদের স্ব স্ব জায়গায় থেকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যেতে। কিন্তু জগতজুড়ে এবং উপমহাদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল যেমন পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর দৈশিক ও ভৌগোলিক মানচিত্রের বদল, কমিউনিজমের উত্থান ও প্রভাব, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, জমিদারি-প্রথার বিলুপ্তি, নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন, জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি আবিষ্কার ইত্যাদি পুরুষের সেই আরামদায়ক ও নিশ্চিন্তের মজবুত আসনটিকে নড়বড়ে করে দিল একেবারে গোড়া থেকে। সভ্যতায় নারীর অবদানকে যত-ই অস্বীকার করার চেষ্টা করা হোক না কেন, প্রান্তিকী পর্যায়ে আটকে পড়া নারীও তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে শুরু করে। কখনো নারী নিজেই এগিয়ে যান সংস্কৃতির কোনো শাখার হাত ধরে, কখনো পুরুষের অগ্রসরকে এগিয়ে দেন নারী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। অন্তঃপুরে নিক্ষেপিত নারী আবার ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন পৃথিবীর মুক্ত আলোতে উচ্চতর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। যতদিন এই তথাকথিত ‘কুলনারী’ বা ‘সতীনারী’ রা পূর্ণ বন্দি ছিলেন অন্তঃপুরে, বাইরে অবস্থানরত তথাকথিত ‘মন্দনারী’ বা ‘বারবনিতারা’ সভ্যতার হাল ধরে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও চিন্তাকে বদ্ধ জলাশয়ে আটকে থাকতে না দিয়ে তাদের সমৃদ্ধির জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। বর্তমানে গৃহবধূ ও সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীদের সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য বা অভিনয়কলায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আগেকার দিনের কঠিন সামাজিক বাধা অনেকটাই দূর হয়ে গেছে। ফলে গণিকালয়ের গণিকারা আজ তাদের পূর্ব মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি হারিয়ে কেবল পুরুষদের দেহ ও মনোরঞ্জনের জন্যে নিজের যৌবন, চপলতা আর রূপকেই মূলধন করে নিষিদ্ধপল্লীতে কোনো মতে জীবনধারণ করে চলেছে।
শিক্ষার প্রসার, নারী-বান্ধব আইনের সংযোজন, সৃজনশীলতা ও চিন্তার উন্মেষ এবং বিকাশে ইংরেজদের সহযোগিতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায়ের মতো মানুষদের, বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের, নারী-কল্যাণ ও নারীর অবস্থা উন্নয়নে নানাবিধ সামাজিক সংস্কারসাধন, শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতীর পরিশীলিত সাহিত্য ও শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের মতো গীতিকার/সুরকারের আবির্ভাব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত জনগোষ্ঠির নতুন উন্মাদনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া, এবং নিজ দেশ-সংস্কৃতি-স্বদেশী দ্রব্যের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফেরানো, ইত্যাদি বহু কারণে ধীরে ধীরে রঙমহলে বন্দি বাংলার সংস্কৃতি ছাড়া পেয়ে আবার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের গৃহের অভ্যন্তরে অথবা খোলা অবারিত মঞ্চে জায়গা করে নিতে শুরু করে। আবির্ভূত হন রানী চন্দ, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, ফিরোজা বেগম, অমলা দাশ, সাহানা দেবী, তৃপ্তি মিত্র, সরলা দেবী চৌধুরাণী, সুচিত্রা সেন, নভেরা, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মতো শিল্পী-মহারথীরা। আমরা দেখতে পাই। আরতি সাহার মতো দৃঢ় অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাশীল নারীদের যারা বহু চেষ্টা করে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হন, দেখি শিপ্রা ও নিশাত মজুমদারের মতো মেয়েদের যারা দুরূহ এভারেস্ট জয় করেন। পাই রানী হামিদের মতো শান্ত মাথার বিচক্ষণ দাবাড়ু।
নিচে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাংলার বিখ্যাত কিছু নারীর নাম উদ্ধৃত করা হলো, যাঁরা বাংলার সংস্কৃতির জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন :
১. আঙুরবালা (১৯০৬-১৯৮৪)
২. আরতি সাহা (গুপ্ত) (১৯৩৩-১৯৯৪)
৩. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০)
৪. ইন্দুবালা (১৮৯৯-১৯৯৪)
৫. কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০)
৬. কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)
৭. কাদম্বরী দেবী (১৮৫৯-৮৪)
৮. কানন দেবী (১৯১৫-১৯৯২)
৯. কুসুমকুমারী (১৮৭৬-১৯৪৮)
১০. গওহরজান (১৮৭০-১৯৩০)
১১. গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) (১৯/২০ শতক)
১২. তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-১৯৮৯)
১৩. নভেরা আহমেদ (১৯৩৯-২০১৫)
১৪. ফিরোজা বেগম (১৯৩০-২০১৪)
১৫. বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪২)
১৬. রওশন জামিল (১৯৩১-২০০২)
১৭. রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭)
১৮. রানী রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১)
১৯. সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)
২০. সাহানা দেবী (১৮৯৭-১৯৯০)
২১. সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১)
২২. সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪)
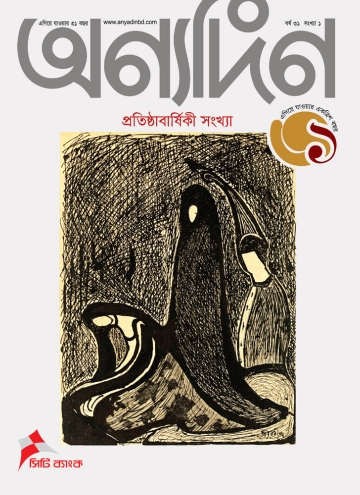










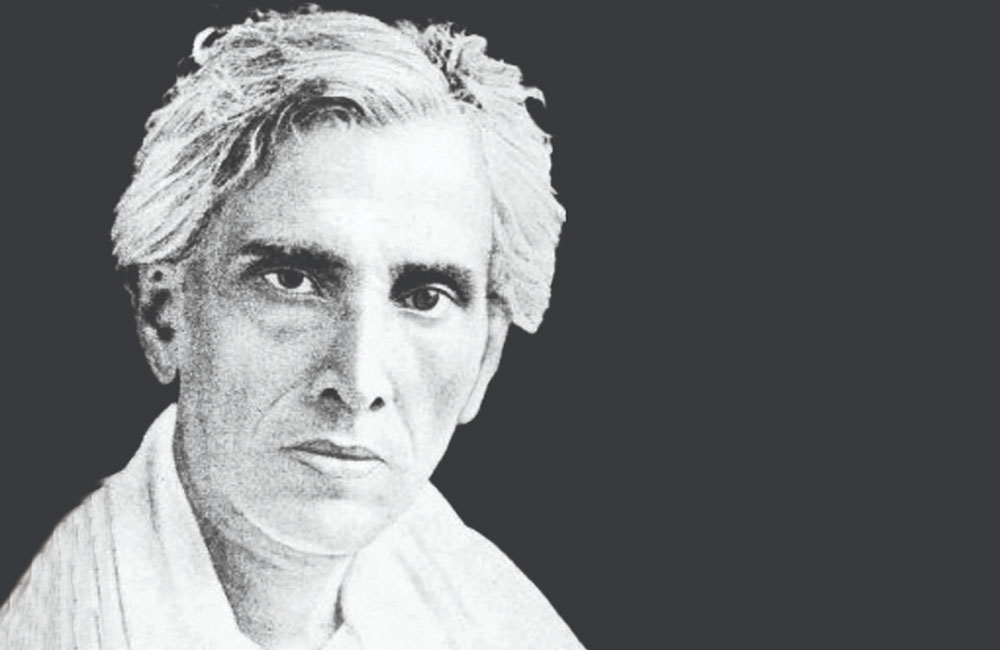



Leave a Reply
Your identity will not be published.