[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
৫১) ফজিলাতুন্নেসা রেণু (১৯৩০-১৯৭৫) : বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমানের সহধর্মিণী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক সংকটময় সময়ে যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, সেসব ক্রান্তিকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে দলের নেতাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বেগম মুজিব। তিনি দলের নেতাকর্মীদের সব সময় খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের মধ্যে যখন যার বিশেষ প্রয়োজন, তখন তিনি তার বাজার ও চিকিৎসার টাকাও দিতেন নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। বেগম ফজিলাতুন্নেসা পাকিস্তানি শাসকদের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধু ও দলের নেতাকর্মীদের মাঝে সংবাদ বিনিময় করতেন। বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি শাসকদের অবহেলা ও নির্যাতন সহ্য করতে পারতেন না বলে বঙ্গমাতা কখনো করাচি বা পাকিস্তানের কোথাও যান নি। শেখ হাসিনার মতে, ‘আমার মায়ের মতো এমন সঙ্গ না পেলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো ভিন্নরকম হতে পারত’। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁর স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, দেবর, তিন পুত্র ও দুই পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি জীবন হারান রাজধানীর ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে।
বেগম ফজিলাতুন্নেসা রেণু ছিলেন একজন নিরহংকার, নির্লোভ, ত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, প্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা নারী। আদর্শ বধূ, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের রাজনীতিতে ও গৃহাঙ্গনে প্রেরণাদায়িনী ও শক্তিদায়িনী। শেখ মুজিবের লিখিত গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ রচনায় প্রেরণাদায়িনীও ছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা রেণু। ১৯৬৬-১৯৬৯ সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাবস্থায় শেখ মুজিব আত্মজীবনী লিখেছেন। তার উপক্রমণিকাতে আছে, ‘আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, বসেই তো আছ, লেখো তোমার জীবনকাহিনি।’ লেখার ব্যাপারে শেখ মুজিব দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু যেদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে লেখার জন্য কয়েকটি খাতা দিয়ে গেলেন এবং যখন হাতে একটি মোক্ষম সুযোগ পেলেন, তখন থেকেই লিখতে বসে গেলেন। স্মৃতিনির্ভর এ বইটিতে তিনি বহু প্রসঙ্গের অবতারণাসহ বেশ অনেক জায়গায় তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে লিখেছেন।
স্ত্রীকে শুধু তিনি বই লেখার প্রেরণাদায়িনী হিসেবে তুলে আনেন নি, তাঁকে তুলে ধরেছেন একজন স্বামীঅন্তঃপ্রাণ স্ত্রী হিসেবে, একজন স্নেহময়ী মা হিসেবে, একজন স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেবরের প্রতি নিবেদিত ও শ্রদ্ধাবান গৃহবধূ হিসেবে, একজন কষ্টসহিষ্ণু, সর্বংসহা সংবেদনশীল নারী হিসেবে। আত্মজীবনীতে মুজিব লিখেছেন, ‘আমার স্ত্রীর ডাক নাম রেণু।’ মুজিব ও তার স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান প্রায় ১০ বছর। তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স তের বছর হতে পারে।’ এই বাল্যবিবাহের কারণ হিসেবে তিন বছর বয়সে রেণু’র পিতৃবিয়োগ ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের কথা এসেছে। শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘রেণুর দাদা আমার দাদার চাচাত ভাই। রেণুর বাবা মানে আমার শ্বশুর ও চাচা তার বাবার সামনেই মারা যান। মুসলিম আইন অনুয়ায়ী রেণু তার সম্পত্তি পায় না। রেণুর কোনো চাচা না থাকায় তার দাদা (শেখ কাশেম) নাতনি ফজিলাতুন্নেসা ও তার বোন জিন্নাতুন্নেসার নামে সব সম্পত্তি লিখে দেন।
‘রেণুর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, ‘তোমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার এই নাতনির বিবাহ দিতে হবে।’ রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা; মুরব্বির হুকুম মানার জন্য রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। রেণু তখন কিছু বুঝত না, কেননা তাঁর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে।’
রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান আর দাদা মারা যান সাত বছর বয়সে। তারপর রেণু শেখ মুজিবের মা’র কাছে চলে আসেন এবং তার ননদ, দেবরদের সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির অপত্যস্নেহে বড় হতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে তাঁদের বিয়ে হলেও শেখ মুজিবের লেখা থেকে জানা যায়, তাঁদের ফুলসজ্জা হয়েছিল ১৯৪২ সালে। তিনি পড়াশোনা ও রাজনীতির আংশিক খরচ এমনকি সিগারেট খাওয়ার টাকাও স্ত্রীর কাছ থেকে নিতেন। টাকা প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, “আব্বা, মা, ভাই-বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। ‘অমঙ্গল অশ্রুজল’ বোধ হয় অনেক কষ্টে বন্ধ রেখেছে। তবে এবারে একটু অনুযোগের স্বরে বললেন, একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না, এবার কলেজ ছুটি হলে বাড়ি এসো।” শুধু টাকা-পয়সাই দেওয়াই নয়, সশরীরে বিএ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়ে তিনি স্বামীকে প্রণোদনা দিয়েছেন। শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘রেণু কলকাতায় এসে হাজির, কেননা রেণুর ধারণা পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।’
মুজিব ছিলেন মনে-প্রাণে রাজনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার আগে বেশ কয়েকবার জেলে গেছেন। কিন্তু তাঁর পত্নী তাঁকে কখনো রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বলেন নি। তিনি বলতেন, রাজনীতি করো আপত্তি নেই, কিন্তু পড়াশোনাটি করবে। তারপরও যখন রাজনীতির কারণে সঠিকার্থে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে আমরণ অনশন করছিলেন তখন রেণু বললেন, ‘জেলে থাকো আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো।’ পৃথিবীতে যে নারীর কেউ নেই, ছোটবেলায় মা-বাবা-দাদা মারা গেছেন, তার পক্ষে স্বামীকে কণ্টক, রাজনীতির ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়া কঠিন ছিল। সে কঠিন কাজটি করেছিলেন একজন অবলা, অনাথ, স্বল্পশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, গ্রামীণ মহিলা।
১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে খবরটি গভীর রাতের আগে স্ত্রীকে জানাতে পারেন নি। কেননা তিনি ছিলেন বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা দমনে ব্যস্ত। ইনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘রাত চার ঘটিকায় বাড়িতে পৌঁছালাম, শপথ নেওয়ার পরে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়িতে আসতে পারি নাই। আর দিনভর কিছু পেটেও পড়ে নি। দেখি রেণু চুপটি করে না খেয়ে বসে আছে, আমার জন্য।’ ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো মন্ত্রী হন, তবে তার মন্ত্রিত্বের আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। ৯২(ক) ধারা জারি হলে তিনি লিখেছেন, ‘বাসায় এসে দেখলাম, রেণু এখনো ভালো করে সংসার পাততে পারে নাই। তাকে বললাম, আর বোধহয় দরকার হবে না। কারণ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিবে, আর আমাকেও গ্রেফতার করবে। ঢাকায় কোথায় থাকবা, বোধহয় বাড়িই চলে যেতে হবে। আমার কাছে থাকবা বলে এসেছিলা, ঢাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ হবে, তা বোধহয় হলো না। নিজের হাতের টাকা পয়সাগুলোও খরচ করে ফেলেছ।’
তারপর বাড়িতে পুলিশ এসেছে। এর পরে আবার জেলের প্রস্তুতি। রেণু তার স্বামীর কাপড়চোপড় আমৃত্যু সুন্দর করে গুছিয়ে দিতেন। শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘রেণু আমাকে খেতে বলল। রেণু আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দিল এবং কাঁদতে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রেণুকে বললাম, তোমাকে কী বলে যাব, যা ভালো বোঝ করো।’ নিজের স্ত্রীর সক্ষমতা ও কর্মকৌশলতার প্রতি কতটা দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে সব দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে হাসিমুখে জেলে যেতে পারতেন শেখ মুজিব।
স্বামী-সন্তানের প্রতি যেমন, তেমনি শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতিও রেণুর ছিল অনন্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। তাঁদের অসুখবিসুখে কাছে থাকা ছিল তাঁর রুটিন কাজ। সেদিনের একটি ঘটনা শেখ মুজিবের লেখায় এসেছে। তিনি তখন জেলে, তাঁর বাবা অসুস্থ। শ্বশুরের অসুস্থতার খবর টেলিগ্রাম মারফত পেয়ে রেণু বাড়িতে ছোটেন। তবে যাওয়ার কালে টেলিগ্রামের কপিটি সংযুক্ত করে শেখ মুজিবের মুক্তির আবেদন করে যান, যার ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে মুক্তিও দেওয়া হলো। রেণু যে শুধু তাঁর প্রতি বা তাঁর নিকটজনের প্রতি সংবেদনশীল ও মানবিক ছিলেন তা নয়, তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতিও অতিশয় সংবেদনশীল ছিলেন, তার প্রমাণও নেতার লেখায় মেলে। তিনি মাদারীপুর বোনের বাড়ি যাচ্ছিলেন—দুজন শুভাকাক্সক্ষী সহযাত্রী সঙ্গে ছিলেন। শীতের রাতে তাদের কোনো চাদর না থাকায় কষ্টের অন্ত ছিল না। রেণু তার নিজের গায়ের চাদর খুলে তাদের দিয়েছিলেন।
৫২) ফিরোজা বেগম (১৯৩০-২০১৪) : ফিরোজা বেগম প্রথিতযশা নজরুলসংগীত শিল্পী। সমস্ত ভারত উপমহাদেশে তিনি নজরুলসংগীতের জন্য বিখ্যাত এবং অমর হয়ে আছেন। ফিরোজা বেগমের জন্ম ১৯৩০ সালের ২৮ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলার রাতইল ঘোনাপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে। তাঁর বাবার নাম খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল এবং মায়ের নাম বেগম কওকাবুন্নেসা। শিশুকালেই তাঁর সংগীতের প্রতি অনুরাগ জন্মে। ১৯৫৪ সাল থেকে কলকাতায় বসবাস করেন। ১৯৫৫ সালে নজরুলের সহচর বিখ্যাত সুরকার, গায়ক ও গীতিকার কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নজরুল ইসলামের অনেক গানে কমল দাসগুপ্ত সুরারোপ করেন। ১৯৬৭ সালে ফিরোজা বেগম সপরিবারে ঢাকায় ফিরে আসেন। এ দম্পতির তিন সন্তান : তাহসিন, হামিন ও শাফিন। হামিন ও শাফিন দুজনেই রকব্যান্ড দল মাইলসের সদস্য। কমল দাশগুপ্ত ২০ জুলাই, ১৯৭৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।
১৯৪০-এর দশকে ফিরোজা বেগম সংগীতভুবনে পদার্পণ করেন। অতি অল্প বয়সে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান করেন। ১৯৪২ সালে ১২ বছর বয়সে বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি থেকে ৭৮ আরপিএম ডিস্কে তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় ইসলামি গান নিয়ে। এর কিছুদিন পর কমল দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে একটি উর্দু গানের রেকর্ড হয়। দশ বছর বয়েস ফিরোজা বেগম কাজী নজরুলের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে তালিম গ্রহণ করেন। নজরুলের গান নিয়ে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৪৯ সালে। কাজী নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর ফিরোজা বেগম নজরুলসংগীতের শুদ্ধস্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি প্রায় চার শ’ একক সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। নজরুলসংগীত ছাড়াও তিনি আধুনিক গান, গজল, কাওয়ালি, ভজন, হামদ ও নাতসহ বিভিন্ন ধরনের সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন।
১৯৭২ সালে কলকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন-মঞ্চে কমল দাশগুপ্তের ছাত্রী ও সহধর্মিণী হিসেবে তিনিই ছিলেন মুখ্য শিল্পী। কমল-ফিরোজার দ্বৈতসংগীত সকল শ্রোতা-দর্শককে বিমুগ্ধ করে। জীবনকালে বহু সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন। তার মধ্যে স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র পুরস্কার, সত্যজিৎ রায় পুরস্কার, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি স্বর্ণপদক, সেরা নজরুল সংগীতশিল্পী পুরস্কার (একাধিকবার), নজরুল আকাদেমি পদক, চুরুলিয়া স্বর্ণপদক উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট পান।
এ ছাড়াও জাপানের অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিবিএস থেকে গোল্ড ডিস্ক, ২০১১ সালে মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার অর্জন করেন। ১২ এপ্রিল ২০১২ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ‘বঙ্গ সম্মান’ পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কিডনির জটিলতায় মৃত্যুবরণ করেন।
৫৩) বদরুন্নেসা আহমেদ (১৯২৭-১৯৭৪) : জন্ম কলকাতায়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল ও লেডি ব্রেবোর্নে পড়াশোনা করেন। দেশভাগের পর বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। রাজপথ থেকে ধ্বনিত এখানকার কর্মঠ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের আহ্বানে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও এমএড করেন।
বদরুন্নেসা আহমেদের স্বামী ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম সেক্রেটারি নুরুদ্দীন আহমেদ। রাজনীতি ছাড়াও নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদরুন্নেসা কলেজ তার সম্মানার্থেই নামকরণ হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদে প্রথম দুই নারী মন্ত্রীর অন্যতম বদরুন্নেসা আহমেদ। তিনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৯ সালে সমাজসেবার জন্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানকর বেসামরিক স্বীকৃতি ‘স্বাধীনতা পদক’ পুরস্কারে ভূষিত হন (মরণোত্তর) সমাজসেবার জন্য। দেশের রাজনীতি ও নারী আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ভাষাআন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সরব উপস্থিতি ভুলবার নয়।
৫৪) বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪) : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নি উর্মিলা দেবীর পূর্ণ সহযোগিতা ছিল দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগে। বিক্রমপুরের মেয়ে বাসন্তী দেবীর ছিল অসামান্য সাহস। আইন অমান্য কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দেশবন্ধু কারাবন্দি হলে বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে উর্মিলা দেবী ও অন্যরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বড়বাজারে আইন অমান্য করে হরতাল ঘোষণা করায় উভয়েই গ্রেফতার হন। সারা বাংলায় সেই সময় নারীরা জাগরিত হতে থাকে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে। চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপস্থিতিতে বাসন্তী দেবী ‘বাঙলার কথা’ পত্রিকা পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি অসহযোগ সংগ্রামের অন্যতম নেত্রী ছিলেন।
৫৫) বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪২) : বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বনামখ্যাত দর্শকনন্দিত অভিনেত্রী। ঊনবিংশ শতকের বাংলা মঞ্চের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী। তাঁর ১২ বছরের স্বল্পকালীন অভিনয় জীবনের মধ্যেই তিনি মঞ্চাভিনয়ে বিপুল সফলতা অর্জন করেন।
তিনি একেবারে বারবনিতার পরিবেশ থেকে উঠে এসে ১২ বছর বয়সে বাংলা মঞ্চে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র মাসিক দশ টাকা বেতনে, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ‘শত্রুসংহার’ নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ছোট্ট ভূমিকায়। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করা শুরু হয় ১৮৭৩ সালে। বছরখানেকের মধ্যেই বিনোদিনী সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন । ১৮৭৭ সালে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তাঁকে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা ও মনোযোগে বিনোদিনীর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। নাচ-গানে পারদর্শী বিনোদিনী খুব তাড়াতাড়ি অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৭৪ থেকে একটানা ১২ বছর তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তিনি শেষবার অভিনয় করেন। সর্বমোট ৫০টি নাটকে তিনি ৬০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
পৌরাণিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক যে-কোনো রকমের চরিত্র রূপায়ণেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। একই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রেও সফলতার সঙ্গে অভিনয় করেন। যেমন মেঘনাদবধের সাতটি চরিত্রে বা দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা ও তিলোত্তমার মতো দুটি ভিন্নমুখী চরিত্রে। একই রজনীতে তিনি একাধিক নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন। পুরুষ চরিত্রের অভিনয়েও তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর অভিনীত পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চৈতন্য, প্রহ্লাদ প্রভৃতি। বিনোদিনী করুণরসাত্মক, ভক্তিরসাত্মক, গুরুভাবাপন্ন এবং হাস্যরসাত্মক যে-কোনো রকম চরিত্রের রূপায়ণে দক্ষ ছিলেন ।
সমাজের সকল স্তরের মানুষই তাঁর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন । তাঁর প্রশংসকদের তালিকায় ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ফাদার লাঁফো, এডুইন আরনল্ড, কর্নেল অলকট প্রমুখ। রামকৃষ্ণদেব তাঁর চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখে তাঁকে গ্রীনরুমে গিয়ে ‘চৈতন্য হোক’ বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে বিনোদিনীর মধ্যে দিয়ে সফলভাবে গড়ে উঠতে দেখেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর বহু প্রশংসা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ‘কি করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়’ শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনায় বিনোদিনীর জীবনচর্চাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সংবাদপত্রগুলো বিনোদিনীকে ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ স্টেজ, মুন অফ স্টার কোম্পানি, প্রাইমাডোনা অফ দি বেঙ্গলী স্টেজ আখ্যা দিয়েছিল।
১৮৮৩ সালের দিকে গিরিশ ঘোষ স্টার থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন। কারণ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ছিলেন একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরী, যিনি থিয়েটারকে ব্যবসা হিসেবেই দেখতেন। তাই তাঁর অধীনে কাজ করা গিরিশ ঘোষ এবং বিনোদিনী কারও পক্ষেই সহজ ছিল না। থিয়েটার গড়ে তোলার জন্য যে রকম টাকা-পয়সা দরকার ছিল, তা গিরিশ ঘোষের ছিল না। একজন ২০-২১ বছরের ব্যবসায়ী গুরমুখ রায় অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। থিয়েটারের চেয়ে তার বিনোদিনীর প্রতিই বেশি আকর্ষণ ছিল। গুরমুখ রায়ের রক্ষিতা হন বিনোদিনী। এই ঘটনায় তাঁর পূর্ববর্তী মালিক ধনী জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি লাঠিয়াল দিয়ে নতুন থিয়েটার ভেঙে দিতে চেষ্টা করেন। সেই ধনী জমিদার তলোয়ার হাতে বিনোদিনীর শোবার ঘরে প্রবেশ করে তাকে খুন করতে উদ্যত হন। কিন্তু বিনোদিনী উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সে যাত্রা বেঁচে যান। গুরমুখ রায় এর আগে নগদ ৫০,০০০ টাকায় বিনোদিনীকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর অভিনয় না করেন। বিনোদিনী সেই টাকার প্রতি লোভ না করে নাটকের জন্যে নতুন থিয়েটারের অর্থায়নের জন্যে গুরমুখ রায়ের কাছে অর্থ চাইলেন, বিনিময়ে তিনি তার রক্ষিতা হতে রাজি হলেন, যদিও তিনি তখন আরেকজন পুরুষকে সর্ব মনপ্রাণদেহ দিয়ে ভালোবাসতেন। থিয়েটারের জন্যে এমন স্বার্থত্যাগের ঘটনা আর শোনা যায় না।
বিনোদিনীর ইচ্ছা ছিল যে নতুন থিয়েটার তৈরি হবে তা বিনোদিনীর নামে বি-থিয়েটার হবে। কিন্তু কিছু মানুষের প্রতারণার শিকার তিনি হন। যাঁদের মধ্যে তাঁর নিজের অভিনয় গুরু গিরিশচন্দ্রও ছিলেন। বিনোদিনীর ত্যাগ স্বীকারে যে নতুন থিয়েটার তৈরি হয় বিনোদিনীর নাম তাতে থাকে নি। এই নতুন থিয়েটারের নাম হয় স্টার থিয়েটার। এই বিশ্বাসঘাতকতায় যখন বিনোদিনী দুঃখে বেদনায় কাতর তখনই রামকৃষ্ণদেব তাঁর ‘চৈতন্যলীলা’ নাটক দেখতে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এর দু’বছর পরেই ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২২-২৩ বছর বয়সে তিনি রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে যান। তারপর দীর্ঘদিন জীবিত থাকলেও কখনো অভিনয়ে ফিরে আসেন নি। ফলে বাংলা থিয়েটার বঞ্চিত হয় এক অসামান্য অভিনেত্রীর প্রতিভা এবং অভিনয় থেকে।
বিনোদিনী নারীদের অভিনয়ে বাঙালি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বিশ শতকের গোড়ায় যখন গ্রামোফোন চালু হয়, তখন বিনোদিনী গান শুরু করেন। তাঁর গানের গলা ছিল উঁচুমানের। জীবনে তিনি মোট তিনজন ধনীর রক্ষিতা ছিলেন। এর মধ্যে শেষ ব্যক্তির সঙ্গে তিনি ছিলেন ৩১ বছর। তিনি বিনোদিনীর জন্য বাড়তি কিছু সম্পত্তি রেখে যান। তাই স্বচ্ছলতা মধ্য দিয়েই তিনি ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বিনোদিনী লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী আমার কথা ও দুটি কবিতা গ্রন্থ বাসনা এবং কনক। নানা দুর্নাম ও প্রলোভন উপেক্ষা করে তিনি নাটক এবং অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় করেন। গিরিশচন্দ্রের মতো বিনোদিনীর মতো প্রতিভাশালী অভিনেত্রী সর্বদেশেই বিরল। স্টার থিয়েটারকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রতি সকল পুরুষ নাট্যকার-নাটকপৃষ্ঠপোষকদের ব্যবহারে ব্যথিত বিনোদিনী ‘আমার কথা’-য় অসংকোচে নিজের মনের কষ্ট ও ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেছেন। আগাগোড়া তিনি নিজেকে পতিতা, রক্ষিতা, বারবনিতা বলে উল্লেখ করেছেন।
৫৬) বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬) : স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব এবং স্ত্রী সরলা দেবীর ঘরে জন্ম নেন অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী কল্যাণী দাস (১৯০৭-৮৩) ও বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬)। বেণীমাধব ছিলেন নেতাজি সুভাষ বসুর সবচাইতে প্রিয় শিক্ষক।
অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, ছাত্রী সংঘ প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিভিন্ন ঘরের মেয়েরা এসে যুক্ত হছেন তখন। সেই উত্তাল সময়েই বেড়ে ওঠা প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত এবং বেণীমাধব-সরলা দেবীর দুই কন্যার মতো বিপ্লবীদের।
বীণা দাসের চার বছরের বড় কল্যাণী দাস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ছাত্রী সংঘের একজন সংগঠক ছিলেন এবং স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। বিপ্লবীদের একটি গোপন মিটিংয়ের নিষিদ্ধ লিফলেটকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে আদালত তাঁকে কারাভোগের শাস্তি দেয়। কল্যাণী দাস অনার্স গ্রাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণির বন্দির কাতারে রাখা হয়। এক সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়ে সেই কারাবাসের অবর্ণনীয় কষ্ট খুব কাছ থেকে লক্ষ করেন কল্যাণী দাসের ছোট বোন বীণা দাস। বোনের এই আত্মত্যাগ তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে উপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তার কয়েক বছর পরে যখন বীণা দাসকে দেখা যায় গভর্নরকে গুলি করার পর আদালতে নির্ভীকচিত্তে ইংরেজিতে তার জবানবন্দি দিতে—তখনো বীণা দাস উল্লেখ করেন বোনের আত্মত্যাগ থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা নেওয়ার কথা।
বীণা দাস ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে তাঁর দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, দৃঢ় সংকল্প, উদার চিন্তাভাবনা তাঁর পরিবার থেকেই লাভ করেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির।
বেথুন ও ডায়সেশন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করা বীণা স্নাতক হন ১৯৩১ সালে। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল, বীণা তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। তিনি অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। ওই বছরই কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন এবং ধীরে ধীরে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন-শোষণের ওপর ক্রমশ জমে ওঠা প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিচ্ছটার সংস্পর্শে গান্ধীজির অহিংস মতবাদ থেকে সরে এসে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক পন্থাকেই বেছে নেন তিনি। ১৯৩২ সালে বীণা দাস তাঁর জীবনের সবচাইতে দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করার।
এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বীণা দাস সাহায্য নেন তাঁর বোন কল্যাণীর বান্ধবী কমলা দাসগুপ্তের। কমলা দাসগুপ্ত ‘যুগান্তর’ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীণা দাস যুগান্তরের সদস্য না হলেও তাঁর সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে কমলা দাস গুপ্ত তাঁকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। ।
১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি, গভর্নর স্ট্যানলি যথাসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আসেন। গভর্নর যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অভিভাষণ পাঠ শুরু করছেন তখন বীণা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে গুলি করলেন। অল্পের জন্য বীণা দাসের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বীণাকে গ্রেপ্তার করা হল। টানা ৪৮ ঘণ্টা বিরতিহীনভাবে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। রিভলবারের উৎস জানতে বীণার ওপর চালানো হলো নির্যাতন। বীণা মুখ খুললেন না। আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে সকল দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে জবানবন্দিতে তিনি বললেন, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুবরণ করা এবং যদি আমাকে মরতে হতো, আমি চেয়েছিলাম মহান মৃত্যু...এই ভারতবর্ষে এই পরিমাণ অন্যায়, অত্যাচার এবং বিদেশি শোষণের মধ্যে গুমরে কাঁদার চাইতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে জীবন বিসর্জন দেওয়া কি অধিকতর ভালো নয় ?’
একতরফা বিচারে বীণা দাসের ৯ বছরের জেল হল। তাঁকে একেক সময় একেক কারাগারে, একেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। কুমিল্লার কিশোরী বিপ্লবী শান্তি সুনীতি’র সঙ্গে তিনি এক কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হয়ে থাকার পর গান্ধীজির প্রচেষ্টায় অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দির সঙ্গে বীণাও মুক্তি পান। সাত বছর জেলে কাটিয়ে ১৯৩৯-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন।
জেল থেকে মুক্তির পর বীণা থেমে থাকেন নি। সেসময় বিপ্লবীদের অনেকে, বিশেষত তরুণেরা, গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ বেছে নেন। আরও অনেকের মতো বীণা দাসও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকাও ছিলেন। টালিগঞ্জের চালকল বস্তিতে গিয়ে বস্তিবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তিনি তাদের চরম দুর্গতিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এর পাশাপাশি সেসময় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও দেশাত্মবোধক চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় কমলা দাসগুপ্ত সম্পাদিত ‘মন্দিরা’ পত্রিকায়।
১৯৪২-এ ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন শুরু হলে বীণা দাস দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন হাজরা পার্কে। সভা ছিল বেআইনি। সেখানে একজন সহকর্মীকে সার্জেন্ট ব্যাটন দিয়ে প্রহার শুরু করতেই বীণা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পুলিশ আবারও বীণাকে গ্রেপ্তার করে। এবারে তিনি রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে প্রেন্সিডেন্সি জেলে তিন বছর আটক থাকেন। এ দফায় ১৯৪৫-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন করে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রভাব বীণা দাসকে ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বীণা দাসের স্বামী ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ শ্রী যতীশ ভৌমিক। স্বামীর মৃত্যুর পর বীণা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান রাজনীতি থেকে।
কখন যে তিনি হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। ঊনবিংশ শতকের নবম দশক। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর। হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে এক অজ্ঞাতপরিচয় বয়স্কা মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রেও খবরটি উঠেছিল। পরে অজ্ঞাতনামা মহিলার পরিচয় জানা গিয়েছিল। সেই নারীই ছিলেন বীণা দাস। কী মর্মান্তিক প্রস্থান অগ্নিকন্যার! সকলের চোখের আড়ালে-অজ্ঞাতে-নিভৃতে।
৫৭) বেগম ফজিলাতুন্নেছা : জন্ম ১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইল সদর থানার নামদার কুমুল্লী গ্রামে। পিতার নাম ওয়াজেদ আলী খাঁ, মাতা হালিমা খাতুন। তিনি ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে ইডেন কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। ফজিলাতুন্নেছা ১৯২৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে গণিত শাস্ত্রে এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (গোল্ড মেডালিস্ট) হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯২৮ সালে বিলেতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন। নিখিল বঙ্গে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। উপমহাদেশে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলাত থেকে ডিগ্রি এনেছিলেন। তাঁর পড়াশোনার জন্য করটিয়ার জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) বিশেষ উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য করেন। বিলেতে তাঁর অবস্থানকালীন সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে প্রথম ডিপিআই খুলনা নিবাসী আহসান উল্ল্যাহর পুত্র এ এ জোহাও লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। লন্ডনে জোহা সাহেবের সঙ্গে ফজিলাতুন্নেছার পরিচয় হয়। পরে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় প্রথমে স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালের আগস্টে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় মুসলিম সমাজসেবক-সংঘে’র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যটি নারী জাগরণের মাইলফলক হয়ে আছে। এই অধিবেশনে তিনি বলেন, ‘নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন ও বলেন। নারী সমাজের অর্ধাঙ্গ, সমাজের পূর্ণতা লাভ কোনোদিনই নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব হতে পারে না। সেই জন্যেই আজ এ সমাজ এতটা পঙ্গুত্ব হয়ে পড়েছে।’ তিনি আরও বলেন, The highest form of society is one in which every man and woman is free to develop his or her individuality and to enrich the society what is more characteristic of himself or herself.
কাজেই এ সমাজের অবনতির প্রধান কারণ নারীকে ঘরে বন্দি করে রেখে তার ওহফরারফঁধষরঃু বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখা। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে এতটা কথা আজ বলছি তার কারণ সমাজের গোড়ায় যে-গলদ রয়েছে সেটাকে দূরীভূত করতে না-পারলে সমাজকে কখনই সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারা যাবে না। ’
তিনি ১৯৩৫ সালে বেথুন কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। বেথুন কলেজে চাকরিরত অবস্থায় দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে এসে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ১৯৪৮ সালে।
বেগম ফজিলাতুন্নেছা ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক বিভাগসহ ইডেন কলেজ ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয়। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি সম্পর্কে সওগাতসহ অনেক পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হয়।
এই বিদূষী নারী ১৯৭৭ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিরক্ষার্থে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭ সালে ফজিলাতুন্নেছার নামে হল নির্মাণ করেন।
৫৮) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২) : রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন মুসলিম মহিলা বাংলা সাহিত্য সাধনা করে যশ অর্জন করেন, বেগম রোকেয়া তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। উনিশ শতকের শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। এক রক্ষণশীল পরিবারে সম্পূর্ণ প্রতিকূল এক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে নিজের চেষ্টা ও মনোবল সম্বল করে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।
সম্ভ্রান্ত ঘরে বেগম রোকেয়ার বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্নেহশীল ও মুক্ত মনের অধিকারী স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি লেখাপড়া করার ও চিত্ত বিকাশের সুযোগ পান। কিন্তু স্বামীর সান্নিধ্যসুখ তাঁর বেশিদিন ভোগ করার সৌভাগ্য হয় নি। বিবাহের মাত্র দশ বছর পরে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে তিনি সমাজসংস্কার ও সমাজগঠনমূলক কাজে নিজেকে সঁপে দেন।
বেগম রোকেয়ার প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি মুসলিম মহিলাদের অশিক্ষিত ও কুশিক্ষা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি স্বামীর স্মৃতিস্মারক ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ স্থাপন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকে মুক্ত করে সৎ ও সুন্দর পথে মুসলিম নারী জাতিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধতা ও সমবেত প্রচেষ্টা। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি ‘আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীনে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা করেন।
মুসলিম নারী সমাজের উন্নতি সাধন এবং সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই তিনি সাহিত্যচর্চায় স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করেন। উনিশ শতাব্দীতে যখন বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রঙ্গলালের কলমে উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিদ্বেষ দেখা দিচ্ছিল তুমূলভাবে, সেই পটভূমিতে উনিশ শতকের শেষে বাঙালি-মুসলমানের নবজাগরণ ঘটতে শুরু করল, প্রধানত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হলো প্রচুর সৃজনশীল শিল্পী। তাদের মধ্যে একমাত্র বেগম রোকেয়াই ছিলেন নারী শিল্পী। সৈয়দ এমদাদ আলী প্রকাশিত মাসিক ‘নবনূর’ পত্রিকায় রোকেয়ার আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ‘অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে’ লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেগম রোকেয়া সমকালীন হিন্দু-মুসলমান লেখিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে ‘নবনূর’-এর পৃষ্ঠাতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর চিন্তা ও কর্মাদর্শের বাণীরূপ। ‘মতিচূর', ‘পদ্মরাগ', ‘অবরোধবাসিনী’, ‘সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি লেখিকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তার শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি তা নিয়ে সাহিত্য সমাজে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ‘মতিচূর’ শ্রেষ্ঠ, আবার কেউ বলেন, ‘অবরোধবাসিনী’ শ্রেষ্ঠ। প্রবন্ধ, গল্প ও রূপক রচনায় ‘মতিচূর' সমৃদ্ধ। গ্রন্থের বিষয়সূচি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশের মুখ্য উদ্দেশ্য নারী মুক্তি ও আদর্শ প্রচার। বেগম রোকেয়া রচিত ‘অবরোধবাসিনী’ ১৯২৮ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। খান্দানী জমিদার ঘরে, কি সাধারণ সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরে অবরোধের নামে নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা এ দেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। এই অবরোধ প্রথার কঠোর অনুশাসনে কত রমণীর সম্ভাবনাময় জীবন যে অকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তার অনেক করুণ চিত্র এঁকেছেন বেগম রোকেয়া তাঁর এ গ্রন্থে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, অবরোধ ছিন্ন মানে পর্দাহীনতা নয়।
‘পদ্মরাগ’ বেগম রোকেয়া রচিত একটি উপন্যাস। সম্ভবত ‘পদ্মরাগ’ লেখিকার সর্বশেষ রচনা। বিবাহিত জীবন তথা সংসার ধর্ম পালনই যে নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সেই বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে নায়িকা সিদ্দিকার কণ্ঠে।
৫৯) ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৫-১৯১১) : সংস্কৃতিমনা আইরিশ পরিবারের কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল পড়াশোনা শেষ করে বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে ভগিনী নিবেদিতারূপে তাঁর পুনর্জন্ম হয়। বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৮ সালে ভারতে এসে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক নানাবিধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে স্বামীজির মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন। স্বদেশি আন্দোলন থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটে বিপ্লবী আন্দোলনে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। আইরিশ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষের।
৬০) মণিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭) : বরিশাল জেলার জমিদারের ম্যানেজারের কন্যা মনিকুন্তলার দাদু ছিলেন শহরের শ্রেষ্ঠ উকিল ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও জমিদারের সম্পত্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত পিতার কন্যা হওয়ায় পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতায় ও উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনে ধর্মীয় প্রভাব ছিল গভীরÑসেইসঙ্গে ছিল নারীদের প্রতি সহানুভূতি। পিতামাতা দুজনেই স্বদেশি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতেন। ১৯২৩ সালে গান্ধীজি বরিশাল এসে পতিতাদের পুনর্বাসন ও সম্মানজনক জীবনযাপনের আহ্বান জানিয়ে তাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। মনিকুন্তলা ও তাঁর ছোড়দি তখন কংগ্রেসের এই কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত শুরু করেন। প্রতিবেশীর মাধ্যমে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হন। বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপিত মনিকুন্তলা মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট মতবাদের অনুগামী হন। চল্লিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকে প্রথম সারির নারী সদস্য ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার মন্বন্তরে ক্ষুধার্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন। সহকর্মিণী রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহিলাদের সাহায্যে গঠিত হয়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এই সমিতির শাখা-প্রশাখা চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়াকালীনই তিনি পরিপূর্ণভাবে মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারাজীবন তিনি ধর্ম ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন কীভাবে মার্কসবাদীরা যান্ত্রিক উপায়ে নিরীশ্বরবাদ ডেকে এনে মেয়েদের রাজনীতিতে আসার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। তিনি সারাজীবন মেয়েদের ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি দেখেছেন এই মহিলাদের দেবদেবীতে বিশ্বাস যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে শোষকের প্রতি ঘৃণা। মুক্তির পথে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস পরিপন্থী নয় বলে মনিকুন্তলা মনে করতেন। রাজনীতি ও সমাজের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বৈততার প্রসঙ্গে নারীত্ব ও পুরুষপ্রধান মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব নিয়েও যথেষ্ট চিন্তা করেছেন মনিকুন্তলা। বিপ্লবের নামে অতিবামপন্থা ও অমানবিক কঠোরতার বিরোধিতা করতেন তিনি। মুক্তিকামী পথের যাত্রী লাখ লাখ নারীর কাছে শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। এই নারীর জন্য সামাজিক পরিচয়ও সমান প্রয়োজন। এই দুই পরিচয়ের ভেতর দিয়েই স্থির হয় এক মুক্তিকামী নারীর সামাজিক রাজনৈতিক সামগ্রিক সত্তা। হিন্দু কোড বিল পাসের আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী মনিকুন্তলা বৈবাহিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সারা জীবন ব্রতী ছিলেন। এ ছাড়া পতিতাদের পুনর্বাসন এবং বস্তিবাসী ও শ্রমজীবী মেয়েদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে কারারুদ্ধ হন।






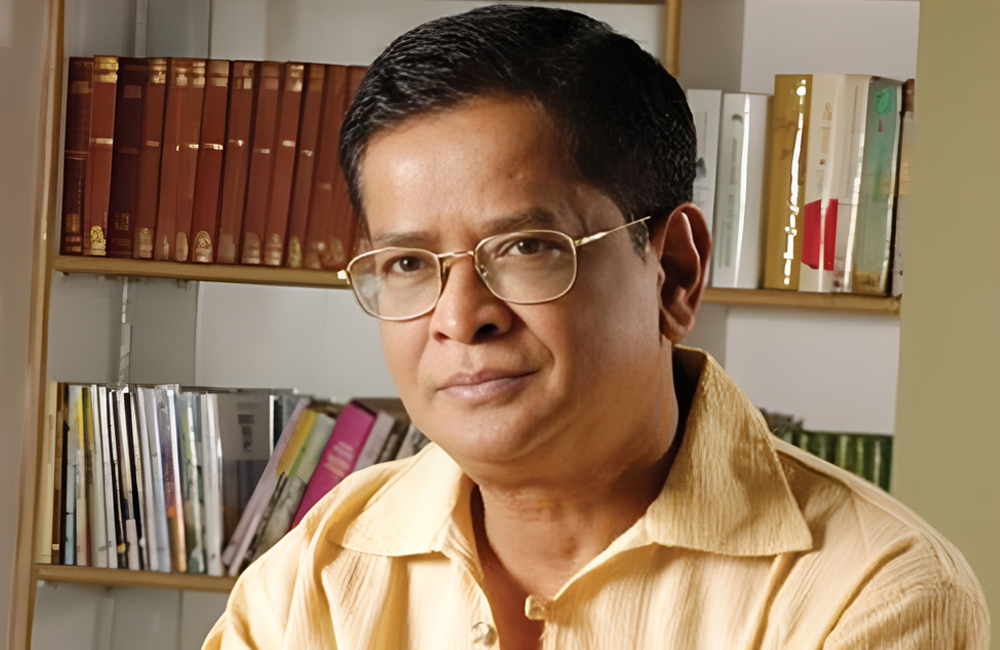
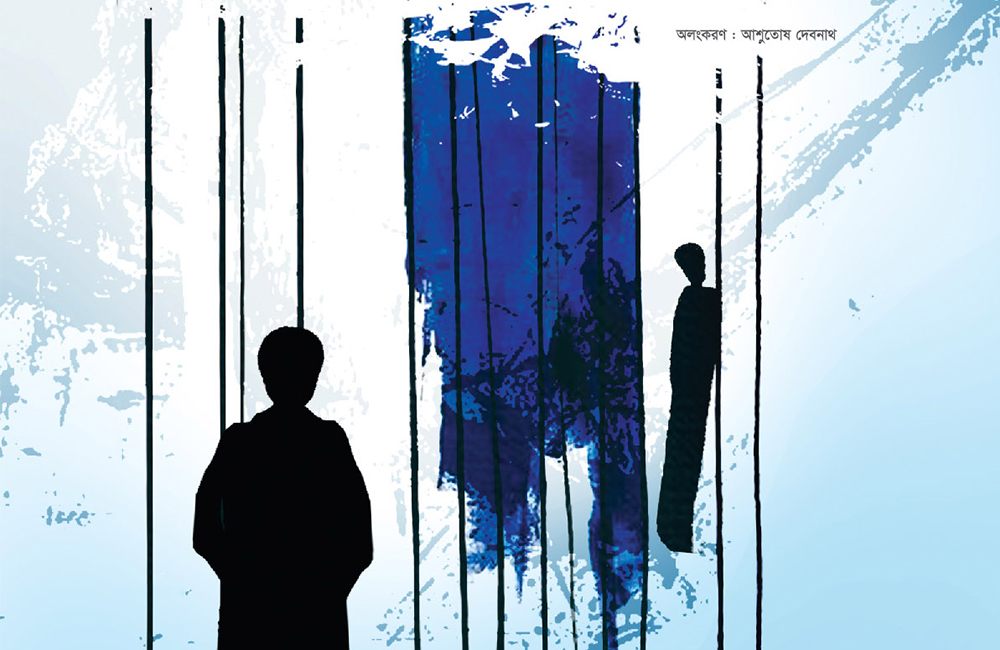

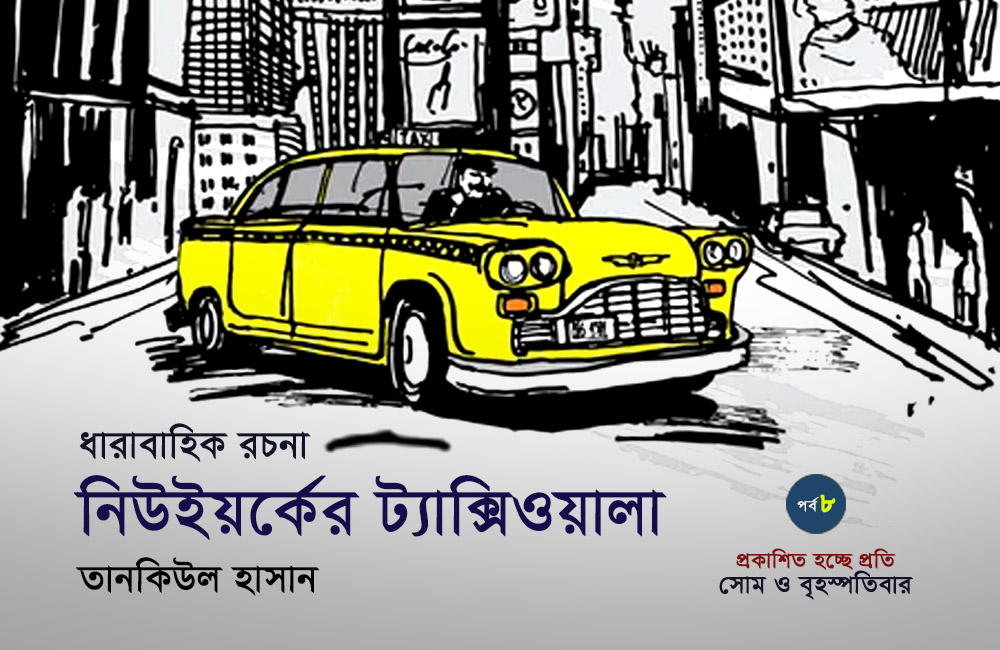





Leave a Reply
Your identity will not be published.