বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মতো একটা সমাজে বিরাজমান সাধারণ মনোভঙ্গির মধ্যে কেউ যদি নিজেকে সাংস্কৃতিক অনুশীলনে সক্রিয় রাখতে চান তাহলে তাঁকে সে সমাজে ভুল বোঝা খুবই স্বাভাবিক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা মাত্রায় দেখে মনে হয়েছে আমাদের সমাজের গঠনটাই এমন যে, এখানে তিনি অনেক বেশি খণ্ডিতভাবে বোঝা একজন মানুষই হওয়ার কথা। এর একটা কারণ খণ্ডকেই সমগ্র ভাবার অনুশীলন আমাদের বেশি, আরেকটা কারণ সামগ্র্যকে বুঝতে পারায় আমাদের নিদারুণ অক্ষমতা।
সাধারণভাবে লক্ষ করলেও অনুভূত হয় যে, একটা মানুষকে পেশাগত পরিচয় দিয়ে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। আমার ধারণা, বেঁচে থাকার জন্য কিংবা সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে প্রতিপত্তির মাত্রা বুঝবার জন্য বহুবছর ধরে এই একটাই মাত্র যেন পরিমাপক আছে আমাদের। এমন কথা যে মনে হলো তার কারণ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম একজন কৃতী গল্পকার-ঔপন্যাসিক হলেও যদি শিক্ষক হিসেবে পেশাগত পরিচয় না থাকত তাহলে লেখক হিসেবে এই মনোযোগ তিনি পেতেন কি না আমার সন্দেহ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হলেই আমাদের সমাজ কাঠামোতে একজন ব্যক্তি খানিকটা মর্যাদা পান। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, যদি এই পরিচয় কোনোভাবে অড়ালে রেখে কাউকে শিল্পরসিক বা শিল্পকলার সমালোচক পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয় তাহলে তিনি কিন্তু পেছনের সারিতে চলে যাবেন। ব্যক্তিত্বের এই ধরনের অনেকগুলো মাত্রার কারণে সমাজে তিনি সব সময়ই প্রায় ভাস্বর ছিলেন। এতক্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বে সমাহৃত যে গুণগুলোর কথা বলা হলো তা একত্র করলে যে পরিচয় দাঁড়ায় তাতে তিনি যেমন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তেমনি গল্পকার-ঔপন্যাসিক ও একই সঙ্গে শিল্পকলার রসিক। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণত সাহিত্য-সমালোচক সত্তা চলে যায় সাহিত্যের শিক্ষক পরিচয়ের আড়ালে। তাঁর ক্ষেত্রে তেমনটি হয়তো হয় নি তাঁর ব্যক্তিত্বে এতগুলো গুণের একত্র সমাহার ঘটায়। কিন্তু এই ক’টি পরিচয় দিয়েও তাঁকে তো সমগ্রভাবে ধরা যায় নি। তিনি যে একজন উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল মানুষ তার পরিচয়ও যে তাঁর ব্যক্তিত্বসামগ্র্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় তা ভুলে গেলেও যে চলবে না! বাংলাদেশে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে জন্ম নেওয়া সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জীবনের একটা দীর্ঘ পর্ব রয়েছে যার অস্তিত্ব একদিকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিকতার বাইরে, একদিকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিকতার সম্প্রসারণে আর রয়েছে বাইরের সাংস্কৃতিকতাকে আত্মীকরণে। এই সবগুলো দিক থেকে তাঁকে দেখতে না পারলে তাঁকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে বুঝে ওঠা যাবে না।
২
আমার মনে পড়ছে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আধখানা মানুষ’ প্রকাশিত হলে আমি একটি আলোচনা লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলাম, বইটি পড়তে শুরু করার পর অনুভব করেছি, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কথাসাহিত্যচর্চাকে মোটেও হালকাভাবে নেন নি। সাহিত্য-সমালোচনা বা নন্দনতত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী রচনার পাশাপাশি তিনি গল্প-উপন্যাস রচনাকেও তাঁর শৈল্পিক চেতনা প্রকাশের প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছেন। আরও লিখেছিলাম, ‘আধখানা মানুষ’ উপন্যাসের পেছনে যে দীর্ঘদিনের সাহিত্যিক প্রস্তুতি ছিল, তা এই উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ, চরিত্রায়ন এবং বর্ণনাশৈলী থেকে সহজেই প্রতীয়মান।
আমার পরিষ্কার মনে আছে, নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রাবন্ধিক-সমালোচক হিসেবেই ছিলেন পরিচিত ও সমাদৃত। ১৯৯৬ সালে প্রবন্ধের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন বলে এবং দৈনিক সংবাদে দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলা ‘অলস দিনের হাওয়া’র রচনাগুলোর জন্য তাঁর প্রাবন্ধিক-সমালোচক পরিচয়ের সিলমোহর লেগে গিয়েছিল। সেই বিবেচনায় আমিও দ্বিধান্বিত ছিলাম তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়ের যথার্থতা নিয়ে। ততদিনে গল্প প্রকাশিত হলেও তাঁকে গল্পকার হিসেবে বিবেচনা করার চেয়ে তাঁর গল্পগুলোকে মনে করা হয়েছিল বড়জোর প্রাবন্ধিকের খেয়াল হিসেবে! ‘যোগাযোগের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক’ নামে ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে তিনি যে যৌথ একটা উপন্যাস লিখেছিলেন সেটিকে সাহিত্যের এলিট সমাজ পছন্দ করে নি। এমনকি দীর্ঘকাল পরে বই আকারে প্রকাশিত হলে এটিকেও সুনজরে দেখেন নি সাহিত্যের শিরোমণিরা। এমনকি বইটি নিঃশেষিত হলে পুনর্মুদ্রণ করতেও অনুমতি দিতে পারেন নি তিনি সমাজের এই বিরোধপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করতে না পারার জন্য! তাঁকে সামগ্রিকভাবে বুঝবার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের শিরোনামে উল্লিখিত ‘যোগাযোগের গভীর সমস্যা’ কথাটিরও যে একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে তা আমাদের ভাবতে হবে।
বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠনে গভীর অবহিতি তাঁকে যে জীবনবোধে ঋদ্ধ করেছে তার প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রেই আমাদের সমাজ বাধার সৃষ্টি করে। তিনিও অনেকক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়েছেন বা তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। কোনো নতুন উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানালে আমাদের সমাজ বিবেচনা করে উদ্যোগের বাস্তবতা ও সৃজনশীলতার চেয়ে হালনাগাদ জ্ঞানের অভাবপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। পাশ্চাত্যে যেসব তত্ত্ব যাপিত জীবন সম্পর্কে বিবেচনায় আসে তার অনেককিছু যেমন আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় আবার অনেককিছু প্রযোজ্য সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সচেতন। ফলে তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা ছিল অনেক বেশি উদার। এই উদারতাকেও আমাদের সংকীর্ণতা অনেক সময় ভুল বুঝেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জীবনদৃষ্টি—যাকে তিনি মনে করতেন জগৎদৃষ্টি—তাঁর বিচারবোধকে উদার করে তুলেছিল। তাঁর অনুশীলনকে আমরা হয়তো আরও ভালোভাবে অনুভব করতে শিখতাম তাঁর জীবনকাল দীর্ঘতর হলে।
৩
১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় ‘স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প’ বইটি, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রথম ছোটগল্প-সংকলন। এই বইয়ের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে নিজের অবস্থান ঘোষণা করেন। এর আগ পর্যন্ত তাঁর পরিচয় সীমিত ছিল প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে। যদিও ১৯৭৩ সালে তাঁর গল্প ‘বিশাল মৃত্যু’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’র মতো বহুল প্রচারিত পত্রিকায়। তা সত্ত্বেও নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ তথাকথিত অর্থে মননশীল লেখকের পরিচয়েই চিহ্নিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ‘প্রশিক্ষণে একজন সমালোচক এবং বাধ্যতামূলকভাবে একজন লেখক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ লেখকসত্তাকে তিনি সৃজনশীল ও মননধর্মী লেখক এমন দুই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। তাঁর বিবেচনা ছিল লেখকমাত্রই সৃজনশীল; মনন ছাড়া তিনি সৃজন করতে পারেন না। ফলে সৃজনশীল রচনা বলে চিহ্নিত তাঁর রচনার পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন যে তিনি মননশীল লেখক। বই প্রকাশের বিবেচনায় দেখলে তাঁকে প্রচলিত অর্থে সৃজনশীল লেখকই বলতে হবে।
তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলোর মধ্যে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ, মানবিক সম্পর্কের জটিলতা এবং সমাজের অসঙ্গতি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের সংগ্রাম, এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। দেখা যাচ্ছে সবমিলিয়ে মোট ১১টি গল্প-সংকলন বেরিয়েছে তাঁর। এ ছাড়াও বেরিয়েছে নির্বাচিত গল্পের সংকলনও। নামগুলো এখানে গ্রথিত করে রাখছি। ‘স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প’ (১৯৯৪), ‘থাকা না থাকার গল্প’ (১৯৯৫), ‘কাঁচ ভাঙ্গা রাতের গল্প’ (১৯৯৮), ‘অন্ধকার ও আলো দেখার গল্প’ (২০০১), ‘প্রেম ও প্রার্থনার গল্প’ (২০০৫), ‘বেলা অবেলার গল্প’ (২০১২) ‘তালপাতার সেপাই ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৭), ‘মেঘশিকারী’ (২০১৫), ‘ভুলে থাকা গল্প’ (২০১৬), ‘একাত্তর ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৭),
‘বিচিত্র স্বাদের গল্প’ (২০১৭), ‘কয়লাতলা ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৯),
‘দেখা অদেখার গল্প’ (২০২২) তাঁর লেখা গল্প-সংকলন। এর মধ্যে ‘ভুলে থাকা গল্প’ বইটি মূলত প্রথম দিকের দুটি বইয়ের গল্পের সম্পাদিত পাঠ হলেও নতুন দুটি গল্পও যুক্ত হয়েছিল।
উপন্যাসেও রয়েছে জীবনবীক্ষণের নিরীক্ষা। মননশীলতার নির্দেশনায় এগিয়ে চলেছে উপন্যাসের আখ্যান। তাঁর উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সুর জনজীবনে মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত ও পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সমালোচনা। এই ব্যবস্থা যেমন পৃথিবীর নিসর্গকে ধ্বংস করছে তেমনি ধ্বংস করছে মানুষের অন্তর্প্রকৃতিকেও। তাঁর উপন্যাসগুলোরও নাম টুকে রাখা হলো এখানে। ‘আধখানা মানুষ’ (২০০৬), ‘তিন পর্বের জীবন’ (২০০৮), ‘কানাগলির মানুষেরা’ (২০০৯), ‘আজগুবি রাত’ (২০১০), ‘দিনরাত্রিগুলি’ (২০১৩), ‘শকুনের ডানা’ (২০১৩), ‘নন্দীছড়ার যোদ্ধারা’ (২০২৩) [কিশোরপাঠ্য উপন্যাস]।
৪
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রবন্ধ-সমালোচনার বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘নন্দনতত্ত্ব’ (১৯৮৬), ‘কতিপয় প্রবন্ধ’ (১৯৯২), ‘অলস দিনের হাওয়া’ (২০১৩), [আশির দশকে ‘সংবাদ’ সাময়িকীতে বহুবছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া রচনার নির্বাচিত সংকলন।] ‘লেখাজোখার কারখানাতে’ (২০২৫), ‘আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ (২০১৬), ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ’ (২০১৯); এ ছাড়া লিখেছেন জীবনীও, ‘ইতিহাসের রূপকার তাজউদ্দীন আহমদ’ (২০১৯)। প্রবন্ধ-সমালোচনাধর্মী বই সংখ্যায় কম দেখালেও সর্বমোট লেখা কম নয় বলে আমার ধারণা। বহু রচনা বিচিত্র প্রয়োজনে রচিত ও সংকলিত হয়েছে, যা হয়তো তিনি গ্রন্থভুক্ত করবারও সময় পান নি।
বাংলা একাডেমির ভাষাশহীদ গ্রন্থমালার আওতায় প্রকাশিত তাঁর ‘নন্দনতত্ত্ব’ বইটি বহুল পঠিত। বাংলাদেশে এ ধরনের বই সংখ্যায় বেশি নেই বলেও হয়তো এটি মনোযোগ পেয়েছে। তবে এ কথাও মানতে হবে এ বিষয়ে এই বইঅতিক্রমী রচনাও তো বাংলাদেশে আর লেখা হয় নি। সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা মূলত গভীর পাণ্ডিত্য, নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ, এবং আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক (উত্তর আধুনিক) ভাবনার জন্য বিশেষ পরিচিত। মন মুক্ত ছিল বলে তাঁর সমালোচনার মূল সুর ছিল সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল। মূল্য বিচারে শিল্প ও সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পায়।
তিনি কেবল সংবেদনশীল সাহিত্যিক নন, একজন মানবিক বুদ্ধিজীবী হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন। নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। সাহিত্যকে দেখতে পছন্দ করতেন সমাজের অস্থিরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের আয়নায়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ায় তাঁকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানত বিদেশি সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে গভীর আলোচনা করতে হতো, সেসব আসত তাঁর লেখায়ও। সে সময়ে যা বাংলাদেশের পাঠক ও লেখকদের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।
সাহিত্য-সমালোচনার পাশাপাশি তিনি একজন খ্যাতনামা চিত্রকলার সমালোচকও ছিলেন। শিল্পকলার নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্রও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাঁর লেখায় দেখা যেত। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণশেষে দেশে ফিরে দৈনিক ‘সংবাদ’-এ তাঁর নিয়মিত কলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই কলামে তিনি বিদেশি সাহিত্য ও শিল্পকলাসহ নানা বিষয়ে সহজ ভাষায় আকর্ষণীয় ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, ফররুখ আহমদ এবং শামসুর রাহমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্যকর্মের ওপর বিচিত্র লেখায় তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য সমৃদ্ধ।
কথাসাহিত্যের পাশাপাশি তাঁর সমালোচনামূলক লেখাতেও
উত্তর-আধুনিক প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়, যেখানে তিনি চিরায়ত গল্পের রীতিনীতিকে প্রশ্ন করেন। কথাসাহিত্যের সমালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, নিজের গল্পে যেমন মায়া বাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়ালিজম এবং পরাবাস্তবতা বা স্যুররিয়ালিজমের মিশ্রণে নতুনত্ব এনেছিলেন, তেমনই তিনি সাহিত্যের নতুন নতুন আখ্যানরীতির বিশ্লেষণ করতেন। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করতে পারতেন ভারী ও জটিল বিষয়বস্তুকেও, যা সাধারণ পাঠকের কাছেও হয়ে উঠেছিল গ্রহণযোগ্য।
৫
যদিও এমন কোনো কথা তিনি নিজে কোথাও স্পষ্ট করে বলেছেন বলে জানি না তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম নিজেকে প্রচলিত অর্থে প্রধানত ‘সৃজনশীল লেখক’ হিসেবেই সম্ভবত চিহ্নিত করতে চাইতেন। কারণ নব্বই দশকের পর তাঁর প্রকাশিত বইয়ের তালিকাতেও সে আভাস রয়েছে। গল্প ও উপন্যাসই প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর প্রকাশনার অগ্রভাগে; তুলনায় প্রবন্ধের সংখ্যা কম। অথচ শিল্পকলাবিষয়ক তাঁর লেখালিখি ও নানা কর্মপ্রচেষ্টা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও সেগুলো গ্রন্থাকারে গেঁথেছেন কম।
সৃজনশীল ও মননপ্রধান সব রচনা থেকেই সামগ্রিকভাবে বোঝা যায়, পাশ্চাত্যের তত্ত্বনির্ভর কাঠামোয় তিনি নিজেকে আবদ্ধ করেন নি, আবার সেখান থেকে যে পুরোপুরি সরে থেকেছেন তা নয়; বরং বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকেই গড়ে তুলেছিলেন এক সমন্বিত, স্বাধীন বোধ। উত্তর-আধুনিক চিন্তার প্রভাব তাঁর ভাবনায় অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা ছিল বাঙালি সাংস্কৃতিক সত্তার ভেতর দিয়ে পরিশ্রুত। হাসন রাজার রচনা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে বাংলার লোকায়ত চেতনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটি দৃশ্যমান ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে এই সূত্রে তাঁর চিন্তার গভীরতা অনুধাবনের জন্য আরও নিবিড় পাঠ জরুরি।
দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর রচনার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, তাঁর সংস্কৃতিচিন্তা বহুমাত্রিক। এতে আন্তঃশাখাগত বোধের উপস্থিতি আছে, যা কেবল সাহিত্য বা শিল্পকলার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও জনজীবনের চলমান গতির সঙ্গেও যুক্ত। তিনি সংস্কৃতিকে আলাদা, উচ্চস্তরের বা উৎকর্ষের জগৎ হিসেবে দেখতে চান নি; বরং মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, ভাষা, রুচি, ক্ষমতার সম্পর্ক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্কৃতিকে দেখেছেন এক জীবন্ত শক্তি হিসেবে।
স্থানীয়তা ও বৈশ্বিকতার সম্পর্ক নিয়েও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়মুখী—তিনি চাইতেন স্থানীয়তার ধ্বনি যেন বৈশ্বিক পাঠে প্রতিধ্বনিত হয়। পরিবর্তন, গণমাধ্যম ও সময়ের প্রবাহকে তিনি সর্বদা এক চেতনায় দেখেছেন, কখনো স্থিতাবস্থাকেই শেষ কথা ভাবেন নি। সবশেষে বলা যায়, তাঁর সংস্কৃতিচিন্তা কখনোই নৈতিক ও মানবিক প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়াকে তিনি অন্যায়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত এক বৌদ্ধিক-সক্রিয় মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখেছেন।
৬
রচনাটি শুরু করেছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের সার্বিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। যাঁরা তাঁর সামান্যও সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই অনুভব করেছেন তাঁর সংবেদনশীলতা। এর পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অজস্র ফেসবুক পোস্টে। তিনি যে ব্যক্তি হিসেবে কেবল ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যেই নয় নানা পরিপ্রেক্ষিতের মানুষের মনে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান যে একটা গভীর বিয়োগব্যথা হয়ে উঠেছে সকলের কাছে তা অনেক মানুষের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু কর্ম ও কৃতিতে আছেন। জীবনব্যাপী কর্ম নিয়ে তাঁর অতীতের থাকা ও বর্তমানের সশরীরে না-থাকার মাধ্যমেই তিনি আমাদের ভবিষ্যতে থাকবেন। ০
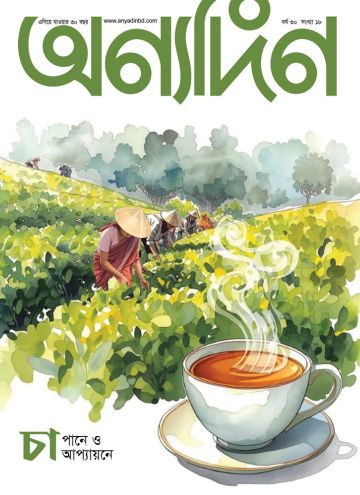






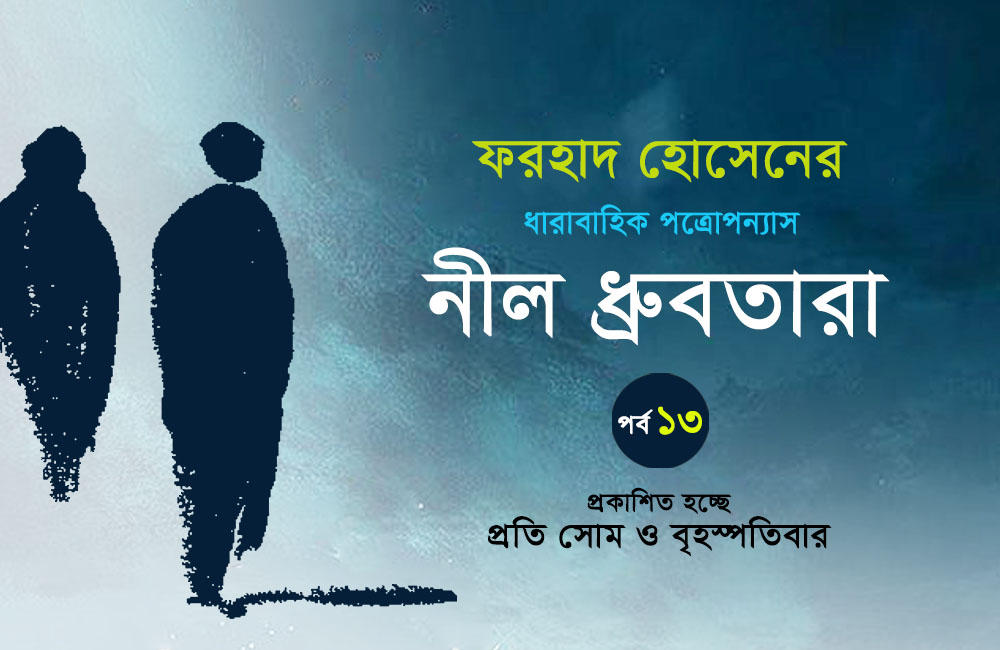



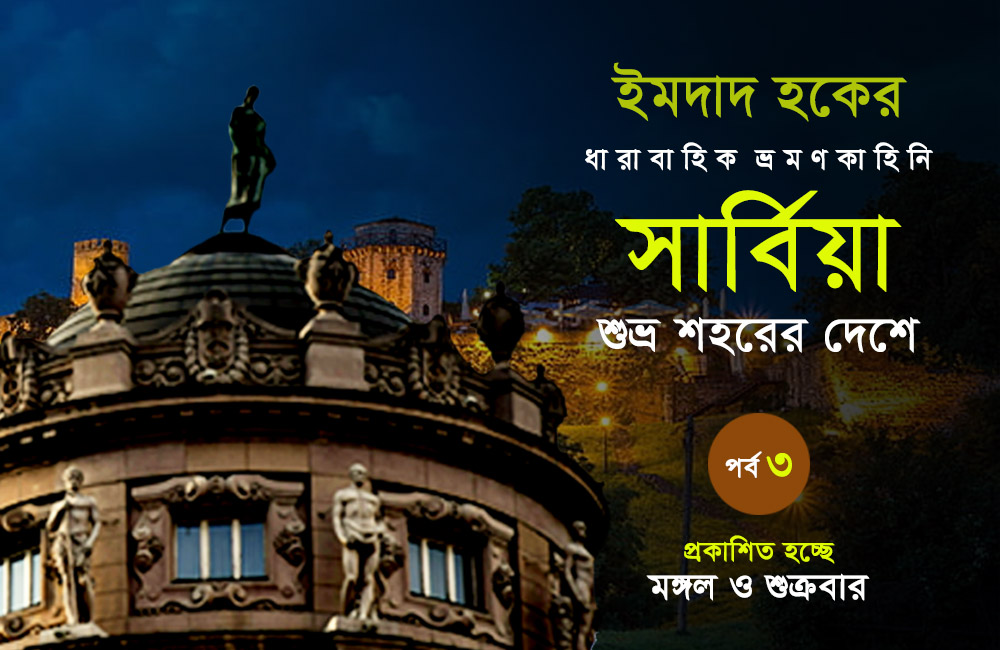



Leave a Reply
Your identity will not be published.