তিনি একজন শিক্ষাবিদ। মুক্তমনা। একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাধীন ‘গোলাপি প্যানেল’-এর অংশ ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার-সম্মেলন-কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করেছেন। কথাসাহিত্যিক। গল্প ও উপন্যাসে, দুই ক্ষেত্রেই সৃজনশীলতার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও খ্যাত এবং এক্ষেত্রে তিনি সেই বিরল বুদ্ধিজীবীদের একজন, যিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে সমানভাবে দক্ষ। এদেশের সমালোচনা সাহিত্যকেও তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, শামসুর রাহমানের ওপর তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম রয়েছে। শিল্প সমালোচক হিসেবেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
তিনি প্রয়াত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এই দীপ্র মনীষার সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।
গতকাল, ১৮ জানুয়ারি, ছিল সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এই লেখাটি পত্রস্থ হলো।
নানা রঙের দিনগুলি
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এই পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেন ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারি। সিলেট শহরে। মণিপুরী রাজবাড়ি এলাকায়। বাবা সৈয়দ আমিরুল ইসলাম। মা রাবেয়া খাতুন। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন শিক্ষক। তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর আপন ভাগ্নে। উল্লেখ্য, মনজুরদের সিলেটের বাসায় একবার বেড়াতে এসেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তিনি ‘কিশোর মনজুর’-এর অটোগ্রাফ খাতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চার লাইন লিখে নিচে ‘হুর-নানা’ স্বাক্ষর দিয়ে বলেছিলেন, ‘পড়বে এবং লিখবে’। তিনি ছিলেন সৈদ মনজুরুল ইসলামের অনুপ্রেরণা।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জীবনের প্রথম পাঁচ বছর কেটেছে সিলেটে। যে জায়গায় তিনি সপরিবার থাকতেন, সেখানে ছিল মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। তাদের একটি মণ্ডপ ছিল। হিন্দুদের ছিল দুটি মন্দির। আর মসজিদ তো ছিলই। মণিপুরী মণ্ডপের পাশে ছিল একটি মাঠ। সেখানে বালক মনজুর খেলাধুলা করতেন, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে। মণ্ডপে গান হতো, পূজা হতো। কখনো-সখনো সেই গান শুনতেন, পূজা দেখতেন বালক মনজুর। বলা যায়, ছোটবেলায় একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে তিনি দিন কাটিয়েছেন। আর বাবা-মা তাঁকে সব ধর্মের মানুষদের সম্মান করতে শিখিয়েছেন। বিষয়টি মনজুরের হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায়। আর পরিবারে মুক্তচিন্তার চর্চাও হতো। এই বিষয়টিও তাঁর চেতনায় প্রভাব ফেলেছে।
সিলেটের পর কুমিলায় বসবাস। চার বছর। সেখানে নবাব ফয়জুন্নেসা স্কুলে মা শিক্ষকতা করতেন। কুমিল্লায় মনজুররা থাকতেন চমৎকার পরিবেশে। বাড়ির একদিকে রানীর দিঘী, অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া কলেজ। রানীর দীঘিতে মনজুর সাঁতার কাটতেন। কোর্ট বাড়িতে গিয়ে পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতেন। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ততা ছিল। বলা যায়, তখন ছিল মনজুরের পানি ও ডাঙার জীবন। ...কুমিলায় প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ছিল মনজুরের। ছিল অবারিত মাঠ। সেখানে প্রিয় খেলা ক্রিকেটের শুরু।
মা যেহেতু ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, সেহেতু তাঁর কাছেই মনজুরের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। আর তিনি ছিলেন মনজুরের ভাষায় ‘উত্তর আধুনিক মানুষ’। ছেলেকে পড়াশোনায় চাপ দিতেন না, পড়লে পড়বে, না পড়লে না। এই জন্য মনজুর মনের আনন্দে পড়তেন। নানা ধরনের বই। এটি কাজে দিয়েছিল। আর ছোটবেলা থেকেই মনজুরের অসুখবিসুখ লেগেই থাকত। তাই স্কুলে প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন কুমিল্লায়, একটি প্রাইমারি স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণিতে।
সিলেট শহর ও স্কুলজীবন
১৯৬১ সালে মনজুর সপরিবার আবার ফিরে এসেছিলেন জন্মভূমি সিলেটে। সিলেট তখন ছিল অসাধারণ শহর। সাইকেলে চড়ে সেই প্রিয় শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন মনজুর। শহরের নানা মাঠে ক্রিটে খেলতেন। এক সাক্ষাৎকারে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন, এই সময়ের ছেলেরা খেলাধুলা তেমন করে না বলেই কিশোর অপরাধ বাড়ছে। আরও বলেছেন, খেলাধুলার মাঠে যে বন্ধুত্ব হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। যা হোক, মনজুরের স্কুলে যেমন ক্রিকেট টিম ছিল তেমনি ছিল পাড়াতেও। ফলে সেই কিশোর বয়সে শুধু পাড়ায় নয়, অন্য পাড়াতেও ক্রিকেট খেলতে যেতেন তিনি। ভাড়াটে খেলোয়াড় হিসেবে। অর্থ পেতেন সামান্যই। দুই আনা। সেটি খরচ হয়ে যেত বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াতে।
সিলেটে ভর্তি হয়েছিলেন দুর্গাকুমার পাঠশালায়। এখানেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শিক্ষার ভিতটা তৈরি হয়েছিল, এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন। এরপর মনজুর ভর্তি হন সিলেটের সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করেন, দুটি বিষয়ে লেটারসহ।
কলেজজীবন
মাধ্যমিক তথা এসএসসি পাশ করার পর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ভর্তি হন সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ তথা এমসি কলেজে। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী কলেজটি শহরের টিলাগড় এলাকায় অবস্থিত এবং বৃহত্তর সিলেটের সবচেয়ে পুরোনো ও শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন।
এমসি কলেজে পড়ার সময়ই সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম রাজনীতির সঙ্গে কিছুটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সেই সময় এই বিষয়ে দেশের নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এমনই এক সফরে তিনি ওই বছরের ১২ মার্চ সিলেট আসেন। তখন বঙ্গবন্ধুকে সামনা-সামনি দেখেন মনজুর। তাঁর বক্তৃতা শোনেন। এটি রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করে তোলে মনজুরকে। তিনি দেশ, রাজনীতি আর সেই সময়ের পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখতে শুরু করেন। তখন মনজুরের বন্ধুদের বড় ভাইয়েরা সক্রিয় রাজনীতি করতেন। তারা একদিন বললেন, “তোমাদের মিছিলে আসতে হবে না, আন্দোলনে যোগ দিতে হবে না, তোমরা শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবে।” আসলে সেই সময়ে যারা রাজনীতি করতেন, তারা আদর্শের রাজনীতি করতেন। তাই বন্ধুদের বড় ভাইদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন মনজুর এবং তাঁর বন্ধুরা।
বিশ্ববিদ্যালয়জীবন এবং ১৯৭১
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬৮ সালে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পালা। তাই তিনি রসায়নে ভর্তি হওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। পথে বাসের মধ্যে শার্টের একটি বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই বোতামটি ছিল মনজুরের পকেটে। ফলে ভাইবা পরীক্ষা দেওয়ার সময় ফ্যানের বাতাসে বুকের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। সেই সময় যে শিক্ষক প্রশ্ন করছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন মনজুর বেয়াড়া টাইপের ছেলে। তিনি ওই শার্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নেতিবাচক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর এই কথাটি যে সত্যি নয়, তিনি যে বেয়াড়া টাইপের নন, সেটি জানিয়ে প্রকৃত অবস্থাটি ব্যক্ত করেছিলেন মনজুর। পকেট থেকে শার্টের বোতামটি বের করে দেখিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। রসায়ন বিভাগের সেই শিক্ষকের মনের বরফ তো গললই না, তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাই রসায়ন বিভাগে আর ভর্তি হওয়া হলো না মনজুরের।
বিষণ্ন মনে মনজুর গেলেন বিখ্যাত সাংবাদিক, এদেশের ইংরেজি সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, ডেইলি স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী তথা এস এম আলীর কাছে। তিনি সব শুনেটুনে বললেন, “ভালোই হয়েছে। সাংবাদিক হও। তুমি ইংরেজি পড়ো। ইংরেজি পড়লে সারা বিশ্ব তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।” মনজুর রাজি হলেন। এস এম আলী রাজি করালেন মনজুরের বাবা-মাকেও। ফলে মনজুর ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। যেহেতু ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়তে আনন্দ পেতেন, পাঠ্যবিষয়ের বাইরেও প্রচুর সাহিত্যের বই পড়তেন, আর এ বিষয়ে মায়েরও ছিল সমর্থন। তাই ইংরেজি সাহিত্য তিনি পড়তে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে। ভালোবেসে। সেই সময় দেশ তো বটেই পুরো ঢাকা শহরের পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে ছাত্র-জনতা। মিছিল, কলাভবনের বটতলায় সমাবেশ ও বক্তৃতা লেগেই আছে। সেই সময় ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছিলেন মনজুর নিজেও। তাই ক্লাস শেষে মিছিলে ছুটে যেতেন; বটতলার সমাবেশে যোগ দিয়ে ছাত্রনেতাদের বক্তৃতা শুনতেন।
অন্যদিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গেও মনজুর সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের শরিফ মিয়ার দোকানে যেমন সহপাঠী-বন্ধুদের সঙ্গে বিরিয়ানি খেতেন তেমনই সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলোচনাও করতেন। একই অবস্থা ছিল টিএসসির আড্ডায়। আবার মধুর ক্যান্টিনে হতো রাজনীতির আড্ডা। অন্যদিকে আর্ট কলেজে আড্ডা দিতেন সেখানকার শিক্ষার্থী, বন্ধু মারুফ আহমেদ (স্বনামধন্য অভিনেতা ইনাম আহমেদের ছেলে)-এর সঙ্গে। তখন কাছ থেকে দেখেন জয়নুল-কামরুল-সফিউদ্দিনকে। চিত্রকলা এবং চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে। হাতে-কলমে শিখেন এচিং এবং উডকাট কীভাবে করতে হয়। এইসব বিষয় পরবর্তী সময় চিত্রকলা সমালোচনায় কাজে লেগেছিল।
প্রথম বর্ষে পড়ার সময় দেয়াল পত্রিকা যেমন বের করেছেন তেমনই সৈয়দ আনোয়ারুল হক এবং শান্তনু কায়সারের সঙ্গে ‘অর্কেস্ট্রা’ নামে একটি পত্রিকাও বের করেছিলেন। পত্রিকাটির একটি মাত্র সংখ্যাই বের হয়েছিল এবং তাতে ছিল যত্ন ও আন্তরিকতার ছোঁয়া। বিভিন্ন একুশে সংকলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন মনজুর। না, তখনো জোরেশোরে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হন নি তিনি। তবে মাথার ভেতর চিন্তা জন্মেছিল। পরে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লাইব্রেরিতে গিয়ে নানা বিষয়ের বই পড়েছেন মনজুর। সূর্যসেন হলের ছাত্র ছিলেন। তাই হলের কিছু দায়-দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে।
এক পর্যায়ে দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় ছিলেন মনজুর। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণও শুনেছিলেন। তবে ১৭-১৮ মার্চে চলে গিয়েছিলেন সিলেটে। বিবিসি আর আকাশবাণীর সংবাদে জানতে পারেন ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ঢাকাতে সংঘটিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের কথা। তারপর মর্মান্তিক এক ঘটনার কথা শুনতে পান। তাঁর ছোট মামাকে বিহারিরা তুলে নিয়ে মিলিটারিদের হাতে তুলে দিয়েছে। তিনি নিহত হয়েছেন। এই সংবাদে মনজুরের মা রাবেয়া খাতুন ভেঙে পড়েন। তাই সারাটা জীবন মনজুরের মনে একটি খেদ ঘুরপাক খেয়েছে। সেটি হলো, একাত্তরে তিনি তো টগবগে তরুণ ছিলেন। কেন তিনি অন্য সব তরুণের মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না ? আসলে মায়ের কারণেই তিনি যুদ্ধে যেতে পারেন নি। যা হোক, যুদ্ধে না-যাওয়ার গ্লানিকে ভোলার জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মনজুর মুক্তিযুদ্ধের এমন সব গল্প লিখেছেন, যেখানে প্রান্তিকদের মধ্যে যারা প্রান্তিকÑসেইসব মানুষের সংগ্রাম, একাত্তরে তাদের সাহসী ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। যেমন চা-বাগানের কুলিদের মুক্তিসংগ্রাম। আর এইসব গল্প তিনি লিখেছেন সত্যি ঘটনা অবলম্বনে। এভাবেই তিনি পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
১৯৭২ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিএ সম্মান পরীক্ষায় পাশ করেন। এম এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। এই দুই পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি যথাক্রমে পোপ স্মারক স্বর্ণপদক ও ফজলুর রহমান স্মারক স্বর্ণপদক লাভ করেন।
১৯৭৬ সালে মনজুর বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যান কানাডার কিংস্টন শহরের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে চার বছর পড়াশোনা শেষে লাভ করেন পিএইচডি ডিগ্রি, ইয়েটস-এর কবিতায় ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের দর্শনের প্রভাব বিষয়ে।
শিক্ষকতা
১৯৭৪ সালে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে।
শিক্ষক হিসেবে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন অসাধারণ। তিনি এক্ষেত্রে কোনো ফাঁকি দেন নি। সময় মেনে চলতেন সব সময়। সব শিক্ষার্থীর প্রতিই ছিল তাঁর সমান নজর। এমনকি শেষ বেঞ্চে যারা বসতেন, তারাও ঠিকমতো তাঁর লেকচার শুনছে এবং অনুধাবন করছে কি না এ বিষয়ে তিনি সজাগ থাকতেন। আর ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া তিনি কোনো ক্লাস নিতেন না।
শিক্ষকতার শুরুতে অনার্স প্রথম বর্ষ এবং প্রিলিমিনারির একটি ক্লাস নিতে হতো সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে। অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে তিনি ভীষণ আনন্দ পেতেন। তবে প্রিলিমিনারির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। তাদের আস্থা অর্জন করাটা ছিল কঠিন। একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আর সেই চ্যালেঞ্জটা মনজুর নিয়েছিলেন। তাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন।
১৯৭৬ সালের জুনে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইডি করতে যান মনজুর। ছিলেন চার বছর। সেখানে জানাশোনা আর পড়াশোনার দিগন্তটা প্রসারিত হয়েছিল। আর সেটি ঢাবি’র শিক্ষার্থীদের পড়ানোর ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। অন্যদিকে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন আন্তরিক, বন্ধুর মতো। ক্লাসে কোনো কোনো শিক্ষক গেঞ্জি পরে আসতেন। টেবিলে পা তুলে ক্লাস নিতেন। মনজুর ‘স্যার’ বললে তারা আপত্তি করতেন। নাম ধরে ডাকতে বলতেন। এই যে ছাত্র-শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, এই বিষয়টি মনজুরের মনে দাগ কেটেছিল। ফলে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি ঢাবি’র ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে লাগলেন।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মেহেদী আরিফ লিখেছেন : “মেধার সঙ্গে যদি জীবনের সংযোগ ঘটাতে না পারা যায়, তবে সেই মেধা কোনো কাজেই আসে না, কথাটি প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আমার শিক্ষাগুরু। মনজুরুল স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এসএমআই নামে সমধিক পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ-যাবৎ যত মেধাবী শিক্ষক তৈরি করেছে, তার মধ্যে এসএমআই একজন উর্বর শিক্ষক। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে এসএমআইর অনেক ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি।...ক্লাসে স্যার একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমার ক্লাসে কোনো অর্ধঘুমন্ত শিক্ষার্থীকে দেখতে চাই না, ঘুমাবে না হয় ক্লাস করবে।’ স্যারের ক্লাসে ঘুম! প্রশ্নই আসে না। তিনি দুপুরের পরে ক্লাস নিলেও যথারীতি শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীতে পরিপূর্ণ থাকত। স্যারের অসাধারণ ক্লাস করার জন্য আমরা চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় থাকতাম। স্যার দারুণভাবে মর্ডানিজম ও পোস্টমর্ডানিজম পড়াতেন। পড়িয়ে ছিলেন ক্রিস্টোফার মার্লের অনবদ্য নাটক ‘ডক্টর ফস্টাস’। আজও স্যারের ক্লাসগুলোর কথা মনে পড়ে ভীষণ।” (প্রিয় শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম/ মেহেদী আরিফ, পাতাদের সংসার, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সংখ্যা, সম্পাদক হারুন পাশা, পৃ.২১)।
শুধু ক্লাসেই পড়িয়ে মনজুর ক্ষান্ত হতেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা প্রয়োজনেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর এক ছাত্রী মার্জিয়া লিপি লিখেছেন : “দুপুরে ক্লাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে আসে, তাদের বিবিধ প্রয়োজনে ও নানা পরামর্শের জন্য। আনন্দের সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্নভাবে স্যার এ কাজটি করে আসছেন দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে।” প্রিয় শিক্ষক মনজুর স্যার/ মার্জিয়া লিপি, পাতাদের সংসার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০)।
দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ২০১৭ সালের জুনে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ যোগ দেন। ২০২০ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইমেরিটাস অধ্যাপক ঘোষণা করে।
প্রাবন্ধিক-গবেষক সত্তা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছোটবেলা থেকেই ভীষণ পড়ুয়া। এক্ষেত্রে তাঁর মায়ের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাও ছিল। ফলে গল্প-উপন্যাসসহ নানা বিষয়ের বই পড়তেন। সেই পাঠাভ্যাস আরও প্রগাঢ় হয় শিক্ষকতা করার সময়; কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সময়। অন্যদিকে মনজুর দ্রুত পড়তে পারতেন। ঢাবি’র ইংরেজি বিভাগের একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে শিখেছিলেন স্পিড রিডিং কৌশল। কানাডায় এই বিষয়ে একটি কোর্সে অংশগ্রহণও করেছিলেন। আর সেখান থেকে ১৯৮১ সালে ফেরার সময় জাহাজে করে প্রচুর বই ও পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষকেরা অনুদানও দিয়েছিলেন। অন্য কথায়, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য ভান্ডার তিনি কানাডা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তাই সেই সময় তাঁর একাডেমিক লেখার পাশাপাশি সাহিত্য সম্পর্কিত লেখালেখিও গতি লাভ করেছিল। তখন তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতায়, সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাতের অনুরোধে। কলামটির নাম ছিল ‘অলস দিনের হাওয়া’। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত ‘পরিক্রমা’ ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত ‘কণ্ঠস্বর’ পত্রিকায়ও লিখতেন।
দৈনিক সংবাদে ‘অলস দিনের হাওয়া’ কলামটির আড়াই থেকে তিন শ’ কিস্তি ছাপা হয়েছিল। যার বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। ৪৮টি নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে পরে শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে একটি গ্রন্থ বের হয় ‘অলস দিনের হাওয়া’ নামেই। গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে এক মলাটে বিশ্বসাহিত্য পাঠ হিসেবে বিবেচিত হবে। গ্রন্থে ঠাঁই পাওয়া প্রবন্ধগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর নানান দেশের নানান কালের সাহিত্য-সাহিত্যিকের সমালোচনামূলক লেখা, ব্যক্তিগত জীবনপাঠ, বিশ্বসাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক-কবিদের পুরস্কারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, পুরস্কার প্রাপ্তি-উত্তর কারণ সন্ধান ইত্যাদি। আর শুধু গল্প-উপন্যাস-কবিতা নয়, চিত্রকলাবিষয়ক প্রবন্ধও ঠাঁই পেয়েছে এখানে। আর প্রবন্ধগুলো বাঙালি পাঠকের সামনে লেখক-কবিদের পরিচিতিমূলক লেখা নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের নতুন পাঠ কিংবা নতুনভাবে পাঠের স্বাদ পরিবেশন করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। লাতিন আমেরিকার সাহিত্য কিংবা সাহিত্যিকদের প্রতি যে তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল, সেটি বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই তিনি গুন্টার গ্রাস, মারিয়ো বার্গাস ইয়োসা, গাসির্য়া মার্কেজ, বোর্হেস, অক্টাভিও পাজ, অগাস্টো রোয়া বাস্তোস প্রমুখ সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন। আর লিখেছেন শুধু ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে নয়, সমকালীন বিশ্বসাহিত্যে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের জনপ্রিয়তা-গ্রহণযোগ্যতা ও পুরস্কারের মানদণ্ডে স্বীকৃতিপ্রাপ্তির কারণে। আবার ‘অলস দিনের হাওয়া’ পাঠ করলে কোনো কোনো পাঠকদের মনে হতে পারে যে, লেখকের মনোযোগ বোধহয় চেক সাহিত্যের দিকেই বেশি। আবার সালমান রুশদী, নাইপল, নয়নতারা সাইগলও ঠাঁই পেয়েছেন ‘অলস দিনের হাওয়া’-য়। আর এইসব প্রবন্ধ লেখা হয়েছে পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভঙ্গিতে নয়, বরং মজলিসে গল্প বলার ভঙ্গিতে। অন্য কথায়, এইসব লেখা একাডেমিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ নয়, তাতে টিকা-টিপ্পনী-পাদটিকা নেই কিন্তু রয়েছে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য তথ্য, যা সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের পঠন-অভিজ্ঞতা ও প্রতীতির প্রকাশ।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘নন্দনতত্ত্ব’ (১৯৮৬)। বাংলাদেশে এ বিষয়ে লেখা প্রথম বই। গ্রন্থটিতে রয়েছে সাতটি অধ্যায়। যেমন, ‘নন্দনতত্ত্ব’, ‘নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন’, ‘শিল্পে রূপ ও রস’, ‘শিল্পের সুন্দর ও অসুন্দর’, ‘শিল্পের প্রকাশ ও ভাষা’, ‘শিল্পবিচার’, ‘হৃদয়ের সঙ্গে যোগ’। অধ্যায়গুলোর নামের মধ্যেই ফুটে উঠেছে সেগুলোর বিষয়বস্তু। আর ‘শিল্প বিচার’ প্রবন্ধে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম খুবই চমৎকার একটি কথা বলেছেন, “শিল্পবিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই, চূড়ান্ত কোনো রায় নেই। বস্তুমাত্রই যেমন শিল্পবস্তু নয়, তেমনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মাত্রই শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়া নয়। বিচারকের দায়িত্ব শিল্পবস্তু কেন প্রথমেই শিল্পবস্তু, এর কারণ অনুসন্ধান করা এবং কীভাবে তা শিল্পবস্তুতে পরিণত হলো, এর পরিচয় নির্ণয় করা।” অন্যদিকে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের দৃষ্টিতে ‘হৃদয়ের সঙ্গে যোগ’ হলো, “মানুষের সৃষ্টির সাথে এর সম্পর্ক এবং মানুষের কর্মকাণ্ডেই এর বৈধতা, এসব মিলিয়েই নন্দনতত্ত্ব।”
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের আরেকটি প্রবন্ধগ্রন্থ ‘লেখাজোখার কারখানাতে’। এ হলো শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধান ও কৌতূহলের এক উজ্জ্বল প্রয়াস। হ্যাঁ, এখানে লেখালেখির কলাকৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঠিকই আবার সেই লেখার অবয়বের রূপ-রহস্যেরও উদ্ঘাটন করেছেন তিনি। সংক্ষেপে এই গ্রন্থে রয়েছে শিল্পের সৃষ্টি প্রক্রিয়া, সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, সাহিত্যের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক লেনদেন, বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদল নিয়ে মনজুরের গভীর আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও তাদের রচনা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, পাঠপর্যালোচনা ইত্যাদি। এছাড়া নন্দনতত্ত্ব, আধুনিকতা উত্তরাধুনিকতা, শিল্প-সাহিত্যে রাজনৈতিক দায়, উপনিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ও উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন মনজুর।
শেষে বলা যায়, প্রবন্ধ সাহিত্যে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন সর্বত্রগামী সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ জীবনের নানা বিষয় নিয়ে যেমন প্রবন্ধ লিখেছেন তেমনি লিখেছেন শিল্প-সাহিত্যের অলিগলি নিয়েও।
চিত্রকলার সমালোচক
সাহিত্য নিয়ে লেখার আগেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম চিত্রকলা নিয়ে লেখালেখি করেছেন। ইংরেজি খবরের কাগজ ডেইলি অবজারভার-এর তৎকালীন সহকারী সম্পাদক মনজুরের কাছে একটি লেখা চানÑবিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী পিকাসো মারা যাওয়ার পর। মনজুর তাকে নিরাশ করেন নি। অবজারভারে লিখেছেন পিকাসো সম্পর্কে। ইংরেজিতে। উল্লেখ্য, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বাংলাদেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন, যিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে সমভাবে দক্ষ ছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি এই সময়ের বাংলা গদ্যের সেরা লেখকদের একজন ছিলেন। আর মনজুর খুব বেশি ইংরেজিতে লিখেন নি বা লিখতে পছন্দ করেন নি, কিন্তু যখন তিনি লিখেছেন, তখন তাঁর ইংরেজি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এটি পাঠযোগ্য এবং নান্দনিক।
হ্যাঁ শুধু সাহিত্য নয়, চিত্রকলার সমালোচক হিসেবেও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম খ্যাতি কুড়িয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাহিত্য সাময়িকী এবং গ্রন্থে চিত্রকলাবিষয়ক তাঁর বহু লেখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সাহিত্য সাময়িকী ‘কালি ও কলম’-এর এক লেখায় খুঁজে পাই। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন : “ছবির ভাষার কোনো সুনির্দিষ্ট বাক্য বিন্যাস নেই, মুখের ভাষায় যা আছে; কোনো শব্দভান্ডার নেই, মুখোর ভাষায় যা আছে। প্রশ্ন হলো, এগুলো যদি না থাকে, তাহলে ছবির ভাষা আমরা কীভাবে বুঝি ? এমনকি বিমূর্ত ছবির ?”
চিত্রকলার সমালোচক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হকের ভাষ্য হচ্ছে : “দেশবিদেশের ছবি ও চিত্রশিল্পীদের নিয়ে তাঁর মূল্যায়নগুলো আমাদের জন্য বড় কাজের এক ভান্ডার হয়ে আছে। ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ’ বইতে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের নানা শিল্পীর ওপর দৃষ্টিপাত আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, সেইসঙ্গে বিশ্বের শিল্প জগতের সঙ্গে সেতু তৈরি করে দিয়েছে।”(সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : ভবিষ্যতের স্মৃতিতে/ হামামী কামরুল হক)
বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিমূর্ত ধারার অন্যতম পথিকৃৎ মোহাম্মদ কিবরিয়া; যাঁর সমান অবদান রয়েছে চিত্রশিল্প ও ছাপচিত্রশিল্পে। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ‘মোহাম্মদ কিবরিয়া’ নামের এই গ্রন্থটির সহলেখক সুবীর চৌধুরী। বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।...বাংলাদেশের চিত্রকলা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় মনজুরের লেখা দুটি বই ২০০২ ও ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক ও বোদ্ধামহলে প্রশংসিত হয়েছে।
চিত্রকলাবিষয়ক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বই থেকে একজন পাঠক শুধু চিত্রকলার তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কেই জানতে পারবে না, এর প্রায়োগিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও অবগত হবে। এছাড়া দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের সৃষ্টিশীলতার উৎস ও তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে।
উল্লেখ্য, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের ওল্ডহামে ও ২০০৪ সালে লাহোরে বাংলাদেশি শিল্পকলার দুটি প্রদর্শীর কিউরেটর ছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত শিল্পীসহ অসংখ্যা তরুণ শিল্পীর ওপর পরিচিতিমূলক লেখার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের আর্ট জার্নাল তিনি বাংলাদেশের শিল্পকলা নিয়ে নিয়মিত লিখেছেন। যুক্ত ছিলেন বেঙ্গল শিল্পালয় থেকে প্রকাশিত শিল্পকলাবিষয়ক পত্রিকা ‘যামিনী’-র সঙ্গেও।
গল্পের ভুবন
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রথম গল্প লিখেন বাবা সৈয়দ আমীরুল ইসলামের নির্দেশে। বাবার কর্মস্থল ‘শিক্ষক সমাচার’-এ সেটি প্রকাশিত হয়। এরপর ‘রংধনু’ পত্রিকাসহ আরও কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর গল্পসহ নানা লেখা আলোর মুখ দেখে। তবে সত্যিকার অর্থে তিনি ১৯৭৩ সালে গল্প লিখেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রদায়ক রেজা-ই-করিমের অনুরোধে। বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদৎ হোসেনেরও আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যে, মনজুর তাঁর পত্রিকায় গল্প লিখুন। গল্পটির নাম ছিল ‘বিশাল মৃত্যু’। যা হোক, এরপর ‘বিচিত্রা’সহ আরও কয়েকটি পত্রিকায় মনজুরের গল্প ছাপা হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ শামসুল হক ও আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রশংসা তাঁকে অনুপ্রাণিতও করে। কিন্তু এরপর তিনি গল্প লেখায় দীর্ঘ বিরতি নেন। ১৯৮৯ সাল থেকে আবার গল্প লেখায় মনোযোগী হন, সিরিয়াসভাবে। সেই থেকে মনজুর গল্প লিখে গিয়েছেন বিরামহীন। আর সেইসব গল্প ঠাঁই পেয়েছে তাঁর নানা গল্পগ্রন্থে।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে, স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৯৫), থাকা না-থাকা গল্প (১৯৯৬), কাঁচভাঙ্গা রাতের গল্প (১৯৯৮), অন্ধকার ও আলো দেখার গল্প (২০০১), প্রেম ও প্রার্থনার গল্প (২০০৫), বেলা অবেলার গল্প (২০১২), মেঘশিকারি (২০১৫), সেরা দশ গল্প (২০১৬), তালপাতার সেপাই ও অন্যান্য গল্প (২০১৭), একাত্তর ও অন্যান্য গল্প (২০১৭), বিচিত্রা স্বাদের গল্প (২০১৭), কয়লাতলা ও অন্যান্য গল্প (২০১৯), গল্পসকল প্রথম খণ্ড (২০২০), দেখা অদেখার গল্প (২০২২)।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে রয়েছে, পাতকুয়া, কাঁঠালকন্যা, রেশমি রুমাল, ডিডেলাসের ঘুড়ি, শালবনে জ্যোৎস্না, কুসুম্বাপুর আবিষ্কার, পিণ্ডমেঘের আলো, তাজমহল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রয় বিক্রয়, জলপুরুষের প্রার্থনা, দুই খুনী, অপরাহ্নের গল্প, বাক্স হাতে একজন, ফেরিঘাটের রান্নাবান্না, অমরত্ব, ব্রাজিলের জার্সি, চশমা, তালপাতার সেপাই, গনি মিয়ার পাথর, কাঁচভাঙ্গা রাতের গল্প, একাত্তর, লোকটা, সম্মতি, বাঁদর, দুই সাক্ষী, কয়লাতলা ইত্যাদি।
বাংলা ছোটগল্পকে সমকালীন ধারায় পৌঁছে দিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম সৈয়দ মনজরুল ইসলাম। অবশ্য সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পচয়ন শাশ্বত বাঙালির। অন্য কথায়, তাঁর অধিকাংশ গল্পে গল্প বলা ও গল্প লেখার ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। এমন চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায় মার্কেস, বোর্হেস-এর মতো আরও কয়েকজন বিখ্যাত গল্পকারের গল্পে। মোটা দাগে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। সেগুলো হলো : ১. তিনি যতটা না গল্প লেখেন, তার চেয়ে বেশি গল্প বলেন; ২. তাঁর গল্প জাদুবাস্তববাদী; ৩. তাঁর গল্প উত্তরাধুনিক গল্পের দৃষ্টান্ত।
এবার মনজুরের গল্পের আরও কয়েকটি দিক বলা যাক। যেমন, তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র থেকে খুবই সহজে চলে যান তাদের যাপিত জীবনের অন্ধকারে। আর অনেক সময় তিনি পাঠকের ওপরই ছেড়ে দেন গল্পটির সমাপ্তির দায়িত্ব। অবশ্য এটি রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ হইয়া হইল না শেষ’-এর মতো নয়। আর মনজুরের গল্পে লক্ষ করা যায় বাস্তবতা ও জাদু। তবে এ জাদু যতটা জাদুবাস্তববাদী, তার চেয়ে অধিক অতিপ্রাকৃত ও ফ্যান্টাসি। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্প সম্পর্কে মনোজিৎকুমার দাশের ভাষ্য হচ্ছে : “বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি তাঁর লেখা প্রতিটি গল্পই সমকালীন অনুষঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি সমাজের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যক্তিস্বার্থ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পগুলোতে।” (সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সাহিত্যে বহুমাত্রিকতা/ মনোজিৎকুমার দাস, পাতাদের সংসার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬)
উপন্যাসের জগৎ
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের পছন্দের মাধ্যম ছিল ছোটগল্প। তিনি ছোটগল্প লিখতেই বেশি ভালোবাসতেন। অবশ্য তাঁর উপন্যাসও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেখানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের সম্পর্কও। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো হলো : আধখানা মানুষ, দিনরাত্রিগুলি, আজগুবি রাত, তিন পর্বের জীবন, যোগাযোগের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক (সহযোগী লেখক ব্রাত্য রাইসু), কানাগলির মানুষেরা, শকুনের ডানা।
‘আধখানা মানুষ’ মনজুরের প্রথম উপন্যাস। এখানে আমাদের গৌরবজনক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চাল”িত্র এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল লতিফ, পদ্মার ভাঙনে যার পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সে নিজেকে আবিষ্কার করে আধখানা মানুষ হিসেবে। উপন্যাসের আখ্যানের মধ্য দিয়ে লেখক এটাই বলতে চেয়েছেন যেন, এদেশের ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে কেবলই সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। এই সমস্যা বা সংকট থেকে উত্তরণহীনতা তথা নৈরাশ্য মানুষের নিয়তি বা ভাগ্যলিপি।
‘দিনরাত্রিগুলি’ উপন্যাসে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এক ব্যক্তির, সমাজবিকাশের পিএইচডির মার্জিত ভদ্রলোকের গল্প বলতে চেয়েছেন। পোড়খাওয়া ওই মানুষটি তার ইতিহাস বা গল্পটি শুনিয়েছে চিকিৎসার আর লেখককে। অবশ্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে লোকটি চিকিৎসকের কাছে যায় নি।, কেননা নিজের সমস্যা সে ভালোই জানে। জানে অতীতে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর দায় তার নয়, যদিও সে ফলভোগী। উপন্যাসটি সম্পর্কে মোহাম্মদ আজমের ভাষ্য হচ্ছে : “দিনরাত্রিগুলি উপন্যাস নানা কারণে আকর্ষণীয়। গল্পের আকার বা প্লটে নতুনত্ব আছে। ঝকঝকে স্মার্ট ভাষার সৌন্দর্য আছে। আরও আছে ব্যক্তির গল্পে সমাজ-প্রতিবেশকে যথাসম্ভব এঁকে দেওয়ার সাফল্য। কিন্তু বাংলাদেশের সমসাময়িক কথাসাহিত্যে এ উপন্যাসের বিশেষ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের এক নিরাসক্ত কথকতায়। আমাদের বলা হয়েছে, গল্পকথক ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ গল্প-বলিয়ে। আরও জানানো হয়েছে, নিজের গল্প নয়, সে বলতে পছন্দ করে অন্যের গল্প। মুক্তিযুদ্ধে নিজের অংশগ্রহণের যে অভিজ্ঞতা সে বর্ণনা করেছে, তা এক অর্থে অন্যের গল্পই বটে। অন্যের বলেই নিজের। দশের সঙ্গে একের একাকারতা আর তার মধ্যেই একের স্বাতন্ত্র্য, এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক প্রস্তাব।” (দিনরাত্রিগুলি : সামষ্টিক যেভাবে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে/ মোহাম্মদ আজম, পাতাদের সংসার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-৬১)
‘আজগুবি রাত’ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রিয় উপন্যাস। এটি তাঁর অন্য সব উপন্যাস থেকে আলাদা। ভাষা, উপস্থাপনা সব দিক থেকেই। শুধু তাই নয়, এখানে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ ঘটেছে, অলংকারেরও শেষ নেই। এখানে নদীতে ভেসে আসা এক কাটা হাতকে ঘিরে উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে, নানা ভুতুড়ে ঘটনার জন্ম দিয়েছে। পাশাপাশি এটি একই সঙ্গে প্রবল শক্তিকে কখনো মাঝির ছেলেকে পরীর স্বপ্ন দেখায়; হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার স্পন্দিত হৃদয় দেখায় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক লাকি খানকে; কোনো এক প্রেমিকার হাত হিসেবে চিহ্নিত করে এক সচিব; শিক্ষক তার সততার স্বাক্ষর দেখতে পায়। বলা যায়, কাটা হাতটা যেন সবার বিবেক ও মানস জগতকে জাগিয়ে তোলে। উপন্যাসটি সম্পর্কে শামীম রেজার ভাষ্য হচ্ছে : “...‘আজগুবি রাত’-এর আখ্যান কোনো আধিপত্যের অধীন যেমন নয়, তেমন নয় আধিপত্যের স্পষ্ট বিরোধী কোনো বিষয়, মূলত এই স্বাধীন ব-দ্বীপের দক্ষিণের উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গল্প এক রাতের মধ্যে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।” (বাস্তবের জাদু, জাদুর বাস্তব ‘আজগুবি রাতে’র আখ্যান/শামীম রেজা, পাতাদের সংসার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০)
‘তিন পর্বের জীবন’ হলো এক সাংবাদিক কাম এক রাজনৈতিক দলের মানুষ শাহীন-এর জীবনের আখ্যান। বাস্তব ও স্বপ্নে মার খাওয়া মানুষের উপাখ্যান।
‘কানাগলির মানুষেরা’ হলো যতটা না মানুষের গল্প, তার চেয়ে বেশি মেসের কাহিনি। অন্য কথায়, মেস জীবনকে ঘিরে কয়েকজন মানুষের জীবনগাথা।
‘শকুনের ডানা’ উপন্যাসে মনজুর হাওর অঞ্চলে কানা শকুনের বসবাস এবং মানুষ শকুনের রূপবৈচিত্র্য ও ক্ষতিসাধনের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। অন্য কথায়, এটি হলো হাওর অঞ্চলের সৌন্দর্য রক্ষা ও প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ বাঁচানোর তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন।
এছাড়া সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে মিলে লিখেছেন আরেকটি উপন্যাস, ‘যোগাযোগের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক’।
টিভি ও মঞ্চনাটক
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিটিভি, চ্যানেল আই এবং একুশে টিভির জন্য অনেকগুলো নাটক লিখেছেন। এগুলোর বেশির ভাগই মৌলিক, তবে কয়েকটি নাটক রবীন্দ্রনাথ ও একটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের নাট্যরূপ। তা ছাড়া মঞ্চনাটকের জন্য তিনি কয়েকটি অনুবাদ ও মৌলিক নাটকও লিখেছেন। তাঁর ‘ভুবনের ঘাটে’ নাটকটি ২০০৪ সালের শ্রেষ্ঠ মঞ্চনাটক হিসেবে বাচসাস পুরস্কার লাভ করেছিল।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিজ্ঞাপনচিত্রের স্ক্রিপ্টও লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গার ওয়াশিংমেশিনের বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁর লেখা সেই সংলাপটি, ‘এত কষ্ট জীবন নষ্ট’, নিশ্চয়ই এখনো অনেকের কানে বাজে।
বিতর্ক দলের মডারেটর এবং
১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দলের মডারেটর হিসেবে বিতর্কচর্চাকে পুনর্জীবিত করতে ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংরেজি সংসদীয় বিতর্ক অনুষ্ঠানে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর স্পিকারের ভূমিকা পালন করেন এবং সারাদেশে ইংরেজি ভাষায় বিতর্ককে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রাখেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দলের মডারেটর হিসেবে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া-সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে দলের নেতৃত্ব দেন।
ব্যক্তিগত জীবন
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালের জুন মাসে সানজিদা মইনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মিসেস ইসলাম ইউনিসেফ, বাংলাদেশ-এ প্রোগ্রাম কম্যুনিকেশন উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান শাফাক ইসলাম (জন্ম ১৯৮০) যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্ডারগ্রাজুয়েট পড়াশোনা শেষ করে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ল’ স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং ২০০৫ সালের মে মাসে জে ডি ডিগ্রি লাভ করেন।
শেষ যাত্রায় প্রাণ ও প্রকৃতির অশ্রুবিসর্জন
এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের মায়া ছেড়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম না-ফেরার দেশে চলে গেছেন গত ১০ অক্টোবর, বিকেলে। ১১ অক্টোবর তাঁর মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে আনা হয়। এখানে ইংরেজি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ফুল দিয়ে মনজুরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
এরপর মুষল ধারার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, বিশিষ্টজন ও সর্বস্তরের মানুষ। বলা যায়, কাকভেজা হয়ে সবাই প্রিয় মানুষটিকে বিদায় জানান। এ সময় অনেকেরই চোখ ছিল অশ্রুসজল। তাদের কান্না ও প্রকৃতির বৃষ্টি একাকার হয়ে গিয়েছিল।
শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদে জোহরের নামাজের পর তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে মিরপুরের বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়, বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে।
শেষ কথা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন প্রজ্ঞা আর মুক্ত মনের মেলবন্ধন। শুধু শিক্ষা, সাহিত্য আর শিল্প বিষয়েই তাঁর ভাবনা ছিল না, দেশ, সমাজ ও রাজনীতি নিয়েও তিনি ভাবতেন। কথা বলতেন। তবে সেইসব কথায় কোনো দলীয় রাজনীতির গন্ধ থাকত না। এ বিষয়ে তিনি নির্মোহ ও নিরপেক্ষ ছিলেন।
তিনি ছিলেন একজন বিরল গোত্রের আলোকিত মানুষও। মৃত্যুর পরও তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে। আর আমাদের কাছে, ‘অন্যদিন’ পরিবারের একজন হিসেবে, ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে’।
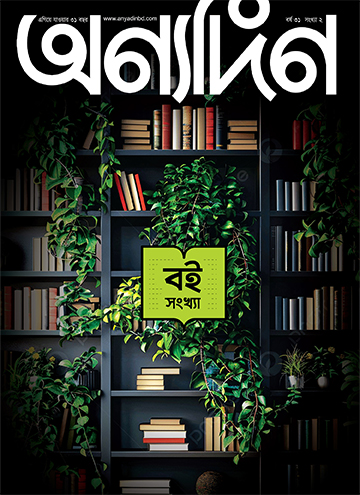





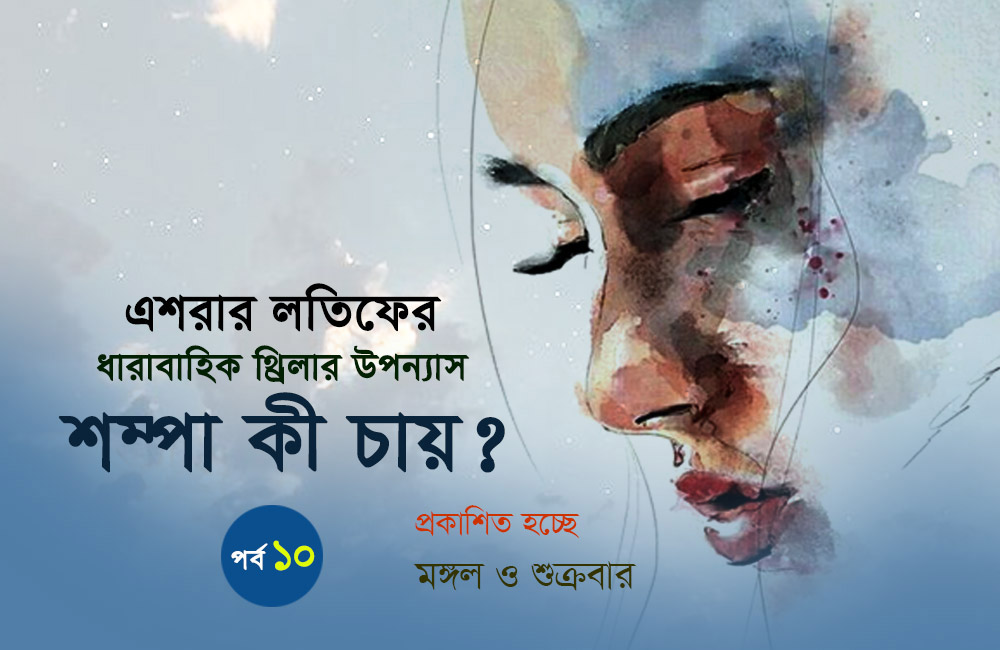






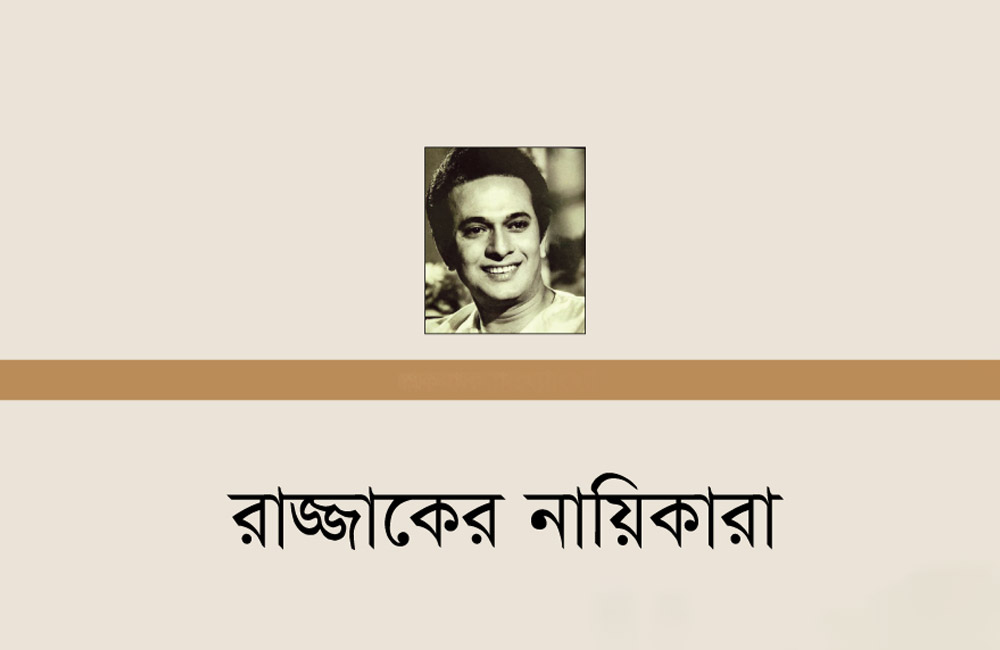

Leave a Reply
Your identity will not be published.