শারমিনদের বাড়ি খুঁজে পেতে তেমন সময় লাগল না। ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভার ছিল অল্প বয়সী একটা ছেলে। দেখেই বোঝা যায় লেখাপড়া জানা, স্মার্ট। উত্তরা এলাকায় এসে ঠিকানা বলতে প্রায় একবারেই নিয়ে এলো বাড়ির কাছে।
কিন্তু বাড়ির একেবারে কাছে আমি নামলাম না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামলাম। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দশটা টাকা টিপসও দিলাম। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে প্রথমে শারমিনদের বাড়ির দিকে তাকালাম। ছবির মতো সুন্দর দোতলা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে রাস্তা, রাস্তার ওপারে লেক। লেকের পারে সবুজ ঘাস, নানা রকমের ফুল পাতাবাহারের বাড়ি। আর বেশ অনেকখানি জায়গা ছায়া করে রাখা একটা বকুলগাছ। বসন্তকাল বলে পাতাগুলো যেন একটু বেশি সবুজ, শীতভাব কাটিয়ে সতেজ হয়ে উঠেছে। দুপুর শেষ হওয়া রোদে ঝিমঝিম করছিল চারদিক। হু-হু করা একটা হাওয়া বইছিল। সেই হাওয়ায় চারদিকে তাকাতে তাকাতে শরীরের খুব ভেতরে কেমন কাঁপন লাগল আমার।
এই জায়গাটাই তো!
সাত বছরে অনেক বদলেছে। বাড়ির পর বাড়ি হয়ে ভরে গেছে লেকের দু’পার। বকুলগাছটা তখন শিশু। লেকের পারে ফুল পাতাবাহারে ঝোঁপঝাড় এতটা ছড়ায় নি। পায়ের তলার ঘাস মাত্র গজাচ্ছিল।
এই জায়গাটাই তো!
শারমিনদের বাড়ির কথাও তারপর মনে পড়ে আমার। মাত্র তৈরি হচ্ছিল। নাকি একতলা হয়ে গিয়েছিল, দোতলার কাজ চলছে? বাড়ির সামনে ইটের পাঁজা, বালি, সুরকি, রড আর কাঠবাঁশ।
ভেতরে ভেতরে আমি তারপর দিশেহারা হয়ে গেলাম। এতকাল পর নিয়তি আমাকে এ কোথায় টেনে আনল! শারমিনের জন্য কোথায় এসে দাঁড়ালাম আমি!
আমার চোখে কী রকম একটা ঘোর লেগে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরপায়ে হাঁটতে থাকি আমি।
মনে পড়ে। আমার সব মনে পড়ে।
আমি থাকতাম নানাবাড়িতে। বড় খালার কাছে। নানাবাড়িটা ছিল তিন শরিকের। আমার নানা আর তাঁর দুইভাই। নানা ছিলেন বড়। আমার জন্মের বহুকাল আগে তিনি মারা যান। নানি মারা যান আমার বড়ভাইয়ের জন্মের কয়েকমাস পর।
আমার কোনো আপন মামা ছিল না। মা-খালারা তিনবোন। বড়খালা নিঃসন্তান, বিধবা। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। স্বামীর দিককার জায়গা-সম্পত্তি কিছুই পান নি। থাকতেন বাপের বাড়িতে। তিন শরিকের বাড়িটির দক্ষিণের অংশ আমার নানার। সেখানে অনেকগুলো কামরাওয়ালা বিশাল একটি টিনের ঘর। পুবপাশে বনেদি ধরনের রান্নাঘর। রান্নাঘরের লাগোয়া দক্ষিণে মাঝারি ধরনের একটা পাটাতান করা ঘর। এই ঘরটি সব সময় তালাবদ্ধ থাকত। থাকার লোক ছিল না।
বড়ঘরটির সামনের দিকে একটি দরজা। সেটা উত্তরমুখী। ওই দরজা দিয়ে বেরুলে উঠোন। উঠোনের দু’পাশে মেজোনানা, ছোটনানার ঘরদুয়ার। দুই শরিকের মাঝখান দিয়ে উত্তরে বারবাড়ি, তারপর শস্যের মাঠ। বড়ঘরের সামনের দরজায় দাঁড়িয়েই আলমগীর মামাকে মার খেতে দেখেছিলাম আমি। এসব আমার সেই বয়সের কথা।
বড়ঘরের দক্ষিণে ছিল আম, জাম আর নিমগাছের বিশাল বাগান। সারাদিন পাখি ডাকত সেই বাগানে, সুমসাম নির্জনতায় হু-হু করা হাওয়া বইত। এসবের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র মানুষ। বড়খালা, আমি আর বাড়ির বহুকালের পুরনো কাজের লোক আলফু।
বিলের দিকে বহু ধানের জমি ছিল নানার। বিক্রি হতে হতে আমার কিশোরকালে পাঁচ-সাত কানীতে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজের চাষবাষের লোকবল ছিল না বলে জমিগুলো ছিল বর্গা দেয়া। একচাষের জমি। অর্থাৎ বছরে ফসল ফলত একবার। আমন আউসের সঙ্গে তিল কাউনও কেনা হতো। কিছু তিল, কিছু কাউন ভাগে আমরা পেতাম আর তিনচারজন মানুষের বছর চলার পরও বিশ-পঞ্চাশ মণ ধান বিক্রি করা যেত। সেই টাকায় খালার সামান্য বাজার, তেল, নুন-দুধ এসব কেনা চলত। শাক-সবজি তো বাগানের দিকেই ফলত। লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, শিম, ঝিঙা, কহি নামের বান্দরলাঠি টাইপের লম্বা একটা পানসে ধরনের সবজি, ধুন্দুল। বছরভর কোনো না কোনো সবজির মাচা আমাদের বাগানে থাকতই। সেইসবের তদারক করত আলফু আর সংসারের মাছটা ধরত গ্রামের খালবিল, পুকুর থেকে। সে এক শান্ত, নির্জীব জীবন।
খরালিকালে তিলফুল ফুটত। তিলের মধু নিতে মৌমাছিরা এসে গুনগুন করত তিলক্ষেতে। কলকের মতো ছোট্ট ফুলের ভেতর ঢুকে যেত মধুর লোভে। আমি আর আলমগীর মামা বাড়ির সামনের বড়ক্ষেতে গিয়ে তক্কে তক্কে থাকতাম। কখন মৌমাছি ঢোকে তিলফুলে। ঢুকলেই টুক করে ফুলের মুখটা টিপে ধরতাম। আমাদের দুজনার হাতে দুটো ফুল। তার ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছে মৌমাছি। সেই বন্দিদশায় কোথায়, তখন ভয়ঙ্কর মৌমাছির বিষাক্ত হুল!
সেই বয়সেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম ঠিকমতো আটকাতে পারলে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম প্রাণীও মুহূর্তেই অসহায় হয়ে যায় এবং মৃত্যুর চে’ বড় অসহায়ত্ব আর কিছুতে নেই। তিলফুলের ভেতর যেভাবে বিষাক্ত মৌমাছি আটকিয়েছি ছেলেবেলায় ঠিক সেইভাবেই সাতবছর আগে আটকিয়েছিলাম প্রায় বৃদ্ধ হয়ে আসা সেলিমগুণ্ডাকে। তিলে তিলে শেষ করা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, তবে শেষ তাকে করেছিলাম। বহু বহু বছর ধরে মনের ভেতর চাপ ধরে থাকা অপমান এবং কষ্ট-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আচ্ছা ‘তিলে তিলে মারা’ কথাটা কোত্থেকে এসেছে! কি ওই গ্রীষ্মকালীন ফসল তিল থেকে এসেছে! যে তিলে তেল হয়, নাড়ু, মোয়া, খাঁজা এসব হয়! নাকি তিলফুলের ভেতর থেকে মধু নিতে আসা বিষাক্ত হুলের মৌমাছিকে আটকে মধু নিতে আসা বিষাক্ত হুলের মৌমাছিকে আটকে ধীরে ধীরে শেষ করে ফেলা থেকে এসেছে তিলে তিলে মারা কথাটা!
আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন খালা। এমন ভালো বোধহয় নিজের সন্তানকেও বাসে না মানুষ। খালার সারাক্ষণের উৎকণ্ঠা ছিল আমাকে নিয়ে। আমি কী খাব, কী পরব ! কখন ঘুমাব, কখন পড়তে বসব, কখন স্কুলে যাব, কখন মাঠেÑ সব নিয়েই ভাবনা ছিল খালার। ঘন দুধের সঙ্গে খেজুড়ে গুড় দিয়ে কাউনের এক-দু’ বাটি ক্ষির করতেন খালা। নিজে কখনো মুখে নিতেন না। কী যে আদর করে খাওয়াতেন আমাকে! আমি ছিলাম তাঁর জান, আত্মা। কিন্তু খালার জন্য আমার তেমন টান ছিল না, তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমার সব টান ভালোবাসা ছিল বাবার জন্য।
কাল সন্ধ্যায় খালা হঠাৎ করে বললেন আজ বিকেলের লঞ্চে বাবা আসবেন। শোনার পর থেকে আমার ভেতরে শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক ছটফটানি। সন্ধেবেলা পড়তে বসে পড়ায় আর মন বসে না। হারিকেনের ম্লান আলোর দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকি। রেকাবিতে দুধভাত নিয়ে মুখে তুলে খাইয়ে দেন খালা, খাবারের দিকে আমার মন থাকে না। রাতেরবেলা খালার বুকের কাছে শুয়ে ঘুম আসে না কিছুতেই। শুধু মনে হয়, কখন সকাল হবে। কখন আসবে আগামীকাল! সকালবেলা মনে হয় কখন দুপুর হবে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কখন আলফুর সঙ্গে নদীতীরের লঞ্চঘাটে গিয়ে দাঁড়াব। কখন নদীর বাঁকে ছবির মতো আস্তেধীরে ফুটে উঠবে একটা লঞ্চ, ভটভট শব্দে এগিয়ে আসবে ঘাটের দিকে। কাছাকাছি আসার পর দেখা যাবে ডেকের ওপর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।
বাবার জন্য এই অপেক্ষা আমার শুরু হয়েছিল শৈশবে। সেই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম চারপাশের মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি আমার বাবাকে। বাবার মতো মায়াবী সুন্দর মুখের মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বাবার মতো ভালোবাসতে কেউ জানে না। আমার মা না, বড় ছোটখালা কেউ না, এমনকি আমার ভাইবোনরাও না।
আমরা পাঁচটি ভাইবোন। দুভাই তিনবোন। প্রথমে বড়ভাই, তারপর দুটো বোন, তারপর আমি তারপর শেষ বোনটি। বাবা চাকরি করেন ওয়াপদায়। কেরানির চাকরি। এই চাকরির আয়ে এতগুলো মানুষের সংসার চলতে চাইত না। মাও সামলাতে পারতেন না এতগুলো সন্তান। এজন্যই আমাকে রেখেছিলেন বড়খালার কাছে।
কিন্তু আমার যেমন বাবার জন্য টান ভালোবাসা, বাবারও তেমনি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। এজন্য ছুটিছাটায় নানাবাড়িতে বাবা আমাকে দেখতে আসতেন। পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ক্লাশ টুতে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।
আমাকে দেখতে এসে এক দুদিনের বেশি থাকতেন না বাবা। যে একটি দুটি দিন থাকতেন, আমি সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে। স্কুলে যেতাম না, পড়তে বসতাম না। খেতাম বাবার সঙ্গে, ঘুমাতাম তাঁর গলা জড়িয়ে। আর কত যে কথা বলতাম বাবার সঙ্গে। ওই বয়সের ছেলেমানুষি কথা। এমনকি গান গেয়েও শোনাতাম বাবাকে। লোকমুখে কিংবা মাই-ট্রানজিস্টারে শোনা গান। ‘আমায় এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলি, প্রাণ কোকিলা রে’।
আসলে এসব ছিল আমার যাবতীয় গুণপনা দিয়ে বাবাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা।
বাবা মুগ্ধ হতেন। যখন-তখন বুকে জড়িয়ে ধরতেন আমাকে। মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন।
সেই বয়সে আমার সবচে’ দুঃখের দিন ছিল বাবা যেদিন চলে যেতেন।
চলে যাওয়ার দিন সকালবেলাই বাবার জন্য গরমভাত আর গুঁড়ামাছের ঝোল রেঁধেছেন খালা। আমাকে নিয়ে খেতে বসেছেন বাবা। কিন্তু আমাদের দুজনার কারোরই গলা দিয়ে ভাত নামে না। বাবার চোখেও পানি আসে, আমার চোখেও পানি আসে।
খাওয়া শেষ করে লাজুক মুখে খালার সামনে দাঁড়ান বাবা। আমার মা এবং ছোটখালার মতো বাবাও বড়খালাকে ডাকতেন ‘বুজি’। লাজুক মুখে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ম্লান গলায় বলতেন, আপনের কাছে কয়টা টেকা হইব বুজি?
অর্থাৎ যাতায়াত খরচটা বাবার কাছে নেই। আমাকে দেখার লোভে কোনোরকমে লঞ্চ ভাড়াটা জুগিয়ে চলে এসেছেন। ফেরার সময় পকেট ফাঁকা।
ধান বিক্রির টাকা কিছু না কিছু খালার কাছে থাকতই। আলমারি খুলে পাঁচ-দশটা টাকা বাবাকে তিনি দিতেন। ওই টাকা পকেটে নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে, মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে পথে নামেন বাবা। বারবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিশব্দে কাঁদতে থাকি আমি।
কাঁধে রেকসিনের বস্তা ব্যাগ, বাবা হেঁটে যান আর ফিরে ফিরে তাকান। দূর থেকে আমি দেখি, থেকে থেকে চোখ মুচছেন বাবা।
বর্ষার মুখে মুখে গ্রামের খালপার থেকে ছইওয়ালা নৌকায় করে লঞ্চঘাটে যান বাবা। আলফু যায় তাঁর ব্যাগ পৌঁছে দিতে। সঙ্গে আমি। কিন্তু নৌকা ছাড়ার পর একদিকে কাঁদেন বাবা আরেক দিকে আমি।
আমার গ্রামজীবনটা কেটেছে এইভাবে। বাবার জন্য কেঁদে।
খালার মৃত্যুর পর আমি ঢাকায় চলে এসেছিলাম। আমি তখন ক্লাশ ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছি। খালার মাথায় কী রকম গণ্ডগোল দেখা দিল। সারাদিন বসে বসে কাঁদত। রাতদুপুরে বিছানায় বসে বিলাপ করত। কী যে বলত, কার কথা যে বলত আমি কিছু বুঝতেই পারতাম না। কখনো-কখনো আমাকে জড়িয়ে ধরেও কাঁদত। জানি না কোথাকার কোন গোপন দুঃখ-বেদনা তাকে ভেতরে ভেতরে ঘায়েল করেছিল। শেষপর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়েছিল খালা। বড়ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ভাঙনের দিকে ঝুঁকে পড়া আমগাছের ডালে নিজের শাড়িতেই ফাঁস দিয়েছিল।
খালার মৃত্যুতে তেমন বড় রকমের কোনো আঘাত আমি পাই নি। কেন, বলতে পারব না। যদিও খালার স্নেহ-মমতার কথা বহুদিন পর্যন্ত মনে পড়েছিল। মনটা একটু একটু খারাপ হয়েছে, এরচে’ বেশি কিছু না।
ঢাকায় চলে আসার পর বাবার জন্য আমার শুরু হয়েছিল অন্য রকমের এক অপেক্ষা। ততদিনে পাঁচটি ভাইবোন আমরা সবাই বড় হয়েছি। বড়ভাই কলেজে পড়ে, বাকি চারজন স্কুলে। সংসারের খরচ বেড় গেছে অনেক। কেরানিগিরির চাকরিতে সংসার কিছুতেই চালাতে পারে না বাবা। এজন্য অফিসের পর নানা রকমের টুকটাক কাজ করতে হতো তাঁকে। টিউশনি করতে হতো। সকালবেলা বাসা থেকে বেরিয়ে ফিরতেন অনেকটা রাত করে। দুপুরে খেতেন কি খেতেন না জানতেও পারতাম না।
কিন্তু রাত যত বাড়ত, বাবার জন্য উৎকণ্ঠা ততই বাড়ত আমার। পড়তে বসে বাবার জন্য আনমনা হয়ে যেতাম, খেতে বসে আনমনা হয়ে যেতাম। অন্যান্য ভাইবোন যে যার মতো পড়াশুনা, খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব করে শুয়ে পড়ত, বাবার কথা হয়তো ভাবতই না, কিন্তু আমি শুতে পারতাম না। কাউকে কিছু না বলে আমি একা একা চলে যেতাম রাস্তার মোড়ে। বাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাবা কখন ফিরবেন?
অনেকটা রাত করে ফিরতেন বাবা। দূর থেকে সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বিষণœ ভঙ্গিতে হেঁটে আসতেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়াবি মুখখানা তাঁর ভরে যেত মোহময় এক হাসিতে।
সংসার চালাবার জন্য তখন প্রায়ই ধার উধার করতে হতো বাবাকে। মাসের শেষদিক থেকে শুরু হতো ধার। মাস মাইনে পেয়ে সেই ধার শোধ করার পর হাতে টাকা-পয়সা বলতে গেলে আর কিছুই থাকত না। রেশনের চাল, গম, চিনি, এক-দু’ টাকার প্রতিদিনকার বাজার, খেয়ে না-খেয়ে কোনোরকমে চলতাম আমরা।
এই অবস্থায় চাকরি চলে গেল বাবার। কী কারণে গেল বলতে পারব না। এমনিতেই হতদরিদ্র সংসার, তার ওপর একমাত্র রোজগেরে মানুষটি গেল বেকার হয়ে। আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এক দু’মাসের মধ্যে ধার দেনায় একেবারেই ডুবে গেলেন বাবা।
সেই সময় ঘটল এক ঘটনা।
কোনো এক লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন বাবা। বেশ কয়েকমাস হয়ে গেছে শোধ করতে পারছেন না। সেলিম নামের মাঝারি সাইজের একটি গুণ্ডাকে বাবার পেছনে লাগিয়ে দিল সেই লোক। টাকা তুলে দিতে পারলে সেলিমকে কিছু দেবে সে।
সেলিমগুণ্ডা যখন-তখন এসে আমাদের বাসায় হানা দিতে লাগল। প্রথম প্রথম বাসায় থেকেও না করে দিতেন বাবা। তারপর সেলিমগুণ্ডার শব্দ পেলেই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতেন।
কিন্তু এভাবে কতদিন?
সেলিমগুণ্ডার হাতে একদিন ধরা পড়ে গেলেন বাবা।
তখন বাবার জন্য সারাক্ষণের উৎকণ্ঠা আমার। বাবা কোথাও গেলেই আমার মধ্যে শুরু হয় এক ছটফটানি। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো কাজই করতে পারি না। স্কুলে গিয়ে ক্লাশ করতে পারি না, খেলতে গিয়ে উদাস হয়ে মাঠের কোণে বসে থাকি। রাতেরবেলা রাস্তার মোড়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি।
সেলিমগুণ্ডার ভয়ে নিজের বাসায় বাবা তখন ফিরতেন চোরের মতো। এক পীর সাহেবের মুরিদ হয়েছিলেন, তাঁর ওখানে যেতেন ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে। আলো ফুটবার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে রোজগারের আশায় এদিক ওদিক চলে যেতেন।
এই করেও রেহাই পান নি বাবা। একদিন সকালবেলা সেলিমগুণ্ডা তাঁকে ধরে ফেলল। ফজরের নামাজ পড়ে হুজুরের ওখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে কোনো কাজে বোধহয় বাসায় ফিরছিলেন তিনি। ওই পথে সেলিমগুণ্ডার আড্ডা। বাবা ভেবেছেন, এত সকালে নিশ্চয় সে থাকবে না! রাতভর মদটদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, উঠবে নিশ্চয় বেলা করে!
কিন্তু ধারণাটা ভুল হয়েছিল বাবার। অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে ঠিক সেই সময়টাতেই বাড়ি ফিরছিল সেলিমগুণ্ডা। বাবা তার মুখোমুখি পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেলিমগুণ্ডা তাঁর বুক এবং কোঁক বরাবর দুটো ঘুষি মারল। এমনিতে চাকরি নেই, পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে অনেক মাসের, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বাবার শরীরে কিছু ছিল না। সেলিমগুণ্ডার ঘুষি খেয়ে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি।
ওই পথে একটা বটগাছ ছিল। বটতলার টংঘরে পান-বিড়ি সিগ্রেটের দোকান চালাত মোটা মতো একটা ঢাকাইয়া বুড়ি। বাবাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে সেই ঘরে বসিয়ে রাখল সেলিমগুণ্ডা। আমাদের বাসায় ছোট্ট একটা ছেলে এসে খবর দিলÑ টাকা না দিলে বাবাকে ছাড়বে না সেলিমগুণ্ডা। মারের কথাটা বলল না।
বাবাকে আটকে রেখেছে শুনে মা খুবই দিশেহারা হলেন। বোনগুলোর মুখ শুকিয়ে গেল। বড়ভাই মুখ গোঁজ করে বসে রইলেন আর আমি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলাম। আমার বড়ভাইটি বাবাকে তেমন পছন্দ করত না। আর ছেলেবেলা থেকে একটু যেন দায়িত্ব এড়ানো টাইপের। নিজের স্বার্থ ছাড়া বিশেষ কিছুই বুঝতে চায় না। সিলিমগুণ্ডার হাত ধরা পড়েছে এতে বাবা যেন মান-সম্মান তাঁর একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে এমন একটা মুখ করে বাসা থেকে বেরিয়ে বোধহয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে চলে গিয়েছিল সে।
যাহোক সেই দোকানটির সামনে ছুটে এসে দেখি মলিন পাজামা-পানজাবি পরা আমার অসহায় বাবা চিরকালীন দুঃখী মানুষের মুখ করে বসে আছে। পানজাবির একদিককার কনুয়ের কাছে ধুলো-ময়লার একটা আস্তর লেগে আছে।
বাবার মুখ দেখে বুকটা হু-হু করে উঠল আমার। পাশের চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চে বসে চায়ের পরোটা চুবিয়ে চুবিয়ে খাচ্ছে সেলিমগুণ্ডা আর আড়চোখে বাবাকে দেখছে। অর্থাৎ পাহারা দিচ্ছে।
একপলক সেলিমগুণ্ডাকে দেখে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি কথা বলার আগেই ম্লান গলায় বাবা বললেন, আফতাব মিয়ারে একটু ডাইকা আনো বাজান।
আফতাব মিয়া আমাদের বাড়িওয়ালা। একসময় খুবই সম্মান করত বাবাকে। অনেকটা জোর করেই নিজের এই বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিল বাবাকে। কারণ তখন সে ওয়াপদায় টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করত। বাবার সাহায্য দরকার ছিল তার। কিন্তু চাকরি চলে যাওয়ার পর বাবাকে সে আর পাত্তা দেয় না। ভাড়া বাকি পড়েছে বলে যখন-তখন এসে কথা শুনিয়ে যায়, উঠে যেতে বলে, জোর করে তুলে দেয়ার হুমকি দেয়। একই মানুষের যে কত রকমের চেহারা হতে পারে, এই আফতাব মিয়াকে দেখে আমি তা প্রথম বুঝে ছিলাম। প্রয়োজনের সময় কী যে তোয়াজ করত বাবাকে! আর বাবার অসময়ে বাড়ি ভাড়ার জন্য কত অপমান করেছে তাঁকে।
সেই আফতাব মিয়াকে বাবা কেন ডেকে আনতে বলেছেন?
পরে বুঝলাম আফতাম মিয়া সেলিমগুণ্ডার খুবই পরিচিত। সে এসে বললে বাবাকে সেলিম ছেড়ে দেবে। টাকা কবে দেবে সেসব বিষয়ে একটা সমঝোতা করিয়ে আফতাব মিয়া নিশ্চয় বাবাকে ছাড়িয়ে নেবে।
আমি দিশেহারার মতো আফতাব মিয়ার বাড়ির দিকে ছুটছি। দোকানের মোটা বুড়িটা হাতের তালুতে পানের টুকরো নিয়ে খয়ের লাগাতে লাগাতে হায় আফসোসের গলায় ফিসফিস করে বলল, আহা রে, যেই দুইডা ঘুষি বেডারে মারছে!
শুনে পা থেমে গেল আমার, মুহূর্তের জন্য মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। বুঝে গেলাম কী কারণে বাবার পানজাবির কনুইয়ের কাছে ধুলো ময়লার চাপড় লেগে আছে।
বাবা আবার বললেন, তুমি যাও বাজান। কিন্তু বাবাকে ছাড়াতে সেদিন আসে নি আফতাব মিয়া। উল্টো আমাকে বলল, দুই-চাইরদিনের মইদ্যে বাড়িভাড়ার টেকা না পাইলে সেলিমগুণ্ডার লগে আমারও কনটাক করণ লাগব। অরে দিয়া ঐ টেকাডা উডান লাগব। আমি আবার দৌড়ে এলাম বাবার কাছে। বাবা অসহায় গলায় বললেন, আইলো না?
না।
সেলিমগুণ্ডা তখনো সেই চায়ের দোকানের সামনে বসা। ফুকফুক করে সিগ্রেট টানছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে বিশাল এক ক্রোধ। ওই লোকটা মেরেছে আমার বাবাকে! আমি যদি ওর বয়সি হতাম, গায়ের জোর ওর মতো থাকত বা না-থাকত ওকেও আমি মারতাম। ও আমার বাবাকে দুটো ঘুষি মেরেছে, আমি ওকে গজারি লাকড়ি দিয়ে বেদম পিটাতাম। পিটিয়ে একেবারে মেরে ফেলতাম। তবে আমি সেলিমকে একদিন মারবই। আজ হোক, দশ-বিশ বছর পরে হোক, আমার বাবার গায়ে হাত তোলার প্রতিশোধ আমি নেবই।
তারপর থেকে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও ঘটনাটা আমি ভুলতে পারি নি। সময়ে, অসময়ে, ঘুমে, জাগরণে আমি কেবল দেখেছি সেই টংঘরে বসে থাকা, খেয়ে না খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকা, বুকের পাঁজরে এবং কোঁকসায় ঘুষি খাওয়া আমার অসহায় বাবার মুখ। আমার বুক জ্বলে গেছে। সেই জ্বলুনি কমেছে সাত বছর আগে। সেলিমগুণ্ডাকে মেরে প্রতিশোধ নিতে একুশ বছর সময় লেগেছিল আমার।
যাহোক সেদিন শেষপর্যন্ত সেলিমগুণ্ডার হাত থেকে বাবাকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম আমি নিজে। বুকের বিশাল ক্রোধ চেপে রেখে সেলিমগুণ্ডার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার বাবারে আপনি ছাইড়া দেন। সামনের মাসের সাত তারিখে আপনের টেকাডা আমরা দিয়া দিমু।
কোত্থেকে টাকা দেব, কেমন করে দেব কিছুই জানি না, তবু বললাম। শুনে সেলিমগুণ্ডা চিন্তিত চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক তো?
ঠিক।
যদি না দেছ?
দিমুঐ।
আমার গলায় কী ছিল কে জানে, সেলিম আচমকা বলল, আইচ্ছা যা। তয় সাত তারিখে এই দোকানের সামনে আইয়া টেকাডি দিয়া যাবি।
আইচ্ছা।
বাবাকে নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরেছিলাম আমি। বাবা এবং আমি ছাড়া কেউ জানতে পারে নি কী অপমান বাবাকে সেলিমগুণ্ডা করেছিল। সবাই জেনেছিল বাবাকে শুধু আটকে রাখা হয়েছিল।
কিন্তু সাত তারিখের টাকা?
সমস্যাটা মিটিয়ে ছিলেন ছোটখালা। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন। আমার খালু ব্যবসায়ী মানুষ, কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে অতিশয় খচ্চর। একটি টাকা কাউকে ধার দেয়ার মধ্যে নেই, দুটি টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করেন না। বিয়ের পর খালাও তাঁর স্বামীর মতো হয়ে গেছেন। তবু ছোটখালার কাছে গিয়েছিলেন মা। টাকা ধার চাইতে না, বাপের সম্পত্তি তাঁর আগে যেটুকু আছে সেটুকু ছোটখালা যদি কিনে নেন। যদি তিনি না কেনেন তাহলে ভাগ-বাটোয়ারা করে মার অংশটা যত দ্রুত সম্ভব বুঝিয়ে দিলে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে ফেলবেন মা।
নানার জায়গা-সম্পত্তির মালিক আমার খালারা তিনবোন। নানার কোনো ছেলে ছিল না বলে তাঁর ভাইরাও কিছুটা অংশ পেতেন। ‘বেরাদারি হক’ না কী যেন বলে ব্যাপারটাকে। বড় খালা বেঁচে থাকতে আমার বাবা উদ্যোগী হয়ে এই সমস্যাটা মিটিয়ে ছিলেন। সুতরাং এখন বিলের জমি এবং বসতবাড়ি, বাড়ির দুখানা ঘরের একচ্ছত্র মালিক আমার মা-খালারা। বড়খালা মারা গেছেন, তাঁর অংশের ভাগও পাবেন মা এবং ছোটখালা।
ছোটখালার কাছে গিয়ে অদ্ভুত একটা তথ্য জানা গেল। বড়খালা মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে ছোটখালা যে একবার গ্রামে গিয়েছিলেন তখন নাকি বড়খালা তাঁকে বলেছিলেন তিনি তাঁর জায়গা সম্পত্তির ভাগ আমাকে দিয়ে যাবেন। যেহেতু তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে নেই, আমার প্রতিপালন করেছেন তিনি, আমিই নাকি তাঁর ছেলে। শুনে আমাদের গরিব সংসারে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।
কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার খুব অবাক লাগে। স্বামীর সংসারে গিয়ে স্বামীর চরিত্র ধারণ করার পরও এই কথাটা কেন বলেছিলেন ছোটখালা? চেপে গেলেই তো পারতেন। চেপে গেলে বড়খালার অংশের অর্ধেক ভাগ পেতেন তিনি। বেশ কিছু টাকা হতো তাঁর।
আসলে মানুষের মনোজগৎ বড় অদ্ভুত। কত যে রহস্য সেখানে!
ছোটখালা তারপর আমার মায়ের এবং মৌখিকভাবে পাওয়া আমার অংশ কিনে নিয়েছিলেন। বাজারদর অনুযায়ীই কিনেছিলেন। এককালীন বেশ কিছু টাকা পেলাম আমরা। সেই টাকায় সেলিমগুণ্ডার ধার শোধ করা হলো সাত তারিখে। আফতাব মিয়ার বাড়িভাড়া শোধ করা হলো। সংসারের চেহারা ঘুরে গেল।
এসবের কয়েক মাস পর ওয়াপদার পুরনো চাকরিটাও ফিরে পেয়েছিলেন বাবা। তাঁকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই মর্মে একটা কেস করেছিলেন তিনি। কেসে জিতে গেলেন। পঁচিশ মাস পর পুনর্বহাল হলেন এবং পঁচিশ মাসের পুরো বেতনটা এককালীন পেয়ে গেলেন। আমাদের সংসার সুখে ভাসতে লাগল।
কিন্তু আমার মনের ভেতর স্থায়ীভাবে খোদাই হয়ে আছে সেই দিনটি, মার খাওয়া বাবার অসহায় মুখটি। যখন-তখন ইচ্ছে করে সেলিমগুণ্ডাকে গিয়ে গলা টিপে ধরি, মুখের ভেতর থেকে জিহ্বাটা ওর হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে আনি, আর নয়তো ঘুষাতে ঘুষাতে রাস্তায় ফেলে দিই জারজটাকে, জুতো পরা পায়ে চেপে ধরি গলা। আমার পায়ের তলায় মরণযন্ত্রণায় কাতরাক শুয়োরের বাচ্চা।
বুকে ক্রোধ চেপে দিন কাটে আমার।
আমি তখন আস্তে ধীরে বড় হচ্ছি। কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছি। রাস্তাঘাটে কখনো কখনো দেখা হয় সেলিমগুণ্ডার সঙ্গে। টের পাই আমার বুকের ভেতর আড়মোড় ভাঙছে একটা সিংহ। তক্ষুণি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেলিমগুণ্ডার ঘাড়ে।
না, এইভাবে না। আমি প্রতিশোধ নেব অন্যভাবে। গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধি দিয়ে ছেলেবেলায় যেমন প্রতিশোধ নিয়েছিলাম আলমগীর মামার ওপর।
সাত তারিখে টাকা পেয়ে যাওয়ার পর থেকে ওই অতটুকু আমার ওপর কেমন একটা সমীহের ভাব তৈরি হয়েছিল সেলিমগুণ্ডার। রাস্তাঘাটে দেখা হলে আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলত সে।
কি মিয়া, খবর কী? ভালা আছ?
আমি হুঁ হ্যাঁ করে জবাব দিতাম, পা চালিয়ে হেঁটে যেতাম। বুকটা জ্বলত। কবে সেইদিন আসবে। কবে তোকে আমি দেখে নেব কুত্তারবাচ্চা!
দেখে সেলিমগুণ্ডাকে আমি ঠিকই নিয়েছিলাম। একুশ বছর পর। তখন সে প্রায় বৃদ্ধ। চারদিক থেকে প্রচণ্ড মার খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো অবস্থা। দেখা হলে ভিখিরির মতো পাঁচ-দশটি টাকার জন্য হাত পাতে। টাকা পেলে বাংলা মদ খেয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে।
এই সুযোগটা আমি নিয়েছিলাম। বদ্ধ মাতাল করে এক ভোররাতে তাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানটায়। পকেটে ছিল শক্ত লাইলনের দড়ি সেই দড়ি দিয়ে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে যখন তার হাত পা বাঁধছি গুণ্ডাটা তখন এতই মাতাল, শব্দ পর্যন্ত করতে পারছিল না। তারপর আমি তার মুখে গুজে দিয়েছিলাম রুমাল। লেকের ধারে নিয়ে আলতো করে ঠেলে দিয়েছিলাম। ভারি পাথরের মতো লেকের পানিতে গিয়ে পড়েছিল সে আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বুকে একুশ বছর ধরে চেপে থাকা ক্রোধের ভার পাথরটিও আস্তে ধীরে গড়িয়ে গিয়েছিল কোনো অনন্তে। বুকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল আমার। ভুলে গিয়েছিলাম সব। সাত বছর পর আজ ওখানটায় এসে আবার সব মনে পড়ল।
বকুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরালাম। কখন যে বিকেল হয়ে এসেছে টের পাই নি। সিগ্রেট টানতে টানতে শারমিনদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, শারমিন, তুমি কোথায়?
বর্ষ ৮ সংখ্যা ১২, ১৬-৩১ জুলাই, ২০০৩
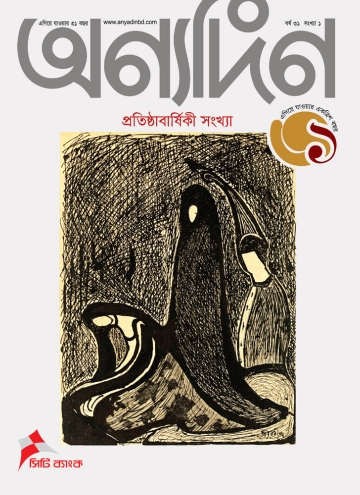














Leave a Reply
Your identity will not be published.