ভোর রাতে রায়হান এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল।
স্বপ্নটা এ রকম— সকালবেলা তার ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা গ’লে এসেছে সোনালি রঙের রোদ। এক অদ্ভুত আলোয় ভরে আছে ঘর। চোখ ফিরিয়ে ঘরের যে— কোনো দিকে তাকালেই মন ভরে যাচ্ছে। কী সুন্দর টিপটপ গুছানো সবকিছু। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। সে শুধু কান পাতলে টের পাচ্ছে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তার এ বাড়ি একটু একটু করে জেগে উঠছে।
সে স্বপ্নের মধ্যেই আলগোছে একটা হাই তোলে। হাত-পা টানটান করে দিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করে। তখন দরোজার পর্দা সরে যায়। সাহানাকে দেখা যায়। পর্দা সরিয়ে চায়ের কাপ হাতে সাহানা ভেতরে ঢুকছে। তাকে টানটানে হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সাহানা হাসে— উঠেছ তাহলে? একবার ডেকে গেলাম। কিন্তু তোমার কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে কিছু না বলে হাসিমুখে উঠে বসবে। মশারি একদিকে ওঠানো। সেদিকে সরে এসে পা নামিয়ে দেবে মেঝে বরাবর। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেবে। সে টের পাবে চায়ের চমৎকার সুঘ্রাণ তার ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে। সে চুমুক দিতে যাবে চায়ে, সাহানা কৃত্রিম অনুযোগের গলায় বলবে— সকালবেলা খালি পেটে চা, এ তোমার বড় বাজে অভ্যেস।
স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। সে চোখ মেলে দেখে রাত ফুরোয় নি। পাশে সাহানা ঘুমে নিথর। সে আরেক পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না। সে, অস্থির, ছটফট করে। এ রকম একটা স্বপ্ন, তার মনে হয়, সে বুঝতে পারে না, কেন দেখল! তবে কি দীর্ঘ বিশ বছর পরও তার মনে, সংগোপনে, ওরকম ইচ্ছে, নাকি সে সাধ বলবে, রয়েই গেছে? অথচ গত বিশ বছরে এরকম কোনো দৃশ্যের কথা ভাবে নি সে। হ্যাঁ, বিশ বছর আগে ভাবত। বিশ, নাকি একুশ-বাইশ বছর আগে? তা, হোক বিশ, কিংবা একুশ অথবা বাইশ, তারচেয়ে বড় কথা, এত দীর্ঘদিন পর ওই স্বপ্নের ফিরে আসা।
তখন অদৃশ্য স্বপ্ন ছিল না। তখন ছিল সাধ, তার কল্পনা। সে ভাবত— ঠিক ওভাবেই আরম্ভ হবে তার প্রতিটি সকাল। তারপর বিয়ের পর ওই কল্পনা, নাকি সাধ, হেজে— মজে গেছে। তখন সময় অনেকটা একটানা খরার মতো। তাই হেজে— মজে যেতে সময় লাগে নি। কখনো, কোনো সকালে হঠাৎ যদি ক্ষীণ মনেও হয়েছে, সে উড়িয়ে দিতে পেরেছে সে চিন্তা। ধাৎ, সে ভেবেছে, বিয়ের আগে ওইসব কত কী ভাবে মানুষ! ওসব মনে রাখতে নেই, ধরে রাখতে নেই, তাতে কষ্ট। অবশ্য জোর করে মনে রাখার ব্যাপারও ছিল না। তখন, সেই প্রথম থেকেই, এবং তারপর প্রতিদিন সংসার সামলাতে এমন হিমশিম অবস্থা, সে ভুলেই গিয়েছিল সবকিছু। সকালবেলা সোনা রোদে ভরে যাবে ঘর, তার কোমল শয্যার পাশে কয়েকটি কোমল উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে— চায়ের কাপ হাতে জীবনসঙ্গিনী, এসব সে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল।
তাই হঠাৎ এ স্বপ্ন তাকে অস্থির করে তোলে। এ স্বপ্ন কেন হঠাৎ, সে বারবার ভাবে। সে বুঝতে পারে না। এই না— বোঝা অবস্থায় সে আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে ঘণ্টা দুয়েক পর। রোজ যেভাবে ওঠে, সেভাবেই সে বিছানা ছেড়ে উঠতে যায়। তখন হঠাৎ তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। হাসি পায় তার। ঘরের চারদিকে সে তাকায় একবার। না, জানালা গলে এ ঘরে সোনালি রোদ আসার কোনো সুযোগ নেই। ঘরের বাইরের দিকের দুটো জানালাই বন্ধ। খোলা যায় না কখনো। জানালার ঠিক বাইরেই ড্রেন। রাজ্যের আবর্জনা নিয়ে সব সময় উপচেপড়া অবস্থায়। জানালা খুললে ঘরে তাই দুর্গন্ধে থাকা যায় না।
আরেকবার হেসে নিয়ে রায়হান আড়মোড়া ভাঙে। মশারির এখানে ওখানে তালি, এমন পুরোনো, দেখে মনে হয় কোনোদিন ধোয়া হয় নি। বিছানার চাদরের অবস্থাও সেরকম। ঘরের অবস্থাও ভিন্নরকম কিছু নয়। কোথাও কোথাও পলেস্তরা খসে গেছে, গত সাত— আট বছরে চুনকাম করা হয় নি। বেশিক্ষণ এ ঘরে থাকলে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। রায়হানদের অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেছে। তারা আলাদা আলাদা করে না দেখলে ওসব আর টের পায় না।
ডান দিকে ফিরে সাহানাকে দেখে রায়হান। আলনার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় দেখছে। দেখছে মানে, রায়হান জানে, নোংরা হয়েছে, ধুতে হবে এমন কাপড়গুলো সাহানা আলাদা করছে। তার পরনেও একটা আধ-ময়লা শাড়ি। খুঁজলে রিপুও পাওয়া যাবে। রায়হান নিজে নিজেই হেসে সাহানার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করে।
সাহানার চমকে যাওয়ার কথা। চমকায় না, নিরাসক্তভাবে পেছনে তাকায়, বলে— উঠেছ? তোমার বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে, জলদি করো।
একটা পুরোনো ওয়াল— ঘড়ি আছে এ ঘরে। রায়হান সেদিকে তাকায়। খুব যে একটা সময় আছে হাতে, তা নয়; তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এমনও নয়। সে বিকট শব্দে একটা আড়মোড়া ভাঙে, হালকা গলায় বলে, আজ ভোর রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। শুনবে কি দেখেছি?
সাহানা তখন তখনই কিছু বলে না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। কোনাকুনি একবার রায়হানের দিকে— বলো শুনি, স্বপ্নের কথাই যখন।
না থাক। ওসব স্বপ্নের কথা বলে কী হবে!
তাও ঠিক...কী হবে!...তুমি এখনো স্বপ্ন দেখ?
রায়হান হেসে ফেলে— ধাৎ, স্বপ্ন দেখার আবার তখন— এখন আছে নাকি?
আছে। আমি তো এখন আর কাউকে বলার মতো স্বপ্ন দেখি না।...তোমারটা বলোই না।
নাহ। তুমি বরং এককাপ চা করে দাও আমাকে।
চা! বেড টি? বেড টি-র স্বপ্ন দেখলে নাকি?
রায়হান অবাক হয়ে যায়— তুমি কী করে বুঝলে?
না, মনে হলো। শোন, বেড টি’র স্বপ্ন আর দেখো না।
দেখলে কী হবে?
চিনির কেজি. কত, জানো?
বাজারে যখন যাই, জানি বৈকি।
গুঁড়ো দুধের দাম?
আহা, বললাম না বাজারে যখন যাই...।
ঠিক আছে, দিচ্ছি এক কাপ করে। সাহানা রায়হানের দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলে। কিন্তু এরকম স্বপ্ন আর দেখবে না।
বেশ। রায়হান ঘাড় কাত করে। বেশ, দেখব না আর।...কে চায় দেখতে! চা করতে সাহানার মিনিট তিনেক লাগে। সেই চায়ে চুমুক দিয়ে রায়হানের ভালো লাগে না। কাপে পেঁয়াজের গন্ধ নাকি? আর চায়ে কোনো স্বাদ নেই। সে সাহানাকে বলে— মানুষ বেড টি খাওয়ার মতো এমন অদ্ভুত অভ্যেস কেন যে করে!...আমার ভালো লাগছে না।
সাহানা ঘরের এটা— ওটা টুকটাক গুছাতে গুছাতে মৃদু হাসে।
আর আমাদের চা, বুঝেছ, ভালো চা সব বাইরে চলে যায়। আমাদের এখানে থাকে তিন নম্বর কোয়ালিটি। আর আমাদের জন্যে তো আরও খারাপ।... এগুলো যে আমরা চা খাই না কী খাই!
ওই চায়ে খুব সুন্দর গন্ধ ছিল, না?
কোন চায়ে? রায়হান অবাক চোখে তাকায়।
স্বপ্নে যে চা খেলে?
হ্যাঁ, ছিল। রায়হান লাজুক হেসে বলে।
আর চায়ের কাপটা ছিল খুব সুন্দর, তাই না?
রায়হান বোকার মতো মাথা ঝাঁকায়।
আমি কি চা নিয়ে আসার সময় গরদের শাড়ি পরে ছিলাম?
রায়হান স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে থাকে।
চা শেষ করে ঝটপট উঠো তো। সাহানা তাড়া দেয়।
রায়হান বিমূঢ় গলায় বলে, তুমি এসব জানলে কী করে?
সাহানার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো কিংবা উত্তেজনা নেই। সে সহজ গলায় বলে— জানলাম, কারণ এরকম একটা দৃশ্যের কথা তুমি আমাকে বলেছিলে।
কবে? রায়হানের বিস্ময় কাটে না।
অনেক আগে। তোমার মনে থাকার কথা নয়।
আহা, বলোই না। তোমার তো মনে আছে।
সাহানা তবু গা লাগায় না। সে মশারি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রায়হান আবার বলে— সাহানা, বলেই ফেলো না। আমি একদম বুঝতে পারছি না।
সাহানা সামান্য হাসে— বিশ বছর আগে বলেছিলে, বুঝেছ? আমাদের বিয়ের পরপর।
সেই কথা তোমার আজও মনে আছে?
সাহানা আবার হাসে— আমার সবকিছুই মনে থাকে।
রায়হান এবার বোকার মতো হাসে— তা অবশ্য থাকে।... আমার কিন্তু কোনো মাথাব্যথা নেই।
কী নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই? সাহানার মশারি খোলা শেষ।
চায়ে ভালো গন্ধ নেই, কিংবা তোমার পরনে গরদের শাড়ি নেই, আমাদের ঘরে সকালবেলা সোনালি রোদ আসে না— তো কী হয়েছে! এসব নিয়ে আমি ভাবি না।
সাহানা মুখ টিপে হাসে— তবে আজ যে বড় স্বপ্ন দেখলে?
রায়হানের চেহারা আবার বোকা বোকা হয়ে যায়— কে জানে কেন দেখলাম! কিন্তু সাহানা আমি বুঝতেই পারছি না তুমি কী করে বুঝলে আমি ওই স্বপ্ন দেখেছি?
বুঝি নি। আন্দাজ করে বলেছি।
ধাৎ, আন্দাজ কখনো এত যথাযথ হয় নাকি!
হয়েতো গেল।...শোন। সাহানা এসে রায়হানের পাশে দাঁড়ায়। আমি কীভাবে আন্দাজ করলাম জানো? আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।...তুমি ওঠ তো জলদি করে। তোমার কিন্তু সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।
নাস্তার টেবিলে রায়হান একা। সাহানা কখনো তার পাশে বসে, কখনো উঠে রান্নাঘরে গিয়ে এটা-ওটা দেখে আসে। নাস্তার টেবিলে একটু বেশি সময় নেয় রায়হান। এটা তার শখ, বিলাসিতা। নাস্তা খেতে খেতে সে খবরের কাগজে চোখ বুলোয়। আর সাহানা তার পেছনে লেগে থাকে, তাড়া দেয়। আজ অবশ্য সামান্য সময় পরেই খবরের কাগজ নামিয়ে রাখে রায়হান। সাহানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে— বিবাহবার্ষিকী, না? আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।
সাহানা তখন রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আঁচলে মুখ মুছছে— ভুলে তো যেতেই পারো। কম দিন তো আর হলো না।...ভাবলে আমারই অবাক লাগে।
কিন্তু তুমি তো ঠিকই মনে রেখেছ।
আমি তো আর তোমার মতো ব্যস্ত থাকি না।
রায়হান সাহানার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক।
কী দেখছ অমন করে? তোমার তাকানো দেখে মনে হচ্ছে গতকাল বিয়ে হয়েছে আমাদের।
রায়হান মৃদু হাসে— তুমি খুব ভালো সাহানা।
সাহানা যেন অবাক হয়— ওমা, আমি আবার কী করলাম।
বিবাহবার্ষিকীর কথা দুজনেরই মনে রাখা উচিত। আমি মনে রাখি নি। অথচ আমি ব্যস্ত থাকি এরকম একটা কারণ দেখিয়ে তুমি ব্যাপারটা হালকা করতে চাইলে।...অন্য কোনো মেয়ে হলে রাগ করত।
মেয়েদের খুব ভালো চেন দেখছি।...কিন্তু তুমি তো সত্যিই ব্যস্ত থাক রায়হান। প্রথম প্রথম ঠিকই মনে রাখতে।
রায়হান সামান্য উদাস হয়— ঠিক ব্যস্ততা হয়েতো নয়...ব্যস্ততা তো আছেই...আসলে আমি ভীষণ ক্লান্ত।
জানি। বাদ দাও।...ক্লান্তির কথা ভাবলে ক্লান্তি বাড়ে।
রায়হান হেসে মাথা ঝাঁকায়— হ্যাঁ, বাদ। তবে বিবাহবার্ষিকী যখন, ভালো-মন্দ কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।
মাসের ক’তারিখ আজ?
সে যাই হোক না কেন। গত বিশ বছর হলো মাসের এ তারিখেই আমাদের বিবাহবার্ষিকী হচ্ছে।
সাহানা হাসে— হ্যাঁ, ও তারিখ বদলানোর সম্ভাবনা নেই। অবশ্য তুমি যদি দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাব, তবে একটা সম্ভাবনা অবশ্য দেখা যায়।
সে তো তুমিও ভাবতে পারো। এ সংসারে তোমার কোনো আশাই পূরণ হলো না— এই ভেবে।
এসব ভাবার সময় নেই আমার।...ঠিক আছে, রাতে পোলাউ হবে।
ম্যানেজ করবে কীভাবে?
করব। তোমার ভাবতে হবে না। তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা ক’রো। ....আর, আরেকটা ব্যাপার। তোমার খেয়াল নাও থাকতে পারে। আকাশের...।
এটা আমার খেয়াল আছে সাহানা।
কোনো ব্যবস্থা হয়েছে? ওর ডাক্তার নাকি পরশুই চলে যাচ্ছে?
যাচ্ছে। সেরকমই শুনেছি।...কিন্তু এদিকে কোনো ব্যবস্থা হয় নি।
ডাক্তার হঠাৎ করে চলে যাচ্ছে বলেই তো ঝামেলা। সেজন্যেই টাকাপয়সার কোনো ব্যবস্থা হয় নি।
দ্যাখো। আজ কোথাও কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।
সে তো দেখবই। নইলে দেড়-দু’মাস পিছিয়ে যেতে হবে।
রায়হানের নাস্তা শেষ। সে চায়ের কাপ টেনে নেয়— এখন খবরের কাগজগুলো স্রেফ ব্যবসা করে বুঝেছ? সামনের পাতায় শুধু রগরগে খবর।...কোথায় কোন মেয়ে রেপড্ হয়েছে, সেটাই লিখেছে আধা— পৃষ্ঠাজুড়ে।...আকাশ কোথায়?
পড়ছে। ওকে ওখানেই খাবার দিয়েছি।
কী দরকার! এখানে, আমাদের সঙ্গে বসলেই তো পারে।
পারে। কিন্তু তাহলে নদীকেও ডাকতে হয়। মেয়েটার বদভ্যাস কী জান, একবার যদি পড়ার টেবিল ছেড়ে ওঠে তাহলে আর বসবে না।
হুঁ। চা শেষ করে রায়হান উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা হয়েছেও ভালো। কোনোমতে ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারত, আমি বিয়ের চেষ্টা করতাম।
ম্যাট্রিক ও পাস করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। সাহানা টেবিল গুছাতে গুছাতে বলে। তুমি এখন থেকেই ছেলের খোঁজে থাকো।
থাকলাম।...মেয়ের নেই বিদ্যে, বাপের নেই টাকা, মেয়ে সুন্দরী, শুধু এতে কি পার করা যাবে?... দাও, বাজারের ব্যাগটা দাও।
যাবে। মেয়ে সুন্দরী আর লক্ষ্মী। অনেক ছেলেরই পছন্দ হবে। তুমি ভেবো না। আর শোন, তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি। একটা মুরগি কিনবে।
রায়হান হেসে ফেলে— তুমি পারও বটে সাহানা। এই টানাটানির মধ্যে তুমি টাকা জমাও কী করে?
ওটা সিক্রেট, বলা যাবে না। সাহানা মুখ টিপে হাসে।
বেশ। ব্যাগ দাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।
বাজার থেকে ফেরার পর রায়হানের আর অবসর নেই। সে বাজারের ব্যাগ রান্নাঘরে নামিয়ে রেখেই গোছল সেরে নিতে ছোটে। সাহানা এই ফাঁকে টুকটাক রান্নার ব্যবস্থা করে। রায়হানের সঙ্গে দেবে, লাঞ্চ।
গোছল সেরে বেরিয়ে নদী আর আকাশের সঙ্গে দু’চারটে কথা হয় রায়হানের। সেসব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সে নদীকে জিজ্ঞেস করে— পড়াশোনা কেমন করছিস মা? ম্যাট্রিকে তো আর বেশি দিন বাকি নেই।
নদী খুব গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকায়— পড়াশোনা করছি বাবা। না বুঝলে ভাইয়ার কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছি।
ভাইয়া মানে সাগর। রায়হান আর সাহানার বড় ছেলে। এবার ইউনিভার্সিটিতে, ফার্স্ট ইয়ার। তার কথা শুনে রায়হান গম্ভীর হয়ে যায়— ও কি বুঝিয়ে দেবে তোকে! ও কি সময় পায়? নদী বলে— আমি যেসব যেসব বুঝি না, সেসব দাগ দিয়ে রাখি। ভাইয়ার যখন সময় হয় তখন বুঝিয়ে দেয়। রায়হান মৃদু গলায় বলে, ওর কখনো সময় হবে না। একটু গলা উঠায় সে, নদীকে বলে— আমি আর তোর মা তো আছিই। তুই যা বুঝবি না সেটা আমাদের কাছে জেনে নিবি। নদী ঘাড় কাত করে, হ্যাঁ, বুঝে নেবে সে।
সাগর এক অদ্ভুত ছেলে, রায়হান নিজেই তাই বলে। তার নিজেরই ছেলে, অথচ তাকে বোঝে না সে। অপ্রয়োজনে একটির জায়গায় দুটি কথা কখনো বলে না সে ছেলে। প্রথম থেকেই এরকম নির্বিকার— নিরাসক্ত। রায়হানের নিজের ছেলেকে মনে হয় সন্ন্যাসী। জগৎ-সংসার, পরিবার— এসব কিছুর প্রতিই তার কোনো আকর্ষণ নেই। এ বয়সে ছেলে এমন নিস্পৃহ হবে কেন, রায়হানের মাঝে মাঝে কান্না পায়, কেন নিজের ছেলেকে মনে হবে অচেনা! সে তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে নি। ছেলের উদাসীনতা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেশি বেশি সময় দিয়েছে। তাকে নিয়ে খামোখাই ঘুরতে বেরিয়েছে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে বসেছে।
কিন্তু কিছুই ছেলেকে বাঁধতে পারে নি। বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রতি মোহ আরও কমে গেছে সাগরের। এখন রাতে বাসায় ফেরে না প্রায়ই। প্রথম প্রথম আতঙ্কিত হয়ে পড়ত সে আর সাহানা। ঘুম হতো না সারা রাত, এখন সয়ে গেছে অনেক, কিন্তু কষ্ট কমে নি। ছেলে কেন এত বাইরে বাইরে থাকবে, কেনই বা কোনো কোনো রাতে বাড়ি ফিরবে না! আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে, থাকবে নিজের মধ্যে। নিজের উপস্থিতি কাউকে বুঝতে দেবে না, অন্যের উপস্থিতি গ্রাহ্য করবে না।
নদী তখনো পাশে দাঁড়িয়ে। রায়হান তাকে জিজ্ঞেস করে— কাল রাতে সাগর বাড়ি ফিরেছিল?
নদী অবাক হয়ে তার বাবার দিকে তাকায়, বলে— না তো।
নদীর অবশ্য অবাক হয়েই তাকানোর কথা। রায়হান কখনো তাকে কিংবা আকাশকে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন করে না। তাদের বড়ভাই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং তা নিয়ে বাবা— মা খুব চিন্তিত— রায়হান আর সাহানা চায় না এরকম কোনো ধারণা নদী কিংবা আকাশের মনে ঠাঁই পাক। তবে আজ হঠাৎ করে প্রশ্নটা বেরিয়ে যায়। এবং পরমুহূর্তে সে আবার নদীকে জিজ্ঞেস করে— বাড়ি না ফিরে রাতে কোথায় কোথায় থাকে, তোদের বলে কিছু?
নদী একটু যেন ভেবে নেয়— না, কখনো কিছু বলে না। আর আমরাও কখনো কিছু জিজ্ঞেস করি না। ভাইয়া যে গম্ভীর। এমনিই কথা বলতে চায় না...।
রায়হান ভুল শুধরে নেওয়ার জন্যে তখনই মাথা ঝাঁকায়— থাক, কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না তোদের। ও বোধ হয় মাঝে মাঝে জরুরি কাজে আটকা পড়ে বাড়ি ফিরতে পারে না।
নদী ঠোঁট উল্টোয়— হবে হয়তো।
দুই
রায়হানের অফিস সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস— এটা কথার কথা। কোনো দিনই ছটার আগে বেরুনো হয় না। অধিকাংশ দিনই সাড়ে ছয়টা বাজে। এ জন্যে অবশ্য কোনো ওভারটাইমের ব্যবস্থা নেই। ওদিকে আবার সকাল দশটার জায়গায় কিছু দেরি করে আসার জো নেই। কথা তো শুনতেই হয়, তেমন ঘনঘন লেট হলে চিঠিও ইস্যু হয়ে যায়।
অফিস ছুটির পর রায়হান যায় টিউশনিতে। সপ্তাহে ছদিন, শুক্রবার যেতে হয় না, অর্থাৎ তার অফিসের মতো। ছাত্রটি অল্পবয়সী, ক্লাস ফাইভে পড়ে। তবে ফাইভের বিদ্যে তার নেই, বলতে গেলে কিছুই জানে না। না— জানুক, তার বাবার টাকা আছে, এটা সে এ বয়সেই জেনে গেছে। এবং যথেষ্ট টাকা থাকলে প্রাইভেট টিউটরদের যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা চলে, এটাও ছাত্রটির জানা। রায়হান অবশ্য এতে কিছু মনে করে না। দীর্ঘদিন দেখতে দেখতে সে জেনেছে, এইসব ছোটখাটো বিষয়ে কিছু মনে করলে তার মতো লোকদের চলে না। কারণ তাতে অবস্থার কোনো রকমফেরই ঘটে না বরং এসব মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। বেশি খারাপ লাগলে চোখও বুজে রাখতে হয়।
এ টিউশনিটাও অবশ্য তার পাওয়ার কথা নয়। ছাত্রের বাবার যে রকম আর্থিক সঙ্গতি, তাতে নামকরা স্কুলের পেশাদার শিক্ষকই মানানসই হতো। কাকতালীয়ভাবে সে টিউশনিটা পেয়ে গেছে। পেশাদার শিক্ষক হলে সপ্তাহে ছদিন আসার জন্যে নিদেনপক্ষে তিন হাজার কী চার দিতে হতো। তাকে তো হাজার দিয়েই খালাস। এ নিয়েও তার কোনো আপত্তি নেই। বরং মাসে হাজার টাকা বাড়তি আয়, তার টানা-হ্যাঁচড়ার সংসারে কিছু হাঁ-মুখ অভাব মিটছে, এই তার কাছে অনেক বড়।
ছাত্রের ফাইনাল পরীক্ষা মাসদেড়েক পর। পাস করাতে হবে। ছাত্র পাস না করলে টিউশনিটা হারাতে হতে পারে, এ আশঙ্কা আছে। তবে বড় কথা, সে সপ্তাহে ছদিন পড়িয়ে একজনকে ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠাতে পারবে না, এটা তার জন্যে বড় কষ্টের কারণ হবে। সুতরাং এখন সে ছাত্রটির পেছনে কিছু বাড়তি পরিশ্রম করছে। আগে সময় দিত এক ঘণ্টা, এখন দিচ্ছে দেড় ঘণ্টা। এখন তাই বাড়ি ফিরতে তার প্রায় নটা বাজে।
দিন কয়েক হলো সে ভাবছে, বাড়ি ফিরে কোনো কোনো দিন, শরীর যদি আপত্তি না জানায়, তবে সে নদীকে নিয়ে বসবে। মেয়েটির এসএসসি পরীক্ষারও খুব— একটা দেরি নেই। ঘষে মেজে যদি মেয়েটাকে সেকেন্ড ডিভিশনে পার করা যায় তবে বড় একটা ঝামেলা মেটে। তখন নদীর বিয়ে দিয়ে দেবে সে। নদী এমনিতে লক্ষ্মী মেয়ে, ঘরের সব কাজ জানে, স্বভাব— চরিত্র ভালো, ঠান্ডা মেজাজ। কিন্তু আজ কালকার বাজারে এসব পর্যাপ্ত গুণ নয়। সুতরাং এখন তার উচিত নদীকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।
সাহানারও সেরকম ইচ্ছে। তেমন করে বলে না কখনো, তবে বোঝা যায়। আর আজ নদীর সঙ্গে কথা বলে তার মনে হয়েছে, মেয়েটি আসলেও লেখাপড়ার অনেক কিছুই বোঝে না। মেয়েটি বলল বটে, মাঝে মাঝে নাকি সাগরের কাছ থেকে পড়া বুঝে নেয়, কিন্তু তাতে লাভজনক কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। সাগর নিশ্চয় নদীকে পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা দায়িত্ব হিসেবে নেয় নি। নিলে সেটা কখনো কখনো ঘটত না, ধারাবাহিকভাবে চলত।
রায়হান অবশ্য ভেবে রেখেছে একরকম। তার ছাত্রটির ফাইনাল পরীক্ষার পরও হাতে সময় থাকবে মাস সাড়ে তিন, চার। এ সময়টুকু পুরোটাই সে ব্যয় করবে মেয়ের পেছনে। ওতেই হয়ে যাবে নিশ্চয়। মেয়ের তো আহামরি রেজাল্ট দরকার নেই, একটা সেকেন্ড ডিভিশন হলেই চলে যায়। অফিসে পৌঁছে নিজের সিটে বসতে বসতে সে নদীকে পড়ানোর এই পরিকল্পনাটাই চূড়ান্ত করে নেয়।
অফিসে তার খুব খারাপ সময় কাটে। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। সেরকম কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু সে বাধ্য হয়। অফিসে কিছু পাওনা রয়েছে তার, আরও অনেকের। প্রায় এক বছর হলো তাদের নামে একটা বিল পাস হয়ে আছে। সে বিল শোধ করার ব্যাপারে অফিসের টুঁ শব্দটি নেই। অ্যাকাউন্টসে গেলে বলে অথরিটি দিতে আরম্ভ করতে বলে নি। তবে যারা করিতকর্মা, চোখেমুখে কথা বলতে জানে, তারা অ্যাডভান্সের নামে সে টাকা তুলে নিয়েছে। সে অনেকটা ইচ্ছে করেই সে টাকার জন্যে কোনো তাগিদ দেয় নি। থাকুক, হঠাৎ বড় কোনো দরকারে কাজে দেবে, এরকম সে ভেবে রেখেছিল।
এখন জরুরি দরকার, আগামীকাল দরকার টাকা। আকাশকে কাল ডাক্তার দেখাতে না পারলে ঝামেলা হয়ে যাবে। ছমাসে একবার দেখাতে হয় আকাশকে। ওর রক্তে কিছু সমস্যা আছে। হিমোগ্লোবিন কমে যায়। তখন হিমোগ্লোবিন দিতে হয় শরীরে। ডাক্তার বললে ছমাসে একবার, আবার ডাক্তারের কথা অনুযায়ীই এই গ্যাপ বাড়ে কিংবা কমে। গত ছ-সাত বছর হলো এভাবেই চলে আসছে। আর কতদিন চলবে, তার জানা নেই। কিংবা আর কত দিনই বা সে এমন একটা বড় খরচ চালিয়ে যেতে পারবে! ছেলের হিমোগ্লোবিন যেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই বাড়ে, সে জন্যে চেষ্টার কমতি নেই তার আর সাহানার। কলিজা প্রতিদিন সম্ভব হয় না, তবে লালশাক, কাঁচা— কলা নিয়মিত থাকে ছেলের জন্যে। তাতে যে খুব— একটা লাভ হচ্ছে, তার মনে হয় না, তবু সান্ত্বনা, হাল না ছেড়ে দেওয়ার সান্ত্বনা। অসুখটা ভালো নয়, জানা আছে, সে অসুখের বিরুদ্ধে এই অভাবের সংসারেও শক্ত পায়ে লড়াই করে যাচ্ছে তারা।
কাল ডাক্তার দেখাতে হবে। দামি ও নামি ডাক্তার পরশু বিদেশ যাবে মাস দেড়েকের জন্যে কীসব সেমিনারে যোগ দিতে। এরকমই শুনেছে সে এক কলিগের মুখে। তারপর ডাক্তারের চেম্বারে ফোন করে তার অ্যাসিস্টান্টের মুখে শুনে নিশ্চিত হয়েছে। তখনই সে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়েছে। এখন কাল দেখাতে হলে অন্তত ডাক্তারের ফি’জটা জোগাড় করা চাই।
এদিক— ওদিক ভেবে সে দেখে, টাকা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কোথাও। এসময় সহকর্মী কারো কাছে ধার চাওয়া যায় না। তা ছাড়া সাহানার এতটুকু ইচ্ছে নয় সে কখনো ধার করুক। সেও দেখেছে, ধার করলে পরে শোধ করার সময় বড় কষ্ট হয়। মনে হয় বিনা কারণে নিজের টাকা সে অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে। তবে এরকম জরুরি দরকারে ধার নিশ্চয় করা যায়, আর সাহানাও বুঝবে। কিন্তু মাসের এ সময়ে চাইবে কার কাছে? অফিসে প্রাপ্য টাকার কথা মনে পড়ে যায় তার। সে ওই প্রাপ্য টাকার বিপরীতে একটা অ্যাডভান্সের দরখাস্ত লেখে। সেটা নিয়ে যায় ম্যানেজার সাহেবের রুমে।
তার দরখাস্ত দেখে ম্যানেজার অবাক চোখে তাকায়। যেন তার সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে এই প্রথমে সে অ্যাডভান্সের দরখাস্ত দেখছে। এর পাশাপাশি এমন একটা ভাবও সে চোখেমুখে ফুটিয়ে তোলে, যেন সে বিস্মিত শুধু নয়, অধস্তন কর্মচারীর আবদারে হতভম্বও। ম্যানেজারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এরকমই হয়, জানা আছে তার। সে তাই ভড়কে না গিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ম্যানেজার তখন চোখ মুখের চেহারা ক্রমশ পাল্টে ফেলে। দরখাস্তটা টেবিলের একদিকে হেলাফেলায় ছেড়ে দিতে দিতে বলে— অ্যাডভান্সের দরখাস্ত আমি কখনো পাস করতে চাই না রায়হান সাহেব। ইটস্ এ ব্যাড হ্যাবিট। ম্যানেজার একটু কাঁধ ঝাঁকায়— তবু... আপনার ব্যাপার যখন, সামনের মাসে দেওয়ার চেষ্টা করব। তিন ছেলেমেয়ের নাম সে আর সাহানা রেখেছে প্রচণ্ড আবেগ থেকে। সাগর— নদী— আকাশ। আকাশ এবার ক্লাস সেভেনে। এমন মায়া— কাড়া চেহারা। রক্ত কম বলে ফ্যাকাশে দেখায়। বড় অসহায় মনে হয় ছেলেটিকে। আকাশ কি কখনো এমন অসহায় হয়! রায়হান ভেবেছিল, ছোট ছেলেটি হবে আকাশের মতো বিশাল ও উদার। কখনো হবে হালকা নীল মেঘমালার মতো শান্ত, আবার কখনো, প্রয়োজনমতো, গর্জে উঠবে। রোগে ভুগে আকাশ এখন এ বয়সেই অস্বাভাবিক রকম শান্ত। তবে প্রয়োজনমতো অসুখের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারে না। এ নিয়ে রায়হানের কোনো দুঃখ নেই, বরং তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই ছোটটির প্রতিই তার এখন অপরিসীম ভালোবাসা।
মাঝে মাঝে সে নিজেই অবাক হয়। আকাশের প্রতি এমন অপরিসীম মমতা জন্মেছে কেন! ও সবার আগে চলে যাবে বলে? বাবা হয়ে ছেলে সম্পর্কে এরকম ভাবতে কখনো ইচ্ছে করে না। কিন্তু এ কথা ভাবতে হয় না, এ কথা ছেলের মুখ চোখের সামনে ভাসলেই মনে পড়ে যায়। তবু শেষতক চেষ্টা বলে একটা কথা আছে। সাহানাও সেরকম, সেও লড়াই করতে চায় শেষপর্যন্ত। পরশু ডাক্তার চলে যাবে বিদেশে, সুতরাং কাল আকাশকে দেখানো জরুরি।
রায়হান ম্যানেজার সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। তারপর খুব শীতল গলায় বলে— টাকাটা আমার আজই হাতে পেতে হবে।
সম্ভবত তার শীতল গলা ম্যানেজারের মেজাজ গরম করে দেয়— আজই পেতে হবে মানে? আপনি কি ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছেন?
টাকাটা আমার খুবই দরকার স্যার, কাল আমার ছোট ছেলেকে ডাক্তার দেখাতেই হবে। ওর কথা তো আপনি জানেন না স্যার। ওর হিমোগ্লোবিন...।
ডাক্তার দেখাতে এত টাকা লাগে না। ম্যানেজার সজোরে মাথা নাড়ে।
তাই দেখে তার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে যায়। দু শ’ টাকা ডাক্তারের ফি, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর যদি ডাক্তার বলে— ‘রক্ত দিতে হবে’? কিংবা যদি তেমন কোনো দামি ওষুধ কিনতে হয়? ম্যানেজার জানে এ সব! তার কথাতো শুনলও না।
সে গম্ভীর গলায় বলে— লাগে। আমার ছেলের কী অসুখ সেটা না জানলে আপনি বুঝবেন না কেন লাগে।
ওয়েল, আপনার ছেলের কী অসুখ সেটা আমার জানার কথা নয়। সেটা জানার জন্যে আমি এ চেয়ারে বসিও নি।
আমি সে কথা বলছি না। স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না।
কেনই বা বলবেন? আমি যা বুঝি তা হলো অফিস এখন টাকা দিতে পারবে না।
স্যার, অ্যাকাউন্টসে আমি কথা বলে রেখেছি। টাকা আছে। আপনি দরখাস্তটা ওকে করে দিলেই ওরা টাকা দিয়ে দেবে। ওরা বলেছে স্যার।
আমি সই করার আগেই অ্যাকাউন্টসে বলে রেখেছেন! আপনি তো খুব করিতকর্মা লোক রায়হান সাহেব। শুধু যদি অফিসের কাজের সময় এমন কর্মদক্ষতা দেখাতে পারতেন! যাকগে, অ্যাকাউন্টসে টাকা তো থাকবেই।
রায়হান দাঁড়িয়ে থাকে।
আমি দুঃখিত রায়হান সাহেব, অফিসে এখন ক্রাইসিস যাচ্ছে। আপনার অ্যাডভান্সের দরখাস্তে আমি সই করতে পারি না।
কোম্পানির ক্রাইসিস যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সেটা ম্যানেজারের চেয়ে রায়হান এ মুহূর্তে ভালো বলতে পারবে। একদম আপ— টু ডেট হিসেব দেবে, কারণ তার কাজই ওই ডিপার্টমেন্টে। সে অবশ্য ওই প্রসঙ্গের ধার দিয়েও যায় না। সে গলার স্বর আরও নরম করে আনে— টাকটা আমার সত্যিই খুব দরকার স্যার। সে মনে করে এরকম নরম গলায় কথা বললে কাজ নিশ্চয় হবে।
তার নরম গলা অবশ্য ম্যানেজারকে স্পর্শ করে না, বরং ম্যানেজার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে— আপনি ওই বিলের অ্যাগেইনস্টে অ্যাডভান্স চেয়েছেন কেন!... আশ্চর্য!...এটা যে করা যায় না আপনি জানেন না? অফিস ডেকোরাম মানবেন না?
তখন তার মেজাজ আবার বিগড়ে যায়। সে কতক্ষণ ম্যানেজারের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। তারপর কেটে কেটে বলে— এভাবে আগেও অনেকে অ্যাডভান্স নিয়েছে, তারা কোম্পানির এ ব্রাঞ্চেরই স্টাফ, এবং আপনিই তাদের দরখাস্তে সই করেছেন।
ম্যানেজার সবেগে মাথা নাড়ে— নো, নেভার।
এইভাবে তাদের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয় এবং সেটা বেশ কিছুক্ষণ চলে। সে কোথাও কখনো গলা উঁচিয়ে কথা বলে না। সে জানে, জোর গলায় কথা বলার ব্যাপারটা বহু আগেই তার ভেতর মরে গেছে। আজ সে গলা ম্যানেজারের পাশাপাশি অনেক উঁচু পর্যন্ত তোলে। তখন, বহুদিন পর সে টের পায়, গলা উঁচুতে তোলার মধ্যে অদ্ভুত এক শারীরিক আনন্দ আছে। তবে গলা উঁচুতে তুললে সব সময়ই যে কাজ হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, এটাও সে বোঝে। এই যেমন, অ্যাডভান্সের দরখাস্তে ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত সই করে না।
ম্যানেজারের রুম থেকে সিটে ফিরে সে নিজেকে কচ্ছপের মতো গুটিয়ে রাখে। এইভাবে অনেকটা সময় যায়। সে চোখ তুলে কোনো দিকে তাকায় না। তার কান্না পায়? এ অফিসের অনেকেই যা পারবে, সে কেন তা পারবে না! সে কেন বঞ্চিত হবে, প্রয়োজনের সময়েও? এসব ভাবতে ভাবতে হু হু করে তার ক্রোধ বেড়ে যায়। ক্রোধ বাড়তে বাড়তে ভেতরে ভেতরে একসময় তার কান্না বেড়ে যায়। সে খুব কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে। সে ক্রোধ এবং কান্না দুটোই আর সবার কাছে থেকে গোপন রাখতে চায়। সে সহকর্মীদের কাউকেই কিছু বুঝতে দিতে চায় না। কারণ সে জানে, সহকর্মীরা জানলে যেমন অর্থহীন সহানুভূতি জানাতে ছুটে আসবে, তেমনি পাশাপাশি অনেকে মুখ টিপে হাসবেও।
অফিসে সারা দিন সে কোনো কাজ করে না। নিতান্তই বাধ্য হয়ে দুটো ফাইল ছেড়ে দেয়, নইলে অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজ আটকে থাকে। বাকি সময় সে চুপচাপ বসে থাকে। তার ক্ষমতা আসলে কত কম, চুপ করে থাকলে সে ক্রমশ বোঝে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয় তার ক্ষমতা কম, আসলে তার কোনো ক্ষমতাই নেই, সে তো তা জানেই। তবু এসব মুহূর্ত বড় অস্বস্তিকর। এসব সময়ে নানা রকম ইচ্ছে হয় তার। এই যেমন এখন হচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ম্যানেজারের গলা টিপে ধরে বলবে— শালা, ইয়ার্কি পেয়েছ! কিংবা পেপার— ওয়েট ছুড়ে ছুড়ে এ অফিসের সব জানালার কাচ ভেঙে দেবে। সবার টেবিল থেকে ফাইল উঠিয়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।
এসবের কিছুই অবশ্য করা হয় না। কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে পারলে অবশ্য ভালো লাগবে, সে জানে। কিন্তু অফিসে সে সুযোগ কই! বারবার তার চোখের সামনে আকাশের মুখ ভাসে, ফ্যাকাশে, অসহায় এবং মায়াকাড়া। মায়া, মায়া, এই মায়াটাই যত নষ্টের মূল। নইলে কবে সে সংসার ছেড়ে চলে যেত বহুদূর অচেনা কোনো জায়গায়।
সন্ধ্যায় ছাত্রকে পড়ানোর সময় বারবার তার ভুল হয়ে যায়। সে অফিস থেকে বেরিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে। ইচ্ছে করেই, ম্যানেজার যখন অ্যাডভান্সের দরখাস্তে সই করে নি তখন এটা একটা বিদ্রোহ। অফিস থেকে আগে বেরনোর কারণে ছাত্রের বাসায় অনেক সময় কাটে। তবে অনেকটা সময় কাটিয়েও সে ওঠে না। ছাত্র অবাক হয়, আড়মোড়া ভাঙে, বারবার তার দিকে তাকায়। শেষে জিজ্ঞেস করে— স্যার, আজ আর কতক্ষণ পড়াবেন?
তোমার বাবা ফিরেছেন? সে জানতে চায়।
না। ছাত্রটি মাথা নাড়ে। বাবা কখন ফিরেন তা তো আমরা কেউ জানি না।
সে একটু মাথা ঝাঁকায়— ঠিক আছে, তুমি ভেতরে চলে যাও, আমি তোমার বাবার জন্যে অপেক্ষা করব। কথা আছে।
ছাত্রটির বিস্ময় আরও বেড়ে যায় এবং শঙ্কাও। সে উঠতে চায় না। বারবার বই— খাতা গুছোয়, বারবার রায়হানের মুখের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে থেকে বলে— স্যার, আজকে তো হোম— টাস্ক সব করাই ছিল।
তা ছিল। হোমটাস্ক তুমি করেই রেখেছিলে। সে বলে।
তাহলে বাবাকে আপনি কী বলবেন? ছাত্রটি জিজ্ঞেস করে।
সে একটু হাসে— তোমার সম্বন্ধে কিছু বলব না। সে অন্য ব্যাপার।
ছাত্রটির বাবা ফেরেন আধঘণ্টা পর। তাকে দেখে অবাক হন। সে সামান্য হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে— আসলে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।
তাই! বলুন। আজ আমি আর্লি ফিরেছি, তাই দেখা হলো। তা, কী বিষয়ে বলবেন? আপনার ছাত্রটি কি একদম পড়াশোনা করছে না? ওর কাছ থেকে পড়া আদায় করে নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্য আপনার।
হ্যাঁ, সে দায়িত্ব আমার। সে অল্প অল্প হাসি মুখে বলে। আপনি ভাববেন না, আপনার ছেলে আগের চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ করেছে।...আমি একটু অন্য ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।
অন্য ব্যাপারে?...বলুন।
সে তখন খুব বিনীত ভঙ্গিতে অনুরোধ করে, সামনের মাসের বেতন কি তাকে এ মাসে দিয়ে দেওয়া সম্ভব? তার খুবই জরুরি দরকার।
ভদ্রলোক যেন তার কথা শুনতেই পান না, বলেন— ছেলেকে কিন্তু আপনি শাসন করবেন। তবে ওর মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কিছু করতে যাবেন না।
রায়হান বোকার মতো হেসে ফেলে— আমি ওরকম কিছু করি না কখনো।
গুড। ভদ্রলোক মাথা নাড়েন। আপনি নিয়মিত আসেন তো?
রায়হান একবার ভাবে বলবে সেটা আপনারা বাসার অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। সে অবশ্য বলে— জি, রোজই আমি আসি। আর এখন ওর পরীক্ষা এসে গেছে বলে বাড়তি সময় দিচ্ছি।
ভদ্রলোক আবার বলেন— গুড। দ্যাখেন, কদ্দুর কী করতে পারেন।
আমি চেষ্টা করছি। আপনার চিন্তা করার কিছু নেই।...আমার ব্যাপারটা...?
ভদ্রলোক এবার বেশ কায়দা করে মাথা নাড়েন— উঁহু, এখন তো পারব না। সামনের উইকে একবার মনে করিয়ে দিয়েন।
সামনের উইকে তো এ মাসই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু নিজেকে এমন ছোট মনে হয়, রায়হান সেটা আর ছাত্রের বাবাকে মনে করিয়ে দেয় না। ছাত্রের বাবাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ‘চা খেয়েছেন?’ বলে ভেতরে ঢুকে যান। রায়হান বেরিয়ে রাস্তায় নামে। বাড়ি ফিরতে তার ইচ্ছে করে না, কিন্তু সে বাড়ির দিকেই রওনা দেয়।
তিন
মন্দ কি! সাহানার মনে হয়। বরং ভালোই লাগত তার। আসলে এরকম কিছু কিছু কল্পনা তো তারও ছিল। রায়হানের মতো সেও কি ভাবে নি? হ্যাঁ, সেও ভেবেছে, তার নিজের মতো করে।
প্রায় বিশ বছর আগের সেই দিনটার কথা তার এখনো মনে আছে। রায়হান তাকে একদিন হঠাৎ করেই বলেছিল—শোন, আমি না বিয়ের আগে একটা কথা প্রায়ই ভাবতাম।
কী ভাবতে? সে ছোট করে জিজ্ঞেস করেছিল।
তেমন কিছু নয় অবশ্য। রায়হান যেন লজ্জা পেয়েছিল।
আহা, বলোই না শুনি।
না, মানে আমার মনে হতো কী, জানো? সকালবেলা খুব সুন্দর একটা ঘরে আমার ঘুম ভেঙে যাবে। অর্থাৎ যে ঘরটায় আমরা থাকি সেটাই খুব সুন্দর। ঘুম ভাঙলেও আমি উঠব না বিছানা ছেড়ে। তার একটু পর তোমাকে দেখব ঘরে ঢুকতে। তুমি গোছল সেরে একটু সেজেছ, তোমার পরনে একপাল্লা করে পরা শাড়ি। তুমি আমার জন্যে বেড-টি নিয়ে এসেছ।
এই কথা! সাহানা বলেছিল। এই কথা বলতে তুমি লজ্জা পাচ্ছিলে?
পাচ্ছিলাম।
দাঁড়াও। তোমার বেড-টির ব্যবস্থা তাহলে করতে হয়।
তবে সে সময়ে বেড-টির ব্যবস্থা করা অত সহজ ছিল না। শোওয়ারঘরের মধ্যেই খাওয়ার ব্যবস্থা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সাহানাকে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হতো। তা ছাড়া তখন টাকার টানাটানিও খুব। তবে এর মধ্যে সকালবেলা রায়হানের ঘুম ভাঙার পর এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা নিশ্চয় সাহানা করতে পারত।
রায়হানের বলার পরের দিন সাহানা তা করেও ছিল। কিন্তু সেই নিয়ে তার পরপরই তার আর রায়হানের সে কী হাসাহাসি!
রায়হান হেসে বলেছিল—তাহলে তুমি বেড-টি বানালে?
হ্যাঁ, বানালাম। সাহানার মুখেও হাসি।
কিন্তু ঘরের চেহারাটা দেখছ?
সে তো দেখছিই।
এ ঘরে বেড-টি কি মানায়?
সত্যিই মানাচ্ছে না বুঝি?
না, ঘরের যে ছিরি! আর চায়ের কাপটা দেখ! বেড-টি খেতে হয় দামি কাপে।
আচ্ছা! দামি কাপে খেলে বুঝি চায়ের স্বাদ বদলে যায়?
তা একটু নিশ্চয় যায়। তা ছাড়া যে চা-টা খেলাম ওটার স্বাদ সত্যিই এত বাজে। বেড-টি মানেই ভালো চা, দারুণ ফ্লেভার।
তাহলে কী করা যায়?
তোমার শাড়িটাও মানানসই হয় নি। একপাল্লা করে অন্য ধরনের শাড়ি পরতে হয়।
আহা, সে জন্যেই তো আমি জানতে চাচ্ছি কী করা যায়?
রায়হান কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভেবে বলেছিল—একটা কাজ অবশ্য করা যায়। বেড-টির ব্যবস্থা এখন নয়, পরে করলে চলবে।
পরে কবে?
যখন আমাদের অবস্থা বদলাবে। যখন আমাদের অনেক টাকা হবে।
সেদিন এই নিয়ে, সবকিছু মিলে অনেকক্ষণ হেসেছিল তারা। সাহানা বলেছিল—ঠিক আছে। তবে তাই হবে। যখন আমাদের অবস্থা বদলাবে তখন তোমাকে তোমার মনের মতো করে বেড-টি দেব আমি।
অবস্থা বদলায় নি।
সে নিয়ে অবশ্য সাহানার কোনো অভিযোগ নেই। তবে বেড-টির ব্যবস্থা আর করা হয় নি।
কখনো কখনো এ নিয়ে কথা, হাসি-ঠাট্টা হয়েছে তাদের। তারপর সংসারের নানা চাপে তারা নিজেরাও একসময় ভুলে গেছে। ঠিক ভুলে হয়তো যায় নি, ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে আরও অনেক কিছুর আড়ালে।
আজ বহুদিন পর ওই প্রসঙ্গ আবার ওঠে। সাহানার খারাপ লাগে। তাহলে ব্যাপারটা রায়হানের মনে থেকেই গেছে! কিন্তু এখন তো আর অবস্থা বদলানোর প্রশ্ন ওঠে না। আসলে জীবন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বহু আগে। এখন শুধু ওই নির্দিষ্ট পথে সময় পার করে দেওয়া। তবে সাহানা বোঝে, এইসব ছোটখাটো ব্যাপারই মাঝে মাঝে অনেক বড় হয়ে যায়।
এমন আর কী, সকালবেলা এক কাপ চা-ই তো। তার প্রতি রায়হানের খুব যে আগ্রহ, তাও নয়। নিছক একটা সাধ। অথচ এই সাধকে কেন্দ্র করেই আরও কত কী চোখে ধরা পড়ে। রায়হানের জন্যে তার মনের মতো করে বেড-টির ব্যবস্থা করা হয় নি, এটাই বলে দেয় বিশ বছরে তাদের অবস্থা বদলায় নি। আর এ নিয়ে হয়তো রায়হানের লজ্জা কিংবা কষ্ট। সাহানার এটাই খারাপ লাগে। তার তো কোনো কষ্ট নেই। তবে রায়হান কেন কষ্ট পাবে কিংবা তার কাছে লজ্জা! তার যদি কোনো অভিযোগ থাকত রায়হানের প্রতি, তাহলেও এক কথা ছিল।
এসব অবশ্য ভেবেই বা কি! সে ভাবেও না কখনো। রায়হান সকালবেলা স্বপ্নের কথা বলল বলেই না উঠল। তবে সে মনে রেখেছে সবকিছু। রায়হান কবে কী বলেছে, তার কিছুই সে ভোলে নি। এটি রায়হানের প্রতি তার ভালোবাসা না অন্য কিছু, সে বোঝে না। বোঝার অবশ্য কোনোরকম প্রয়োজনীয়তাও সে বোধ করে না। অত সময়ও কখনো থাকে না তার হাতে।
সেই ভোরবেলা থেকেই আরম্ভ। রায়হান কিংবা তিন ছেলেমেয়ে ওঠার অনেক আগেই সে বিছানা ছাড়ে। হাত-মুখ ধুয়ে নিতে রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর ঘর গুছানো, নাস্তার পালা। নাস্তা একসঙ্গে খায় না। সাগর হয়েছে অদ্ভুত এক ছেলে, কখনো সবার সঙ্গে খেতে বসে না। আবার কোনো কোনো দিন সে সাগর, নদী, আকাশের পড়ার টেবিলেই নাস্তা পাঠিয়ে দেয়।
তারপর রায়হান যায় অফিসে। সাগরের আছে ভার্সিটি, নদী আর আকাশের স্কুল। ছোট দুজনের জন্যে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হয়। সবাই বিদায় হলে সাহানা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্না নিয়ে। প্রায় রোজই তাকে এই রান্নার ব্যাপারটা সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। পাঁচটা মুখ, অল্প পয়সার বাজারে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু তাই বলে হাত-গুটিয়ে বসে থাকারও উপায় নেই। সাহানা ভাজি-ভর্তা করে কোনোমতে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
আজ অবশ্য আরও অসুবিধে। ঠিকে ঝি আসে নি। এরকম আসে না মাঝে মাঝে। কিন্তু তাকে কিছু বলার উপায় নেই। স্রেফ মুখের ওপর বলে দেবে এ বাড়িতে কাজ করার আর কোনো ইচ্ছে নেই তার। সুতরাং তোয়াজ করে চলতে হয়। সাহানা অবশ্য ভেতরে ভেতরে ভীষণ রেগে থাকে।
আজ অবশ্য সাগর নেই বাসায়। রাতে ফেরে নি এদিকে নদীও বায়না ধরেছে আজ স্কুলে যাবে না। ছেলেমেয়েদের এসব কিছু আবদার প্রশ্রয় দেয় সাহানা। এমনিতে সংসারের যে অবস্থা তাতে ওদের কোনো শখই মেটে না। সুতরাং তার পক্ষে মেটানো সম্ভব এমন আবদার ধরলে সাহানা কখনো না করে না। তা ছাড়া এমনিতেও বেশি বেশি ‘না না’ করতে নেই, সে জানে।
আকাশের স্কুলের সময় হলে সে অবশ্য নদীকে বলে—যা, তুই ওকে একটু আনন্দদের বাসায় দিয়ে আয়।...সাবধানে যেতে বলিস ওদের।
আনন্দ আকাশের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। পাঁচ ছটা বাড়ি পরে থাকে। এমনিতে অন্যান্য দিন নদীর সঙ্গে স্কুলে যায় আকাশ। ওদের স্কুল পাশাপাশিই। এটা একটা সুবিধে।
নদী তখনই রাজি হয়ে যায়। তাই দেখে তাকে শাসায় সাহানা—তুই কিন্তু দেরি করবি না।
তোর যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে, ফিরতে পাঁচ মিনিট, মোট দশ মিনিট।
নদী মাথা ঝাঁকায়—না মা, আমি যাব আর আসব। দেরি করব না।
সে আমার জানা আছে। সাহানা একটু ধমকে উঠে বলে। যা এখন।
নদী আধঘণ্টার আগে ফিরবে না, জানে সে। মেয়েটা গল্প করতে বড় ভালোবাসে। আনন্দদের বাসায় নির্ঘাত পনেরো-বিশ মিনিট কাটিয়ে আসবে। তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামায় না। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে রায়হানের আনা বাজার নিয়ে। আজ নিজে বলে মুরগি আনিয়েছে সে। বিয়ের বিশ বছর হলো যখন, তখন কিছু-একটা করা দরকার। কিছু-একটা কীইবা করা যায় একটু ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা ছাড়া। বাসায় পোলাও-এর চাল আছে। আর তার ছিল কিছু জমানো টাকা। ও টাকার কিছু গেল মুরগির পেছনে। যাক। আজ রাতে পোলাও আর মুরগির রেজালা খাবে তারা।
সাহানার অবশ্য একটু লজ্জাও করে। বিশ বছর পর এসব একটু কেমন কেমন যেন লাগে। বড়লোকরা অবশ্য খুব হইচই করে এসব করে, কেক-টেক কাটে। তবে বড়লোকদের ব্যাপারই আলাদা। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে চলে না। তাদের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, সেটুকুই সে করছে। আর এসব করা উচিত। বাড়িতে একটু হইচই হয়। এরকম ভেবে সে লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠতে চায়। তবে সে ঠিক করে নেয়, ছেলেমেয়েদের কাউকেই কিছু জানাবে না। তবে সত্যিই তার লজ্জা করবে। অবশ্য রায়হানের যে মুখ হালকা, হয়তো খাওয়ার টেবিলে হা হা করে হেসে উঠে সব বলে দেবে।
সাহানা দ্রুত হাত চালায়। নদী ফিরলে বলতে হবে ঘরগুলো গুছাতে। আজ কিছু কাপড় ধোয়ার দরকার ছিল। জানালার পর্দা, বিছানার চাদর সবই ময়লা। কিন্তু আজ কাজের মেয়েটা আসে নি। তাকেও অবশ্য এত কাপড় একসঙ্গে ধুতে দেওয়া যাবে না। সাহানা বিছানার চাদর নিজেই ধোবে ঠিক করে। কাজের মেয়ে মন মতো পরিষ্কার করতে পারে না। তবে আজ নয়, আজ অত বড় কাপড় ধোয়ার সময় পাওয়া যাবে না। আর আজ তার বিবাহবার্ষিকী, আজ কাপড়-টাপড় ধোয়া নয়।
এই রকম ভেবে সাহানা হেসে ফেলে। রায়হানকে বললেই হতো—শোন, তোমার আজ অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। আজ আর অফিস-টফিস যাওয়া নয়।
এ কথা বললে রায়হান কী বলত? রায়হান যে পাগলাটে, সাহানার মনে হয়, ও হয়তো নির্ঘাত মাথা দোলাত। তখনই রাজি হয়ে গিয়ে বলত—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ আর তাহলে অফিসে যাচ্ছি না।
তাহলে কেমন হতো?
এখন এরকম মনে হলে সাহানার খারাপ লাগে। সে বললেই পারত রায়হানকে। একদিন নাহয় অফিস কামাই-ই করত। তাতে নিশ্চয় এমন কিছু ক্ষতি হতো না রায়হানের। বেশি প্রয়োজন থাকলে ওপরের ফ্ল্যাট থেকে না হয় ফোন করে জানিয়ে দিত, সে যাচ্ছে না। তারপর সারা দিন তারা দুজন বাসায়। নদীকে জোর করে স্কুলে পাঠিয়ে দিলে আর কেউ তো থাকত না। একটা পুরো দিন তারা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারত।
সাহানার আবার লজ্জা লাগে। তবে লজ্জাটুকু সে পরমুহূর্তে এড়িয়ে যেতে পারে। কারণ সে জানে, সে এসব যত না নিজের জন্যে ভাবছে, তার চেয়ে বেশি ভাবছে রায়হানের জন্যে। লোকটার জন্যে মাঝে মাঝে তার বড় কষ্ট হয়। বিয়ের পর দিনে দিনে শুনেছে সে, কতরকম পরিকল্পনা যে ছিল রায়হানের। এই করবে, সেই করবে। তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবারও একটা বিশাল পরিকল্পনা ছিল। রায়হান বলেছিল তারা যাবে কক্সবাজার, সমুদ্র দেখবে, তারপর সেখান থেকে টেকনাফ। এর পরের বছর তারা যাবে ইন্ডিয়া, কমপক্ষে এক মাসের জন্যে। তাও তো ইন্ডিয়ার কিছুই দেখা যাবে না। রায়হান পুরো পরিকল্পনাটাই করত। বলত—এক মাস সময়, বুঝেছ, ইন্ডিয়া দেখার জন্যে মোটেই বেশি সময় নয়। মাত্র এক মাসে আমরা আসলে তেমন কিছুই দেখতে পাব না। যে বিশাল একটা দেশ।...কিন্তু এক মাসের বেশি সময় ম্যানেজ করাও তো মুশকিল।
ওসব কিছুই হয় নি। ইন্ডিয়া দূরে থাক, যাওয়া হয় নি কক্সবাজার। আর এখন তো ঢাকা শহরের মধ্যেও কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। সাহানার খেয়াল আছে, মাস পাঁচেক আগে সে বাড়ি থেকে শেষ বেরিয়েছে। তাও সেটা বেড়াতে যাওয়া নয়, রায়হানের এক দূরসম্পর্কের মামা মারা গেলে সে বাসায় হাজিরা দেওয়া। রায়হান অবশ্য মাঝে মাঝেই বলে—বাসায় থাকতে থাকতে শ্যাওলা পড়ে যাবে তোমার শরীরে। আমি নাহয় ফিরতে দেরি করি। কিন্তু তুমি একলা বেরুলেও তো হতো।
হয় না। একলা বেরুনো হয় না। আর কোথায়ই বা যাবে সে! রায়হান সঙ্গে থাকলে সে না হয় যেত কোনো পার্কে। বিকেলবেলা একটু হেঁটে আসত। কিন্তু এ বয়সে একা একা তো আর পার্কে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া কোথাও যেতে তার ভালোও লাগে না। দুপুরে খাওয়ার পর বাইরে বেরোনোর যেটুকু সময় হাতে থাকে, শরীরে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্লান্তি থাকে। আর বেড়ানো-ফেড়ানো খুব যে তার ভালো লাগে, তাও নয়।
তার খারাপ লাগে রায়হানের জন্যে। লোকটার ছিল বেড়ানোর ইচ্ছে। নইলে কক্সবাজার-টেকনাফ বেড়ানোর পরিকল্পনা শেষ না হতেই ইন্ডিয়া বেড়ানোর পরিকল্পনা হয়ে যায়। অথচ ওসবের কিছুই হলো না। তখন তো ওসব সম্ভব ছিল না। সব পরিকল্পনার পেছনেই শর্ত ছিল একটা—অবস্থা যখন বদলাবে, তখন। কিন্তু অবস্থা আর বদলাল কই! ওসব হলো না—এসব নিয়ে কোনো কষ্টে ভোগে না সাহানা। তবে তার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে দিনগুলোই ভালো ছিল। তখন সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু পরিকল্পনা ছিল। এখন সামর্থ্য নেই, পরিকল্পনাও নেই।
পরিকল্পনা নেই কেন? এ কথা মনে হলে সাহানার খুব অবাক লাগে। তবে কি ক্লান্তি? নিজের কথা জানা আছে তার, ক্লান্ত সে। তবে সে বোঝে, রায়হান আরও বেশি ক্লান্ত। সে তো নিজের চোখেই দেখছে। বড় অদ্ভুত লাগে তার। রায়হানের কৈশোর সে নিজের চোখেই দেখেছে। বড় অদ্ভুত লাগে তার। রায়হানের কৈশোর আর বিয়ের আগের সময়ের কথা তার জানাই আছে। সেও বড় কষ্টের সময় ছিল। তবে কি একটা লোক সারাজীবন শুধু পরিকল্পনা করেই যাবে? অথচ তার কোনো সাধ-আহ্লাদ, শখ-আকাক্সক্ষা কিছুই মিটবে না? তার সব পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যাবে?
নিজের কথা মনে হয় না সাহানার। তার রায়হানের জন্যে কষ্ট হয়। এখন রায়হানের চোখে মুখেও এক হতাশার ছাপ। চামড়ায় ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করেছে। অথচ কী এমন বয়স হয়েছে তার! তার যদি বিয়াল্লিশ হয়, রায়হানের আটচল্লিশ-ঊনপঞ্চাশ। এ বয়সে এখন কতজন দিব্যি তরুণ থাকে। রায়হান নাহয় না-ই থাকল তরুণ, বয়স অনুযায়ী ঠিকই থাকলে হতো।
অবশ্য এতটাও চায় না সাহানা। আসলে সে চায় রায়হানের মন প্রফুল্ল থাকুক। বিয়ের পর পর করা ওসব পরিকল্পনার কথা কি মনে নেই রায়হানের? নিশ্চয় আছে, সাহানা নিশ্চিত। আর সে জন্যে রায়হানের কী কষ্ট, সাহানা তাও বোঝে। যারা কল্পনা বেশি করে, যাদের স্বপ্ন বেশি, কষ্ট তো তারাই বেশি পায়। এমন কোনো উপায় যদি থাকত, সাহানার মনে হয়, রায়হানকে যদি এখনো আগের মতো রাখা যেত! এখনো যদি ফিরে, বিয়ের পরের দিনগুলোর মতো, কোনো-না-কোনো পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে বসে যেত। খাতা-কলমে তৈরি হয়ে যেত তাদের ইন্ডিয়া যাওয়া, তাদের ঘর সাজানো, তাদের ছোট্ট একটা বাড়ি।
তাই কি আর হয়, সাহানা মনে মনে হাসে। রায়হান এখন বাড়ি ফেরে রাত আটটা, সাড়ে আটটায়, কোনো কোনোদিন নটায়। তখন যে ক্লান্ত দেখায় তাকে, সাহানা বোঝে, তখন আর রায়হানের কিছুই করার ইচ্ছে হওয়ার কথা নয়। সে তো নিজের দিকটা বিচার করলেও বোঝে। সারাটা দিন তারও যে কীভাবে কাটে! তারপর রায়হান ফিরলে সে তাকে আর কতটুকুই সঙ্গ দিতে পারে! সামান্য যে কথা হয়, তাতো অভাব অনটন, টানাটানি, এ সংসার ঘিরেই। এ সবের বাইরে কিছু বলার মতো সেও খুঁজে পায় না।
আজ আবার রায়হানের বাড়তি ঝামেলা। আকাশকে ডাক্তার দেখানোর টাকা জোগাড় করতে হবে। এখন গোনা-গুনতি কিছু টাকা আছে। তা দিয়ে কোনোমতে মাসটা পার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু আকাশকেও ডাক্তার না দেখালেই নয়। তার কাছে অবশ্য টাকা আছে শ’ তিনেক। না, শতিনেক নেই, পঞ্চাশ তো আজ রায়হানকে দিল মুরগি কেনার জন্যে। আছে আড়াই শ’। রায়হান যদি আজ টাকা জোগাড় করতে না পারে তবে আড়াই শ’ থেকে দুশ যাবে ডাক্তারের ফি’জ হিসেবে। বাকি থাকবে পঞ্চাশ। কিন্তু ডাক্তার যদি দামি দামি ওষুধ কিনতে বলে, কিংবা বলে আকাশকে ‘এখন আবার রক্ত দিতে হবে’? অবশ্য সে কথা ভেবেই বা কী! রায়হান টাকা জোগাড় করতে না পারলেও তার জমানো টাকা দিয়ে আকাশকে ডাক্তার দেখানো যাবে, এটুকুই সান্ত্বনা।
তারপর ডাক্তার যদি দামি ওষুধ কেনার বা রক্ত দেওয়ার কথা বলে, তখন টাকা জোগাড় হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। আগে থেকে ভেবে অস্থির হয়ে লাভ নেই, সাহানা ঠেকে শিখেছে।
নদী ফেরে চল্লিশ মিনিট পর। এতক্ষণ নদীর কথা মনেই ছিল না সাহানার। কিন্তু তাকে দেখেই তার মেজাজ গরম হয়ে যায়—কিরে, এতক্ষণ কি তুই রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি?
নদী একটু বোকার মতো হাসে।
হাসিস না। এই আধঘণ্টা তুই ছিলি কোথায়?
এই তো মা, আনন্দদের বাসায়ই ছিলাম। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।
সাহানার ভ্রু কুঁচকে যায়—ওদের জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? বুঝলাম, ছিলি ও বাসায়। কিন্তু তোর ফেরার কথা কখন?
আহা মা, এতদিন পর গেছি, একটু গল্প করলাম। সায়মা আপা ছাড়ছিল না।
তোর ঠ্যাঙ দুটো ভেঙে দেব। তোর পাড়া বেড়ানো বন্ধ হবে। তখন বুঝবি।
মোটেই আমি পাড়া বেড়াই না।
মুখে মুখে তর্ক করিস না নদী।
বেশ, পাড়া বেড়াই আমি।
ঠিক আছে, তুই পাড়া বেড়াস না। একটু হাসে সাহানা। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন। তুই জলদি করে ঘরগুলো গুছিয়ে নে। এতে তো পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আমি এই ফাঁকে চুলোয় মুরগি চড়িয়ে দেব। কিন্তু রান্না করবি তুই। বুঝতে পারছিস?
আমি? নদী অবাক হয়ে বলে। তুমি কী করবে?
আমি বসে থাকব। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। বিশ বছর হলো।
কী? নদী যেন আরও অবাক হয়ে যায়।
সাহানা ধমকে ওঠে—কিছু না। যা বলেছি তাই কর।
সাহানা সত্যি সত্যি মুরগি চুলোয় চড়িয়ে নদীকে ডাকে। কিছু না বুঝলে আমাকে ডাকিস, বলে সে চলে আসে নিজেদের ঘরে। বিছানায় বসে ভাবে এখন কী করা যায়। নদীকে রান্না দেখার কথা বলার সময়ও তার ধারণা ছিল না যে সে কী করবে। এখনো সে বুঝতে পারছে না। তবে একটা ইচ্ছে করছে তার। বিশ বছর আগের দিনটার কথা ভাবতে বড় ইচ্ছে করছে।
তার খুব অবাক লাগছে এই ভেবে, দীর্ঘ বিশ বছর পার হয়ে গেছে। তবে তাতে বিশ বছর আগের দিনটির কথা ভাবতে কোনো অসুবিধা নেই। সবকিছু তার স্পষ্ট মনে আছে। তার পরনে ছিল কমলা রঙের বেনারসি, রায়হান পরেছিল পাজামা-পাঞ্জাবি। খুব যে একটা হইচই হয়েছিল, তা নয়। কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল নিতান্তই ঘরোয়া।
সাহানার বাবা ছিল না। বিয়েতে মুরুব্বি ছিল দু চাচা। আর রায়হানের তো কোনো মুরব্বিই ছিল না বলতে গেলে। দূরসম্পর্কের এক খালু, কয়েকজন অন্যান্য আত্মীয় আর বন্ধু। এক বন্ধুর নাম ছিল শফিক, এখন বিদেশে, সে খুব ইয়ার্কি মারতে পারত, তার মনে আছে।
বিয়ের পর থেকে তারা দুজন একদম একা একা। সে প্রায় ছোটবেলা থেকেই রায়হানের মা-বাবা নেই। আত্মীয়স্বজনও নেই তেমন। সাহানারও বাবা নেই অনেক দিন হলো। কেউ কেউ অবশ্য বলেছিল, এবার সাহানার মা গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকুক। রায়হানেরও তেমন ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সাহানা জানত, মা যদি আসে, ছোট বাড়িতে তারা খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। মা আসেন নি, বলেছিলেন—নতুন করে অন্য জায়গায় গিয়ে তার ভালো লাগবে না।
মা থাকতেন চাচাদের সঙ্গে। দেশে বাবার কিছু জমিজমা ছিল। চাচারা ভালো, সেই জমি নিয়ে কখনো গন্ডগোল করে নি। প্রতিবছর বাবার প্রাপ্য তারা মা-কে বুঝিয়ে দিত। তবে চাচারাও দেশের বাড়িতে থাকত না বলে সেই জমি সাহানার বিয়ের দু বছর পর বেহাত হয়ে যায়। এক প্রভাবশালী লোক কীভাবে কীভাবে যেন সেসব দখল করে নেয়। চাচারা সে লোকের সঙ্গে এটে উঠতে পারে না। মা মারা যান তার পরের বছর।
তারপর চাচাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ক্রমশ আলগা হয়ে যায়। এখন তো দু বছরেও তাদের সঙ্গে একবার দেখা হয় না। এ নিয়ে মাঝে মাঝে তার খারাপও লাগে বৈকি। চাচাদের একান্নবর্তী পরিবারে সে বেশ ভালোই ছিল। সচ্ছলতা ছিল এমন নয়, মাঝে মাঝে যে অভাবে পড়তে হয় নি মা-কে, তাও নয়। বেশ বড় বাসা, লোক ছিল অনেক। অনেক চাচাত ভাইবোন, তাদের সঙ্গে নানা ভাবে সময় কেটে যেত।
বিয়ের পর প্রথম প্রথম তাই সে ফাঁপরে পড়ে যেত। ছোট একটা বাসা, লোকজনও নেই। রায়হান অবশ্য এটা বুঝত। তাই অফিস ছুটির পর সোজা বাসায়। কোনো কোনো দিন চলে আসত আগেই। কিন্তু মাঝখানে দীর্ঘ সময় একা থাকতে হতো সাহানাকে। রায়হান বলত—তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেরিয়ে তোমার চাচাদের বাসায় গেলেও তো পার। আমি আবার অফিস থেকে ফেরার পথে তোমাকে নিয়ে আসব।
কিন্তু সাহানা রাজি হতো না। চাচার বাসায় একা যেতে তার ইচ্ছে হতো না। সে চাইত রায়হান যাক সঙ্গে, যতক্ষণ সে থাকবে, ততক্ষণ থাকুক তার পাশে। সে তো শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সম্ভব ছিল। কিন্তু দেখা যেত, সেদিনও ঘরে কত কাজ। সাহানার তাই যাওয়া হতো না। মা অবশ্য আসতেন মাঝে মাঝে।
নদীর ডাকে সাহানার ঘোর কাটে। সে একটু বিরক্ত হয়েই দরোজায় দাঁড়ানো নদীর দিকে তাকায়—কী বলছিস?
তুমি একটু যাও তো রান্নাঘরে। আমি একটু ছাদে যাব।
ছাদে কি ধন-দৌলত আছে?
রোদ আছে মা। আমার সালোয়ার-কামিজগুলো শুকোতে দিয়ে আসি।
সাহানা ওঠে। রান্নাঘরে এসে ছোট একটা আড়মোড়া ভাঙে। মুরগির ডেগচির ঢাক নি খুলে চেখে দেখে। হয়ে গেছে প্রায়। নদী তার সালোয়ার-কামিজ শুকাতে দিতে ছাদে গেছে। ধুলো কখন? সাহানা অবাক হয়। রান্না দেখতে দেখতে ধুয়ে ফেলল? তাহলে কোনো একটাতে নিশ্চয় ফাঁকি দিয়েছে? সাহানা হেসে রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
দুই বার্নার গ্যাসের চুলা। এতক্ষণ এক বার্নারই জ্বলছিল। সাহানা মুরগির মাংস নামিয়ে ভাবে এখন একটায় ভাত একটায় ডাল চড়িয়ে দেবে সে। পরমুহূর্তে সে জিব কাটে। একটা ভুল হয়ে গেছে। মুরগি তো তার রাতে রান্না করার কথা। দুপুরে তো রায়হান ফিরছে না। সাহানা বোকার মতো হাসে। বিশ বছর সংসার করার পর এরকম ভুল নাকি কারও হয়! সে তখন ঠিক করে, স্কুল থেকে ফিরে খেতে বসলে শুধু আকাশকে সে একটুকরো মাংস দেবে। বাকিটা তুলে রাখবে।
এখন অন্য একটা তরকারির ব্যবস্থা করতে হয় দুপুরের জন্যে। অসুবিধে হবে না, রায়হান হিসেব করেই বাজার এনেছে। একটা কাজ বাড়ল আর কি। তবে রাতে আবার একটা কাজ কমে যাচ্ছে। সাহানা ‘নদী’ বলে ডাকে। নদী এসে চালটা ধুয়ে দিলে তার কাজ কিছু কমে। তবে শুধু সে জন্যেই নয়। মেয়েদের এসব কাজ ভালো মতো শিখে রাখাও দরকার।
কিন্তু নদীর কোনো সাড়া নেই। সাহানা অবাক হয়, রেগেও যায়। নদী কি সারা দিন ছাদে কাটাবে বলে স্কুলে যায় নি? সে আবার গলা উঁচিয়ে ডাকে। নেই, অর্থাৎ নিশ্চিত হওয়া যায় ছাদ থেকে নামে নি। একবার রান্নাঘরে চোখ বুলোয় সাহানা। তারপর বেরিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগোয়। সিঁড়ি বাড়ির এক পাশে। এখন ছাদে উঠলে একতলায় পুরোটাই কিছু পরিমাণে অরক্ষিত থেকে যায়। সাহানা তাই সিঁড়ির মুখে এসে নদীকে আবার ডাকে। নদী শুনলে আরেকটা সুবিধা। তাকে আর অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।
কিন্তু নদী শোনে না।
এতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করে না। হাঁপ ধরে যায়। পারতপক্ষে তাই ছাদে উঠতে চায় না সাহানা। কিন্তু এখন কী উপায়! নদীর ওপর খুব রাগ হয় তার। সে ঠিক করে খুব ভালো করে ধমকাবে সে নদীকে।
তিনতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে উঠে সে একটু থামে। এখন বাঁয়ে তিনটা সিঁড়ি টপকে চিলেকোঠার মতো জায়গাটুকু পেরোলেই ছাদ। সামনে যেন মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ। সাহানা বোঝে না। সে বাঁয়ের সিঁড়ি তিনটে টপকে নদীকে ডাকার জন্যে মুখ খোলে। নদীকে ডাকা হয় না তার, তার খোলা মুখও বন্ধ হয় না।
প্রথমে যেন সে কিছুই বোঝে না। তারপর তার কান্না পায়। ছেলেটাকে চিনতে পারে সে। দোতলার জসিম সাহেবের ছেলে ইমরান। ছেলেটা তাকে যেন কেয়ারই করে না। পাশ কাটিয়ে নেমে যায় দ্রুত। আর নদী কেঁদে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকে। নদীর কোনো দোষ নেই। সাহানা ওই দৃশ্য দেখেই বুঝেছে। কিন্তু তার সব রাগ নদীর ওপরই গিয়ে পড়ে। সে প্রচণ্ড এক চড় কষায় নদীকে। তারপর প্রায় টেনে-হেঁচড়ে নামায় নিচে। তাতেও তার রাগ পড়ে না। কেন নদী ছাদে গিয়েছিল! কেন ও ছেলেটাকে দেখে বাজে মতলব বোঝে নি। সাহানা নদীকে মেরেই যায়। সে শুধু চোখের সামনে দেখে, তার মেয়ে, নদী, এক জানোয়ারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। সে জানোয়ার পাশ কাটিয়ে চলে গেছে সাহানার, তাকে ধরা যায় নি। সাহানা নিজের মেয়েকে ধরে এনেছে।
মারতে মারতে একসময় সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে যায়। চেঁচিয়ে বলে—কেন, কেন তুই চিৎকার করে আমাকে ডাকিস নি? এ প্রশ্ন করেই সে অবশ্য বোঝে, চিৎকার না করে নদী ভালোই করেছে। এসব চিৎকার করে কাউকে জানানোর ব্যাপার নয়। তখন সাহানার রাগ হু হু করে আবার বেড়ে যায়। সে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় নদীকে, যা, সরে যা আমার সামনে থেকে।
নদীকে সরিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সাহানা। মাংসের ডেগচি উপুড় করে দেয় মেঝেতে। কিন্তু তার রাগ কমে না। তার কান্নাও পায় ভীষণ।
চার
স্কুল ছুটির পর নদীর কাজ আকাশদের স্কুলে যাওয়া। স্কুল পাশাপাশিই, সুতরাং নদীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু এ ব্যবস্থাটা তার পছন্দ নয়। সে একটু বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসবে, সেটা হয় না। আকাশের সামনে অনেক কথাই বলা যায় না। এমন চোখে তাকিয়ে থাকবে যে লজ্জা পেতে হবে। কিংবা, বলা যায় না, বাসায় এসে বলেও দিতে পারে। আকাশ তো ওর বন্ধুদের সঙ্গেই দিব্যি যেতে-আসতে পারে। এই যেমন, আকাশের সঙ্গে পড়ে আনন্দ। আনন্দদের বাড়ি ওদের বাড়ির কাছেই। ওরা দুজনই যেতে-আসতে পারে। কিন্তু মা নাকি তাতে স্বস্তি পায় না। তাই স্কুল যাওয়া-আসার সময়টুকুর আনন্দ মাটি হলেও নদীকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছে।
কোনো কোনো দিন একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়। জেসমিন আর আনিসা এমন হারামি, রাস্তার মধ্যেই তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করে। তারা পাঁচজন বাড়ি ফিরছে একসঙ্গে। সে আনিসা, জেসমিন, তৃষ্ণা আর আকাশ। জেসমিন হাঁটতে হাঁটতে গম্ভীর মুখে তাকে চিমটি কাটে—ওই যে, আসছে।
নদী জানে কে আসছে। সুতরাং সে কিছু বলে না, তাকায়ও না কোনোদিকে।
জেসমিন তখন আবার চিমটি কাটে, আহা, দ্যাখ না নদী, তোর ইমরান খান আসছে।
আসুক। তাতে তোর কী?
আমার কিছুই না। কিন্তু ইমরান খান যে আমাদের পেছনে পেছনে আসছে, এটা তুই নাও জানতে পারিস। তাই তোর একটু উপকার করার চেষ্টা করছি।
দরকার নেই।
কী যে বলিস! আমরা তোর বন্ধু না। এবার আনিসা বলে।
বন্ধু হলে দয়া করে চুপ করে থাক। আকাশ শুনলে বাসায় গিয়ে লাগাবে আর আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।
আরে ধাৎ, ও কিছু বুঝবে না।
তৃষ্ণা হাসে—ও কথা বলিস না আনি। বুঝবে ঠিকই। ছেলে কম বড় হয়েছে?
কত বড় হয়েছে রে। জেসমিন মুখ টিপে হাসে। তুই মনে হচ্ছে কোনো গোপন খবর জানিস?
তৃষ্ণা সে হাসি ফিরিয়ে দেয়—বড় হয়েছে রে। তুই ওকে একটা চিঠি লিখে দ্যাখ, উত্তর যদি না দেয়।
তোর মনে হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
ওর বয়সী আমার একটা মামাত ভাই আছে রে। চান্স পেলেই...।
চান্স পেলেই, কী?...নাকি তুই উল্টো চান্স দিস ওকে।
ইমরান বিরক্ত হয়—তুমি শুধু কথা প্যাঁচাও।
কখনো না। আমি যা বলি সোজাসুজি বলি।
তাহলে তুমি সোজাসুজি বলছ যে তোমাকে আদর করতে দেবে না?
কী বলে, নদী, এ কথার উত্তরে? ইমরানের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর থেকে সে এমনিতেই ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে। বাড়িতে জানাজানি হলে কী কেলেংকারি যে হবে, সে বুঝতে পারে। তার ওপর ইমরানের এই বাড়াবাড়িতে সে অস্থির হয়ে যায়। কতরকম যে আবদার ইমরানের। হঠাৎ একদিন বলে বসলো—তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?
নদী অবাক—কোথায় আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি না। এই তো বলছি।
না, তুমি শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে, একটু একটু কথা বলো আমার সঙ্গে।
নদী হেসে ফেলে—সবার সামনে কি তোমার সঙ্গে কথা বলা যায়, বলো?
সে আমি বুঝি না। আমি চাইলেই তোমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে।
এরকম কত পাগলামি যে আছে ইমরানের। অথচ পড়াশোনায় কোনো মনোযোগ নেই। ম্যাট্রিকে তো একবার ফেল করেছে, নদী জানে। ইন্টারমিডিয়েটেও যদি সেরকম কিছু করে বসে! পরীক্ষারও আর বেশি বাকি নেই। নদী বলে বলে হয়রান। অথচ পড়াশোনার কথা ইমরান শুনতেই চায় না। নদী কিছু বললেই বলে—আরে, রাখ তো ওসব আজে-বাজে কথা। এতসব পড়াশোনার আলাপ আমার একদম ভালো লাগে না।
ভালো লাগে না বুঝলাম। কিন্তু পাস তো করতে হবে।
সে দেখা যাবে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা। এখন ওসব বলে কি হবে?
এটা একটা কথা হলো!
কিন্তু কে বোঝায় ইমরানকে। নদী তাকে সামাল দিতে দিতে অস্থির। আর সপ্তাহ দুয়েক হলো নতুন বাতিক হয়েছে তার, নদীকে সে আদর করবে। প্রথমে শুনে তো ভয়ে একদম সিটিয়ে গেছে নদী। কিন্তু ইমরান নাছোড়বান্দা। কোনো কথাই শুনতে সে রাজি না। আর একের পর এক এমন সব যুক্তি খাটায়। গত পরশু বলল—সত্যি করে বল তো, তুমি আমাকে ভালোবাসো?
নদী সন্ধেবেলা একটু সময় করে চিলেকোঠায় এসেছে। এখনই চলে যেতে হবে। নইলে মা হয়তো সন্দেহ করবে। ইমরানকে বেশিক্ষণ না দেখে সে থাকতে পারে না বলেই এই রিস্কটুকু নেওয়া। আর ইমরান কিনা এ সময়ে এই প্রশ্ন করে বসে! নদী রেগে যায়—এইসব কথা কেন বলো তুমি! তুমি কি বোঝ না আমি তোমাকে ভালোবাসি কি ভালোবাসি না?
না, বুঝি না। তুমি কখনো ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছ?
এ কথার উত্তরে কিছু বলার নেই। যদি কেউ না বোঝে তাকে কি জোর করে বোঝানো যায়! নদী এই যে এতকিছু করছে, লুকিয়ে দেখা করছে, চিঠি লিখছে; এসব কি ইমরান বুঝবে না? নদীর খুব রাগ হয়। সে অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে, কী প্রমাণ দিতে হবে আমার ভালোবাসার?
তোমাকে আদর করতে দিতে হবে।
কয়েকদিন হলো কানের পাশে ‘আদর আদর’ শুনতে শুনতে, এখন নদীরও যে একটু একটু ইচ্ছে করছে না, তা নয়। বরং এ কথা সে অনেক আগেই ভেবেছে। আর তার নিজেরও ভীষণ ইচ্ছে করে ইমরানকে আদর করতে। কিন্তু তার লজ্জা আছে না! তা ছাড়া ইমরান বললেই সে যদি রাজি হয়ে যায় তবে ইমরানই বা কী ভাববে তাকে? সে গম্ভীর গলায় বলে, আমি যদি তোমাকে আদর করতে দিই, তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি?
ইমরান একটু বোকা বনে যায়—আদরটা তো ভালোবাসারই ব্যাপার।
বুঝলাম। কিন্তু এখন না। সময় হলে হবে।
সময় কখন হবে?
বিয়ের পর।
ইমরান রেগে যায়—আমার অনেক বন্ধু ওদের প্রেমিকাদের সঙ্গে কী কী করে তা যদি তুমি জানতে!
জানলে কী হতো?
আমাকে না করতে না।
ঠিক আছে। নদী মাথা ঝাঁকায়। আমি তোমাকে আদর করতে দেব।
তাহলে চল কাল এক বন্ধুর বাসায় যাই আমরা। তুমি স্কুলে না গিয়ে আমার সঙ্গে চলে যাবে। সারা দিন থাকব আমরা। তারপর আবার ছুটির আগে তোমাকে স্কুলের সামনে পৌঁছে দেব।
শুনে নদী শিউরে ওঠে। সে রাজি হয় না। শেষে ঠিক হয়, এখানেই। প্রস্তাবটা ইমরানই দেয়। এখানে, এই চিলেকোঠায়—শুনে নদী এবারও আঁতকে ওঠে।
কেন, এখানে কীসের অসুবিধা বলো। কেউ তো এখানে আসে না। তা ছাড়া পায়ের শব্দে আমরা তো টের পাবই কেউ আসছে কি না।
নদী নিমরাজি হয়। এবং প্রায় তখনই সে নিচে নেমে যায় মার ডাক শুনে।
তার পরদিন নদীকে আটকায় ইমরান। বিকেলের দিকে ভিসিআর দেখতে সে পাশের বাসায় যাচ্ছিল। ইমরান জিজ্ঞেস করে—তাহলে কী ঠিক করলে তুমি?
নদী বলে—কিন্তু সন্ধের সময় আমি যদি বাসা থেকে বের হতে না পারি? সেদিন পেরেছি বলে রোজই যে পারব এমন তো কোনো কথা নেই।
সন্ধ্যার সময় কেন! ইমরান বলে। তুমি দুপুরবেলা আসো।
দুপুরবেলা? নদী অবাক হয়ে যায়। আমার স্কুলে যেতে হবে না!
একদিন নাহয় না-ই গেলে স্কুলে। তুমি ভেবে দেখ, দুপুরবেলাই সবচেয়ে সেফ।
ভেবে দেখলে, তাই। কিন্তু দুপুরবেলা ব্যাপারটা ঘটবে কীভাবে? সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ইমরান বলে—তুমি তো স্কুলে যাবে না। তারপর বারোটা, সাড়ে-বারোটার দিকে কাপড় শুকোবার নাম করে চলে আসবে ছাদে। তারপর আবার একটু পরই তো নেমে যাবে। তোমার মা বুঝতেই পারবে না।
এ পরিকল্পনাই চূড়ান্ত হয়েছে।
জেসমিন আর আনিসার কথা শুনে নদীর খুব রাগ হয়েছিল। সে একবার ভেবেছিল ওদের মুখের ওপরই বলে দেবে—কীসের প্রেম আমরা করি, তা তোরা দেখতে চাস? তাহলে কাল দুপুরে আমাদের ছাদে চলে আয়।
সে অবশ্য ওদের বলে নি কিছুই। সে কি বোঝে না, কেন ওদের এসব খোঁচা-মারা কথা। হিংসা, হিংসা ওদের, সে ঠিকই বোঝে। ঠিক আছে, করুক হিংসা, সে ওদের কিছুই জানাতে যাবে না।
সে গম্ভীরমুখে ওদেরকে এড়িয়ে আকাশের পাশে চলে গিয়েছিল। কিছুদূর এগিয়ে দুদিকে পথ। জেসমিন, আনিসা আর তৃষ্ণা, ‘তবে যাইরে সুন্দরী, এবার তোর ইমরান খানকে নিয়ে তুই একা একাই যা’ বলে অন্য পথে চলে গেল। আর সামান্য হাঁটলেই বাড়ি। নদী একবার পেছনে ফিরে তাকাল। ইমরানের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। এখনো পেছনে পেছনে আসছে। নদী চোখের ইশারায় সরে যেতে বলল, ইঙ্গিতে দেখাল আকাশকে। কিন্তু ইমরান যেন ওসব কিছুই বুঝল না। সে বরং দ্রুত পায়ে আরও কাছে চলে এল। নদী আর আকাশকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল—কাল ঠিক সাড়ে বারোটায়। মনে থাকে যেন।
নদী একবার আকাশকে দেখল। না, আকাশ কিছুই শোনে নি ও বোঝে নি। নদী তখন মনে মনে হেসে ফেলল। ইমরানের কী যে সাহস আর পাগলামি! সাহস আর পাগলামোটুকু অবশ্য ভালোই ভাগে তার।
বিছানায় উপুড় হয়েও নদী তার কান্না থামাতে পারে না। কে জানত, ইমরানের ওই সাহস আর পাগলামোই শেষপর্যন্ত সর্বনাশ হয়ে দাঁড়াবে! মা তাকে মেরেছে খুব, কিন্তু ব্যথা করছে না তার। তার শুধু ভয় হচ্ছে। বাবা ফিরলে মা নিশ্চয় বাবাকে বলবে। তারপর বাবা যদি গিয়ে ইমরানের বাবাকে বলে দেয়! নদী ভেবে কূল পায় না, তখন কী হবে! এই ভয়ে সে কান্নাও থামাতে পারে না। তবে সে স্বস্তিও বোধ করে এর পাশাপাশি, মা এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারে নি।
সকালে সে যখন মাকে বলে, আজ সে স্কুলে যাবে না, মা কিছুই বলে না। তারপর হঠাৎ যখন মা তাকে রান্নার দায়িত্ব দেয়, তখন সে শঙ্কা বোধ করে। হয়তো দেখা যাবে মুরগি রান্না হতে হতেই সময় পেরিয়ে গেছে। অবশ্য মা যখন জানায় আজ তাদের বিবাহবার্ষিকী তখন আবার স্বস্তি বোধ করে সে। তাহলে মা-র মেজাজ আজ নিশ্চয় ভালো থাকবে। ছাদে যদি একটু দেরিও করে সে, মা কিছু বলবে না।
মা তাকে রান্নার দিকে নজর রাখতে বলে ভেতরের ঘরে চলে যায়। তার একটু পরই সে বাথরুমে ঢুকে একটা সালোয়ার-কামিজ পানিতে ভিজিয়ে রাখে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে। বার দুয়েক রান্নার দিকে নজর দেয়। তারপর ঘরে গিয়ে মাকে বলে একটুক্ষণের জন্যে রান্নাঘরে যেতে, সে কাপড় শুকাতে দিতে যাবে ছাদে। ভয়ে তার বুক ঢিব ঢিব করে। বারবার তার মনে হয় মা বুঝি সব টের পেয়ে গেছে। বলবে, না, এখন তার যাওয়া লাগবে না ছাদে।
সে রকম কিছু আবশ্য ঘটে না। মা শুধু একটু বিরক্ত হয়। নদী এক ছুটে চলে আসে চিলেকোঠায়। আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে সে। ইমরান তাকে দেখে গম্ভীর গলায় বলে, এতক্ষণে তোমার সময় হলো! আমি সেই কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।
নদী হাসে—বোঝ না তো, কতরকম যে ঝামেলা।
ইমরান তখনই তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। নদী ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে—আরে আরে, কাপড়গুলো আগে শুকোতে দিয়ে আসি।
সে কাপড়গুলো ছাদে বাঁধা দড়ির ওপর মেলে দিয়ে ফিরলে ইমরান আবার তাকে জড়িয়ে ধরে। নদী বলে—শোন, একবার কিন্তু।
হু একবার! ইমরান মুখ নামাতে নামাতে বলে। কত কষ্টে তোমাকে কাছে পেয়েছি।
দেরি হলে কিন্তু মা সন্দেহ করবে।
কথা বোলো না তো। আদর করতে দাও।
প্রথমে সামান্য আড়ষ্ট নদী। সে অনেকটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রমশ সে টের পায় শরীরে কোথায় যেন কাঁপুুনি। সে ক্রমশ বোঝে, কোথায় যেন নয়, আসলে সারা শরীরই কাঁপছে তার। শরীরের এই কম্পন থামানোর জন্যই সে যেন ইমরানকে সবেগে জড়িয়ে ধরে। সে ক্রমশ, কী এক ঘোরের মধ্যে চলে যায়। সে বোঝে সময় থেমে গেছে চারপাশে এবং নিজের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
একটিবার, ইমরান তাকে একটিবার আদর করবে, এমন কথা ছিল। কিন্তু এখন নদী যেন অনন্তকাল এভাবে থেকে যেতে প্রস্তুত। যতটা বিক্রম ইমরান দেখায়, সে তারচেয়ে কম যায় না। এই ঘোর কাটে হঠাৎ করে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো। সে আর্তনাদের মতো করে ওঠে—না ইমরান, না। তুমি ওখানে কেন হাত দিচ্ছ!
ইমরান তার কথা শোনে না।
প্লীজ ইমরান, এখন আমাকে যেতে হবে।
না, আরেকটু।
আরেকদিন, প্লীজ, আরেকদিন হবে। দেরি হলে মা সন্দেহ করবে।
না, আমি তোমাকে দেখব।
দেখছই তো।
না, এভাবে নয়। আমি তোমার সবটা দেখব।
নদী কঁকিয়ে ওঠে। তার একবার মনে হয়, দেখুক ইমরান। ইচ্ছে করে তার। ইচ্ছে করে ইমরান আরও প্রবল হয়ে উঠুক। কিন্তু, বাধা দেওয়া উচিত—তার এমনও মনে হয়। সে তখন নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ছটফট করে ওঠে।
ইমরান আরও জোরে ধরে রেখেছে তাকে। নদী বোঝে, এখন কিছুই শুনবে না সে ছেলে। সে তাই আপ্রাণ চেষ্টা করে। কেন এসেছিল, এই ভেবে তার কান্না পায়। ইমরানের হাতের টানে তার কাঁধের কাছে কামিজটা অনেকখানি ছিঁড়ে যায়। সে তখন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ধাক্কায় সে সরিয়ে দিতে চায় ইমরানকে। ঠিক তখনই সে দেখে, তার পাশেই বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে মা।
দুপুরে খেতে যায় না নদী। মা একবার এসে গম্ভীরমুখে ডেকে যায়। সে ওঠে না। মা কতক্ষণ পাশে বসে তার চুলে হাত বুলোয়। নদী মুখ তোলে না।
চিলেকোঠার পাশেই মাকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কী সর্বনাশ হয়ে গেল! কিন্তু সেটা বড়জোর মিনিটখানেকের জন্যে। তার পরপরই সে অনুমান করেছিল, মা আসলে কিছুই বুঝতে পারে নি। মিনিট-তিনেকের মধ্যে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে যায়। একটা কথাও সে বলে না। শুধু মা-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোঁপায়।
আর তারপর, মা যখন পাশে বসে তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়, সে নিজেকে আরও গুটিয়ে ফেলে। সে বোঝে, এখন সহজ হওয়া যাবে না, এখন এত তাড়াতাড়ি সহজ হয়ে উঠলে মা-র সন্দেহ হতে পারে। পাশাপাশি ইমরানের ওপরও প্রচণ্ড রাগ হয় তার। সে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়েই যায়।
বিকেলের দিকে সে বিছানায় উঠে বসে। এখন বোধহয় একটু সুস্থির হওয়ার ভান করা যায়। এখন ঠান্ডা মাথায় একটু ভাবতেও হবে। সামনে বিপদ দুটো, অনুমান করা যায়। এক, মা এখন তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখবে। ইমরানের সঙ্গে তার দেখা করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দুই, বাবা ফিরলে মা তাকে সব বলে দেবে। বাবা তখন রাগের মাথায় ছুটে যেতে পারে ইমরানের বাসায়। তখন ইমরানও পড়বে ঝামেলায়। তা ছাড়া তখন যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ...।
তবে, নদী অনুমান করতে পারে, প্রথমটির ভয় বেশি। মা তাকে আগলে রাখবে বলে সে ইমরানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে না। সুযোগ না পাওয়াই ভালো, সে মনে মনে বলে। ইমরানের ওপর খুব রাগ হচ্ছে তার। ওর জন্যেই তো এতসব ঝামেলা।
ইমরানের প্রতি তার এই রাগ অবশ্য ক্রমশ কমে যায়, বরং তার জন্যে কী এক কষ্ট হতে থাকে তার। সে ঠিক করে, ইমরানকে আজ রাতেই চিঠি লিখবে সে। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে ইমরানকে চিঠি লিখবে। জানাবে, তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মা কিছুই বুঝতে পারে নি। আর, আরেকটা কাজ তাকে করতে হবে। তাকে লেখা ইমরানের চিঠিগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে আরও গোপন কোনো জায়গায় যেন কেউ কোনোভাবেই কোনো খোঁজ না পায়।
পাঁচ
সাগর, অ্যাই সাগর।
বায়েজীদ দুবার ডাকে, সাগর সাড়া দেয় না। সে শুধু পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বায়েজীদ। সাড়া না পেয়ে ক্ষুণœ হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখে সাগর উঠে বসে। সে সবই দেখেছে। কিন্তু বায়েজীদকে রাগাতে তার ভালো লাগে। এত অল্পতেই তার মুখ এমন থমথমে হয়ে যায়।
সাগর উঠে বসে বায়েজীদের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। দুটান দিয়ে সে গলা তুলে বায়েজীদকে ডাকে। জানা আছে, এখন আস্তে ডাকলে সে আসবে না ঘরে। বায়েজীদ যেন আরও বিরক্ত হয়। সে ঘরে ঢুকে রাগ রাগ চোখে তাকায়—অমন হেড়ে গলায় চিল্লাচ্ছিস কেন?
আমার গলা হেড়ে, দোস্ত?
হ্যাঁ। ডাকছিস কেন তাই বল?
তোর মুখ অমন থমথমে কেন, সেটা জানতে ইচ্ছে হলো।
আমি ছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অতদূর থেকে তুই কীভাবে বুঝলি আমার মুখ থমথমে? আমার মুখও তো দেখিস নি।
বুঝলাম দোস্ত। সাগর একটু হাসে। আফটার অল আমি তোর বন্ধু, এটুকুও যদি না বুঝি...।
হ্যাঁ, ধন্য করেছিস আমাকে। তবে আমার মুখ কেন থমথমে সেটা তোর জানার দরকার নেই।
আমি অবশ্য কিছুটা বুঝতে পারছি।
কী বুঝতে পারছিস তুই?
এই যেমন তোর বিছানায় আমি শুয়ে আছি, যখন যা ইচ্ছে হচ্ছে তোর ফ্রিজ খুলে খাচ্ছি, তোর সিগারেট ধ্বংস করছি। কিন্তু যাওয়ার নামটি করছি না। এ কারণে বোধ হয় তোর মুখ থমথমে।
বায়েজীদের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়।
সাগর নিপাট ভদ্রলোকের মতো বলে—তোর প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট নিয়েছি আমি। মাইন্ড করিস নি তো?
বায়েজীদ কটমট করে তাকায়।
অনেকক্ষণ হাসে সাগর—আচ্ছা, তোর এমন মেয়েদের স্বভাব হয়েছে কেন বল তো?
আমার স্বভাব মেয়েদের মতো?
হ্যাঁ, কিছু বললেই তোর চোখ এমন ছলছল করে! যেন প্রেমিক প্রেমিকাকে কিছু রুঢ় কথা শোনাল। তুই এমন কেন করিস?
তবে কি তোর মতো করব?
হ্যাঁ, আমার মতো করবি।
তাহলে তো আমাকে আবার গরিব হতে হবে।
কেন কেন?
তুই গরিব, তোর ঘোড়া রোগ হয়েছে। কিন্তু দোস্ত, আমি বড়লোক, আমার তো আর তোর মতো ঘোড়া রোগ হতে পারে না।
হাসতে হাসতে বিষম খায় সাগর—তুই শুধু বড়লোক নারে, তুই দেখছি বুদ্ধিমানও।
বুদ্ধি ছাড়া বড়লোক হওয়া যায় না। আমার বাবা বুদ্ধিমান ছিল, আমিও।
কিন্তু আমার যে মাঝে মাঝে মনে হয়, তোর চেয়ে আমার বেশি বুদ্ধি। তবে আমি কেন বড়লোক হতে পারি না?
নাথিং নিউ। বায়েজীদ হাসে। সব গরিবই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। আসলে তা নয়।
সাগর অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বায়েজীদের দিকে। একসময় সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায়—হয়তো তাই-ই। হয়তো ঠিকই বলেছিস তুই। সব গরিবই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু আসলে তা নয়।
তোর হয়েছেটা কী?
কোথায়?
আজ একটু বেশি বেশি আবোল-তাবোল বকছিস।
আজ আমার বেশি বেশি মনে হচ্ছে আমি গরিব, আমি গরিব। কে যেন কানের পাশে অনর্গল এই কথা বলেই যাচ্ছে।
তুই নিজেই বলছিস।
সাগর একটুক্ষণ ভাবে—হবে হয়তো।...আমার তো সমস্যা আসলে এই একটাই—আমি কখনো গরিব থাকতে চাই না।
কোনো গরিবই গরিব থাকতে চায় না।
এতসব থিওরি ঝাড়িস নাতো। তোর মতো ননীর পুতুলদের মুখে এসব কথা মানায় না।
না মানাক, বুঝি তো।
তুই ছাই বুঝিস। আমি আর সব গরিবের মতো নই।
তাই নাকি? আমি তো তোকে শুধু গরিবই বলে জানি।
আমি গরিব বটে, তবে ইন্টেলেকচুয়াল গরিব।
সেটা তো আরও খারাপ রে। শুধুই কষ্ট।
সাগর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আরেকটা ধরায়। বায়েজীদের দিকে তাকিয়ে বলে—ঠিকই বলেছিস তুই। শুধুই কষ্ট। বলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।
বায়েজীদ হাসি মুখে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। ফ্রিজ খুলে সে দুটো বিয়ারের ক্যান বের করে। একটা ছুড়ে দেয় সাগরের দিকে—বাড়ি ফিরবি না?
না।
আসলে তুই-ই আছিস ভালো।
রাতে বাড়ি ফিরব না—এটাকে তুই ভালো থাকা বলছিস? জানিস না আমি কেন ফিরব না?
জানি। ওই অভাবের মধ্যে তোর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।
হ্যাঁ। ওই অভাবের মধ্যে আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।
এখানে থাকলেই তুই বড়লোক হয়ে যাবি না। বরং পার্থক্যটা বেশি বেশি চোখে পড়বে। তখন আরও বেশি বেশি খারাপ লাগবে।
আবার আঁতেল মার্কা কথা ঝাড়ছিস! সাগর রেগে যায়।
বায়েজীদ নির্বিকার মুখে বলে—তুই বড়লোক হতে চাস?
সাগর সামান্য হাসে—যদি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেতাম...।
পাবি না। বায়েজীদ মাথা নাড়ে। তাছাড়া যারা বড়লোক তারা কি সবাই আশ্চর্য প্রদীপ পেয়ে বড়লোক হয়েছে?
আমার পেতে ইচ্ছে করে। অন্য কোনোভাবে আমার পক্ষে বড়লোক হওয়া সম্ভব না।
ঠিক গরিবের মতো কথা বলেছিস। আসলে তোর মানসিকতাও গরিব। মাঝে মাঝে বোঝা যায়।
সাগর হাসে—সারাক্ষণ হাঁ-অভাবের মধ্যে থাকলে তুই-ও আমার মতোই ভাবতি।
তোকে অবশ্য বড়লোক হওয়ার একটা বুদ্ধি আমি বাতলে দিতে পারি। প্রথমত, কবিতা লেখাটা ছেড়ে দে। কবিতা অবশ্য তুই খুবই ভালো লিখিস। তবু বলছি, ছেড়ে দে।
সাগর এবার সত্যি সত্যিই রেগে যায়—লাত্থি মারব হারামজাদা। তুই কবিতার কী বুঝিস যে ছেড়ে দিতে বলছিস! তুই একটা গাধা, নইলে তুই বুঝতি কবিতার সঙ্গে গরিব বা বড়লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। কবিতা অন্য ব্যাপার।
বায়েজীদের মুখে মিটি মিটি হাসি—তুই কোনোদিন বড়লোক হতে পারবি না সাগর।
কেন? কবিতা লেখা ছাড়তে পারব না বলে?
হ্যাঁ। তোকে যে বললাম, কবিতা লেখা ছেড়ে দে—এটা একটা কথার কথা। আসলে বড়লোক হতে গেলে জীবনের অনেক প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিতে হয়।
আবার থিওরি?
বাদ।...এখন খাবি?
তোদের বাসার সবাই খেয়েছে?
আমাদের বাসার সবাই খেয়েছে কি-না, তা দিয়ে তোর কি দরকার?
না, ধর, নিচে নেমে খাবার টেবিলে বসার পর তোর মা-র মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তোর মা আমাকে একেবারেই দেখতে পারেন না।
বায়েজীদ হাসে—সেটাই স্বাভাবিক নয়? আমার বাবা বনেদি বড়লোক। কিন্তু আমার মা গরিব ফ্যামেলী থেকে এসেছে। বাবার বোধহয় মা-র চেহারা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।...যাকগে, নিজেও গরিব ফ্যামিলি থেকে এসেছে বলে মা তোকে দেখতে পারে না।
তাই নাকি!
ঠাট্টা ভাবিস না। সত্যিই তাই। হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেলে কোনো গরিবই আর অন্য গরিবকে সহ্য করতে পারে না।
তুই কি গরিবদের নিয়ে রিসার্চ করছিস বায়েজীদ? আমি কি অনেক গিনিপিগের একটি?
যা ভাবিস।...দাঁড়া, আমি বরং এ ঘরেই খাবার দিতে বলে আসি।
বায়েজীদ বেরিয়ে গেলে সাগর বিছানা ছেড়ে নামে। বিয়ারের ক্যান নিয়ে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুই তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে সবকিছু এমন অর্থহীন মনে হয়। এই এখন যেমন সে বিয়ারের ক্যান হাতে দাঁড়িয়ে আছে বায়েজীদের ঘর-সংলগ্ন বারান্দায়, এটাও তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বা করবে সে! সে বিয়ারটুকু শেষ করে ক্যানটা ছুড়ে দেয় ঘরের ভেতর। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা ফেলে দেয় নিচে। এসবে বায়েজীদের খুব আপত্তি। সে পাশে থাকলে এখন বলত, সবকিছুরই নির্দিষ্ট জায়গা আছে। তাই কি, সবকিছুরই কি নির্দিষ্ট জায়গা আছে? আর, সবার অবস্থানও কি আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে? এই, তার যেমন? হাঁ-মুখ অভাবের ভেতর তার জন্ম। সেই অভাবের ভেতরই কি তার সারাজীবন থেকে যেতে হবে? বাবার মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে, মা-র মুখ, তারপর নদী আর আকাশের। সজোরে মাথা নাড়ে সে। না, মানে হয় না, কোনো অর্থ হয় না এই জীবনের। সে তো সেই কবে থেকে দেখছে কী অসার, কী ফাপা এই জীবন! তারা জোর করে হাসে, জোর করে আনন্দ করে, তারা প্রতিনিয়ত সুখী হওয়ার ভান করে। সাগর জানে, সে যদি বাবা কিংবা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—এ জীবনে তুমি কি সুখী; তবে উত্তর আসবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু ওটা অ্যাবসার্ড, ওটা সুখের ভান করা। ও জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব না।
এই ভানটুকু খুব অপছন্দ সাগরের। তার মনে হয় বাড়ির সবাই প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে। তাই বাড়ি ফিরতে তার ইচ্ছে করে না। আর অত অভাবের মধ্যে ফিরেই বা কি। শুধু এটা নেই, ওটা নেই। তার পরীক্ষার ফি’জ নেই, নদীর সালোয়ার কামিজ কেনার টাকা নেই, আকাশকে ডাক্তার দেখানোর উপায় নেই। এত নেই নেই-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে আরও অসহায় মনে হয় সাগরের। হ্যাঁ, বায়েজীদকে সে ঠিকই বলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা তার কানের পাশে কে যেন বলেই যায়—তুমি গরিব, তুমি গরিব। আর তাই সে পালিয়ে বেড়ায়।
বায়েজীদ ফিরে আসে। সাগর তার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক ঠিক উত্তর দিবি?
খাবার এ ঘরে দেওয়ার কথা বলে এলাম। বায়েজীদ বলে।
আহা। সাগর বিরক্ত হয়। আগে আমার কথাটার উত্তর দে। তোর কি কখনো মনে হয় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি?
কোত্থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস? এ দেখি আবার মারফতি লাইনের কথা আরম্ভ করলি।
না। তুই দ্যাখ, এই যে আমি লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই না, এড়িয়ে যাই, এই যে আমি নিজের বাসায়ও ফিরতে চাই না অভাবের মুখ দেখতে হবে বলে—এটাকে তুই পালিয়ে বেড়ানো বলবি? আমি কি তবে এসকেপিস্ট?
বায়েজীদ অল্প অল্প হাসে—এটা আর নতুন করে বলার কী আছে? তুই তো প্রতিমুহূর্তেই রিয়ালিটি থেকে এসকেপ করছিস।
আমি তাহলে পরাজিত?
বায়েজীদ কতক্ষণ স্থির চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, বিয়ার খেয়ে তোর নেশা হয়ে গেছে রে গরিবের ছেলে, বিয়ার খেয়েই তোর নেশা হয়ে গেছে।
সাগর বড় একটা হাই তোলে—আমি গিয়ে এখন শুয়ে পড়ব। ডাকিস না যেন আমি ঘুমাব।
রাতে না খেয়ে শুতে হয় না।
এবার সাগর শব্দ করে হেসে ফেলে—তুই না সত্যিই মেয়েদের মতো। ছোটবেলায় মা বলত এভাবে। তুইও দেখি সেভাবেই বলছিস!...অবশ্য এ জন্যেই তোকে আমার বেশি ভালো লাগে।
তাই নাকি? শুধু এ জন্যে?
তুই অবশ্য ভালো নকলও করতে পারবি। মেমোরিও খুব ভালো তোর।
এসব আবার কী বলছিস?
বলব না মানে! শালা! তুমি এতক্ষণ আমার কথাগুলোই আমাকে ঝাড়লে। গরিবদের সম্পর্কে যা যা আমি বিভিন্ন সময়ে বলেছি, তাই তুমি সুযোগ বুঝে আবার আমাকে ঝেড়ে দিলে।
এটা তো একটা বিশেষ যোগ্যতা। তাই না দোস্ত?
হ্যাঁ, বড়লোকেরা অন্যের জিনিস খুব তাড়াতাড়ি হজম করতে পারে। নইলে তো আবার বড়লোক হওয়া যায় না।
এটা খুব অ্যাগ্লেসিভ কথা হয়ে গেল।
আমি সব সময়ই অ্যাগ্রেসিভ। তুই বুঝতে পারিস না।
বেশ। এখন খেতে আয়।
নাহ। আমার এতটুকু খেতে ইচ্ছে করছে না।
বায়েজীদের জেদাজেদিতে সাগর শেষ পর্যন্ত খেতে বসে। তবে দু-তিন গ্রাসের পরই সে উঠে পড়ে। তাই দেখে বায়েজীদ অবাক হয়—কিরে, কী হলো তোর?
বললাম না, খেতে ইচ্ছে করছে না।
নাকি তোর বাবা-মা, ভাইবোন এত ভালো খাবার খেতে পারছে না, সেই কষ্টে তোর গলা দিয়ে খাওয়ার ঢুকল না?
সাগর হেসে ফেলে—আমার সঙ্গে থেকে তোর সত্যিই উপকার হচ্ছে।
সত্যি!
হ্যাঁ, তুই কথা শিখছিস।
ঘণ্টাখানেক পর বায়েজীদ অনেকটা জোর করেই ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। ঘরের দরোজা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলে বারান্দা থেকেও আলো আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই নিয়ে সাগরের খুব আপত্তি—তুই আলো নেভালি আবার দরোজাও বন্ধ করে দিলি?
দিলাম। রাত হয়েছে অনেক, এখন ঘুমাব।
অন্ধকার আমার এতটুকু ভালো লাগে না।
মাঝে মাঝে তোকে আমার মানসিক রোগী মনে হয়।
অন্ধকারে সাগরের হাসির শব্দ অদ্ভুত শোনায়—তোর আর কি মনে হয়, আমার নিজেরই নিজেকে মানসিক রোগী মনে হয়।...বারান্দার দরোজাটা অন্তত খুলে দে। তোদের এখানে তো আর চোরের ভয় নেই।
বায়েজীদ বিরক্ত হয়ে উঠতে উঠতে বলে, সামান্য আলোর মধ্যেও আমার ঘুম আসতে চায় না।
সাগর আবারও হাসে—দরোজা গ’লে সামান্য এসেছে চাঁদের আলো, এর মধ্যেই তুই ঘুমোতে পারবি না! শালা, তুইও তো মানসিক রোগীরে।
বায়েজীদ গম্ভীর গলায় বলে—মানসিক রোগী আমরা সবাই, কোনো-না-কোনো ভাবে।
আবার আঁতলামো। সাগর রীতিমতো বিরক্ত হয়। চুপ করে থাক।
বায়েজীদ সত্যিই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। বেশ অনেকক্ষণ পর সে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে—ঘুমিয়েছিস?
না।
কী ভাবছিস?
কবিতা।
কি, কবিতাই ঠেকাতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ?
মাদারচোৎ।
কে, আমি?
না, যারা ওসব কথা বলে। যারা বলে তারা ছাগল, ব্যর্থ কবি...কবিই না।
ওরা তো বলে মানুষের মুক্তির জন্যে কবিতা। তুইও কি মানুষের মুক্তির জন্যে কবিতা লিখিস।
সাগর খরচোখে বায়েজীদের দিকে তাকায়। কিন্তু এই প্রায় অন্ধকার ঘরে সেটা বোঝা যায় না। সে বলে—তুই তো জানিস কবিতা নিয়ে কোনোরকম বাজে ইয়ার্কি আমার পছন্দ নয়।...না, আমি মানুষের মুক্তির জন্যে কবিতা লিখি না। ওসব বোগাস। আমি নিজের জন্যে কবিতা লিখি।
তাহলে পত্রিকায় ছাপতে দিস কেন?
সেটাও নিজের জন্যে।
কিন্তু তোর নিজের জন্যে লেখা কবিতা যদি অন্য কারও ভালো লেগে যায়?
সাগর নির্বিকার গলায় বলে—তখন বুঝি, আমি মানুষকে স্পর্শ করতে পেরেছি।
তাহলে দেখা যাচ্ছে তুই মানুষকে স্পর্শ করার জন্যে কবিতা লিখিস।
না, আমি নিজের জন্যে লিখি। যখন কোনো লেখা মানুষকে স্পর্শ করে তখন বুঝি ওটা কবিতা হয়ে উঠেছে।
মানুষকে স্পর্শ না করলে কবিতা হয় না?
না, ওটা তখন রচনা হয়।
সাগর হঠাৎ উঠে বসে। বিছানা ছেড়ে নামে। বায়েজীদের দিকে একবার তাকায় একা।
সে ফ্রিজ খুলে এক ক্যান বিয়ার বের করে। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিয়ে শার্টের পকেটে রাখে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসে সে। পা তুলে দেয় বারান্দার রেলিঙের ওপর। এভাবে বসা পছন্দ হয় না তার। বারান্দার এক পাশে দোলনা টাঙানো আছে। সাগর চেয়ার ছেড়ে দোলনায় গিয়ে বসে।
বিয়ারের ক্যান খুলে এক ঢোকে অনেকটা সে গিলে ফেলে। একটা তেতো ঢেকুর ওঠে। শার্টের হাতায় মুখ মুছে সে সিগারেট ধরায়। কদিন হলো একটা কবিতার দুটো লাইন খেলছে মাথার ভেতর। সে সাজাতে পারছে না। ‘যতবার সম্পূর্ণ মানুষ হতে চাই’ ‘দেখি বাঘ হয়ে গেছি ডোরাকাটা অথচ হরিণ।’ এ দুটো লাইনই ঘুরেফিরে বারবার আসছে। কিন্তু দুলাইনে কবিতা হয় না। হয় হয়তো, তবে এটা হবে না।
ব্যর্থতার গ্লানি মাঝে মাঝে এত তীব্র হয়ে ওঠে যে অস্থির হয়ে যেতে হয়। সাগর এখন অস্থির হয়ে ওঠে। কবিতাটা হচ্ছে না কেন, আর কতদিন তাকে খোঁচাবে! রেগে গিয়ে সাগর বিয়ারের ক্যানটা ছুড়ে দেয় নিচে, বাগানে। কাল সকালে এ নিয়ে বায়েজীদ খুব হইচই করবে, জানে সে। কিন্তু এখন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ইচ্ছে করে না।
সাগর ও দুটো লাইন বাদ দিয়ে অন্য দুটো লাইন নিয়ে পড়ে। আগের দুটো লাইনের সঙ্গে এ দুলাইনের কোনো মিল নেই। আগের দুই লাইনে ‘আমি’ ব্যাপারটা থাকলেও তাতে ছিল সামগ্রিক অবস্থার প্রতিফলন। ওই ‘আমি’ শুধু সে নয়, যে, কেউ কিংবা সবাই। আর এখনকার লাইন দুটো একান্তই ব্যক্তিগত। ‘নতমুখ তুলে দেখেছিলে তুমি? কতটুকু তার পুড়েছে আর কতটুকু তার পোড়ে নি?’
হ্যাঁ, এ লাইন দুটো হয়তো কারও কারও একান্ত হয়ে উঠতে পারে। কিংবা নাও পারে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না সাগরের। সে যে মেয়েটিকে দেখে এ লাইন দুটো তৈরি করেছে, সে মেয়েকে জনসম্মুখে হাজিরও সে করতে চায় না। বিষয়টি তার একান্তই ব্যক্তিগত। সে মেয়ের কী নাম, ধাম, কোন ডিপার্টমেন্ট, কোন ইয়ার এসব কিছুই তার জানা নেই, এসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না সে।
মেয়েটিকে সে দেখেছে মাস চারেক আগে। লাইব্রেরির বারান্দায়। এমন বিষণœ চেহারা। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। তারপর গত চার মাসে মেয়েটিকে অনেকবার দেখেছে সে। কাছ থেকে, দূর থেকে। আর দেখতে দেখতে একটু একটু করে সে মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে। না, এ কথা সে মেয়েটিকে কোনোদিনও জানাবে না। বায়েজীদ ছাড়া আর কোনো বন্ধুও জানে না। কাউকে কিছু না জানিয়ে সব চাপ একা একা সহ্য করার মধ্যে একটা আলাদা কষ্ট আছে। আর ওই কষ্টটুকু থেকে সে একটু একটু করে আনন্দ শুষে নেয়।
মেয়েটির নাম সে দিয়েছে অপরাজিতা। চেহারার সঙ্গে এ নাম মানায় না। কিন্তু মেয়েটির জন্যে পরাজয় নয়, তার মনে হয়। মেয়েটিকে, তার মনে হয়, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেঁপে-ওঠা প্রদীপের আলোর মতো। মনে হয়, মেয়েটিকে ঘিরে রেখেছে ধূপের গন্ধ। না, অপরাজিতার কথা কাউকেই বলবে না সে। অপরাজিতা একটু একটু করে তাকে পুড়াবে। সে একটু একটু করে পুড়বে। অপরাজিতা নতমুখ তুলে কখনো তা দেখবে না।
দোলনা থেকে উঠে দাঁড়ায় সাগর। একটুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে বহুদূরে। তারপর সে ঘরে ফেরে। বায়েজীদ জেগেই আছে। জিজ্ঞেস করে—কী করছিলি এতক্ষণ বারান্দায়?
দোলনায় বসে ছিলাম। বিছানায় শুতে শুতে সাগর বলে।
দুলছিলি?
হ্যাঁ। তবে সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে—এরকম দুলছি তো সব সময়ই।
কী ভাবছিলি এতক্ষণ? কবিতার কথা?
না, বাসার কথা মনে পড়ছে?
তাই নাকি! আশ্চর্য!
খোঁচা মারিস না। সত্যিই মনে পড়ছে।
আকাশের কথা মনে পড়ছে?
না, বাবার কথা। কল্পনা করলাম—আমি বাবাকে অপরাজিতার কথা বলে দিয়েছি।
তারপর?
তারপর কিছু নেই। শুধু মনে হলো, আমি আর বাবা খুব বন্ধুর মতো বসে অপরাজিতাকে নিয়ে কথা বলছি।
তোর বাবা কী বললেন?
কিছু না। আমিই বললাম।
কিছুই বললেন না?
না। বাবাকে অবশ্য খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।
হুঁ, সেটাই স্বাভাবিক।
কিন্তু বাবা আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।
কেন?
আমি যে বলে ফেললাম।
কী?
বললাম, খুব হঠাৎ করে বললাম—‘কিন্তু আর যাই হোক বাবা, এই দারিদ্র্যের মধ্যে অপরাজিতাকে টেনে আনা যায় না।’
অলংকরণ : চন্দ্রশেখর দে
অন্যদিন ঈদসংখ্যা ২০১৮-এ প্রকাশিত মঈনুল আহসান সাবের-এর কয়েকটি প্রেমপত্র উপন্যাসের অংশবিশেষ।
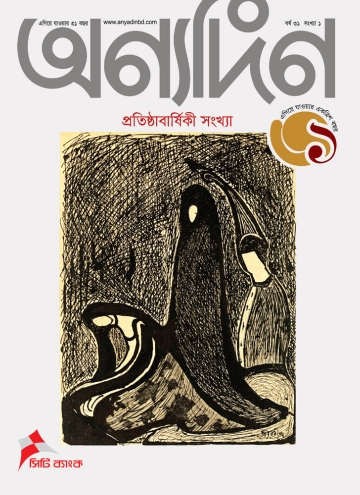














Leave a Reply
Your identity will not be published.