আবদুল কাদির কি পাগল হয়ে গেছে? তার এ রকম ব্যবহারের অর্থ কী?
ভারি অবাক কাণ্ড!
তাহলে কি মানুষ চেনা সত্যিই কঠিন?
এমনকি ছেলেবেলার বন্ধু হলেও?
দোকানে বসে গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে ইদানীং আপন মনে ভাবে আবদুর রহমান।
যে আবদুল কাদিরের কথার নড়চড় হয় না, যে তার জানি দোস্ত সেই নেংটিপরা শৈশব থেকে, যে কিনা একটা বিশাল মুক্তিযুদ্ধে নিজের শৌর্যবীর্য দেখিয়ে ফিরে এসেছে স্বাভাবিক এক জীবনে, যার কথার নড়চড় সহজে হয় না, সে কিনা ‘আমি আগামীকালই আবার আসছি’ বলে আজ ছ’মাস ধরে হাওয়া!
এবং হাওয়া তো হাওয়া, একটা টেলিফোন পর্যন্ত করা নেই! ব্যাপারটা আবদুর রহমানের কাছে বেশ রহস্যজনক মনে হয়।
বিষয়টা আবদুর রহমানের মাথার ভেতরে নড়চড়া করে। বিশেষ করে দোকানে বসলেই তার এরকম মনে হয়। অথচ মনে হওয়ার কথা নয়। আবদুল কাদির তার ছেলেবেলার বন্ধু, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জীবন আর আবদুর রহমানের জীবন এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবহমান।
কারণ আবদুল কাদিরের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে আবদুর রহমানের জীবনের কোনো মিল নেই। অতীতেও ছিল না। এবং কে না জানে জীবনের প্রবহমান অভিজ্ঞতাই মানুষকে ভিন্ন করে দেয়।
তবে বিগত কয়েক মাস আগে এমন কিছু ঘটে গেছে যে আবদুর রহমান কিছুতেই যেন বন্ধুর কথা মন থেকে সরাতে পারছে না। বা সরাতে চাইলেও ভেতরে এমন কিছু নড়াঘটা শুরু করছে যার অস্তিত্ব আবদুর রহমানকে কেমন যেন অস্বস্তির ভেতরে নিক্ষেপ করছে। এই অস্বস্তি আবদুর রহমানের অচেনা। সাদাসিধে মনের আবদুর রহমান এরকম অবান্তর একটা অবস্থার ভেতরে নিজেকে নিক্ষিপ্ত হতে দিতে চায় না। তার ভয় হয় এরকম কিছু হলে সে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সেটা কী ধরনের পরিবর্তন আবদুর রহমান জানে না। আর জানে না বলেই তার দুশ্চিন্তা। সেটা ভালো না খারাপ, নাকি ভালো খারাপের বাইরে আরও অন্য কিছু, সে জানে না। অনিশ্চিত একটা কিছু যেন কোথাও ওঁৎপেতে আছে আবদুর রহমানের জন্যে, মওকা পেলেই লাফিয়ে উঠবে তার ঘাড়ে— এরকম একটা অনুভূতিও আবদুর রহমানকে যেন বিশেষ এক অস্বস্তির ভেতরে ফেলে দেয় মাঝে মাঝে।
অথচ এমন না যে আবদুল কাদির ঢাকা শহরে নেই। তাকে মাঝে মাঝেই পথ চলতে দেখা যায়। যেমন সেদিন ফার্মগেটের মোড়ে দেখা গেল। চুল-দাড়ির জঙ্গলে তাকে চেনা দায়। তাই বলে আবদুর রহমানকে ফাঁকি দেওয়ার মতো তার ক্ষমতা হয় নি। আর একটু হলেই আবদুর রহমান তার হাত চেপে ধরত। কিন্তু ভিড়ের ধাক্কায় সে মওকাটুকু পাওয়ার আগেই আবদুল কাদির জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।
আর মিলিয়ে গেল তো গেলই।
এ যেন ছেলেবেলায় হাটে দেখা পায়রাজাদুকরের খেলা দেখাবার মতোই— এই হাতে পায়রা, ফকফক করে ডানা ঝাড়ছে, আর এই নেই!
আর তাই দেখে হাটের মানুষজন অবাক। বারে বা, তেলেসমাতি নাকি।
দশ বছরের আবদুর রহমান তো আরও বেশি।
তবে এসব তো সেই ছেলেবেলার কথা। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু এখন পরিষ্কার চোখে আবদুর রহমান দেখতে পায়। সব ঘটনার পেছনেই কার্যকারণ থাকে। হাতের পায়রা এই থাকে এই থাকে না, সেখানেও আছে কিছু যৌক্তিক কারণ। এখন সেই পায়রাঅলার সঙ্গে দেখা হলে আবদুর রহমান তার হাত চেপে ধরে বলত, মজা করার জায়গা পাও না মিয়া? পাইছো কী?
কিন্তু মনে মনে একথা ভাবলে কী হবে, আবদুল কাদির তো এখন সেই পায়রা- জাদুকরের মতোই খেল দেখাতে শুরু করেছে। এই চোখে দেখা যায়, এই যায় না। কাছে যেতে না যেতে সরে যায় সে। বন্ধুর সঙ্গে কেন তার এই লুকোচুরি খেলা! আবদুর রহমান বুঝতে পারে না।
এর ভেতরেই আরও একদিন তাকে বায়তুল মোকাররমের সামনে দেখা গেল।
তখন ঈদের বাজার। শাপলা চত্বর থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত একটা জনসমুদ্র যেন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর স্থির নেই, তার ঢেউ এসে পড়ছে বায়তুল মোকাররমে; সেখানে দেখা গেল আবদুল কাদির দাঁড়িয়ে আছে। এককালের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদির। এক ব্রাশফায়ারে তিনজন পাকিস্তানি অফিসার আর পাঁচজন রাজাকার খতম করার মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদির। আবদুল কাদির যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে একটা স্ন্যাকবার। কী যেন একটা খুব চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে সে। খাওয়াটা একটা বুভুক্ষু মানুষের মতো দেখাচ্ছে। এরকম ভাবে তাকে খেতে আবদুর রহমান কোনোদিন চোখে দেখে নি। তার খাওয়া দেখে আবদুর রহমানের বুকের ভেতরে কেমন যেন করে উঠল। কাছে গিয়ে, ‘দোস্ত্, তোমার কী হয়েছে’ কথাটা জিজ্ঞেস করার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু ভিড় ঠেলে সেদিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই রাস্তার এপার থেকেই চেঁচিয়ে উঠে আবদুর রহমান আবদুল কাদিরকে ডাক দিল। কাদির, কাদির, আবদুল কাদির, এই কাদির।
তার গলার স্বর যেন মহাসমুদ্রের গর্জনের ভেতরেই টুক করে মিশে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল আবদুল কাদির।
অথচ এতদিনে আবদুর রহমানের কাছ থেকে আবদুল কাদিরের নেওয়া পাঁচ হাজার টাকার ধার প্রায় শোধ হয়ে যাবার কথা। মাসে মাসে শোধ করলেও। এভাবেই তো আবদুল কাদির নিজে থেকে ধার শোধ করতে চেয়েছিল, নাকি? তবে কি সে ধার শোধ দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?
তাও মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্যে? আশ্চর্য!
এই টাকা শোধ না করলেই বা কি! আবদুর রহমানের তো অর্থের কোনো কমতি নেই। তার বাবা ছিল ব্যবসায়ী, তার ছিল ওষুধের দোকান, আবদুর রহমানও তার বাবার ব্যবসাকেই মূলধন করে শৈলকূপা থেকে ঢাকায় চলে এসেছে। বিয়েও হয়েছে তার অল্প বয়সে, যদিও এখন পর্যন্ত সন্তানাদি হয় নি। তার স্ত্রী রেহানার একটি সন্তানের জন্যে প্রায় আধ পাগল অবস্থা। স্ত্রীর এই অবস্থার জন্য আবদুর রহমান কেন জানি নিজেকেই দোষারোপ করে। যদিও ডাক্তার বলেছে তাদের কারও কোনো দোষ নেই। ঠিক ব্যাটেবলে ম্যাচ করছে না, এই যা। কিন্তু রেহানা বুঝ মনতে চায় না বরং হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে সে মানুষের সঙ্গে দূরদূরান্তে চলে যায়। মানুষ মানে অবশ্যই আত্মীয়স্বজন। কখনো সে শতবর্ষী বটগাছের ডালে মানত করতে যায়, কখনো পীর-ফকিরের আখড়ার সন্ধান পেলে সেখানে ভাই-ভাতিজা নিয়ে ছোটে, একবার তো লালন ফকিরের আস্তানায় সাতদিন এক ফকিরনির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল এবং তার তরিকা মতো বাড়ি ফিরে সাতদিন আবদুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে নি। নাকি ফকিরনির নিষেধ ছিল। এইসব পীর ফকিরের প্রতি আবদুর রহমানের একেবারে বিশ্বাস নেই। তার ধারণা এরা সব অর্থ লুটপাট করার যম। আর আবদুর রহমানের জীবনে অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কারণ তার সন্তানাদি না হলে কে তাকে আর রেহানাকে শেষ বয়সে দেখবে?
টাকাই তো সন্তানহীন দম্পতির শেষ বয়সের সন্তান।
আবদুর রহমানের মনের ভেতরে ভালো-মন্দের হিসাব কেমন যেন টানটান হয়ে যায়।
বন্ধুকে চিনতে কি সে ভুল করল? এতবড় ঝানু ব্যবসায়ী সে।
কিন্তু তা কী করে হয়? আপনমনে দাড়ি মোচড়ায় আর ভাবে আবদুর রহমান।
তার ছেলেবেলার বন্ধু আবদুল কাদিরকে সে কি চেনে না? মুক্তিযুদ্ধ করেও যে এখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার সনদ গ্রহণ করে নি। এমনকি কাউকে সে আগ বাড়িয়ে বলেও না যে সে কোনোকালে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তার বক্তব্য, দেশ যেমন তার সন্তানদের পেলেপুষে রাখে, শস্য দিয়ে, ফল দিয়ে, দুধ দিয়ে, মা যেমন তার সন্তানদের বুকে করে মানুষ করে, রোগে-ভোগে, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে রক্ষা করে, তেমনি মা ও মাতৃভূমির সংকটে দেশের সন্তান হিসেবে তাকেও কিছু পরিশোধ করতে হবে। এবং আবদুল কাদির ঠিক সে কাজটিই করেছে। এবং প্রয়োজন হলে আবারও সে হাতে তুলে নেবে এলএমজি বা এসএলআর। বা গ্রেনেড ছুড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে শত্রুশিবির।
এর ভেতরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, দোস্ত। আবদুল কাদির বলত।
বর্তমানে আবদুল কাদির যে বড় দুঃসময়ের ভেতরে দিন কাটাচ্ছিল সেটা আবদুর রহমান জানত। মুক্তিযুদ্ধের পর, দেশ স্বাধীনের পর, জীবন যেভাবে চলার কথা ছিল ঠিক সেভাবে যেন হয় নি। স্বাধীন একটা দেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বিরামহীনভাবে হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। এই তো মাত্র কিছুদিন আগেই গ্রামে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের চোখগুলো গ্রামের মানুষেরা পালা করে তুলে নিল। যেন মুক্তিযোদ্ধাদের চোখগুলো তুলে নিলেই মানুষের স্মৃতির ভেতরে গলগল করে নেমে আসবে শাদা কুয়াশা, স্মৃতিশক্তি আচ্ছন্ন করে দেবে সেই কুয়াশা, আকাশে আবার পতপত করে উড়বে শাদা-সবুজের ঝাণ্ডা। মুক্তিযুদ্ধ কী, কোথায়, কেন, বঙ্গবন্ধু কি, কে, কেন, সব প্রশ্নের হয়ে যাবে অবসান, সব হয়ে যাবে শাদা ও সবুজ। এবং দেশে কুষ্ঠরোগের মতো সামরিক শাসন কিছুতেই জনগণের ঘাড় থেকে নামবে না।
এসব আক্ষেপের কথা আবদুর রহমান তার বন্ধুর মুখ থেকেই শুনেছে। নইলে এতসব চিন্তা-ভাবনা করার মতো সময় বা যোগ্যতা আবদুর রহমানের যে নেই তা কি সে জানে না? ভালো করেই জানে। তার বন্ধু আবদুল কাদির যে এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, আর কেউ শৈলকূপা থেকে মুক্তিযুদ্ধের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে মরুক, ঢাকায় পা পর্যন্ত রাখে নি, সে কথা কি আবদুর রহমান জানে না? খুব জানে। মুক্তিযুদ্ধের কারণে আবদুল কাদির পড়াশোনা শেষ করতে পারে নি, সেটা অন্যকথা, তার মানে এই নয় যে আবদুল কাদির, অন্যকোনো শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জ্ঞান কম রাখে।
দোকানে বসে এরকম নানা কথা ভাবে আবদুর রহমান, আর তার মনে একটা দুশ্চিন্তা হয়। অন্তত বন্ধুর জীবন যেন স্বাভাবিক হয়ে আসে এটা সে অবশ্যই মনে-প্রাণে চায়।
কিন্তু তার চাওয়ায় কী বা আসে যায়!
মাঝে মাঝে আবদুর রহমানের এমনও মনে হয় যদি এই দেশটাতে মুক্তিযুদ্ধ না হতো, তাহলে কী হতো? যদি পাকিস্তানের খপ্পরের ভেতরেই থেকে যেত এই বাংলাদেশ, তাহলে কী ক্ষতি হতো? আবদুর রহমানের মতো মানুষদের কী ক্ষতি হতো? বাঙালি মুসলমানের তো হাজার বছর ধরে বিদেশি শক্তির অধীনে থাকা অভ্যাস ছিল, সেই অভ্যাসের দাশ হয়েই নাহয় বেঁচে থাকত সকলে।
কথাটা ভাবার সময় নিজের মনের ভেতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। কারণ যত ভাবে তত মনে হয় আবদুর রহমানের মতো মানুষদের তাতে কিছুই হতো না, তারা যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত বা করার চেষ্টা করত সেভাবেই চলে যেত দিন। বিয়েশাদি হতো, টাকা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের মারিতে গিয়ে গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে আসত। লান্ডিকোটালে গিয়ে বাজার করত, লাহোরের হোটেলে উঠে বেড়িয়ে বেড়াত আর ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে উর্দু বলে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করত!
কথাটা ভেবে আবদুর রহমানের কীরকম যেন অস্বস্তি হয়।
কেমন এক অপরাধবোধ। যেন ঠিক সে স্বাধীন বাংলাদেশটাকে মন থেকে মানতে পারছে না।
কিন্তু এতে করে আবদুর রহমানকে দোষ দিলে চলবে না। আবদুর রহমান হলফ করে বলতে পারে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে বহু মানুষের মুখে সে বিলাপ শুনেছে পাকিস্তান আমলই ভালো ছিল। যেমন ছেলেবেলায় সে তার মায়ের মুখে শুনেছিল ব্রিটিশ আমলই ভালো ছিল।
আসলে দেশের মানুষ যদি সোনাকে সোনা বলে চিনতে না পারে, তাহলে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়? সোনা জিনিসটা যে কী তা তো সে চোখেই দেখে নি। কোনোদিন যে জাতি স্বাধীনতা কাকে বলে, নিজের দেশ নিজে চালানো কাকে বলে, নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া কাকে বলে, তা যদি না জানে, তাহলে সেই অপরের আজ্ঞাবহ জাতিকে কি দোষারোপ করা যায়?
আবদুর রহমান এতদিনে বুঝতে পেরেছে স্বাধীনতার মূল্য কী। যদি সে পাকিস্তান আমলেই থাকত তাহলে আজ সে ঢাকায় এসে আরেকটা দোকান দিতে পারত না, নারায়ণগঞ্জে ট্যানারি খুলতে পারত না, ভাইকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে পারত না, কাঁঠালবাগানে তিন কাঠা জমি কিনে তার ওপরে চারতলা ভিতের বাড়ি তুলতে পারত না।
সে থেকে যেত শৈলকূপার চৌরাস্তার মোড়ে, বাবার ওষুধের দোকান সারাজীবন ধরে দেখাশোনা করে।
অনেক কিছুই পারত না আবদুর রহমান বা তার মতো মানুষেরা, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা খটকা বেঁধে থাকে তার মনে। এর মানে কি এই আবদুর রহমানের মতো মানুষ স্বাধীনতার চাপ সহ্য করতে অপারগ?
চাপ? স্বাধীনতার চাপ? স্বাধীন একটা দেশের চাপ?
কথাটা ভেবে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে তার।
বাঙালি মুসলমান দায়িত্ব নিতে ভয় পায়!
যুগের পর যুগ বাঙালি মুসলমান অপরের আজ্ঞাবহ এক জাতি। নিচু জাত থেকে যে বাঙালি ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছে। যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী সে ডোম, চণ্ডাল, মুচি থেকে, নিম্নজাতের হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্ম নিয়ে মানুষ হিসেবে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার ভেতরের সেই দাসত্ব, সেই হীনম্মন্যতা বোধ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সে তুর্কি, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সবার আদেশের কাছে মাথা নিচু করে জীবন কাটিয়েছে, নিজেরই দেশের ব্রাহ্মণের ঘরে কোনোদিন প্রবেশাধিকার পায় নি, কখনো যদি বা কোনো কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের ঘরে সে ভুল করে না বুঝে ঢুকে পড়েছে তো সে সংসারের সবকিছু সে অছ্যুৎ করে দিয়ে এসেছে। হেঁসেলের বাসনপত্র হাঁড়িকুড়ি সব আস্তাবলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ডোম থেকে মুসলমান হয়েও তার সে জাতের পরিবর্তন হয় নি।
সেই মুসলমান হঠাৎ এক প্রত্যুষে তাকিয়ে দেখে তার মাথায় রাজমুকুট! এখন সে কী করে? কোথায় যায়? শেষ ভরসা ছিল তার পাকিস্তান, ভরসা ছিল উর্দু জবান, হায় তাও গেল হারিয়ে!
কিন্তু আবদুর রহমান যা ভাবে তার সবটাই কী সত্যি?
কেন নয়, আবদুর রহমানের আরেক বন্ধু একবার গল্পচ্ছলে তাকে বলেছিল, ভাই দেশ তো স্বাধীন হলো, কিন্তু বাড়িতে যারা এখনো উর্দু জবানে কথা বলে তাদের কী হবে?
২
কিন্তু এসব তো গেল একদিকের কথা। আরও অনেক দিকও তো চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোকেও তো হিসাব করে গুটিয়ে আনা দরকার। ভুল কত প্রকারের এবং কী কী, সেসবও তো হিসাবের ভেতরে আনতে হবে, আবদুর রহমান ভাবে। মুক্তিযুদ্ধের পর কে কীভাবে আখের গুছিয়েছে সেসবও তো একটা ভয়ংকর রকমের ভুল হিসাব। বর্তমানে দেশ এক যুগেরও অধিক কীভাবে সৈনিকের ছাউনির নিচে গা মুড়ে শুয়ে আছে তাও তো একটা ভাববার কথা। যে গণতন্ত্রের জন্যে পাকিস্তান আমল থেকে আন্দোলন এবং পরিণামে যুদ্ধ, সেই দেশ একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রাহুমুক্ত হয়ে স্বাধীনতার মুখ দেখতে না দেখতে আবার সেই খাকি পোশাক, আবার সেই সেনাবাহিনী, আবার সেই উর্দির কারুকাজ, এমনকি শাসকের সাধারণ পোশাকের আড়ালেও হিংস্র বাঘের নখ জামার হাতার আড়ালে গুটিয়ে রাখা। যেমন মারাঠার শিবাজি রাখত। ফলে যিশুখ্রিষ্টের মতো নিজের মৃত্যুর সনদ যূপকাষ্ঠ নিজেই বহন করে টেনে নিয়ে চলেছে দেশ এখন, জগদ্দল পাথরের মতো এই ভার বহন করে চলেছে স্বদেশ দিনের পর দিন, এতসব বড় বড় এবং ভারী কথা তো আবদুল কাদিরের মুখেই শুনেছে আবদুর রহমান।
তবে এসব ব্যাপার নিয়ে আবদুর রহমানের মাথাব্যথা নেই। সে জানে সে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। আর দশজন ব্যবসায়ীর মতো নিজের ব্যবসা কীভাবে বাড়ানো যায়, কীভাবে আরও অর্থ উপার্জন করা যায়, এ নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং এভাবে ব্যস্ত থাকতেই তার ভালো লাগে। এসব নিয়েও সে বন্ধু আবদুল কাদিরের সঙ্গে কত দিন আলাপ করেছে। কতদিন আবদুল কাদির তার সঙ্গে আলোচনা করেছে। ঢাকা শহরে বন্ধু বলতে আবদুল কাদিরের তো একমাত্র তো আবদুর রহমানই আছে। আর আছে তার একটা ওষুধের দোকান, যে দোকানে আবদুল কাদির মাঝে মাঝে এসে বসে। দু-চারটে সুখ-দুঃখের কথা বন্ধুর সঙ্গে বলে। চা-নাস্তা খায়, সময় কাটায়। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির বন্ধুরাও তো মুক্তিযুদ্ধের এই পনেরো-ষোলো বছরে হয় সব দেশ ছেড়েছে অথবা এত বড় বড় সব ব্যবসায়ী যে তাদের সঙ্গে আবদুল কাদিরের যেন আর পড়তাই পড়ে না।
আবদুর রহমান ছাত্রজীবনে ভালো ছাত্র না হলেও স্কুলের ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো। বলতে গেলে বন্ধুঅন্ত প্রাণ আবদুর রহমান। সেই আবদুর রহমানই লক্ষ করেছে পঁচাত্তরের পর তার বন্ধু আবদুল কাদিরের ভেতরে কেমন যেন এক অস্থিরতা কাজ করে। প্রথমত সে আর আগের মতো হাসিখুশি নেই। দ্বিতীয়ত যেখানে সেখানে বসে কাগজ ছেঁড়া তার এক বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোকান বা অফিস, বাজার বা কখনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, হাতের কাছে কাগজ পেলেই সেটা ছিঁড়তে থাকে আবদুল কাদির। এটা কি হতে পারে মুক্তিযুদ্ধে নিজের হাতে শত্রুসেনা ও রাজাকার হনন করার জন্যে তার ভেতরে একধরনের জীবন সম্পর্কে অনীহা এসেছে?
অথবা এমনকি হতে পারে, বঙ্গবন্ধু মারা যাবার পর তার আর নিজের দেশের প্রতি কোনো আস্থা নেই? জীবদ্দশায় এতসব বড় বড় হনন চোখে দেখার পর তার ভেতরেও জীবনের মূল্য কীভাবে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে?
অথবা এমনও তো হতে পারে যে জাতির জনকের তিরোধানের পর হতভ্যাগ্য দেশটাকে ত্বরিতে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে কিছু হনন দরকার ছিল, দরকার ছিল কিছু নিধনের। দরকার ছিল আরও একটি মুক্তিযুদ্ধের যা করার সাধ্য তখন আবদুল কাদিরের ছিল না বা বলতে গেলে এখনো নেই, কিন্তু আক্রোশ এখনো মনের ভেতরে পুষে চলেছে?
কিন্তু ইদানীং আবদুল কাদিরকে দেখলে কেমন যেন একটা করুণা হতো আবদুর রহমানের। তাকে মনে হতো যেন সন্তান স্নেহে আপ্লুত একজন পিতা। আর কিছু নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবদুল কাদির তার চার বছরের পুত্রের গল্প করত আবদুর রহমানের কাছে। কত যে অফুরন্ত সেই গল্পের ভাণ্ডার তা বলে যেন শেষ করতে পারত না। বিয়ের প্রথম দুবছরেও যখন তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় নি, তখন তার স্ত্রী খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল বুঝি আর তাদের কোনো সন্তান হবে না। তারপর তো বাবু হলো। জরিনা-ই শখ করে তার ডাক নাম রাখল সুমন। তারপর সে সুমনের ছ’মাস বয়স হতে না-হতে তার কত যে ভাবভঙ্গি, হাত-পায়ের ছোঁড়াছুঁড়ি, যেন তার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের ভেতরেই আবদুল কাদির খুঁজে পেত পরাবাস্তবতার নানাবিধ সংকেত। যেন পৃথিবীতে একমাত্র আবদুল কাদিরই বাবা হয়েছে এই প্রথম, এরকম মনে হতো তার হাবভাব দেখে। তার গল্প শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আবদুর রহমানের হাই উঠত, মনের ভেতরে বিরক্তির কিরিকিরি রেখা জমে উঠত, কিন্তু বন্ধুর মনে কোনো আঘাত দিতে চাইত না সে। একথাও মুখ ফুটে তাকে বলতে পারত না যে আমার নিজের কোনো সন্তান নেই হে, আমার কাছে এতসব গল্প করে লাভ কী? এতে করে কি আমাকে একরকমের হেয় করা হচ্ছে না?
কিন্তু না, আবদুর রহমান জানত, তার বন্ধুর মনের ভেতরে কখনো একথা উদয় হতো না যে সন্তানহীন মানুষের কাছে নিজের সন্তানের গুণগান করা ঠিক নয়। এমনকি তার ছেলেবেলার বন্ধু আবদুর রহমান যে এত বছর পর্যন্ত সন্তানহীন, একথাটাও সে বেমালুম ভুলে যেত।
৩
বুঝলে দোস্ত, আবার কখনো কখনো আবদুর রহমান যুদ্ধ দিনের কাহিনি বলতে বলতে হঠাৎ বলে উঠত, বুঝলে দোস্ত, যুদ্ধ এমন এক জায়গা যেখানে মায়া করলে চলে না, বিশেষ করে সেই যুদ্ধ যদি হয় মুক্তিযুদ্ধ, নিজেরই মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করার যুদ্ধ।
তারপর বলত, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কীভাবে আমি সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। বন্ধুদের সঙ্গে সারা দিন মিটিং-মিছিল করে রাত প্রায় দশটার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে ফরিদাবাদে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার খাওয়ার দাওয়াত ছিল। রাত বারোটায় আবার যখন হলে ফিরে আসব, তখন হঠাৎ করে রাস্তায় হইচই। তারপর গুলির শব্দ। বাড়ির ছাদে উঠে দেখি আকাশের প্রান্তজুড়ে আগুনের দাউদাউ শিখা।
সেদিন একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম দোস্ত।
তার এক সপ্তাহ বাদেই যখন ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে চলে যাই তখনো জানিনে তারা আমার সতীর্থ বন্ধুদের কীভাবে হত্যা করেছে। কীভাবে আমার মাতৃভূমি লুণ্ঠন করছে, কীভাবে আমার বোনদের অপমান করছে।
আমার হারিয়ে ফেলা বন্ধুদের জন্যে, এই দেখো, তাকিয়ে দেখো, আমার বুকে খোঁড়ল হয়ে আছে। এই খোঁড়ল হাজার যুদ্ধজয় করলেও ভরবে না। এই বলে আবদুল কাদির নিজের বুকের বাম পাশে হাত রেখে আবদুর রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।
বন্ধুর কথা কিছু বুঝত আবদুর রহমান, কিছু বুঝত না। যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন হয়েছে, এটা তো সত্যি কথা। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করেছে এটাও সত্যি, তবু আবদুর রহমানের মনের ভেতরে আবদুল কাদিরের মতো আবেগ জাগাতে পারে নি।
আর জাগাতে পারে নি বলে আবদুর রহমান নিজের কাছেই কেমন যেন অপরাধবোধ করে। মনে হয় তার কি বোঝার ক্ষমতা কম? নাকি তার ভেতরে আবেগের ঘাটতি আছে!
নাকি যুদ্ধের পুরো ন’টা মাস যেমন সে নিদ্রাহীন ছিল, প্রতি মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুভয়ে ছিল, সেই আতঙ্কিত আবস্থা তার মনের আবেগ কেড়ে নিয়ে তাকে শুকনো বাঁশপাতার মতো রসকষহীন করে ফেলেছে!
মৃত্যুভয় মানুষকে যে কত বিকৃত করে তুলতে পারে সে অভিজ্ঞতা তো আবদুর রহমান হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। যার জন্যে স্বাধীনতার প্রথম পাঁচ বছর আবদুর রহমান খবরের কাগজ খুললেই চোখে দেখত একের পর এক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু। আর সেইসব মানুষের বয়স ছিল চল্লিশ, বিয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ। তরুণ তাজা সব মানুষ। আর তারা ছিল অধিকাংশই পুরুষ।
কেন তার বাবাই তো যুদ্ধের ধাক্কা বেশিদিন সামলাতে পারে নি।
তারপর আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে আবদুর রহমান। আর সেটা হলো চুরি। ছিঁচকে চোরে দেশ ভরে গেল স্বাধীনতার পরপর। বাসাবাড়ি বা অফিস বা সরকারি কোয়ার্টার, বা এজমালি রাস্তাঘাট, সামান্য আলপিনও মানুষ সেদিন চুরি করত। পানির কলের নব, কমোডের ঢাকনি, মেঝেয় লাগানো পানি বেরোনোর ঝুরি, রাস্তায় জ্বলে থাকা লাইটপোস্টের মাথার বাল্ব, যে-কোনো লোহার জিনিস শুধু চুরি, চুরি, চুরি। বড় বড় প্রতিষ্ঠানেও চুরি হরদম শুরু হয়ে গেল। এমনকি দেশের একটি মাত্র বিমানের বিমানবালারা বা তাদের সহযোগী কর্মীরা চুরি করতে লাগল বাংলাদেশ বিমানের মনোগ্রাম বসানো বিমানের যাত্রীদের ব্যবহৃত কাঁটাচামচ, কাপ-পিরিচ, গেলাস এবং ঢাকার রাস্তায় সেগুলো বিক্রি হতে লাগল দেদার। আর মানুষজনও এরকম রুচিশীল কাপ-পিরিচ গেলাস দেখে কিনতে লাগল হরদম। সেইপ্রথম ঢাকায় এসে রেহানাও খুশি মনে একসেট কাপ-পিরিচ কিনে আবদুর রহমানকে দেখিয়েছিল। গর্ব করে বলেছিল, মনে করো এই পিরিচ লন্ডন শহর ঘুরে এসেছে, কী মনে করো?
তারপর রাস্তার ম্যানহোলের ঢাকনি একটাও থাকত না, কত মানুষ রাতে রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার সংখ্যাই বা গোনে কে! যেন যুদ্ধ জয়ের পর মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধও কমে গেল। রাস্তায় বা বাড়ির পাঁচিলের ধারে ফুটে থাকা কোনো ফুল বা কুঁড়িও থাকত না। দেশের মেয়েগুলো খাবারের অভাবে চলে যেত বিদেশে শরীর বিকোবার জন্যে। কেউ কেউ মানুষের বাসায় কাজে গেলেও সেখানেও তাদের বিক্রি করতে হতো শরীর। যে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে দেশের মেয়ে-পুরুষ যুদ্ধ করেছে, তারাই আবার পাকিস্তানে গিয়ে মানুষের বাসাবাড়িতে কাজের জন্যে ধরনা দিত, মেয়েরা পাকিস্তানে দেহ বিক্রি করত। এমনকি মরা মানুষের মাংসও খেতে শুরু করেছিল গরিব একজন ডোম। এসব আবদুর রহমানের শোনাশোনা কথা। কতদূর বাস্তব সে তা জানে না। বা আদৌ বাস্তব কী না তাও জানে না। তবে তার মনে আছে সেইসময় তাদের শৈলকূপার দোকান থেকে রমারম ওষুধ চুরি হতো। চোর সন্দেহ করে সে সময় তার বাবা কত কর্মচারীকে যে ছাঁটাই করেছে হিসাব নেই। শুধু বেঁচে গিয়েছিল তসির মিয়া। দেশ স্বাধীন হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর পর দেশের রূপরেখা কী হবে তাই তো মানুষ জানত না। দেশ যে মাত্র নয় মাসে স্বাধীন হয়ে যাবে— কী না সেটাই বা কে ধারণা করতে পেরেছিল! এসব অভিজ্ঞতা আবদুর রহমানের জানা।
এইসব অভিজ্ঞতা আবদুর রহমানের মন তিক্ত করেছে। স্বাধীনতার প্রতি নয়, দেশের মানুষের প্রতি। এমনও তার মাঝে মাঝে মনে হতো, দেশ স্বাধীন হয়ে লাভ কী হলো?
কিন্তু এসব কথা আবদুল কাদিরকে সে বলত না। কারণ সে জানত এসব বলে লাভ নেই। কারণ তার জীবনের অভিজ্ঞতা আর আবদুর রহমানের অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন ধরনের। কারণ আবদুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা, আর সে নয়। এইটাই তাদের দুজনের ভেতরে আকাশপাতাল তফাত করে রেখেছে। জীবন তাদের দুজনকে একেবারে ভিন্ন করে ফেলেছে।
সে খিন্ন চোখে তাকিয়ে থাকত আবদুল কাদিরের দিকে।
আর আবদুল কাদির তার কথা শেষ করে আপন মনে বসে কাগজ ছিঁড়তে থাকত, হোক সে কাগজ পুরোনো দিনের বাতিল পত্রিকা বা ওষুধের ফেলে দেওয়া প্যাকেট, বা শিঙাড়া বা বাদাম খাবার ছেঁড়া ঠোঙা। হাতের কাছে যা পেত তাই। তার চোখের সামনে পড়ে থাকত গরম চা। সেই চা ঠান্ডা হতে হতে পানি হয়ে যেত। আর আবদুল কাদির কাগজ ছিঁড়তে থাকত।
একদিন তো রাস্তা থেকে তাকে কাগজ কুড়িয়েও ছিঁড়তে দেখেছে আবদুর রহমান।
৪
মাঝে মাঝে আবদুল কাদির মুক্তিযুদ্ধে তার অভিজ্ঞতার কথা বন্ধু আবদুর রহমানকে বলত। যখন বলত তখন তার চোখমুখ যেন ঝলমল করে উঠত। স্মৃতির মণিকোঠায় সহমুক্তিযোদ্ধাদের মুখ একের পর এক যেন ভেসে উঠত তার। তাদের নিয়ে কত কাহিনি। খাওয়াদাওয়ার কত কষ্ট। তাদের কমান্ডার মাঝে মাঝে তাদের রুগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, এই কষ্ট কিছুই না, যখন দেশ শৃঙ্খলমুক্ত হবে, সেদিন এই কষ্ট কোথায় হারিয়ে যাবে।
তার মনে আছে কমান্ডার মাঝে মাঝে চুরি করে তাদের জন্যে আলাদা খাবারের বন্দোবস্ত করত। নিজের খাবার থেকে বাঁচিয়ে রেখে দিত তাদের জন্যে। সেই কমান্ডার ব্রিজ ধ্বংস করতে গিয়ে গ্রেনেডের আঘাতে মৃত্যুবরণ করল। সেদিন তাদের কত যে শোক।
তারপরও তারা থেমে থাকে নি। আবার নতুন কমান্ডারের আওতায় যুদ্ধ করতে করতে একদিন আবদুল কাদির নিজেই কমান্ডার হয়ে গেল। সেদিন তার আর তার বন্ধুদের কত যে আনন্দ!
একদিন তার ওষুধের দোকানে বসে আবদুল কাদির গল্পে গল্পে বলেছিল, জানো দোস্ত, যুদ্ধক্ষেত্র একটা অদ্ভুত জায়গা। মৃত্যুকে মাখায় নিয়ে সেখানেও একজনের সঙ্গে আরেকজনের সখ্য হয়। একজনের সঙ্গে আরেকজনের বন্ধুত্ব হয়, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আর সেজন্যে এক সহযোদ্ধা আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেলে আরেক সহযোদ্ধা নিজের জান বাজি করে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। তখন নিজের জীবনের কথা ভাবে না। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দোস্ত। এমনকি শত্রুর জন্যেও মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়, জানো, মনে হয় এই মৃত্যুর খবর যখন তার আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌঁছাবে, কীভাবে শোকের মাতম পড়ে যাবে বাড়িতে। সন্ত্রাসীরও তো মা আছে বন্ধু। দেখ না সন্ত্রাসী মারা পড়লে মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কীভাবে ডুকরে ডুকরে কাঁদে?
এরপর আবদুল কাদির বলল, তাহলে শোন, একবার যুদ্ধক্ষেত্রে সারা দিন গোলাগুলি চলার পর দুপক্ষই সিদ্ধান্ত নিল যে এখন কিছুক্ষণের জন্যে বিরতি। এরকম মাঝে মাঝে হতো। যুদ্ধ তো মানুষ মানুষের সঙ্গে করে। হতে পারে তারা নিকৃষ্ট। আর মানুষ হলেই সারাদিনরাত যুদ্ধ করার পর বিশ্রাম নিতে হয়। এটা দুপক্ষই জানে। সেদিন আমাদের সঙ্গে যেসব পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়েছিল তাদের ভেতরে একজন ছিল তরুণ। আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে সে ছোট ছিল। মনে হয় সবেমাত্র কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছিল তার। কিশোর সুলভ ব্যবহার তখনো তার চরিত্র থেকে যায় নি। সময়টা জুলাই বা আগস্টের কোনো একটা সময়।
যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর কখনো কখনো আমরা তাকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথায় হেলমেট। মাঝে মাঝে হাতে খাবার নিয়ে সে ঝটিতে হাত উঁচু করে আমাদের দেখাত। যেন তার খাবার দেখে অভুক্ত আমরা তাকে হিংসা করি। আবার দাঁত বের করে মজার হাসি হাসত। এমনই অবোধ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে বসেও মৃত্যু নিয়ে তার ভয় নেই! যুদ্ধ বিরতির সময়, বয়সজনিত কারণে অবোধ সে, তার কী খেয়াল হলো, আমাদের সঙ্গে দুষ্টুমি করতে তার মাথায় বুদ্ধি চাপল। মাথায় হেলমেট ছাড়াই হঠাৎ করে মুখ বাড়িয়ে সে চিৎকার করে বলল, জয় বাংলা নেহি, বোলো, জয় পাকিস্তান!
তার চিৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। আর আমার চোখের সামনে তার গলা থেকে মাথাটা ঝুলে পড়ল একদিকে।
কথা বলতে বলতে কেমন অস্থির হয়ে উঠত আবদুল কাদির। চেয়ারে বসা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াত। কপালে ঘাম জমে উঠত তার। মুখের ঘাম মুছে সে বলত, জানো দোস্ত, সেই দৃশ্যটা এখনো আমি মাঝে মাঝেই চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখি। আর নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। কোথায় যেন বিবেক খচখচ করে ওঠে। যুদ্ধ বিরতির সময় যতই সে উস্কানিমূলক কথা বলুক না কেন, তখন তো যুদ্ধ বিরতি চলছিল। কেন আমি তার উস্কানি অগ্রাহ্য করলাম না দোস্ত?
এরপর থপ করে আবদুল কাদির কাউন্টারের পেছনে রাখা চেয়ারটাতে বসে পড়ত। কী যেন ভাবত কতক্ষণ। কপাল থেকে ঘামে ভেজা চুল মাথায় তুলে দিতে দিতে বলত, আমার ছেলেটিও বড় হলে, ষোল বা সতেরো বছরের হলে এরকম ছেলেমানুষি ব্যবহার তো করতে পারে, কোথাও-না-কোথাও, কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে, এমন কোনো অর্বাচীন ব্যবহার, যা তার মৃত্যু ডেকে আনবে?
তার কথা শুনে আবদুর রহমান সান্ত্বনা দিয়ে বলত, আরে না, তোমার কি মাথা খারাপ?
উত্তরে আবদুল কাদির বলত, না, মাথা খারাপ না দোস্ত। আজকাল দেখ না কত সহজে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর হাতের টুইনওয়ানটা হস্তগত করার জন্যে কবরস্থানে ডেকে নিয়ে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করে? বন্ধু এক শ’ টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় না বলে হত্যা করে?
কথা শেষ করে আবদুল কাদির দ্রুততার সঙ্গে পুরোনো কাগজ দুহাত দিয়ে ছিঁড়তে থাকত। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলত, কেমন অসহায় ভাবে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, মাঝে মাঝে আমার চোখের সামনে সেই কিশোর ছেলেটার চেহারা ভেসে ওঠে বুঝলে দোস্ত? অনেকদিন আমাদের ট্রুপ তাদের ট্রুপের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। ট্রেঞ্চে বসে সে যুদ্ধ চলেছিল দিনের পর দিন। জানো বন্ধু, মুখোমুখি যুদ্ধ যখন চলে তখনো কিন্তু আমরা আমাদের শত্রুপক্ষের ব্যবহার লক্ষ্য করি। তাদের চালচলন লক্ষ্য করি, যেমন তারা আমাদের করে। এরপর যখন তাদের একজনকে আমরা হত্যা করতে পারি, পর মুহূর্তে সেই জয়ের আনন্দ উপভোগ করার ফাঁকে ফাঁকেও কিন্তু আমরা সেই শত্রুর জন্যেও একধরনের আক্ষেপ অনুভব করি। যেন শাব্বাশ একটা যুদ্ধ এতক্ষণ চলছিল! টরেটক্কা টরেটক্কার মতো।
জানো তো, বুদ্ধিমান শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেও একটা আনন্দ আছে? সে আনন্দ তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না, কেমন হয়। এটা কাউকে বোঝানো যায় না। ঘুমের ভেতরে শত্রুকে মেরে ফেলে কোনো আনন্দ নেই দোস্ত! যুদ্ধ করে মারাটা যতটা আনন্দের! কারণ শত্রুকেও আমার সাহস আর ক্ষমতা বোঝাবার দরকার আছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী মিন করছি?
তার কথা শুনে আবদুর রহমান বিস্মিত হয়ে বলত, আরে বলো কী, এ তো নতুন কথা শোনালে দোস্ত।
আর আবদুল কাদির বলত, না, নতুন না, দোস্ত, অনেক পুরোনো। কিন্তু সহজে মানুষ কবুল করতে চায় না। পাছে এতে করে তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়।
না, আবদুর রহমান তার বন্ধুর কথা বুঝতে পারত না, কারণ সে কোনোদিন যুদ্ধ করে নি। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা কাউকে মুখে বলে বোঝানো অসম্ভব।
কিন্তু সে কান পেতে বন্ধুর কথা শুনত।
এরপর আবদুল কাদির বলত, তারপর হঠাৎ যখন শুনি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে, তখন আমরা খুব খুশি হলেও মনের ভেতরে কোথায় যেন খচখচ করছিল এই ভেবে যে যুদ্ধটা আরও কিছুদিন চলতেও তো পারত! কিংবা আরও কিছুদিন চললে ক্ষতি কী ছিল, যখন আমরা প্রতিদিনই প্রায় প্রতিটি সীমান্তে জয়ী হয়ে চলছিলাম!
এ যেন হঠাৎ করে হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া, এলএমজি, এসএল আর, গ্রেনেড কেড়ে নেওয়া আর হাসি হাসি মুখে বলা, এবার বাড়ি যাও বাবুরা, এবার যুদ্ধ শেষ!
কিন্তু তা কী করে হবে? বরং যুদ্ধের পর পর উচিত ছিল আমাদের ভীষণ চ্যালেঞ্জিং কোনো কর্মকাণ্ডের ভেতরে সম্পৃক্ত করে ফেলা, যেন আমরা বিপথে যেতে না পারি।
কথাটা বলে আবদুল কাদির জোরে জোরে সিগারেটে টান দিত। দীর্ঘ একেকটা টান। যেন নিজের আবেগকে ধরে রাখার জন্যে এরকম কিছু করতে হবে।
যুদ্ধও যে মানুষকে নেশা ধরাতে পারে, একথা কি বিশ্বাস করো দোস্ত?
এবার বলত আবদুর কাদির।
নেশা? না আবদুর রহমান এটা জানত না।
আবদুল কাদির বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হঠাৎ গলার স্বর নিচু করে বলত, হ্যাঁ, দোস্ত, আমার কাছে শুনে রাখো, নেশা ধরাতে পারে। যার জন্যে দেখ না পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো এক যুদ্ধ শেষ হতে না হতে আরেকটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলে? এটা কি তুমি মনে করো শুধু তাদের অস্ত্র বিক্রি করার জন্যে? না, নেশা, যুদ্ধের নেশা চালিয়ে যাবার জন্যে। বিশ্বাস করো।
এরপর আবদুল কাদির বলত, কিন্তু আমরা যারা হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, যাদের বয়স মাত্র বিশ বছরও হয় নি, যুদ্ধজয়ের পর পর তাদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন ছিল ভীষণ কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। দেশেরই কাজে। কিন্তু তা তো হলো না। ফলে কী হলো জানো, অনেকে বিপথে চলে গেল। কারণ শরীর এবং মনে যে শক্তির এবং সাহসের সঞ্চার হয়েছিল, তাকে চ্যানেলাইজড করার কোনো মাথা তখন কাজ করে নি।
আবদুর রহমান বন্ধুর একথা শুনে একদিন বলেছিল, দোস্ত, এক জেনারেশনে আর কত হবে? বাঙালি কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্র কাকে বলে সেটাই তো জানত না।
এরপর আবার যদি কোনো যুদ্ধ হয় কোনো দেশের সঙ্গে, দেখো কেমন গুছিয়ে বাঙালি যুদ্ধ করে!
কথাটা বলে নিজেই চমকে যেত আবদুর রহমান। মনে মনে নিজেকে বাহবা দিত।
তার কথা শুনে আবদুল কাদির হেসে উঠত। বলত, যুদ্ধ, কার সঙ্গে? নিজের সঙ্গে নিজের?
এরপর অনেকক্ষণ তারা দু’বন্ধু চুপ করে বসে থাকত। রাত হতো। প্রথমে সন্ধে রাত, তারপর গভীর রাত। আপনমনে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেত আবদুল কাদির। আবদুর রহমান নিজে সিগারেট খেত না, কিন্তু বন্ধুর জন্যে স্টারের প্যাকেট সে হাতের কাছে মজুদ রাখত।
তারপর আবদুল কাদির হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলত, বুঝলে দোস্ত, সেই ছেলেটার চেহারা আমি এতদিনেও ভুলতে পারি নি, যখন চোখের সামনে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে, বুঝলে সেদিন রাতে আর আমার ঘুম হয় না।
৫
তবে এসব অনেকদিন আগের কথা।
তারও আগের কথা আছে। যখন শৈলকূপার সকলকে ফেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে এসেছিল আবদুল কাদির। অথচ তার বন্ধুরা সকলেই পড়তে চলে গিয়েছিল যশোর বা রাজশাহী। তারা কেউ ঢাকায় আসে নি। তখন থেকেই আবদুর রহমান জানত তার বন্ধু আবদুল কাদির একটু ভিন্ন ধাতের মানুষ। তার ভেতরে এমন একটা বোধ খেলা করে যা আর দশজনের সঙ্গে সে ভাগ করে নিতে পারে না। এর ফলে ঢাকার সক্রিয় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে আবদুল কাদিরের ঘটেছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। ছাত্রইউনিয়ন যখন দুইভাগ হয় সে ছিল মতিয়া গ্রুপে। তবে রাজনীতি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার তখন ধান্ধা ছিল কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে স্বাবলম্বী হবে। বাবা-মাকে সাহায্য করবে। বোনকে ভালো একটা পাত্রে বিয়ে দেবে। নিজের ভালো একটা চাকরির স্বপ্নও সে দেখত। আর তার ভেতরেই দুম করে বেঁধে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ।
আবদুল কাদির মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধুর কথা বলত, বিশেষ করে যেদিন তাকে আগরতলা মামলা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। সেদিন আবদুল কাদির ফার্মগেটের রোদের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে একনজর দেখবে বলে। তারও আগে সে জনতার সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিত, ‘জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।’
শেখ মুজিব ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়া পেলেন বাইশে ফেব্রুয়ারি, উনিশশো ঊনসত্তর। আর সেদিন সে হাজার হাজার জনতার ভেতরে রোদ মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে। পরে সে কথায় কথায় আবদুর রহমানকে বলেছিল, তখন তো দোস্ত তোমরা সবাই যশোর বা শৈলকূপা বা রাজশাহী। আর আমি ঢাকায়। ভাগ্যিস আমি তখন ঢাকায়, তা না হলে তো এইসব গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান কিছুই চোখে দেখতে পারতাম না। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের নীরব সমর্থক হলেও বঙ্গবন্ধুকে চিনতে ভুল করি নি। সত্তরের নির্বাচনে তাই নৌকায় ভোটের জন্যে দেশে ফিরে ক্যামপেইন করেছিলাম।
এরপর যেন আপন মনে আবদুল কাদির বলত, ভোটের ফলাফল বেরোবার পর থেকেই তো পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা গরম হয়ে গেল। তারপর তো একের পর এক ইতিহাস।
কোনো জাতির জীবনে এত দ্রুততার সাথে ইতিহাস পাতা উল্টেছে কি না, আমার সন্দেহ হয় বুঝলে?
কথা বলে একটা অদ্ভুত হাসি হাসি মুখ করে আবদুল কাদির তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তখন কেন জানি আবদুর রহমানের মনে এক ধরনের ঈর্ষা হতো। যেন আবদুল কাদির কোনো বিশেষ এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে তাদের সকলকে পেছনে ফেলে। যার ভাগীদার তারা কোনোদিন হতে পারবে না। এইটে তার মনের ভেতরে একটা জ্বালা ধরাত, যা সে অবজ্ঞার চোখে, আরে ধ্যাৎ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত।
তারপর এই মুক্তিযুদ্ধ। সেখানেও আবদুল কাদির কীভাবে যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সঙ্গী হয়ে গেল। সে হয়ে গেল বন্দুক হাতে মুক্তিযোদ্ধা। যখন সে তার রণাঙ্গনের কাহিনি বলত, সে আরেক ইতিহাস। আবদুর রহমান এমনও মাঝে মাঝে ভাবত তার বন্ধু আবদুল কাদির যেন ইতিহাস রচনা করার জন্যেই জন্মেছে। সে তাদের সকলের চেয়ে আলাদা। কই আবদুর রহমানের আর কোনো বন্ধু তো প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের জড়ায় নি! হয় পালিয়ে ছিল গ্রামে গঞ্জে গিয়ে, অথবা শহরের ভেতরেই প্রাণ হাতে করে সকাল সন্ধ্যা গালগল্প আর রেডিও শুনে দিন কাটাত।
আবদুর রহমান নিজেই তো তার সাক্ষী।
আর এত সবের ভেতরে আবদুল কাদিরের বিয়েও হয়েছে, হয়তো একটু বেশি বয়সে। তার বিয়ের আগেই বাবা-মার মৃত্যুও হয়েছে। ছোটবোনের বিয়ে সে নিজেই গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে দিয়ে এসেছে, যে ছেলেটি পাটের ব্যবসা করে।
আবদুর রহমানের বিয়ে অবশ্য আবদুল কাদিরের অনেক আগে হয়েছে। দেশ স্বাধীনের বছর তিনেকের মাথায়। একরকম জোর করেই তার বাবা অল্প বয়সে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। একদিন চাচাত এক বোনের সঙ্গে সে খুনসুটি করছিল, হঠাৎ করে তার মায়ের চোখের সামনে পড়ে যায়। মা বাবাকে কী বলে সে জানে না, তবে তিনমাসের ভেতরেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং তখন অনেকটা নিমরাজি হয়েই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়।
কিন্তু এত বছরেও তার সংসারে কোনো সন্তান আসে নি। অথচ আবদুল কাদির বিয়ে করার তিনবছরের মাথায় সে সন্তানের জনক।
আবদুল কাদিরের সমস্যা একটাই। কোনো চাকরিতে সে থিতু হয়ে বসতে পারে না। বসার মতো মনোবৃত্তিই যেন তার নেই। এক চাকরি থেকে আরেক চাকরিতে সে শুধু পাক খেয়ে বেড়ায়। যার জন্যে তার বিয়ে করতেও দেরি হলো।
তবে বেড়াক সে পাক খেয়ে, আবদুর রহমানের তাতে কি। যার যার জীবন তার তার।
আবদুল কাদির তার একজন বন্ধু মাত্র তো আর কিছু নয়।
দোকানের ক্যাশে বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবতে থাকে আবদুর রহমান।
৬
আবদুর রহমানের কাছ থেকে আবদুল কাদির প্রায় ছ’ মাস আগে পাঁচ হাজার টাকা ধার হিসাবে নিয়েছিল। ছেলের অসুখের চিকিৎসা করাবে বলে নিয়েছিল। সেদিন বাক্যালাপটা ছিল এরকম:
দোস্তো।
বলো।
কিছু মনে করবে না তো?
কী?
বড় বিপদে পড়েছি
কী?
ছেলেটার অসুখ জানো তো?
কার ছেলের? অন্যমনস্কের মতো বলে উঠেছিল আবদুর রহমান।
আমার। আমার ছেলে। একটাই তো সন্তান আমাদের।
ওঃ, সুমনের? কী অসুখ? সচকিত হয়ে উঠেছিল আবদুল কাদির।
পেটের। শুকিয়ে একেবারে হাড্ডিসার হয়েছে, দোস্ত। শরীরে কিসের যেন অভাব। দুধ সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া সব সময় বুক ঘড়ঘড় করে। ও পেটে থাকার সময় ওর মায়েরও স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। এখন ছেলেটা ঠিক মতো সুস্থ হয়ে উঠলে হয়।
কাকে দেখাচ্ছ? আবদুর রহমান একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।
পিজির প্রফেসরকে। কিন্তু টাকার বড় অভাব। জানো তো যে চাকরি করি তাতে ঘরভাড়া দিয়ে হাতে আর বিশেষ কিছু থাকে না।
বলো কী!
হ্যাঁ, ভাই। তাই তোমার কাছে কিছু টাকা ধার চাই।
এবার একটু ইতস্তত করে আবদুর রহমান বলল, কত টাকা, বলে তো?
তারা দুজনে এতক্ষণ দোকানে বসে কথা বলছিল। এই প্রথম কথার মাঝখানে আবদুর রহমান নড়েচড়ে বসল। তার ভয় হলো, ধারের অঙ্কটা না বিদঘুটে কিছু হয়। এমনিতে তার ব্যবসা বর্তমানে তেমন ভালো যাচ্ছে না। হয়তো তখন বাধ্য হয়ে না করে দিতে হবে।
আবদুল কাদির এতক্ষণ চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। এবার চোখ নামিয়ে বলল, হাজার পাঁচেক টাকা ভাই, দিতে পারবে?
টাকার অঙ্ক শুনে আবদুর রহমান মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভাবল, যাক, তবু রক্ষা। হাজার দশেক চাইলেও পারত। আজকাল দশ হাজার টাকারই বা মূল্য কী?
পরমুহূর্তে নানা খাপছাড়া চিন্তা তার মনে নাড়াচাড়া হতে শুরু করল।
দেশের এখন এমন অবস্থা যে টাকা আজকাল বাতাসে ওড়ে। যে ধরতে পারে সে পারে। আর যে পারে না সে পারে না, সে না খেয়ে মরে যায়। স্বাধীনতা এসে যাবার পর থেকে এখন সবকিছু যেন এলোমেলো, দিক নিশানাহীন। পর পর দু-দুটো রাষ্ট্রপতি নিহত। একজন তাঁরই দেশের সামরিক বাহিনীর হাতে, আরেকজন নিজের দলেরই সামরিক বাহিনীর হাতে। লাগ ভেলকি লাগ-এর মতো এখন দেশের সার্বিক অবস্থা। দুর্ভিক্ষ এখনো দেশ ছেড়ে যায় নি। বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা ভিক্ষা হিসেবে নিয়ে এসে সেই টাকায় বাদশাহি করছে একদল আর একদল ভাগ না পাওয়ার জন্যে আহামরি করে রাগে ফুঁসছে। মাঝখানে সেদিন এক আমেরিকার মানুষ খবরের কাগজে ঘোষিতভাবে বলল, বাংলাদেশ হচ্ছে তলাবিহীন ঝুড়ি। কিন্তু আসল কথাটা বলল না যে এই তলাবিহীন ঝুড়ি আছে বলেই না আজ দেশের রাজনীতিবিদেরা, ব্যবসায়ীরা, ঋণখেলাপিরা তর তর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এরা সব রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। অর্থ ঠিকই ঢালা হচ্ছে ঝুড়িতে, বিদেশি অনুদানের অর্থ, কোটি কোটি টাকা অনুদান, কিন্তু সবই বেরিয়ে যাচ্ছে তলা দিয়ে অনায়াসে। বেরিয়ে যার সিন্দুকে ওঠার কথা সেখানেই উঠছে।
শুধু কি টাকা উঠছে সিন্দুকে? না। সেখানে কম্বল উঠছে, চাল উঠছে, চিনি উঠছে, ওষুধ উঠছে। সবকিছু সিন্দুকে উঠছে।
বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, চাটার দল সব চেটে খেয়ে ফেলছে।
কতখানি আশাভঙ্গ হলে জাতির জনকের মুখ দিয়ে এরকম কথা বেরোয়?
সেই হিসেবে আবদুর রহমানের দোষ কতটুকু?
এইরকম এক বৈরী পরিবেশে তাকে তো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে।
দোষ? শব্দটা মনের ভেতরে উঠতে আবদুর রহমান একটু নড়েচড়ে বসল। এসব চিন্তা-ভাবনার ভেতরে আবার দোষ শব্দটা কীভাবে মনে এল?
তবে সকলে ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর বুঝি দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। দেশ থেকে ভেজাল দূর হবে, টাকা পাচার দূর হবে, চোরাচালানি দূর হবে, সন্ত্রাস দূর হবে, দেশপ্রেমে দেশ টইটম্বুর হয়ে উঠবে, দুর্ভিক্ষ দূর হবে। বাসন্তীরা আর জাল গায়ে জড়িয়ে ফটো তুলবে না। কিন্তু হলো কি?
এরপর যিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, শোনা গিয়েছিল তিনি খুব ভালো এবং সৎ একজন মানুষ। এমনকি ভোজনেও মিতব্যয়ী। তাঁর আমলে তাঁর সামনে বসে গোগ্রাসে কোনো খাবার কেউ খেয়েছে কি না ইতিহাস নেই। গোগ্রাসে পড়ে মরুক বাঙালির স্বভাব অনুযায়ী টেবিলে খাবার দেখলেই পরিমাণে যতদূর সম্ভব বেশি করে নিজের থালায় খাবার তুলে নেওয়া অভ্যাস, যাতে করে পাশের জন কোনো ভালো ভাগ না পায়! কিন্তু তাঁর সামনে বসে এরকম বেয়াদবি ব্যবহার করতে কেউই কোনোদিন সাহস পায় নি। তিনি একটা ছাড়া দুটো মিষ্টি কোনোদিন মুখে দেন নি, একটুকরো কেকের অর্ধেকটা মাত্র নিজের পাতে তুলেছেন, এক টুকরো মাছ ছাড়া দু-টুকরো মাছ পাতে তোলেন নি, যতদিন বেঁচে ছিলেন, এবং তার সামনে যারা বসে থাকত তাদেরও তুলতে দেন নি, এতখানি মিতব্যয়ী, অথচ তার আমলেই তো মানুষ মারা গেল বেশি। কিছু গোপনে মারা গেল, কিছু প্রকাশ্যে মারা গেল। মুক্তিযোদ্ধারাও তার হাত থেকে রেহাই পেল না। দক্ষ রাজনীতিক এবং দেশের জন্যে অনুগতপ্রাণ নেতারাও নয়। জেলবন্দি নেতারা তো নয়ই।
বৃক্ষ থেকে মানুষ, কেউই তার হাত থেকে রেহাই পেল না। রাতের আঁধার চিরে জেলখানার বন্দিশিবির থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই আকুল চিৎকারও তার মন ভেজাতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এটুকু তাঁর বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে এভাবে নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখা যায় না। কারণ তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তার প্রমাণও পাওয়া গেল। নিজের অনুগত সেনাবাহিনীর হাতেই প্রাণহীন দেহ তার খ-বিখ- হয়ে পড়ে থাকল একটা সুরক্ষিত সার্কিট হাউসের বারান্দায়, সিঁড়িতে, ছাদে ওঠার রেলিঙে। আর জনগণের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতির ভেতরে। যাকে বলে ছত্রাখান তো ছত্রাখান।
এসব আলোচনা তো মওকা পেলেই আবদুর রহমানের কাস্টমারেরাই কাউন্টারের কাচের ঘেরার ওপরে কনুই রেখে আলোচনা করে।
এদেশে রাজনীতি বোঝে না কে? আবদুর রহমান মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে।
সেদিন এক রিকশাঅলা রিকশা দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে দোকানে ঢুকে বলল, টেরামাইসিন দ্যান তো একপাতা, দাম কত?
দাম শুনে মুখ খিঁচিয়ে বলল, শালার প্রেসিডেন্ট আমাগো খালি ধোঁকা দিয়া রাখছে। মাইনষে চাউল কিনবে না ওষুধ কিনবে?
তবু আবদুর রহমানের হিসেব মতো, সেসব দুর্যোগের দিনগুলো দেশবাসী পার হয়ে এসেছে। যখন মনে হয়েছিল এই দুর্যোগ বুঝি আর পার হবার নয়, জাতীয় জীবন বুঝি এভাবেই চলবে, এভাবেই এর ক্ষয় এবং লয়, তবুও পার হয়ে গিয়েছিল এদেশের মানুষ এবং এই টুটাফাটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ।
আঃ সেসব দিনের কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।
বিস্ময়ের কথা আবদুর রহমান মাঝে মাঝে এতদূর পর্যন্তও ভাবে।
নাকি এ সবই বন্ধু আবদুল কাদিরের চিন্তা-ভাবনার কাছ থেকে ধার নেওয়া, নিজেই বুঝতে পারে না সে।
তাই বলে দেশ এখন যে একেবারে সোনায় সোহাগা তা কিন্তু নয়।
এখন যিনি দেশ চালাচ্ছেন, তাঁর বাইরের খোলসটা একেক সময় একেক রকম। কিন্তু বর্তমানে তার চালচলনের ভেতরে কেমন যেন একটা রাজকীয় ভাব ফুটে উঠেছে। একজন বাদশাহ্ বা শাহানশাহ্ জাতীয় ভাব। স্ত্রী রেহানার মুখে আবদুর রহমান শুনেছে ভোরবেলা টেলিভিশনের নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠানে আজকাল নাকি দেশের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে বসে নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়। শেরওয়ানি এবং টুপিপরা বাচ্চারা বর্তমান প্রেসিডেন্টের বৃদ্ধা মায়ের কাছে এমন সব প্রশ্ন করে যা শুনলে মনে হবে দেশের শাহানশাহ্র ছেলেবেলা তারা জানতে চাচ্ছে; যেমন, দাদিমা, আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ছেলেবেলা কী নাস্তা করতে ভালোবাসতেন? তিনি কী পরতে ভালোবাসতেন? গরিব দুঃখীর কষ্ট দেখলে কীভাবে তার প্রাণ কাঁদত?
নাকি তাদের দুঃখে গায়ে জামাই পরতেন না।
আর মহামান্য প্রেসিডেন্টের মা সরল নিষ্পাপ মনে বসে বসে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন।
রেহানা হাসতে হাসতে বলে, দেশ তৈরি করল কে, আর ফুটিভাজা খায় কারা, বলো তো?
রেহানার কথা শুনে আবদুর রহমানও হাসে। তবে তাই বলে বঙ্গবন্ধু মারা যাবার পর তার যতখানি খারাপ লাগবে ভেবেছিল, ততখানি কেন জানি লাগে নি বরং আজকাল তার বঙ্গবন্ধুর কথা ভেবে মন খারাপ লাগে। বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে যন্ত্রণা। এমন কি হয় যে মানুষের শোকও বিরূপ পরিস্থিতিতে থমকে যায়? প্রাণ হারাবার ভয়ে মানুষ শোকও দমন করে ফেলতে পারে? মানুষটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে থিতু হয়ে বসতে না-বসতে চারপাশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। দেশের তরুণ সমাজ পর্যন্ত বিগড়ে গেল পূর্বাপর কোনো চিন্তাভাবনা না করে। যে তরুণ সমাজ সব সময় দেশকে সঠিক পথে চালিত করার দিকনির্দেশনা দিতে পারত বা রাজনীতির সহায়ক হতে পারত, তাদের ভেতরেও দেখা গেল ক্ষমতার লোভ, অর্থের লোভ, পদবির মোহ। শুরু হলো নিজেদের ভেতরে মারামারি, খেয়োখেয়ি। এখন তো আবদুর রহমান শুনছে জাসদে ঢুকলে প্রতি মাসে এক শ’ করে টাকা আর একটা পিস্তল পাওয়া যায়। সত্যি কি মিথ্যে তা আবদুর রহমানের বোঝার ক্ষমতা নেই। সব শোনাশোনা কথা।
বেশির ভাগ কথা তার বন্ধু আবদুল কাদিরের মুখেই শোনা, যে কাদির একাত্তরে নিজের হাতে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করেছে। তিনজন মিলিটারি আর নয়জন রাজাকারের জান খতম করেছে। যে আবদুল কাদির এখন কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। বসলেই যা সে হাতের কাছে পায়, তাই একটু একটু করে ছিঁড়তে থাকে। এজন্যে তাকে যারা চেনে, তারা তার হাতের কাছে পুরোনো খবরের কাগজ এনে রাখে। যাতে সে ইচ্ছেমতো ছিঁড়তে পারে। কেউ কেউ অবশ্য তার এ রকম ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।
হাজার হোক সে একজন অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা ছিল এককালে। সাত নম্বর সেকশনে বীরের মতো যুদ্ধ করে পায়ে গুলি খেয়েছিল একবার। পরে ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করে ভালো হয়।
৭
কিন্তু আবদুর রহমানের মনের এতসব খাপছাড়া চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আবদুল কাদিরের কোনো যোগ ছিল না। ছেলের অসুখের চিন্তায় তার চোখমুখ জটিল আকার ধারণ করেছিল। সে আশ্চর্য এক ব্যাকুলতার সঙ্গে তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।
হ্যাঁ কিংবা না। না কিংবা হ্যাঁ।
যেন জীবন-মরণের অপেক্ষা।
পরে আবদুর রহমানের মুখের ভাবে সম্মতির লক্ষণ বুঝতে পেরে বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠেছিল, আঃ, বাঁচালে ভাই। সকাল থেকে অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে তবে তোমার কাছে কথাটা তুলতে পারলাম। তোমার দেওয়া এই ঋণ আমি মাস তিনেক বাদে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে শোধ দিয়ে দেব। তারপর মাস পাঁচেক লাগবে শোধ দিতে। তুমি ভাই কিছু মনে করতে পারবে না।
বন্ধুকে সেদিন টাকা ধার দিতে পেরে আবদুর রহমানের মনের ভেতরেও কেমন যেন একটু সুখ হয়েছিল। হাজার হোক তারও একটা দাম আছে তার বন্ধুর কাছে। বিপদের সহায়। নইলে কে কাকে বিশ্বাস করে আজকাল টাকা ধার দেয়!
টাকা দেওয়ার আগে আবদুর রহমান দোকানের ভেতরে উঠে চলে গিয়েছিল। তারপর পর্দার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বন্ধুকে ডেকে নিয়েছিল ভেতরে। ভেতরে বসে স্টিলের আলমারি থেকে বের করেছিল টাকার থলি। সেখান থেকে গুনে গুনে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল সে বন্ধু আবদুল কাদিরের হাতে।
দিন চলে গেল। দিনের পর দিন। দিন তো যাবেই। কার সাধ্যি আছে তাকে আটকে রাখে! তবে এইসব দিন পদ্মপাতার ওপর টলমলে পানির মতো নড়বড়ে। দেশের অবস্থার মতো। কখন কী হয় কেউ বলতে পারে না। আবদুর রহমান আজকাল ব্যাংকে টাকা রাখতেও ভয় পায়। কেন জানি তার মনে হয় ব্যাংকের ম্যানেজারগুলোর চোখেমুখে আজকাল কীরকম এরকম একটা লোভের চাহনি ফুটে ওঠে। তাদের চেহারার ভেতরেও কেমন যেন খেত-খামার থেকে উঠে আসার ভাব। সবকিছুতে কেমন ঢিলেঢালা। যেন চব্বিশ ঘণ্টায় দিন নয়, বাহাত্তর ঘণ্টায় একেকটা দিন। ভয়াবহ অবস্থা। টাকা গুনতে তারা গড়িমসি করে। হাতে থুতু মাখিয়ে তারা টাকা গোনে। টাকাগুলোর চেহারাও মলিন। যেন টাকা হলেও তারা মূল্যহীন। এদিকে ব্যাংকের ভেতরে আইরনসেফের ধারে রান্নাবান্নার শব্দ পাওয়া যায়। গোস্ত রান্নার ঘ্রাণ ওঠে।
আবার কোনো কোনো ম্যানেজার ঝিলঝিলে পর্দার আড়ালে নাক ডেকে ঘুমোয়। তার পা দুটো তোলা থাকে টেবিলের মাথায়। দুপুরবেলা এরাই আবার টিফিনক্যারির ভেতরে হাত ডুবিয়ে খপখপ করে ভাত-তরকারি বের করে প্লেটে নিয়ে খায়। রান্না করার বুয়া কখনো কখনো ম্যানেজারের সামনে গিয়ে পান খাওয়া দাঁত মেলে জিজ্ঞেস করে, খানা ভালা হইছনি? কেউ কেউ, বা কোনো কোনো ব্যাংক ম্যানেজার টিফিনক্যারির ভেতরেই হাত ডুবিয়ে ভাত খায়। মাছের কাঁটা বেছে নিজের টেবিলের ওপরেই ফেলে রাখে। কাউন্টারের ক্যাশিয়ার নামাজ পড়ার জন্যে কাউন্টার খোলা রেখেই উঠে যায়। আল্লার ডাক এসেছে, কে তা রোধ করতে পারে? এদিকে কাউন্টারের এপাশে কাস্টমার হাঁকুপাঁকু করতে থাকে। ভাই, আমার এক্ষুনি টাকাটা পেতে হবে, ক্লায়েন্ট বসিয়ে রেখে এসেছি।
আবার খবরের কাগজে এমন একটা মাস যায় না যেখানে খবর ওঠে না যে ব্যাংকের ম্যানেজার কাস্টমারের টাকা নিজেই ব্যাংক থেকে তুলে হাওয়া। কেউ কেউ টাকা চুরির পরে ধরা খেয়ে জেলের গরাদের ভেতরে। গরাদের মোটা রড দুহাতে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার যারা গরাদের বাইরে তাদের পরনে থ্রিপিস স্যুট, গলায় টাই।
এইসব দেখে আবদুর রহমানের বুক ধড়ফড় করে। ব্যাংকটাকে আর ব্যাংক বলে মনে হয় না। জোতদারের আড়ত বলে মনে হয়। তাদের হাতে টাকা রেখে বাড়ি ফিরে আসতে ভয় লাগে। টাকার বান্ডিল বুকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে!
তা সেসব দিনও ক্রমে ক্রমে পেরিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন নতুন ব্যাংক খুলছে চারদিকে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব এসেছে ব্যবসায়ীদের ভেতরে।
গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও দেশ কীভাবে যেন চলার চেষ্টা করছে।
আবদুর রহমান তার দোকানে বসে আপনমনে এইসব ভাবে।
পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করলেও আবদুর রহমান জানত আবদুল কাদিরের কথার নড়চড় হয় না। ঋণের টাকা সে যেভাবে পারে শোধ দেবে। হোক আবদুর রহমান তার ছেলেবেলার বন্ধু, তবু। সে তো টাকাটা সাহায্য হিসেবে চায় নি। সে চেয়েছে ঋণ হিসেবে। সাহায্য যদি চাইত, সেটা অন্য কথা হতো। তবে সে যে এতখানি গরিব হয়েছে তা আবদুর রহমান জানত না। আগে সে খবরের কাগজে একটা চাকরি করত। বেশ কিছুবছর সেই চাকরির বয়স হয়েছিল। তারপর সম্পাদকের সঙ্গে তার কী মতের অমিল হলো, ঝপ করে চাকরিটা সে ছেড়ে দিল। কারও সঙ্গে পরামর্শ করারও তাগিদ অনুভব করল না। অথচ পৃথিবীর যে-কোনো চাকরিই হলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা, একথা তাকে কে বোঝাবে?
আবার কিছুদিন আগে শুনছে সে নাকি নতুন এক অফিসে কাজ শুরু করেছে। কাজটা তখনো নাকি পাকা হয় নি। আর পাকা হলেই বা কি, আবদুর রহমানের মনের ভেতরে থিতু ভাব না এলে কোনো চাকরিই সে করতে পারবে না। প্রতিটা অফিসে কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে আর কতদূর যেতে পারবে?
এতসব কিছুর পরেও বন্ধুর জন্যে মনের মধ্যে কোথায় যেন ভীষণ এক মমতা বোধ করে আবদুর রহমান। বন্ধুর অতীত তো সে একেবারে ভুলে যায় নি। বন্ধু আবদুল কাদিরকে তার ছাত্রজীবন থেকে দেখে আসছে। স্কুলজীবনে আবদুল কাদির ছিল আবদুর রহমানের সহপাঠী। লেখাপড়ায় বলতে গেলে ছিল সে ফার্স্টক্লাস। কিন্তু ওই যা হয়। গরিব চাষির ঘরে মেধার মূল্য কতটুকু! বাবা তাকে বারবার চাষের খেতে টেনে নিয়ে গেলেও আবদুল কাদির পালিয়ে চলে আসত স্কুলে। লেখাপড়ার প্রতি প্রচ- ছিল তার ঝোঁক। অনেকে বলত আবদুল কাদির বড় হয়ে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হবে। তখনকার দিনে এটাই ছিল নিম্নমধ্যবিত্তের একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্ন তারা বংশানুক্রমে মনের ভেতরে লালন করে নিয়ে বেড়াত। কিন্তু আবদুল কাদিরের অবোধ বাবা-মা তার গুরুত্ব বুঝত না বরং ছেলেকে ফসলের মাঠে নিতে পারলে তারা বেদম খূুশি হয়ে যেত।
তবে ক্লাসের মাস্টাররাও তাকে যতœ করে পড়াত। কে বলে স্কুলে মাস্টাররা পড়ায় না? প্রতিভার সাক্ষাৎ পেলে কোনো মাস্টার পড়ায় না?
কিন্তু সেই আবদুল কাদির লেখাপড়া শেষ করতে পারল না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিএ অনার্স কোনোরকমে পাস করলেও এম এ-টা শেষ করতে পারল না। সে তখন দেশে চলে গেল। বাবা-মায়ের কাছে থেকে গেল। বাবা মারা গেলে বোনটিকে বিয়ে দিল। এরপর মা মারা গেলে হঠাৎ একদিন খেতখামার বিক্রি করে দিয়ে ঢাকায় ফিরে এল। তার বাবা খুব বড় কোনো কৃষক ছিল না। সুতরাং আবদুল কাদিরকে চাকরির সন্ধানে কিছুদিন এখানে-ওখানে ঘুরতে হলো। তখনো তার বিয়ে হয় নি। অথচ আবদুর রহমান ততদিনে বিবাহিত। বাবা বেঁচে থাকতেই আবদুর রহমানকে বিয়ে দিয়ে গেছে।
দোকানে বসে আবদুর রহমান তার শৈশবের কথা মাঝে মাঝে মনে করে । তবে খুব কম। কেউ মনে পড়িয়ে দিলে তখন মনে করে। আবদুল কাদিরের ক্লাসে মোটামুটি সব ছেলেই ছিল লেখাপড়ায় ভালো। যে দু-চারজন ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিল তাদের ভেতরে আবদুর রহমান ছিল একনম্বর। অঙ্কের বণিক বাবু আবদুর রহমানের মাথায় গাট্টা মারতে মারতে মাথার একপাশ যেন বসিয়ে দিয়েছিল। তবে আবদুর রহমান যে বুদ্ধিহীন ছিল তা ঠিক নয়, বরং অন্যান্য বাস্তব সব ঘটনাবলির ভেতর দিয়ে আবদুর রহমানের একটা বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। আর ছিল তার ধৈর্য। একভাবে কোনোকিছুর পেছনে লেগে থাকা। এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
এর ফলে যা হওয়ার তাই হলো। তার ক্লাসের অন্য বন্ধুরা স্কুল থেকে বেরিয়ে নানাপ্রকারের শিক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ গেল রাজশাহীতে। কেউ গেল যশোরে। কেউ চুয়াডাঙ্গায় । আর আবদুল কাদির যশোর থেকে আইএ পাস করে চলে এল ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। এবং হলো।
আবদুর রহমান পড়ে থাকল সেই যশোরের শৈলকূপায়। স্কুলের বড় ক্লাসে উঠে কোনো রকমে ম্যাট্রিক পাস করে সে পৈতৃক ব্যবসায়ে লেগে গেল। তার বাবার ছিল শহরের তেমাথার ওপর বেশ বড় একটা ওষুধের দোকান। একজন কর্মচারী ছাঁটাই করে আবদুর রহমান তার বাবার কাজে সহায়তা করতে লাগল।
তারপর আরও কিছুদিন বাদে তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা যখন নানাবিধ কারণে শহর ছাড়ল, তখন আবদুর রহমান বেশ পোক্ত একজন ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে।
সেই সময় তার স্কুলের পুরোনো টিচার, অঙ্কের শিক্ষক বণিক বাবুর ক্যানসার ধরা পড়ল। তখন বণিক বাবু। আগের চাইতেও গরিব। তাকে অর্থ সাহায্য করার মতো এমন কেউ নেই। বণিক বাবুর নিজের ছেলেমেয়েরা তখন ছোট। আবদুর রহমান এইসময় স্যার বণিক বাবুর একমাত্র ভরসা। বণিক বাবুকে সে অর্থ সাহায্য করত ঠিকই, কিন্তু এই নিয়ে তার মনে এক জিঘাংসামূলক আনন্দের সঞ্চার হতো মাঝে মাঝেই।
বণিক বাবুর মৃত্যুর আগে শেষ যে বার দেখা করতে গিয়ে সে টাকা দিয়ে এসেছিল, ফিরে আসার আগে উচ্চকন্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, সবুর কি আপনাকে দেখতে এসেছিল, স্যার?
না, বাবা।
বদরুল হাসান এসেছিল? আপনি তো জানেন, বর্তমানে সে এখানকার সরকারি কলেজের অধ্যাপক হয়েছে?
না, বাবা।
হরিপদ এসেছিল?
ওর কথা আর বলো না, ও একটা অমানুষ।
কাদির এসেছিল, স্যার?
মলিনমুখে বণিক বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, নাঃ।
কথা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।
নিয়ামত এসেছিল, স্যার?
না, না।
স্যারের কথা শুনে খ্যা খ্যা হেসে উঠেছিল আবদুর রহমান। পরিতৃপ্তির হাসি। এরপর করুণায় গলার স্বর বিগলিত করে বলেছিল, ওরা আসবে কি স্যার। ওদের নিজের সংসার নিয়েই টানাটানি। যা রোজগার করে তাতে নুন আনতেই পান্তা ফুরোয়। এখানে এলে আপনাকে সাহায্য করতে হবে বলেই হয়তো আসে না। এরা সব আপনার ভালো ছাত্র ছিল তো স্যার। অংক ভালো বোঝে!
৮
টাকা ধার করার ঠিক পাঁচদিন বাদে একদিন ফোন এল আবদুল কাদিরের। সেসময় দোকানে ভিড় কম ছিল।
আবদুর রহমান দোকানের পেছনে গিয়ে সবেমাত্র ক্যাশবাকসোটা খুলেছে, ওমনি ফোন এল।
ফোন তুলে আবদুর রহমান বলল, হ্যালো?
কে, রহমান?
হ্যাঁ, তুমি কাদির?
হ্যাঁ।
কী ব্যাপার দোস্তো, ভালো আছো তো?
হ্যাঁ, আছি মোটামুটি। কিন্তু আমার ছেলেটা তো ভালো হচ্ছে না। কী যে করি, ভাই! দিনের ভেতরে কতবার করে যে বমি করে, তার হিসাব নেই। ওষুধ দিচ্ছি। নিয়মিত ডাক্তাররা দেখছে। ইনভেস্টিগেশন যা যা করতে বলছে, সব করাচ্ছি। ওইটুকু ছোট বাচ্চাকে গতকাল স্যালাইন দিতে হয়েছে। এসব চোখে তাকিয়ে দেখা কী যে কষ্ট ভাই!
আবদুল কাদিরের কথা শুনে মন খারাপ হলো আবদুর রহমানের। তার কোনো সন্তানাদি নেই, ঠিক কথা। কিন্তু একটি সন্তানের জন্যে মনে মনে হাহাকার আছে। বিশেষ করে তার স্ত্রীর ভেতরে এটা বেশি।
একটু চুপ করে আবদুর রহমান বলল, দরকার হলে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও না?
না, সেটা সম্ভব নয়। এর আগে দুবার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম, চার-পাঁচদিন করে ভর্তিও হয়েছিল। একটু ভালো হতে ওরা ছেড়ে দিল। । বলল, কোনো কোনো বাচ্চার এরকম অসুখ হয়, আবার ঠিক হয়ে যায়। এদিকে তোমার ভাবি আবার নার্ভাস মানুষ। স্নায়ুদুর্বলতায় ভোগে। বাচ্চার অবস্থা দেখে সে এখন ঝাঁড়-ফুঁক করাচ্ছে নারিন্দার পীর সাহেবের কাছে। মাদুলি তাবিজও নেওয়া হয়েছে তরিকা মতো। আবার এদিকে দেদার পয়সা খরচ হচ্ছে। দোয়া করো ভাই, ছেলেটা যেন বাঁচে।
হাঁফাতে হাঁপাতে কথা বলতে লাগল আবদুল কাদির।
একসময় ফোন অফ হয়ে গেল।
আবদুর রহমান বুঝল কোনো দোকান থেকে ফোন করছিল আবদুল কাদির। পয়সা শেষ, তাই লাইন কাটা গেল।
ফোন রেখে আবদুর রহমান চোখ তুলে দেখল মোটা একটা রেক্সিনের ব্যাগ হাতে করে দোকানে এসে ঢুকেছে কে.এস. সোবহান। লোকটা মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। নামকরা এক কোম্পানিতে চাকরি করে। চেহারাটা নরম এবং লাজুক। তবে অন্যদিকে স্মার্টনেস আছে। যার জন্যে বাপের দেওয়া নাম সোবহান মোল্লা কেটে কে.এস. সোবহান করেছে।
তার ভিজিটিং কার্ডে এই নামই ছাপানো।
সোবহান দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, ভালো আছেন, রহমান সাহেব?
ভালো, আপনি কেমন?
এই চলে যাচ্ছে আপনাদের দোয়া। বলল সোবহান
চলে গেলেই ভালো, আজকাল জীবন ঠিকমতো চালানো যে কী মুশকিল, তা তো আমি জানি।
ঠিক বলেছেন ভাই, এই তো দেখুন না আমাদের কোম্পানিতে আবার নতুন এরিয়া ম্যানেজার নিয়োগ হলো, অথচ আমার এবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখানেও সেই নেপোটিজিম। ভাবছি পরেরবার চাকরিতে উন্নতি না হলে এই কোম্পানি ছেড়ে দেব।
তার কথা শুনে একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে আবদুর রহমান বলল, ছেড়ে দেবেন মানে? ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবেন?
উত্তরে কে. এস সোবহান বলল, কোথায় এখনো ঠিক করি নি। তবে দু-তিনটে অফার আছে।
কথার ফাঁকে ফাঁকে আবদুর রহমান আসল প্রসঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ সে জানত কে. এস. সোবহান খামোখা তার দোকানে বেড়াতে আসে নি।
একটু পরে সে বলল, ভালো চাকরি যেখানে সুবিধে হয়, সেখানে করাই ভালো।
তা ঠিক বলেছেন। তবে আজ কিছু মাল এনেছি আপনার জন্যে। বলল এবার সোবহান।
কোন মাল? সেদিন যেগুলোর কথা বলেছিলাম, সেগুলো?
কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল আবদুর রহমান।
আজ বহুদিন হলো কে. এস. সোবহানের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ আছে।
উত্তরে সোবহান বলল, হ্যাঁ। তবে বেশি এখন দিতে পারব না। খুব কড়াকড়ি। আবার যখন নতুন চালান আসবে দেব। তা ছাড়া ডাক্তাররাও খুব ঘাওরা, যে-কোনো ওষুধ লেখার আগে সরাসরি স্যাম্পল চায়।
কথা শুনে আবদুর রহমান বুঝদারের মতো বলে উঠল, তা তো চাইবেই। চিরদিন মুফতে পেয়ে এসেছে। তবে এখন আর কি দেখছেন, আগে তো ডাক্তারদের জন্যে বিদেশ থেকে দামি দামি সব উপহার আসত। বিদেশি কোম্পানিরা খুব দামি সব উপহার পাঠাত। বছর শেষে এমন সব সুন্দর ক্যালেন্ডার পাঠাত যাদের ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ডাক্তাররা তাদের চেম্বার সাজাত। এখন তো দেশি সব কোম্পানি বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে ওষুধ তৈরি করার চেষ্টা করছে। এখনো সব প্রিমিটিভ অবস্থায়। তাদের জান এত বড় না যে মন খুলে ডাক্তারদের উপহার দেবে!
আবদুর রহমানের কথা শুনে কে. এস. সোবহান হাসল, হাসিটা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো দেখালো। কিন্তু সে গলার সুর ধরে রেখে বলল, এগুলো অবশ্য বিদেশি ওষুধ। এর আগে আপনাকে কিছু কোরামিন ইনজেকশন দিয়েছিলাম। সেগুলো কি সব শেষ হয়ে গেছে? এগুলোও সেই কোরামিন। বর্তমানে দেশে এভেইলেবেল না। তবে আমাদের স্টকে আছে প্রচুর পরিমাণে। আমি কিন্তু একটারও কভার দেব না। কারণ সবগুলো অ্যামপুলে ফিজিসিয়ান স্যাম্পেল-এর ছাপ মারা ছিল। তাই এখন বোতলের গায়ে কিছু লেখা নেই।
তার কথা শুনে আবদুর রহমান তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। এসব আমি ম্যানেজ করে নেব। তবে এক্সপায়ারি ডেট-এর কোনো ইনজেকশন দেবেন না। তাহলে ঘাপলা হতে পারে।
তার কথা শুনে কে. এস.সোবহান বলে উঠল, আরে না, না। এখনো ছ’ মাসের জন্যে নিরাপদ। তারপরও যদি স্যাম্পেল থেকে যায় তো আরও ছয়মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারেন। এগুলো হচ্ছে বিদেশি ওষুধ। এক্সপায়ারি ডেট যা লেখা থাকে তার চেয়েও ছ’মাস বা একবছর বেশি পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
উত্তরে আবদুর রহমান চিন্তিতমুখে বলে উঠল, আপনার কথা শুনে গতবার আমি কোরামিন আর অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর মেয়াদ ছ’মাসের মতো তারিখ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেও তো কিছু স্যাম্পেল থেকে গিয়েছে।
একথায় কে. এস . সোবহান বলে উঠল, কোনো অসুবিধে নেই। আপনি ওগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারেন আজ। অথবা নিজেও ডেস্ট্রয় করে ফেলতে পারেন।
একথার উত্তরে মাথা নেড়ে আলতো করে সায় দিল আবদুর রহমান। কিন্তু ওষুধগুলো ফেরত দেওয়ার তাগিদ অনুভব করল না। কারণ সে মনে মনে জানত ওষুধের চালান বাজার থেকে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এক্সপায়ারি ডেট জীবনে আসবে না। তবে চালু ওষুধ শেষ হতেও দেরি হবে না।
এসব কথা হচ্ছিল দোকানের পেছনে একটা আমকাঠের চৌকিতে বসে। সেখানে একটা তিন সিটের সোফাও আছে। অনেক আগে খুব সস্তায় পেয়ে কিনে রেখেছিল আবদুর রহমান। রেক্সিনের কভার দেওয়া পুরোনো সোফা এখনো বেশ কাজে দেয়।
টাকা হাতে নিয়ে ফিরে যাবার সময় কে.এস. সোবহান ইতস্তত করে বলল, দেখেন রহমান সাহেব, আজকের দামটা ঠিক হলো না। ট্রেড প্রাইসের অনেক নিচে আপনাকে আমি স্যাম্পেল বিক্রি করি, আপনি যা দেন তাতে করে আমার রিস্ক কভার হয় না!
তার কথা শুনে আবদুর রহমান হাসল। অমায়িক হাসি। হাসতে হাসতে বলল, মন খারাপ করবেন না সোবহান সাহেব, বিক্রিবাটা কম, পরের বার পুষিয়ে দেব। কোরামিন ইনজেকশন ক’জন ব্যবহার করে? ক’জন মৃত্যুমুখী মানুষ কোরামিন ব্যবহারের সুযোগ পায়?
৯
দোকান ছেড়ে কে. এস. সোবহান চলে গেলে আপনমনে খুব খানিকটা হাসল আবদুর রহমান। মনে মনে বলল, ডাক্তারদের ন্যায্য স্যাম্পেল গোপনে হাতিয়ে নিয়ে বিক্রি করে খাচ্ছে আবার রিস্ক কভারের কথা বলে! হা, হা। সত্যি কথা বলতে ও যা হাতে পায়, তার সবটাই তো ওর লাভ। একেকজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের বাসা আজকাল মেডিসিন-এর স্যাম্পেল দিয়ে সয়লাব। এসব ডাক্তারদের স্যাম্পেল। নিজেরা আজকাল পয়সা দিয়ে ওষুধ তো কেনেই না, তাদের আত্মীয়স্বজনদেরও কিনতে হয় না!
কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দোকানের পেছন থেকে বাইরে বেরোবার সময় তার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন তার দোকানের কাউন্টারের পেছনে তালা লাগানো অবস্থায় থাকে। কারণ মানুষের স্বভাব হচ্ছে চোখের সামনে টেলিফোন দেখলে একটু ফোন করতে চাইবে!
তা ছাড়া কোনো কাস্টমারও টেলিফোন ব্যবহার করতে চাইলে সে মনে মনে খুব নাখোশ হয়। মাঝে একবার একটাকা ফি নিয়ে বাইরের মানুষকে টেলিফোন করতে দিত। তাতেও অনেক ঝামেলা। কেউ একবার ফোন করতে শুরু করলে তার আর ছাড়াছাড়ি নেই।
সরকার ইচ্ছে করলে ঘরে ঘরে টেলিফোনের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে এ রকম সমস্যা হয় না। কিন্তু সরকার তা করবে না। আজকালকার দিনে যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা দেশের ভেতরে নেই বললে চলে, সেখানে ঘরে ঘরে টেলিফোন দিতে অসুবিধে কোথায়? না, তার বা কেবল্ কিনতে নাকি পয়সা লাগে। সরকারের অত পয়সা নেই। অথচ সরকার বোঝে না ঘরে ঘরে টেলিফোন হলে মানুষ রাস্তাঘাটে কম বেরোত। অনেক কাজ টেলিফোনেই সেরে ফেলত। রাস্তঘাটে আজকাল বেরোনো একটা সমস্যা। সামান্য সুযোগ পেলেই মানুষের জানমাল ছিনতাই হয়ে যায়।
দেশে দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাতের বেলা পথ চলতে কত মানুষ যে ম্যানহোলের ভেতরে পা ফসকে পড়ে গেছে, তার হিসেব নেই।
শুধু পড়ে গেছে না, পড়ে মরেও গেছে।
টেলিফোন বেজে উঠতে আবদুর রহমান তার বন্ধু আবদুল কাদিরের কথা মনে করল। । এ ফোন নিশ্চয় তার। নাঃ বন্ধুটা তার ছেলেটিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেছে। মনে মনে ভাবতে ভাবতে সে ফোন তুলে হ্যালো বলল।
কিন্তু না, আবদুল কাদির নয়। রেহানা।
রেহানার গলার স্বর তারের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল। যেমন শান্ত তার গলা, তেমন গম্ভীর ।
এরকম গলা শুনলে আবদুর রহমানের পেটের ভেতরে কেমন যেন গুড়গুড় করে ওঠে। রেহানাকে সে এখনো ভয় করে। অথচ করার কথা না। রেহানা তাকে রোজগার করে খাওয়ায় না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু এতসব হিসাব করে তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয় না।
তবে কোনোদিন-না-কোনোদিন তাকে সাহসী হতে হবে। কীভাবে সেটা হবে সে বিষয়ে যদিও তার মনে কোনো নির্দিষ্ট রূপরেখা নেই।
ভাত খেতে বাসায় ফিরবে না? রেহানা ও প্রান্ত থেকে গোটা গোটা অক্ষরে বলে উঠল।
সাতক্ষীরার মেয়ে হলেও রেহানা ভালো বাংলায় কথা বলতে চেষ্টা করে।
ওঃ, কটা বাজে? একটু যেন বিহ্বল স্বরে বলে উঠল আবদুর রহমান।
দুটো তো বেজে গেছে। আবার আজ রাতে ছোট কাকির বাসায় দাওয়াত। মিনুকে আজ দেখতে আসবে।
স্ত্রীর কথা শুনে মনে মনে একটু বিরক্ত হলো আবদুর রহমান। এই একটা ব্যাপার সে ভালোবাসে না। আর তা হলো অযথা আত্মীয়তা।
কিন্তু রেহানার ভয়ে মনের কথা সে ঠিকমতো কোনোদিন বলতে পারে না। উল্টো সে বরং বলে উঠল, ওঃ, তাই নাকি?
কথাটা বলে তার মনে একটু ভয় হলো। রেহানার বিরাগভাজন হবার ভয়।
আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর রাখা রেহানার একটা বাতিক বলা যেতে পারে। অথবা এইসব নিয়ে থাকতেই যেন সে ভালোবাসে। অবশ্য তা ছাড়া সে সময় কাটাবেই বা কী করে! দূর দূরসম্পর্কের আত্মীয়রাও রেহানার নজর থেকে সরতে পারে না। এর জন্যে রেহানার যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু এর জন্যে আবদুর রহমানকে যে কতখানি খেসারত দিতে হয় তা কারও জানা নেই।
স্ত্রীর কাছে অবদুর রহমান কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করে। আবার রেহানা নিজেও যেন একটা দূরত্ব বজায় রেখে সংসার করতে ভালোবাসে। তাদের যৌনজীবনও বেশ সংক্ষিপ্ত। বিছানায় দুজন দুটো বালিশ জাপটে ধরে ঘুমোতে যেন বেশি ভালোবাসে। আজ দশ বছর তাদের বিয়ে হয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত কোনো সন্তানাদি হয় নি। কেন যে হয় নি, তাও তারা জানে না। ভবিষ্যতে হবে কি না তাও জানে না। অথচ আবদুর রহমান এর মধ্যেই চারতলা ভিতের ওপর দোতলা বাড়ি করে বসে আছে কাঁঠাল বাগানে।
ওষুধের ব্যবসা করলেও আবদুর রহমান এমনিতে নির্জনতা প্রিয় মানুষ। হইচই, বিয়ে, আকিকা, পানচিনি, গায়েহলুদ, সভাসমিতি এসব তার দু’চোখের বিষ। কিন্তু ইদানীং যেন এসবের বেশি বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। শীত আসতে পারে না, বাসভর্তি করে লোকজন বনভোজনে রওনা হয়ে যায়। এতবড় একটা যুদ্ধের পর, দেশে এতসব হত্যা এবং রাহজানির পরও মানুষের মনে যেন স্ফূর্তির অভাব দেখা যাচ্ছে না। এই পিকনিক করতে গিয়েও তো বাস খাদে পড়ে কতসব মানুষ মরছে।
বিয়ে আগে দু-তিন দিনে শেষ হয়ে যেত। এখন বিয়ে হতে কমপক্ষে তেরো দিন সময় ক্ষেপণ হয়। প্রথমে পাকা দেখা, তারপর ছেলেতে মেয়েতে একটু বন্ধুবান্ধব নিয়ে রেস্টুরেন্ট, তারপর বিয়ে ঠিক হলে পর প্রথমে মেয়ের গায়েহলুদ, এবং সেই গায়েহলুদে ছেলেরবাড়ির লোকজনের স্ফূর্তি, তারপর ছেলের গায়েহলুদ, সেই গায়েহলুদে ছেলের বাড়ি গিয়ে মেয়ের স্ফূর্তি, হলভাড়া করে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান, বরযাত্রীর মতো সেই গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনের ভিড়, অজস্র ফুল দিয়ে, বিশেষ করে গাঁদা ফুল দিয়ে গেট সাজানো, হলুদ বাঁটো, মেহেদি বাঁটো বলে তারস্বরে চিৎকার করে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙানো, তার পর আবার ইংরেজি গানের সুরও সমান তালে বেজে যাওয়া, নইলে বিয়ে আধুনিক হয় না, তারপর যেদিন বিয়ে, তার পরদিন জোড় বদল, আবার তার দুদিন বাদে কনের নিজের শ্বশুরবাড়ি পদার্পণ। সেখানেও সারা আত্মীয়স্বজনের ভিড়, এসব দেখে দেখে আবদুর রহমান ইদানীং যাকে বলে ফেডআপ। কারণ এতসব ধুমধাড়াক্কা করে বিয়ে হতে না-হতে হানিমুন থেকে ফিরেই কনের প্রতিবাদ, এই বিয়ে চলবে না!
হাঃ, আবদুর রহমান দোকানে বসে বসে ভাবে। রেহানার সঙ্গে বাধ্য হয়ে তাকে মাঝে মাঝে এইসব অনুষ্ঠানে যেতে হয়। কিন্তু যদি তার একফোঁটা ভালো লাগে! আর আজকাল তার কী হয়েছে, যে-কোনো বিয়ের দোতলা সাইজের ঝকমকে কার্ড হাতে পাওয়ামাত্র তার মনে হয়, এই বিয়ে টিকবে তো? এই দম্পতির বাচ্চাকাচ্চা হবে তো?
এতসবের পরেও আবদুর রহমানকে তাকে নিজস্ব এলাকার মসজিদ কমিটির সভাপতি হতে হয়েছে। সবকিছুর হাত এড়ানো সব সময় তো যায় না।
অথচ রেহানার ব্যাপারে বিষয়টা ঠিক উল্টো। তার স্ত্রী রেহানা হইচই ছাড়া যেন থাকতে পারে না। এটা যে তার বাচ্চা না হওয়ার দুঃখ ভুলে থাকার একটা চেষ্টা, তা অবশ্য আবদুর রহমান জানে। এ ব্যাপারে তার নিজের কিছু অপরাধবোধও কাজ করে। অনেক ডাক্তার এবং ওষুধপত্র করেও এখন পর্যন্ত সুসংবাদ পায় নি। এজন্যে মনে তার প্রচ- হতাশা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে এসব প্রকাশ করে না। সন্তান না হওয়ার মূল দায়িত্ব কেন জানি সে নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছে।
স্ত্রীর টেলিফেন হাতে ধরে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এপ্রান্ত থেকে আবদুর রহমান বলল, আজ আর বাড়ি যেতে পারব না রেনু। অনেক কাজ আছে।
কী কাজ? রেহানা শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল।
আবদুর রহমান মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের কি কোনো হিসেব আছে? আজ নতুন ওষুধের চালান আসবে। হিসাবপত্র করতে হবে। বিকালে তসির মিয়া এলে পরে দোকান ছাড়তে পারব।
তাহলে দুপুরে খাবে কোথায়? রেহানা একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।
উত্তরে আবদুর রহমান বলল, ভাত পাঠিয়ে দিতে পারো বাড়ি থেকে।
রেহানা বেশ সহজেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলল, তাহলে ঠিক আছে। বিকেলে সময় হলে আমি ছোট কাকির বাসায় চলে যাব। তুমি কি দোকান থেকে সোজা ওখানেই চলে যাবে? উত্তরে আবদুর রহমান তড়িঘড়ি করে বলল, সেই ভালো। আমি দোকান থেকে সোজা ওখানেই চলে যাব। রাতে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।
আচ্ছা, বলে টেলিফোন রেখে দিল রেহানা।
আবদুর রহমান একটু চুপ করে থেকে খাতা খুলে ওষুধের স্টক মেলাতে বসল।
ইতিমধ্যে কাস্টমার আসছে যাচ্ছে। কর্মচারী দুজন প্রায় সর্বক্ষণই ব্যস্ত হয়ে আলমারির তাক থেকে ওষুধ নামানো-ওঠানো করছে।
সেদিকেও একটা চোখ রাখতে হচ্ছে। ক্যাশমেমো ঠিকমতো কাটছে কি না খেয়াল রাখতে হচ্ছে।
১০
দোকানের কর্মচারীদের আবদুর রহমান একেবারে বিশ্বাস করে না। যদিও দুজন কর্মচারী সব সময় তার দোকানে থাকে, তবু তারা কেউ পার্মানেন্ট নয়। আজ আছে কাল নেই। মাসের শেষে হিসাব মেলাতে গেলে প্রায় দেখে ওষুধ বিক্রি শেষ কিন্তু টাকার হিসাবে গরমিল। এবং কেন যে গরমিল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এইসব নিয়ে মাসের শেষে আবদুর রহমানের একটা ঝক্কি ঝামেলা যায়। তবু ভাগ্যি তসির মিয়া ছিল। এই লোকটি তার বাবার আমলের। এর বয়স বোঝা যায় না। তসির মিয়াকে সে যৌবনে যেরকম দেখেছে এখনো যেন তসির মিয়া সেরকমই আছে। বাবার আমল থেকে আছে বলে এবং বাবার হাতেই তার কাজ শেখা বলে এখনও তসির মিয়া তার এবং তার পরিবারের প্রতি অনুগত। কিন্তু সে আসে সন্ধ্যার পর। সেই মোটামুটি সবকিছু সামলে রাখে। তা ছাড়া কর্মচারীদের পেটপাতলা স্বভাবও আবদুর রহমান পছন্দ করে না। সে যে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের কাছ থেকে অল্প দামে ওষুধ কেনে ড্রাগ কোম্পানিদের নজর ফাঁকি দিয়ে এখবর একবার রটে গেলে তার ব্যবসার ক্ষতি হবে। এমনিতে সে একটু উদ্বিগ্ন স্বভাবের মানুষ। শুধু তাই না, মানুষকে সে সহজে বিশ্বাস করতেও পারে না।
এমনকি বন্ধু আবদুল কাদিরের প্রতিও তার মনে সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।
বন্ধুর এরকমের ব্যবহার কি শুধু ঋণ শোধ না দেওয়ার জন্যে? তার বন্ধু কি বোঝে না যে আবদুর রহমান ইচ্ছে করলে আজই থানায় গিয়ে তার নামে ডায়েরি করতে পারে? তার ভাড়া বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে দিতে পারে?
অবশ্য সে এসবের কিছু করবে না বা করার চিন্তা এখন পর্যন্ত তার মাথায়ও আসে নি, তবু বন্ধু যদি তাকে নিয়ে ট্রিকস্ খেলতে চায়, তবে সে-ই বা চুপ করে থাকবে কেন?
তার দোকানে প্রত্যেকদিন বিকালে পর্দাঘেরা একটা খোচে একজন ছোকরা ডাক্তার এসে বসে। সদ্য পাস করা ডাক্তার। এখনো বিয়ে থাওয়া হয় নি। তবে মনে হয় বেশ বুদ্ধিমান । আবদুর রহমানের ভাষায়, বেশ চতুর। তাই আবদুর রহমান মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। আরও অপছন্দ এই কারণে যে তার বন্ধু আবদুল কাদিরের সঙ্গে এই ডাক্তারের বেশ ভাব আছে। একদিন দুজনকে নিজেদের ভেতরে হেসে হেসে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতেও সে শুনেছে। আবদুর রহমানের মনে কোথায় যেন এক দুর্বলতা আছে। স্মার্ট বা দৃঢ় চরিত্রের কোনো মানুষকে দেখলে সে মনে মনে নার্ভাস বোধ করে।
তারওপর এই ডাক্তার রিপ্রেজেনটেটিভদের কাছ থেকে পাওয়া ওষুধের স্যাম্পেলগুলো ফার্মেসিতে দান না করে রোগীদের ভেতরে বিলিয়ে দেয়! এতে আবদুর রহমানের ব্যবসায় ক্ষতি। ডাক্তারকে তো বিনা পয়সায় বসতে দিয়েছে, নাকি?
একবার দোকানে তার ছোটশালাকে বসিয়েছিল, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি এবং চালবাজ ব্যবহার দেখে এত ঘাবড়ে গেল যে দোকান থেকে তাকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে তবে মনে শান্তি। এই নিয়ে রেহানার সঙ্গে তার খিটিমিটি বাঁধল বটে, তবে সেটা স্থায়ী হতে পারে নি বেশিদিন।
মনে মনে মাঝে মাঝে নিজেকে বিচার করতে চেয়েছে আবদুর রহমান। ছেলেবেলায় স্কুলে গিয়ে পড়া না পারার জন্যে মাস্টারদের অতিরিক্ত মারধর এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপের জন্যে হয়তো তার ব্যক্তিত্বে কোনো চোট লেগে থাকবে, যে জন্যে নিজের মনের ভেতরেই নিজেকে সে খাটো চোখে দেখতে শিখেছে, যদিও বাইরে সে একজন টাফ বিজিনেস ম্যান। ওষুধের কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তার জমাট লেনদেন। ওষুধ তো সে কোম্পানির কাছ থেকে কেনেই, তারওপর কিছু ওষুধ অবৈধভাবে তার কাছে বিক্রি করে রিপ্রেজেনটেটিভরা। বিশেষ করে ডাক্তারদের স্যাম্পেলগুলো। এ খবর কোম্পানির হেড অফিসও জানে, কিন্তু এসব খবর তারা জেনেও না-জানার ভান করে। এতসব দেখতে গেলে ব্যবসা চালানো যায় না।
কোন ওষুধ কখন বাজারে ছাড়তে হবে, কোন ওষুধ কখন লকারে ভরে ফেলতে হবে, এবং ইমারজেন্সির সময় বেশি দামে বাজারে ছাড়তে হবে, এসব ব্যাপার আবদুর রহমানের নখদর্পণে। তার বাবার কাছ থেকে সব শেখা। এখন তো এসব আরও বেশি। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ বড় দ্রুত জনগণের মাথার ওপর পা দিয়ে বড়লোক হতে চায়। এখনো এদেশে ওষুধের ইন্ডাস্ট্রি বা ওষুধ তৈরির কারখানা সেভাবে গড়ে ওঠে নি। তবে জোর চেষ্টা চলছে। ভালো করে গড়ে উঠতে আরও বহুদিন বাকি আছে। হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন এই দেশ থেকে ওষুধ বাইরে চালান যাবে। তবে ততদিন আবদুর রহমান বেঁচে থাকবে কি না কে জানে!
বর্তমানে অবস্থা এই যে প্রায় সব রকমের ওষুধের জন্যে বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। চেষ্টা করা হচ্ছে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির। বাইরের দুিনয়ার নামকরা ওষুধ কোম্পানিগুলোও চায় তাদের কাঁচামাল এদেশে বিক্রি করে তাদের ছায়ায় রেখে নতুন কোম্পানি তৈরি করে নতুন নতুন ওষুধ বিক্রি করতে। ততদিন অবশ্য এদেশের মানুষেরা গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যখন এদেশ নিজেদের ওষুধ নিজেরাই তৈরি করতে পারবে বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে ততদিনে আবদুর রহমান রিটায়ার করে যাবে এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বা সেরকম অবস্থা আদৌ এ দেশের হবে কিনা সে বিষয়ে তার মনে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। এখন অবশ্য সে দোকান ব্যবসায়ী সমিতির টেজারার পদে নিযুক্ত হয়েছে। সে চায় নি, সকলে জোর করে করেছে। জীবনে খুব বড় হওয়ার তাগিদ অনুভব করে না আবদুর রহমান। সেরকম কোনো উচ্চাশা তার নেই। আজকাল যে-কোনো সংগঠনে বক্তৃতাবাজি করতে হয়। আবদুর রহমান এসবে বড় নিমরাজি। সে জন্যে সে ইচ্ছে করে টেজারার পদ নিয়েছে। তবে অবশ্যই অর্থশালী হতে চায়। অর্থ, প্রচুর অর্থ তার প্রয়োজন। যদি সংসারে তার সন্তান না-ই আসে, তখন অর্থই হবে তার সন্তান। কারণ সন্তানহীনদের জীবন শেষ বয়সে বড় করুণ হয়। আবদুর রহমান এরকম অবস্থায় কিছুতেই পড়তে চায় না।
১১
‘আমি আগামীকালই আবার আসছি’ এই কথা বলে আবদুল কাদির সেই যে চলে গেল, তো আজও গেল কালও গেল।
এই ঘটনার আগে যা ঘটেছিল সেটা হলো তার ছেলের মৃত্যু।
ছেলের মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে আবদুল কাদির শেষবারের মতো তার দোকানে এসেছিল। সময়টা তখন সন্ধে। মাগরেবের আজান হয়েছে মাত্র। আবদুর রহমান দোকানের পেছনে নামাজের পাটিতে তখনো দাঁড়ায় নি। সাধারণত মসজিদে গিয়ে সে নামাজ পড়ে । কিন্তু সেদিন দোকানে কোনো কর্মচারী ছিল না বলে তাকে দোকানেই থাকতে হয়েছিল।
সেদিন আবার সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্যে কামরাঙ্গীরচর থেকে কোনো কর্মচারী আসে নি। তসির মিয়াও দেশে গিয়েছিল। আষাঢ় আসার আগে আগে প্রকৃতির ভেতরে যেমন এক বিষণ্ন ভাব জাগে, তেমনি ছিল আবহাওয়া। আবদুর রহমান সেদিনও বাড়ি ফেরে নি দুপুরের খাবার খেতে। দোকানে খেয়ে দোকানেই সে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে উঠেছিল। অবশ্য তার আগে দোকানের শাটার টেনে দিয়েছিল।
দুপুরে সাধারণত সে ঘুমোয় না। কিন্তু সেদিন ঘুমিয়েছিল বলে ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরে একটা অলসতা জড়িয়ে ছিল কলার মোচার পরতের মতো।
সেদিন সন্ধেও নেমেছিল যেন ধীরপায়ে।
একসময় সন্ধের ছোপ গাঢ় হয়ে এল।
আর তখনই আবদুল কাদির দোকানে এসে হাজির।
বন্ধুর চেহারা দেখে সেদিন আঁতকে উঠেছিল আবদুর রহমান।
এ কী চেহারা!
গাল তোবড়ানো। দু চোখ কোটরে বসা। শার্টের ভেতর দিয়ে কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে আছে। রুক্ষ চুলে পাকার ছোপ বড় ঘন হয়ে বসেছে। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে যেন আবদুল কাদিরের বয়স দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।
আবদুর রহমানের গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরোল, একী, কাদির তুমি?
আবদুল কাদির অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠে বলল, হ্যাঁ, দোস্ত, ছেলেটি আমার মারা গেছে!
তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল আবদুর রহমান। যেন যত যাই হোক না কেন, ছেলেটির মৃত্যু যে হবে না এ বিষয়ে যেন আবদুর রহমান নিশ্চিন্তই ছিল। নইলে ছেলেবেলায় কোন শিশুর না পেটের ঝামেলা থাকে!
কোনোরকমে আবদুর রহমান বলল, বলো কী । কবে?
উত্তর দেওয়ার আগে আবদুল কাদির দোকানের একটি মাত্র চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসল।
তারপর বলল, একটা সিগ্রেট দাও।
আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। ধরিয়ে আপনমনে অনেকক্ষণ ধরে টানল আবদুল কাদির। টানতে টানতে ঝোলানো পা দুটি দোলাতে লাগল এদিক-ওদিক। যেন পা নয়, ঘড়ির পেন্ডুলাম।
একটু পরে সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে সেই পকেট থেকে একটা খালি ইনজেকশনের অ্যামপুল বের করে বলল, শালার ডাক্তারের নামে মামলা করব, আমি তোমার সাথে পরামর্শ করবো বলে এসেছি। এই ইনজেকশনটা দেওয়ার কিছুক্ষণের ভেতরেই ছেলেটি আমার মারা যায়। এই দেখো।
বন্ধুর হাত থেকে অ্যামপুলটা নিয়ে মনে মনে চমকে উঠল আবদুর রহমান। এই সেই কোরামিন। কিছুদিন আগে এই ইনজেকশন তার দোকান থেকেই সাপ্লাই নিয়েছে ছোট কিছু দোকানদার। লক্ষ্মীবাজার ফার্মেসি এবং নারিন্দার ফার্মেসিতে কিছু অ্যামপুল এখান থেকে গেছে। ইনজেকশনগুলোর এক্সপায়ারি ডেট ছিল ছ’মাস আগের। তবে সেটা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। কারণ সেই ডেট সে পাল্টে নতুন করে ডেট বসিয়ে দিয়েছিল। সে জানত বিদেশি ওষুধের এক্সপায়ারি ডেট যা লেখা থাকে তার চেয়েও আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের মানুষের রোগবালাই-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা পশ্চিমা দেশের চেয়ে অনেক বেশি। তা না হলে এতদিনে এইসব দেশের মানুষ মরে সাফ হয়ে যেত!
অ্যাম্পুলটার দিকে চোখ পড়তে মনে মনে চমকে উঠল আবদুর রহমান।
এগুলো সবই কে. এস সোবহানের সাপ্লাই করা অ্যামপুল। কিছুদিন আগে কোরামিন ইনজেকশন বাজারে ছিল না। আবদুর রহমানই মওকা বুঝে বাজারে ছেড়েছে। তার মানে কি কে.এস. সোবহান তাকে ঠকিয়েছে? অনেক আগে এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাওয়া ইনজেকশন সে নিজেই কারসাজি করে মিথ্যে বলে বিক্রি করেছে আবদুর রহমানের কাছে? আর আবদুর রহমান না জেনে সেখানে আবার নতুন করে তারিখ বসিয়েছে? হয়তো একবছর আগেই এই ইনজেকশনগুলো তাদের কার্যক্ষমতা হারিয়েছে।
আরে, কী সর্বনাশ!
অ্যাম্পুলটার দিকে তাকিয়ে আবদুর রহমান কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।
কিন্তু এখন তাল হারালে চলবে না। মাথা রাখতে হবে ঠান্ডা।
সে এখন বন্ধুর হাত ধরে বলে উঠল, এ তুমি কী বলছো, দোস্ত?
সত্যিই বলছি। আবদুল কাদির পা নাড়াতে নাড়াতে বলল।
দেখি, এবার অ্যাম্পুলটা ভালো করে দেখি। আমার হাতে দাও।
একথা বলে অ্যাম্পুলটা আবদুল কাদিরের হাত থেকে নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে সে বলল, এ তো দেখি লাইফ সেভিং কোরামিন। নাঃ, ইনজেকশন তো ভালোই দেখছি। । ছোট বাচ্চাদেরও দেওয়া হয়। তবে অল্প ডোজে। কেন, আমার ভায়রার বাচ্চাটিকেও তো সেদিন এই ইনজেকশন দেওয়া হলো। না, না, এ তোমার ভুল ধারণা ভাই। ডাক্তার তো ঠিক চিকিৎসাই করেছে।
তুমি বলছ তাহলে?
ঘন ভুরুর জঙ্গল কপালের ওপরে তুলে আবদুল কাদির বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।
দেখে প্রাণ কেঁপে উঠল আবদুর রহমানের।
মনে মনে ভাবল কে. এস. সোবহান এবার তার ওপরেই বাটপাড়ি করেছে। এবং বোকা আবদুর রহমান না বুঝে তার ফাঁদে পা দিয়েছে। কিংবা কে জানে হয়তো সোবহান কিছুই করে নি, ছয় মাসের বেশি হয়ে যাওয়ায় ইনজেকশনের গুণাগুণ এমনিতেই কমে এসেছিল বা সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অথচ এত বছর ধরে সে এরকম কাজ মাঝে মাঝেই করেছে, কিন্তু কোনোদিন তো এমন হয় নি।
পুরো ব্যাপারটা আবদুর রহমানের কাছে যেন রহস্য বলে মনে হতে লাগল। এখন আবদুল কাদির ডাক্তার নিয়ে, প্রেসক্রিপশন নিয়ে যত টানাটানি করবে, খবরের কাগজঅলাদের একবার নজরে পড়ে গেলে কতদূর তা গড়াবে কে জানে! হয়তো তখন অন্য অ্যাম্পুলগুলোর খোঁজ পড়বে। মহাখালীর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। এই ওষুধের সাপ্লাইয়ার বর্তমানে তারই দোকান। শেষে কান টানতে মাথা আসবে। দেখা যাবে ওষুধের গুণাগুণ শেষ অথচ বাজারে স্বাভাবিকভাবে বিক্রি হচ্ছে।
ভুলে গেলে চলবে না আবদুল কাদির নিজেই এককালে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করত।
আর দেশ স্বাধীনের পর দেশে আর যা কিছুর ঘাটতি থাকুক, সাংবাদিকদের কোনো ঘাটতি নেই, এ কথা দেশের শত্রুও বলবে!
কথাগুলো চিন্তা করে আবদুর রহমানের মাথার ভেতরে কেমন যেন করে উঠল। বিপদ তো এই ভাবেই আসে, নাকি? ভাবল সে। বন্ধুর হাত ধরে দোকানের পেছনে এনে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ভাই।
কেন? আবদুল কাদির অন্যমনস্ক হয়ে বলল।
বিপদের দিনে তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।
করুণ মুখে বলে উঠল আবদুর রহমান।
না, না, তুমি যথেষ্ট করেছ। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠল আবদুল কাদির। তুমি টাকা না দিলে ছেলেটার চিকিৎসা করাতাম কীভাবে? তাকে আঙুর কিনে দিতাম কীভাবে? জানো, আঙুর খেতে সে বড় ভালোবাসত, ভাই। যদি বিনা চিকিৎসায়, বিনা খাদ্যে মারা যেত, তাহলে কীভাবে নিজেদের সান্ত্বনা দিতাম বলো তো? আমার বেলায় অন্তত—না, দোস্ত আমি ডাক্তারের নামে থানায় কমপ্লেইন দেব, জেনে রাখো। মামলাও করব।
কথা বলার সময় হঠাৎ করে আবদুল কাদিরের গালের মাংস থির থির করে উঠল। কোনো ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে মানুষের যেমন হয়।
অবস্থা দেখে আবদুর রহমানের বুকের ভেতরটা অজানা শঙ্কায় কেমন করে উঠল। তার মনে হলো ব্যাপারটা নিয়ে আবদুল কাদির একটা হেস্তনেস্ত করবেই করবে।
সে হঠাৎ করে আবদুর কাদিরের হাত ধরে বলল, এসো, আগে চা খাই। চা খাওয়ার পরে আমার স্ত্রীর এক আছে, তার কাছে নিয়ে যাই, চলো।
কেন, পীরের কাছে যাব কেন? বন্ধুর কথা শুনে যেন বিস্মিত হয়েছে এমনি ভাবে বলে উঠল সে।
আবদুর রহমান একটা ঢোঁক গিলে বলল, এমনি। সেখানে গেলে মনে শান্তি আসে। আমি তো প্রায়ই যাই।
আমার মনে যে শান্তি নেই, কে তোমাকে একথা বলল?
আবদুর রহমান বিমর্ষমুখে দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে বলল, কেউ বলে নি। তবে তোমার খোকাটা অকালে চলে গেল তো!
আবদুল কাদির একথা শোনার পর পা নাচানো থামিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, দোস্ত, আমি আত্মহত্যা করব! আমার বউ আজ পুত্র শোকে পাগল হয়ে গেছে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা । কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বা কোনো মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সার্টিফিকেট নিই নি। নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করি নি। দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছি, এটা তো দেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। দরকার যদি হয় আবারও যুদ্ধ করব, কিংবা আমার করার সাধ্য না থাকলে আমাদের সন্তানেরা করবে। কিন্তু সেই সন্তান যদি এমনভাবে মারা যায় তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনে, ভাই।
আবদুল কাদিরের সঙ্গে সঙ্গে আবদুর রহমানও চোখ মুছলো। বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। না, সে নিজে মুক্তিযুদ্ধ করে নি বটে, তবে দেশের ভেতরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে নি একথা কেউ বলতে পারবে না। গোপনে ওষুধ দিয়ে সে অনেক মানুষকে সাহায্য করেছে। ওষুধের দোকান তখনো ছিল। তখন ছিল তার বাবার। বাবা মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। দোকানে সেভাবে বসতে পারত না। হয়তো নয় মাসের যুদ্ধের ধাক্কা তার নাজুক হার্ট সহ্য করতে পারে নি। তখন সে দোকান আবদুর রহমানই দেখত। অনেকবছর ধরে দেখত। তারপর ঢাকায় চলে এল সে। এখন আবদুর রহমানের নিজের ওষুধের দোকান। বাবার ওষুধের দোকানটা দেশে তার ছোটভাইয়ের হাতে ছেড়ে এসেছে। সেখানকার আয় থেকে দেশের খরচ চলে। আর তার মেজভাইকে দিয়ে নারায়ণগঞ্জে একটা ট্যানারির ব্যবসা খুলেছে। সে তার পরিবার নিয়ে নারায়ণগঞ্জেই থাকে।
কিছুদিন পরে ঢাকার দোকানটা একটু জমে উঠলে সে দেশ থেকে তার সংসার গুটিয়ে নিয়ে রাজধানীতে চলে এসেছে। কারণ সে জানে, স্বাধীনতার পর ঢাকা আর সেরকম থাকবে না। তা ছাড়া রেহানার বাচ্চাকাচ্চা হয় না, তার জন্যে ভালো ডাক্তার এবং ভালো চিকিৎসার প্রয়োজনটাও মনের ভেতরে অবশ্যই ঘুরপাক খেয়েছে।
আবদুর রহমান ভাবতে লাগল। এইসব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে এটাও ভাবল যে দোকান থেকে ইনজেকশনের অ্যামপুলগুলো সব সরিয়ে ফেলতে হবে। ওষুধ নিয়ে আজকাল প্রায় স্ক্যান্ডাল হচ্ছে। বাচ্চাদের খাওয়ার অ্যাসপিরিনের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে বিষ। অনেক বাচ্চা জ্বরের সময় অ্যাসপিরিন খেয়েই মারা যাচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের ভেতরে নকলের ছড়াছড়ি। মানুষজন ঠাট্টা করে, কোষ্ঠকাঠিন্য যদি না সারে ভাই, তাইলে অ্যান্টিবায়োটিক কিইন্যা খাও, ভালো জোলাপের কাজ করে। একদিনেই প্যাট এক্কেরে সাফ! এইসব নিয়ে কাগজে কত লেখালেখি।
বন্ধুর সহানুভূতি পেয়ে আবদুল কাদির চোখ মুছে বলল, জীবনটা অর্থহীন হয়ে গেল, দোস্ত।
আবদুর রহমানের তো কোনো সন্তান সেই, কোনোদিন হবে বলে সে আর বিশ্বাসও করে না। তবু সে মাথা নেড়ে বলল, জানি।
আবদুল কাদির বলল, সন্তান হারানো যে বাবা-মায়ের জন্যে কী এক শাস্তি, একমাত্র তারাই বুঝবে যারা হারিয়েছে।
আবদুর রহমান মুখ কালো করে বলল, জানি, দোস্ত।
ছেলেটি আমার খুব বুদ্ধিমান ছিল, খুব ভালো ছিল, জানো দোস্ত, মৃত্যুর আগ পর্যন্তও হাসিখুশি ছিল, শুধু ওর মাকে ভালো রাখার জন্যে।
আবদুর রহমান ঢোঁক গিলে বলল, জানি, দোস্ত!
খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিল, বেশি বায়না ধরত না। সামান্য প্লাস্টিকের খেলনা পেলেই খুশি হয়ে যেত।
তাই, না? আবদুর রহমান একথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলে উঠল। তার এখন খুব খারাপ লাগছে। আবদুল কাদির বলে চলল, স্কুলে যাবার জন্যে বায়না ধরত, অথচ মোটে চার বছর ছিল বয়স। ওর মা ওকে প্লে-গ্রুপে ভর্তি করার জন্যে চেষ্টা করছিল।
খুব ভালো ছেলে তো! আবদুর রহমান বলল।
হ্যাঁ, দোস্ত, খুব ভালো ছেলে ছিল।
এবার কথা শেষ করে হা হা করে হেসে উঠল আবদুল কাদির। হাসতে হাসতে বলল, সন্তান হারালে বাবা-মায়ের হৃৎপিণ্ডের ভেতরে কী হয়, জানো? না, জানো না। তার ভেতরে আর রক্ত থাকে না। থাকে শুধু পানি। চোখের নোনতা পানি!
কথা শেষ করে আরও খানিকটা সে হাসল। তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা, এখন যাই, আমি আগামীকালই আবার আসছি।
তারপর একটা লাফ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।
পড়ে থাকল দোকান থেকে কিনে আনা কেতলি ভরা ধূমায়িত চা।
আবদুর রহমান তাকে বাধা দেওয়ারও সময় পেল না। এ কথাও বলতে পারল না যে তোমাকে দেনার টাকাটা আর শোধ করতে হবে না, দোস্ত। তোমার ছেলে তো আমার ছেলেও বটে।
১২
ইদানীং দোকানে বসলেই আবদুর রহমান তার বন্ধুর কথা মনে করে। আর যত মনে করে তত তার মনের ভেতরে কীরকম যেন এক অস্বস্তি হয়। মনে হয় মানুষটার খোঁজ নেওয়া দরকার। সেই যে ছেলের অসুখের সময় সে বেশ ক’দিন খুব দৌড়াদৌড়ি করেছিল, তারপর থেকে হঠাৎ করে যেন সব চুপ। এমনই চুপ যেন মনে হয় এই রাজধানীতে আবদুল কাদির বলে কোনো মানুষ নেই। কোনোদিন ছিল না। মুশকিল যে আবদুল কাদিরের বাসায় কোনো টেলিফোন নেই। সুতরাং তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অত সহজে হওয়ার নয়। আজকাল মানুষের বাড়িতে টেলিফোন লাইন নেওয়া বড় ঝামেলার। একগাদা ঘুষ-ঘাস না দিলে কোনো লাইন পাওয়া যায় না। অনেক তদ্বির-তাগাদার পর তবে লাইন পাওয়া যায়।
সেদিন তো একটা তাজ্জব খবর ছাপা হলো খবরের কাগজে। একজন রিটায়ার্ড মানুষের সারা জীবনের শখ বাড়িতে একটা প্রাইভেট টেলিফোন নেওয়া। টিএনটির কাছে দরখাস্ত করে মাসের পর মাস ভদ্রলোক অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু টেলিফোন কানেকশন মিলল না। অনেক ধরাধরি করেও কানেকশন পেলেন না। তার এই অপারগতা স্ত্রীর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। তিনি স্বামীর পরে রাগ করে বসে থাকলেন। পরে ভদ্রলোক খবর পেলেন কিছু ঘুষ দিলে কানেকশন পাওয়া যাবে। কিন্তু ভদ্রলোক ছাপোষা মানুষ। তার পক্ষে ঘুষ দিয়ে টেলিফোন বাড়িতে আনা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।
এরপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। কিছুদিন বাদে ভদ্রলোক অসুখে মারা গেলেন। যেদিন মারা গেলেন সেদিন দুপুরে টিএনটি থেকে লোক গেল বাড়িতে টেলিফোন কানেকশন দিতে। কিন্তু সেদিন বাড়ির লোকজন মুর্দা গোসল করতে ব্যস্ত। তারপর তাকে কবর দিতে দেশের বাড়িতে নিতে হবে।
ভদ্রলোকের ছেলে রাগ করে টিএনটির কর্মচারীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।
খবরটা একটা দৈনিকে পড়েছিল আবদুর রহমান। সেকথা এখন দোকানে বসে মনে পড়ল তার। মনে পড়ে সে সিদ্ধান্ত নিল নিজেই একদিন আবদুল কাদির যে অফিসে চাকরি করে সেখানে খোঁজ লাগাবে।
অনেক খুঁজে পেতে সে একদিন দোকানে বসে তার নোটবুক খুলে আবদুল কাদিরের অফিসের টেলিফোন নম্বর বের করল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর একজনকে পাওয়া গেল। প্রথমে সে তো আবদুল কাদিরকে চিনতেই পারে না। পরে ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে খবর দিল বিগত তিন মাস ধরে সে আর এই অফিসে যায় না।
চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কি না, তাও সে বলতে পারে না। এসব ওপরের তলার ব্যাপার।
খবরটা জানতে পেরে বন্ধুর জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করলেও এটুকু বুঝল যে ঘটনাটা বেশি দূর গড়ায় নি। যদি গড়াত তাহলে এতদিন সবকিছু এরকম নীরব থাকত না। আবদুর রহমান এটাও জানত যে মানুষের নিকটজন কেউ হঠাৎ মারা গেলে আত্মীয়স্বজনেরা ডাক্তারের ওপরে মারমুখী হয়ে ওঠে। স্বজন হারানোর বেদনা তো সহ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু মানুষের হঠাৎ মৃত্যুর পেছনে ডাক্তার বা ওষুধ ছাড়া যে আরও কিছু কারণ থাকতে পারে এটা সে সময় হয়তো ভাবতে পারে না।
আবদুর রহমানের একটু ক্ষোভ হলো মেডিসিন রিপ্রেজেনটেটিভ কে.এস.সোবহানের প্রতি। ছেলেটা, ছেলেই তো বটে, এখনো তিরিশ পেরোই নি, এমনিতে এত ভদ্র, বিনীত, নিচুস্বরে কথা বলে, টিপি টিপি পায়ে হাঁটে, অথচ শয়তানের হাড্ডি। সেদিন থার্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক যতগুলো সাপ্লাই দিয়েছে, সবগুলোর এক্সপায়ারি ডেট সে নিজেই পাল্টে দিয়েছে তাকে বিক্রি করার আগে।
আবদুর রহমানকে এই খবরটা পর্যন্ত সে জানায় নি। ভাগ্যিস এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে নি।
প্রশ্ন তুলতে তুলতেই সব ইনজেকশন বাজারে বিক্রি হয়ে রোগীর শরীরে চলে যাবে।
তখন আর কে খোঁজ রাখে!
কে. এস . সোবহানের কথা যত ভাবতে লাগল, ততই আবদুর রহমানের মনের ভেতরে অশান্তি হতে লাগল। তার মনে হলো এই লোকটা তার বাড়িতেই মনে হয় নকলের কারখানা বসিয়ে ফেলেছে।
কথাটা ভেবে নিজের ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করে আবদুর রহমান। একবার তার মনে হয় আবদুল কাদিরের ছেলের মৃত্যুর পেছনে কোরামিনের কোনো দোষ নেই । সেটা এই হিসেবে যে ইনজেকশনের কোনো কার্যকারিতাই ছিল না। পানি ইনজেকশন দেওয়া যা, এটাও ছিল ঠিক তাই। আবার ভাবে, মৃত্যু মুহূর্তে কোরামিন কোনো কাজ করতে পারে নি কারণ ওষুধের কার্যকারিতা ছিল না। যদি থাকত তাহলে হয়তো বাচ্চাটাকে সে মুহূর্তে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হতো।
হ্যাঁ, সম্ভব হতো।
হায়, প্রকারন্তরে ছেলেটিকে তো হত্যাই করা হলো!
কথাগুলো ভেবে আবদুর রহমানের বুকের ভেতরে কেমন হাঁকুপাঁকু শুরু হলো। কী রকম যেন এক অস্বস্তি। তার সঙ্গে কেমন একটা আশঙ্কা। যা সে কাউকে মুখ খুলে বলতে পারছে না এ মুহূর্তে। রেহানাকে তো নয়ই।
আবদুর রহমান ইতিমধ্যে অবশ্য পুরোনো ঢাকার দোকানগুলো থেকে তার সাপ্লাই করা ইনজেকশনগুলো ফিরিয়ে এনেছে। টাকাও ফেরত দিয়ে এসেছে কর্মচারী পাঠিয়ে। তবু তার মনে কেন যেন শান্তি আসছে না। বন্ধু আবদুর রহমানকে সে চেনে, একটু ইমোশনাল বটে। তবে অবুঝ নয়। মুখে যত যাই বলুক, ডাক্তারের নামে সে মামলা করবে না। মামলা যে করবে তার তহবিল কোথায়? মামলা করা কি মুখের কথা? আর মামলা করলেও সে কিছুতে প্রমাণ করতে পারবে না যে ডাক্তারের গাফিলতির জন্যে বা ইনজেকশনে কাজ না হওয়ার জন্যে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে
কথাটা ভাবতে গিয়ে আবদুর রহমানের মনের ভেতরে কেমন যেন একটা আক্রোশমিশ্রিত ক্ষোভের জন্ম হলো। মানুষের বিচিত্র মন। নইলে কেন তার মনে এরকম হবে? আক্রোশ বন্ধু আবদুর রহমানের প্রতি। কেন সে মামলা করার স্পর্ধা দেখাবে? আর ক্ষোভ কে. এস. সোবহানের প্রতি। কেন সে এবার তাকে এভাবে ফাঁকি দিল? লাইফ সেভিং ইনজেকশন নিয়ে কেন সে ছেলেখেলা করল?
তাহলে কি এই বাংলাদেশে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই? নয় মাসের স্বাধীনতার ধ্বংসযজ্ঞের পর মানুষের জীবনও কি মূল্যহীন হয়ে গেছে। যেন তিরিশ লাখ যদি মরতে পারে তাহলে আরও কিছু মরলে ক্ষতি কি!
কিন্তু এহ বাহ্য। এখন মৃত্যু সমস্যা নয়, যে মরার সে তো মরেই গেছে। এখন জীবিত যারা, তাদের নিয়ে সমস্যা। আবদুর রহমান এখন মনে মনে এই যুক্তিও খাড়া করতে লাগল যে আবদুল কাদির কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না যে তার সাপ্লাই দেওয়া ইনজেকশনের কারণে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। প্রথম কথা ছেলেটির অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিল। কোনোকিছু পেটে রাখতে পারত না। বমি হয়ে যেত। একজন নয়, দু-তিনজন ডাক্তার ছেলেটিকে দেখেছে। তাদের ভেতরে একজন ডাক্তার ছিল পিজির স্পেশালিস্ট। একথা ঠিক যে ইনজেকশন দেওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়েছে, তা সে যে-কোনো কারণেই হতে পারে। ইনজেকশনের ডোজ বেশি হতে পারে যদি তার পোটেন্সি বজায় থাকে, অর্থাৎ কার্যকারিতা বজায় থাকে। অথবা ছেলেটার শরীর রোগে ভুগে ভুগে এতই কাহিল হয়ে গিয়েছিল যে সামান্য ডোজও তার সহ্য হয় নি। অথবা এই ইনজেকশনই কাজে লাগতে পারত, যদি তার পোটেন্সি না হারাত।
এতসব চিন্তাভাবনা আবদুর রহমানের মাথার ভেতরে যতই ঘুরপাক খেতে লাগল তত তার মনে অশান্তি হতে শুরু করল। সামান্য একটা সরল চিন্তা যেন ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠতে লাগল। ইনজেকশনের পোটেন্সির অভাবে হয় ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে অথবা এমনিতেই তার শেষ সময় এসে গিয়েছিল, যখন কেউ আর কিছু করতে পারে না, এই সোজা চিন্তাটা যেন আর সরল পথে প্রবাহিত হতে পারছে না, বারবারই বেঁকেচুরে যাচ্ছে। লাঠির মাথায় জড়িয়ে রাখা চিটেগুড়ের মিষ্টি তৈরি করতে গেলে যেমন হয়।
অথচ সত্যি বলতে আবদুর রহমান বন্ধু আবদুল কাদিরের ছেলেটাকে জীবনে চোখে দেখে নি। কোনোদিন দেখার সুযোগও হয় নি। সত্য এই যে আবদুর রহমান থাকে কাঁঠাল বাগানে। আর আবদুল কাদির কলুটোলা বা সূত্রাপুর এরকম কোনো জায়গায়। ঘনঘন বাড়ি পাল্টানো আবদুল কাদিরের স্বভাব। বাড়ি ভাড়া যত বাড়ে, তত যেন সে পুরোনো ঢাকার গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবিষ্ট হয়! যত বাড়ি ভাড়া বেশি, তত আবদুল কাদিরের ঘন জনবসতির ভেতরে সেঁদিয়ে যাওয়া। এসব কিছু কিছু জানত আবদুর রহমান।
তবে সুখবর যে খালি অ্যাম্পুলটা আবদুল কাদির আর ফেরত চায় নি। হয়তো সেদিন আবেগতাড়িত ছিল বলে ফেরত নিতে মনে ছিল না। আবদুর রহমানের হাতেই সেটা রয়ে গেছে।
অলংকরণ: আরিফুল ইসলাম
অন্যদিন ঈদসংখ্যা ২০১৮-এ প্রকাশিত আনোয়ারা সৈয়দ হক-এর ফিরে যাবার পথ অনিশ্চিত উপন্যাসের অংশবিশেষ।
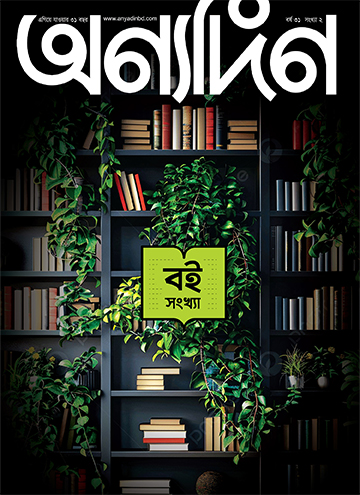









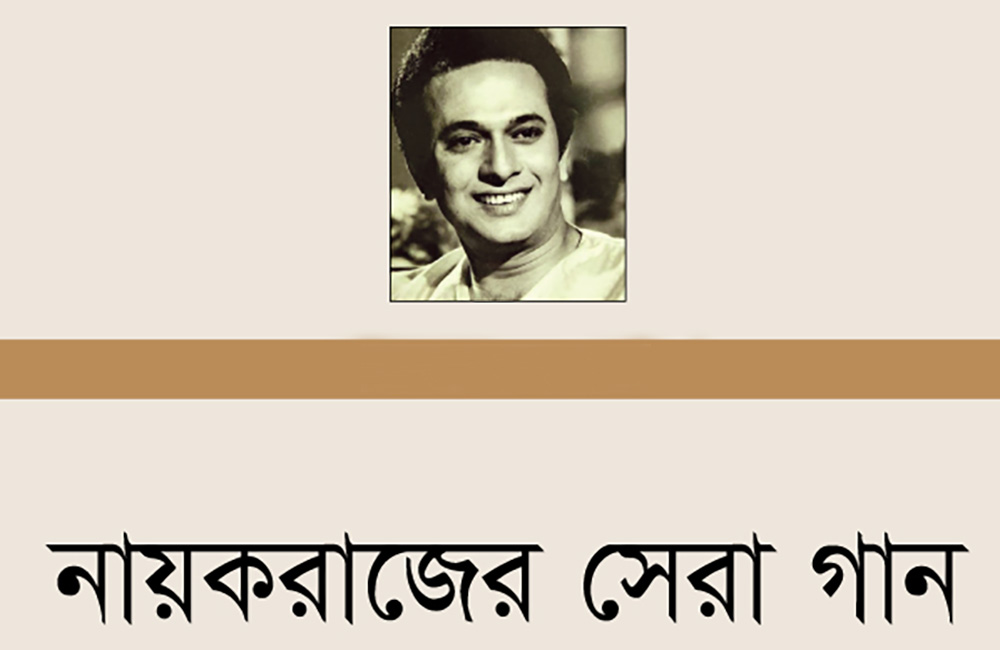




Leave a Reply
Your identity will not be published.