কথাটা উঠেছিল প্রসঙ্গক্রমেই, যেমনটা প্রায়ই ওঠে। দুর্নীতিতে তো ছেয়ে গেছে দেশ; কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হলো সবাই সেটাকে মেনে নিয়েছে। আগের দিনে এমনটা ছিল না। পাকিস্তান হওয়ার পরপরই চেক জালিয়াতি করেছিলেন আমাদের জানাশোনা একজন। সেই টাকা তিনি ব্যবসাতে খাটিয়েছেন, ঢাকা শহরের একটি সিনেমা হলের অর্ধেকটার মালিক পর্যন্ত হয়ে গেছেন; তাঁর সেই হলে আমরা সিনেমা দেখেছি, কিন্তু মালিক যে আমাদের চেনা তা নিয়ে বড়াই করি নি।
তা শেষ পর্যন্ত তিনি ধরাও পড়েছেন, জেলটেল কিছু একটা হয়েছিল বলে শুনেছি; ধরা না পড়লেও সামাজিক স্বীকৃতি যে পান নি সেটা মনে আছে। এখন কে কার পরোয়া করে! দুর্নীতিবাজকে সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রশ্নই ওঠে না, তাদের কাছ থেকে ডাক এলে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।
তবে ‘না বলুন’, ‘না বলুন’ তো চলছে। জঙ্গিবাদকে আমরা ‘না’ বলছি। ধূমপানকে ‘না’ বলার আন্দোলন চলমান রয়েছে। বাল্যবিবাহকে ‘না’ জানিয়ে কিশোরী মেয়েরা মানববন্ধন করছে। রাজনীতিকে ‘না’ বলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যানার টানায়। ঘুষকে ‘না’ বলুন আওয়াজ দিয়ে মিছিল হয়। এমনকি দুর্নীতিকে ‘না’ বলার আওয়াজও ওঠে। অন্তর্যামী যে, আসল কর্তা, এসবে তার তেমন একটা আসে যায় না; সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আগের মতোই রয়ে যায়; ধাক্কা-টাক্কা খেয়ে বরঞ্চ আরও সতর্ক ও কৌশলী হয়ে ওঠে; ঘুষ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, মুনাফার প্রলোভন তুলে ধরে, মিডিয়ার সাহায্যে, আত্মগুণ প্রচার করে সে কায়েমি থাকার বন্দোবস্তকে পোক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।
বোঝাই যাচ্ছে মূল ব্যবস্থাকে ‘না’ বলা প্রয়োজন। কিন্তু কাজটা করবে কারা? মূলধারার রাজনীতিকেরা সেটা করে না, তাঁদের তাল ব্যবস্থাটাকে চালু রেখে তার থেকে সুবিধা সংগ্রহ করে নেওয়ার। বামপন্থীরা করে, কিন্তু তাঁদের তেমন জোর দেখা যায় না। কাজটা বিশেষভাবে করবার কথা বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা করেন, আবার করেনও না। সবকিছুর ভেতর দিয়ে সুবিধা যেটুকু হওয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থারই হয়। ভীষণ অসুবিধা সাধারণ মানুষের।
অমান্য করার কাজটা বুদ্ধিজীবীরা কেন করেন, কতটা করেন এবং কেন করতে পারেন না বর্তমান আলোচনার খানিকটা সে-বিষয়টা নিয়েই। আমরা ইতিহাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত নেব, বিশেষভাবে বিবেচনায় থাকবে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের বিষয়।
বুদ্ধিজীবী কারা সে প্রশ্নও অবশ্য থাকে। বাংলাতে যে আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে একত্র করে বিদ্যাবুদ্ধি বলি, বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিজীবী হয় নিজেদের ওই বিদ্যাবুদ্ধির কারণেই। তাঁদের বিদ্যা থাকে, থাকতেই হবে, নইলে বুদ্ধিজীবী কীভাবে? বিদ্যা গ্রন্থপাঠ থেকে আসে; আসে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও। এই বিদ্যারই অপর নাম জ্ঞান। কিন্তু কেবল বিদ্যাই যে মানুষকে বুদ্ধিজীবী করে তা নয়। বিদ্বানমাত্রেই বুদ্ধিজীবী নন, যদিও বুদ্ধিজীবীমাত্রেই বিদ্বান। বিদ্বানরা পণ্ডিত হন, দক্ষ হন, পেশাজীবী হন, বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন; কিন্তু এসব হওয়া আর বুদ্ধিজীবী হওয়াটা এক ব্যাপার নয়। বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হলো আরও কিছু করা; আর সেটা হচ্ছে বুদ্ধির প্রয়োগ। বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুটিরই প্রয়োগ থাকা চাই; এই দুই শক্তি একে অপরের পরিপূরক হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কটা দাঁড়ায় দ্বান্দ্বিক। এ ক্ষেত্রে যা প্রত্যাশিত তা হলো বিদ্যা ও বুদ্ধি একটি দ্বন্দ্বে যুক্ত থাকবে; তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়বে, কিন্তু কেউ কাউকে ধ্বংস করবে না, এমনকি তাড়িয়েও দেবে না; লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উভয়ের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
বুদ্ধিজীবীর জন্য বুদ্ধির প্রয়োগটাই প্রধান কাজ হওয়ার কথা। বুদ্ধির সাহায্যে পৃথিবীকে তাঁরা ব্যাখ্যা করবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সেটাই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়। অপরিহার্যরূপে যুক্ত থাকে আরেকটি কাজ, সেটা হলো পৃথিবীটাকে বদলানো। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করা, তার অসম্পূর্ণতাকে মেনে না-নেওয়া, এবং তাকে বদলানো বুদ্ধিজীবীর কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। এসব কাজ একা করা যায় না; বুদ্ধিজীবী সেটা নিজের ভেতর থেকেই জানেন, এবং জানেন বলেই বুদ্ধিজীবী হন। বুদ্ধিজীবী সংগ্রহ করেন, তিনি বিজ্ঞ; কিন্তু যা সংগ্রহ করেন তাকে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনে ও অভিভাবকত্বে নতুন করে তোলেন। ইংরেজি ভাষার কবি-সমালোচক কোলরিজের ভাষ্য ব্যবহার করে বলা চলে তিনি ফ্যানসিফুল নন, তিনি ইমাজেনিটিভ। এবং তিনি হৃদয়বানও। হৃদয়বান না হলে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার, এবং যুক্ত হয়ে পৃথিবীটাকে বদলাবার প্রেরণাটা পাবেন কোথা থেকে? আসলে কোনো বুদ্ধিজীবীই বুদ্ধিজীবী নন, যদি তিনি হৃদয়বান না হন। দ্বন্দ্ব থাকে বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ভেতরও।
একসময় ছিল বুদ্ধিজীবীদের কাজটা যখন দার্শনিকেরাই করতেন। তাঁরা প্রশ্ন করতেন, ব্যাখ্যা করতেন, লক্ষ্য থাকত প্রতিষ্ঠিতকে বদলাবার। দার্শনিকেরা তখন বৈজ্ঞানিকের দায়ভারটাও নিতেন। তারপর বিভাজন এসেছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের অভিন্নতাটা ভেঙে গেছে; বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিশালী হয়েছেন, দার্শনিকেরা কিছুটা পিছু হটেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্নতার এই জায়গাটাতে ডাক পড়েছে বুদ্ধিজীবীর; তাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক, কিন্তু বিশেষজ্ঞ নন, এবং তাঁরা প্রশ্ন করেন। সেটা ভাববিলাসের জন্য নয়, দার্শনিকভাবে বুঝবার ও বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে বদলাবার জন্য। যেমন ধরা যাক ফ্রান্সিস বেকনের কথা। তাঁর একটা দার্শনিক অবস্থান ছিল, সেটি ইহজাগতিকতার। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। জ্ঞানকেই তিনি ক্ষমতা বলে জেনেছেন, তবে সে জ্ঞানটা মানুষের জন্য উপকারী হওয়া চাই। অর্জিত বিদ্যা, সক্রিয় বুদ্ধি ও পরোপকারী হৃদয়—এই তিনকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছেন তিনি।
পরের কালে অত্যন্ত বড় মাপের একজন বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন কার্ল মার্কস। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মার্কস দর্শনের ছাত্র ছিলেন। পিএইচডি’র জন্য অভিসন্দর্ভ লিখেছেন প্রাচীন গ্রীক দর্শন বিষয়ে; পেশাগত জীবন শুরুও করেছিলেন দর্শনের অধ্যাপক হিসেবেই, কিন্তু সেখানে থাকেন নি। পেশাজীবী হলেন না, বিশেষজ্ঞ রইলেন না; নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করলেন দর্শনচর্চার সঙ্গে। এবং পৃথিবীটাকে শুধু বুঝলে চলবে না, তাকে বদলানোও চাই, এই সিদ্ধান্তের তাড়নায় ভূমিকা গ্রহণ করলেন বিপ্লবীর। বিদ্যা ও বুদ্ধি সঙ্গে থাকল। থাকল হৃদয়। এবং পৃথিবীকে বদলাবার উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে সংযুক্ত করে ফেললেন যেমনভাবে তাঁর আগে অন্য কোনো বুদ্ধিজীবী করেছেন কি না সন্দেহ। ধর্মপ্রচারকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের অবস্থান ও কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। অগ্রবর্তী ফ্রান্সিস বেকন কাজ করেছিলেন পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠাদানের ব্যাপারে, পরবর্তী কার্ল মার্কস নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন পুঁজিবাদকে সরিয়ে দিয়ে ইতিহাসের অগ্রযাত্রার পথকে বন্ধনমুক্ত করাটাকে। তাঁর দায়িত্বটা ছিল অনেক বড়, বেকনের দায়িত্বের তুলনায়।
বস্তুগত পরিস্থিতিটা বেকনের জন্য অনুকূলে ছিল, মার্কসের জন্য ছিল প্রতিকূলে। যে কারণে তিনি নিজের জন্মভূমিতে থাকতে পারেন নি; তাঁকে এদেশে ওদেশে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। এবং তিনি জীবনযাপন করেছেন ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যে। কিন্তু তিনি নত হন নি। বেকনের চেষ্টাটা ছিল পারলৌকিক ঈশ্বরের একাধিপত্য থেকে মানুষকে মুক্ত করার, মানুষকে নিয়ে আসার, ইহজাগতিক পরিসরে। মার্কস চাইছিলেন ইহজাগতিক নতুন ঈশ্বর, নাম যার পুঁজিবাদ, তার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটিকে মানবিক করে তুলবার ব্যাপারে পথ খুঁজতে। বেকন ও মার্কসের ভেতর যোগাযোগের বন্ধনটা পূর্বসূরীর সঙ্গে উত্তরসূরীর ধারাবাহিকতার নয়; সম্পর্কটা দ্বন্দ্বের। মার্কসের নৈতিকতা এবং কাজ দুটোই উঁচুস্তরের—বেকনের তুলনাতে।
২
বাংলা ভাষা ও বঙ্গদেশে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮২০-১৯১১) পেয়েছি। তাঁর দিকে আমরা একটু বিশেষভাবেই তাকাব। কারণ তিনি যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বান ছিলেন, সাগর ছিলেন বিদ্যার, কিন্তু আবার করুণারও। যে জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হলো বিদ্যা, বুদ্ধি ও হৃদয় এই তিনকে একসঙ্গে কাজে লাগানো। অনেক কিছুকেই ‘না’ বলেছেন। যেমন, বিধবা-বিবাহের অপ্রচলনকে এবং বাল্যবিবাহের প্রচলনকে। ‘না’ বলেছেন বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে। শাস্ত্রানুগত্য তাঁর চরিত্রে ছিল না। উচ্চ বেতনের সরকারি চাকরি করতেন, সম্মত হন নি তাতে আটকে থাকতে। অসম্পূর্ণ যে আত্মজীবনচরিতটি তিনি লিখে রেখে গেছেন তাতে নিজের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে অবাধ্যতা। বলেছেন যে তিনি ‘মাঝেমধ্যে অতিশয় অবাধ্য’ হতেন। জন্মসময়ে তাঁর পিতামহ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে সংসারে একটি এঁড়ে বাছুরের আগমন ঘটেছে। বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন যে তাঁর স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা দেখে তাঁর পিতা তাঁকে ‘এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া’ বলতেন। বিদ্যাসাগরের ভাষ্যে, প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে তিনি ব্যক্তিদের নিকট পিতামহের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “ইনি সেই এঁড়ে বাছুর, বাবা পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়ে হইয়া উঠিতেছেন।”
পিতার এই বক্তব্যকে বিদ্যাসাগর নিতান্ত অযথার্থ মনে করেন নি। অবাধ্য না হলে তিনি অন্যকিছু হতেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতেন না।
রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কটা উত্তরসূরী ও পূর্বসূরীর বলা যাবে না, দেখতে তেমনটা মনে হলেও। এঁরা দুইজন দুই ধারার বুদ্ধিজীবী। রামমোহনকে বলা হয় আধুনিক ভারতবর্ষের পিতা; তা তিনি আধুনিক ছিলেন যেমন, তেমনি পিতৃতান্ত্রিকও ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পক্ষপাত মাতার দিকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাষ্ট্রশাসনটা ছিল পিতৃতান্ত্রিক, রামমোহন ওই শাসনকে সমাজের আরও গভীরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ‘উন্নত’ ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক, ব্যবসা বাণিজ্য চলতে থাকুক, তাদের সংশ্রবে সহবতে স্থানীয় সুবিধাভোগীরা উন্নত হোক, রামমোহন এটা চেয়েছেন। মুদ্রণযন্ত্রের যে স্বাধীনতার জন্য তিনি দেনদরবার করেছেন তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা স্থাপনের জন্য। শাসক ইংরেজ শাসিতদের অভাব অভিযোগ জানতে পারবে, ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেবে, ফলে স্টীম বের হয়ে যাবে, এবং বিপ্লব ঘটবে না, পরামর্শ ছিল এটাই। বিপ্লবের পক্ষে নয়, রামমোহন ছিলেন বিপ্লববিরোধী।
৩
পিতার কাছে বিদ্যাসাগরের অনেক ঋণ; বিদ্যাভ্যাস তাঁর হতোই না, পিতা যদি না অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে অসম্ভব রকমের কষ্ট সহ্য করে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন। ওদিকে আবার ‘বাপের বেটা’ যে ছিলেন তাতে সন্দেহ কী। সরকারি চাকরিতে থাকলে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে আরও উচ্চপদে যে যেতে পারতেন, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই; বেতন ভাতা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল; কিন্তু সে-পথে হাঁটলেন না। বাঙালি উপরওয়ালা প্রশ্ন করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে বিদ্যাসাগর খাবে কী? বিদ্যাসাগর জবাব দিয়েছিলেন আলু পটল বেচে খাবে। তা-ই করেছেন। বই লিখেছেন, নিজস্ব ছাপাখানায় সে বই ছেপেছেন, এবং বই বিক্রি করেছেন নিজে দোকান খুলে, ওই সংস্কৃত কলেজের পাশেই, যেখানে তিনি একদা অধ্যক্ষ ছিলেন। বুর্জোয়া বিকাশের ভেতর যে কর্মোদ্দীপনা থাকে বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেটি পুরোমাত্রায় ছিল; বোধ করি উপচে পড়ছিল।
বিদ্যাসাগর যে ইংরেজ শাসনের সরাসরি বিরোধী ছিলেন তা নয়। ছোট ইংরেজকে তিনি তালতলার চটিজুতা দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বড় ইংরেজকে মেনে নিয়েছেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তবে ইংরেজের তাঁবেদারিতে থাকতে চান নি। আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য রামমোহন ইংরেজিকে মাধ্যম করার পক্ষপাতী ছিলেন, বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়েছিলেন মাতৃভাষার পক্ষে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করতেন বাংলা ভাষায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করাকে। ইংরেজির আধিপত্য থেকে বের হয়ে এসে বাংলাকে অবলম্বন করার এই অভিপ্রায়ের মধ্যে উপাদান ছিল সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবিরোধিতার। রামমোহন ছিলেন তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের যাঁরা ভারতীয় মনে করতেন; বিদ্যাসাগরের চেষ্টা কিন্তু ছিল বাঙালি হওয়ার, যে জন্য তিনি জ্ঞানের অর্জনের এবং সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। এককথায়, বিদ্যাসাগর বাঙালিকে বাঙালি হতে সাহায্য করেছেন। আমরা জানি বিধবা বিবাহের পথপ্রদর্শন করাকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা গদ্যকে মুক্তিদান। এই দুই কাজের ভেতর আসলে কোনো বিরোধ ছিল না। উৎস অভিন্ন। সেটা হলো মাতৃপ্রেম। মাতার হৃদয় ছিল বিদ্যাসাগরের।
কর্মোদ্দীপনা রামমোহনের ভেতর কেবল প্রভূত পরিমাণে ছিল না, ছিল তা অসামান্যরূপে; কিন্তু সেটি ছিল বিত্তবানের। জ্ঞানান্বেষণ ও সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি কোম্পানির চাকরি, ব্যবসাতে লগ্নি, জমি কেনা, সুদের কারবার, এসবও তিনি অবহেলা করেন নি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই ব্রাহ্মণ। রামমোহনের জন্ম বিত্তবান ঘরে, উত্তরাধিকারসূত্রে ভূসম্পত্তি পেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের জন্ম অতিদরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে, উত্তরাধিকারসূত্রে বিদ্যাসাগর অন্যকিছু পান নি, পিতা ও মাতার চারিত্রিক গুণ ভিন্ন; বিশেষ করে মাতার। তাঁর বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনেক পার্থক্য; কিন্তু মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে যেমন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন, অন্য অনেকেই তেমনটা পান নি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে মধুসূদন মাতার হৃদয় দেখেছিলেন। বড়ই সত্য সে-দেখাটা। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্পর্কটা খুব একটা ভালো ছিল না, অপরদিকে বিদ্যাসাগর সর্বসময়ে মায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মায়ের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে তিনি পরিচালিত হতেন। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের কাজটা পিতার মতো; অপর দিকে বিধবা নারী এবং বহুবিবাহের ও বাল্যবিবাহের শিকার কন্যা—এদের যে যন্ত্রণা বিদ্যাসাগর তা বিশেষভাবে জানতেন, নিজের মা ভগবতী দেবী ও মাতৃসমা রাইমণির মাধ্যমে। রাইমণি একটি পুত্রসন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন; কলকাতায় যে বাসাতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর পিতা ঠাকুরদাস আশ্রয় পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন সে-বাড়ির কন্যা। আত্মজীবনীতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, ‘রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত দ্বিতীয় দেখি নাই।’ রাইমণির স্মৃতি তাঁর জন্য অশ্রুপাতের কারণ হতো। বিদ্যাসাগর লিখছেন,
আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এসমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দুজনেই স্রোতের বিরুদ্ধে ছিলেন। এখানে মিল আছে এই দুই বুদ্ধিজীবীর ভেতরে। কিন্তু আবার পার্থক্যও আছে। মিলের জায়গাটা এখানেও যে দুজনেই ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মেনে নেওয়ার ব্যাপারেও ভিন্নতাটা লক্ষ করবার মতো। রামমোহন যেভাবে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগর তেমনটা দেখান নি। রামমোহনের জন্ম ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চার বছর পরে, কোম্পানির দুঃশাসন-সৃষ্ট সেই মহা বিপর্যয়ে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেছে; সে-ঘটনা কিন্তু তাঁকে বিচলিত করে নি। ইংরেজের আগমনকে তিনি উল্টো ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ ঘটনা মনে করেছেন। কামনা করেছেন ভারতবর্ষ পুরোপুরি ইংরেজের উপনিবেশ হয়ে যাক। কারণ এতে তাঁর ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত সুবিধা। কৃষকের কথা যেটুকু তিনি বলেছেন সেটা জমিদারের দৃষ্টিকোণ থেকেই। নীলচাষের প্রতি তাঁর বিলক্ষণ সমর্থন ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল ইংল্যান্ডের দিকে, শেষ পর্যন্ত সেখানেই গেছেন, এবং দেশে আর ফেরা হয় নি, দেহত্যাগ বিদেশেই ঘটেছে।
ওদিকে ইংরেজ শাসন মেনে নিয়েও বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের দেশেরই মানুষ। বিলেতে যাবেন এমনটা কখনো ভাবেন নি। রামমোহনের জন্ম সিপাহি অভ্যুত্থানের অনেক আগে। ওই অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হলে তিনি যে সিপাহীদের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজের পক্ষে অবস্থান নিতেন তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর ওই অভ্যুত্থানটি সামনাসামনি দেখেছেন। না, সিপাহি অভ্যুত্থানকে তিনি সমর্থন করেন নি। সেটা করা কোনো দিক দিয়েই সম্ভবপর ছিল না। তবে সিপাহিদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই; সংস্কৃত কলেজ ভবন ইংরেজ সৈন্যরা দখলে নিয়ে নিয়েছিল, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যেভাবে সিপাহিদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রƒপ করেছেন, তেমনটা বিদ্যাসাগরের ধাতে ছিল না, রুচিতেও নয়। বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে মাতৃভাষার চর্চা করেছেন। গরীব মানুষের সঙ্গে থেকেছেন। শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ তাঁর ওপরও অবশ্যই ছিল। যেমন কৃষক তাঁর চিন্তায় একেবারেই অনুপস্থিত, অনুপস্থিত মুসলমানরাও। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ যখন মুসলমান তখন তাঁর এই উপেক্ষার ব্যাখ্যা করতে হলে শ্রেণিতে প্রসঙ্গ না এনে উপায় থাকে না। কৃষকদের অধিকাংশই যে মুসলমান ছিল সেই সত্যটাও উপেক্ষণীয় নয়। এটাও জানি আমরা যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় কমিয়ে উচ্চশিক্ষার দিকে নজর দিতে তিনি ইংরেজদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অর্থ এমন হতে পারে যে তিনি নিজের শ্রেণির সুবিধার কথাই ভাবছিলেন, কারণ উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি করলে শহরের মধ্যবিত্তের উপকার হতো। প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি আবার জমিদারদের ওপর নতুন শিক্ষা ট্যাক্স বসানোর সঙ্গে যুক্ত ছিল; সে বিবেচনাও বিদ্যাসাগরের ভেতর কাজ করে থাকবে। তিনি জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন না, পক্ষেই ছিলেন।
কিন্তু শ্রেণিগত ওই সীমার ভেতরও বিদ্যাসাগর যে কেবল বিদ্রোহী নন, প্রায় বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন সেটা মানতেই হবে। তাঁর ঝোঁক পিতৃতান্ত্রিকতার দিকে ছিল না। ইংরেজের শাসন ছিল পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক। অনড়ভাবে। সেই পরিস্থিতিতে মাতৃভাষার পক্ষে দাঁড়ানোও একটা প্রায় বৈপ্লবিক ঘটনা। তিনি ছিলেন সংস্কৃতপণ্ডিত, সেখানে থাকেন নি। তাঁর চারপাশে ছিল ইয়ংবেঙ্গলের ইংরেজিপনা, তিনি সে-পথে যান নি; মাইকেল হওয়া, কিংবা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়া কোনোটাই তাঁর পক্ষে কিন্তু সম্ভব ছিল না। আবার যে রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে যাবেন সেটাও ছিল কল্পনাতীত। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ; তখনকার দিনে সেটি একটি বৈপ্লবিক অবস্থান। রামমোহন যতই আধুনিক হোন না কেন তাঁর পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব ছিল না। রামমোহন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন; ধর্মের সীমা অতিক্রম করবেন এমন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। পৌত্তলিক ছিলেন না, কিন্তু একেশ্বরবাদী অবশ্যই ছিলেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলেন কারণ সেটা ছিল অত্যন্ত হাস্যকর পুতুলখেলা। এবং দৃষ্টিকটু; বিশেষ করে ইংরেজদের চোখে। হিন্দু ধর্মকে তিনি আধুনিক করছিলেন, কিন্তু ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের জায়গাতে রাখবেন এটা তাঁর চিন্তাতে আসে নি।
বেদ-উপনিষদের যে অনুবাদ রামমোহন করলেন সেটাও তাঁর নিজের শ্রেণির জন্যই। পাদ্রীরা তখন সাধারণ মানুষের ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের চেষ্টা করছিল, তাদের মোকাবিলা করাটাও দরকার হয়ে পড়েছিল, কিন্তু রামমোহনের অনুবাদ যে ভাষায় সেটা সাধারণ মানুষের অগম্য। এর বিপরীতে বিদ্যাসাগরকে দেখি বেদ-উপনিষদ সরিয়ে রেখে অনুবাদ করছেন সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি সাহিত্য; রচনা করছেন ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, ভাষার ভেতর সঞ্চারিত করছেন প্রাণের নতুন প্রবাহ; একদিকে আনছেন হৃদয়াবেগ, অন্যদিকে ব্যবহার করছেন ইংরেজি বিরতি চিহ্ন। ব্রাহ্ম হয়ে যান নি, যেমন তাঁর বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ইয়ংবেঙ্গলের মতো হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করার আওয়াজও তোলেন নি; ধর্মকে রাখতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের জায়গাতে, তাকে মিশিয়ে ফেলতে চান নি ইহজগতের কাজকর্মের সঙ্গে। ইহজাগতিক শিক্ষাকেই প্রধান করতে চেয়েছেন।
নিজের লেখা পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরের উল্লেখ মাত্র রাখতে চান নি তিনি, সামাজিক চাপে যখন বাধ্য হয়েছেন উল্লেখ করতে তখন বলেছেন ঈশ্বর হচ্ছে নিরাকার চৈতন্য; ভাবটা এই রকমের যে তিনি অদৃশ্য থাকেন, কিন্তু আনুগত্য দাবি করেন না, পূজাও নয়। অনেকেরই ধারণা বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বাস্তববাদী এই বুদ্ধিজীবী জানতেন যে ওই বিতর্ক সামনে নিয়ে এলে ধর্মওয়ালাদেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নয়। বিধবা বিবাহের পক্ষে বলার সময় শাস্ত্রের সমর্থন যে তিনি খুঁজেছেন সেটা ধর্মের প্রতি অনুরাগে নয়, ধর্মীয় বিধান দেখিয়ে সমাজবিরোধীদের কাবু করবার আবশ্যকতাতেই।
কথা ও কাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ফারাক রাখতেন না। সামাজিক পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন, সেখানে কোনো ছাড় দেন নি। উপার্জন করেছেন উঠতি বুর্জোয়াদের মতো। কিন্তু উপার্জনকে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত না করে নিয়োগ করেছেন সামাজিক কাজে। বিধবাবিবাহের প্রচলন ঘটাতে চেয়েছেন। কেবল লিখে ও প্রচার করে ক্ষান্ত হন নি, নিজের পুত্রকে বিধবাবিবাহে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন একের পর এক। তবে হতাশ হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। কারণ অনুরাগী পেলেও সহকর্মী পান নি। নিজের শ্রেণির মানুষদের ভেতর যে সঙ্কীর্ণতা দেখেছেন তা তাঁকে ত্যক্তবিরক্ত করেছে। শেষ জীবনে তাই সাঁওতাল পল্লিতে গিয়ে বসবাসের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেটাও বিদ্রোহ বৈকি।
না, তিনি কার্ল মার্কস নন। হওয়া সম্ভব ছিল না। সেটা হতে পারলে পুরোপুরি বিপ্লবী হতেন। সমসাময়িক হয়েও তাঁরা ছিলেন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। মার্কসের সুবিধা ছিল, তিনি অগ্রসর ইউরোপের মানুষ ছিলেন, এবং ইউরোপ তখন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, যে উপনিবেশের একটিতে বিদ্যাসাগরের জন্ম ও অবস্থান। উপরন্তু উপনিবেশিক শাসনের সহায়তাতেই বিদ্যাসাগর পুষ্ট। মার্কস বিপ্লবী হয়েছিলেন শ্রেণিচ্যুত হয়ে, বিদ্যাসাগরেরও চেষ্টা ছিল শ্রেণিচ্যুত হওয়ার, সেটা সম্ভব হতো যদি সমর্থন দেওয়ার মতো আন্দোলন থাকত। আন্দোলন ছিল না। তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন।
শ্রেণিত্যাগের প্রশ্ন রামমোহনের চিন্তায় আসে নি। এর একটা কারণ অবশ্যই সময়ের ব্যবধান। বিদ্যাসাগরের জন্ম রামমোহনের ৪৮ বছর পরে। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে ব্যবধান সেটি হলো দৃষ্টিভঙ্গির। রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারকের, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় বিপ্লবীর। রামমোহন সেই শ্রেণির হয়ে কাজ করেছিলেন ইংরেজরা যে শ্রেণিটিকে ভারতে তৈরি করতে চাইছিল, তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে। ইংরেজি শিক্ষাদান ছিল ওই চেষ্টারই অংশ। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ছিল ওই শ্রেণি থেকে বের হয়ে যাওয়ার, যে জন্য তাঁর অবস্থান ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উদ্যমের বিরুদ্ধে, মাতৃভাষার পক্ষে। দুটি পথ আসলেই দুদিকে চলে গেছে। রামমোহনের পথ উদারনীতির, সেখানে রাজার পাগড়ি ও সাহেবের ভাষা একসঙ্গে থাকে, অসুবিধায় পড়ে না। বিদ্যাসাগরের পথ সমাজপরিবর্তনের, সেখানে পাগড়িও নেই, সাহেবিয়ানাও নেই। বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছিলেন সাহেব হবেন এই আশাতে নয়, শিখেছিলেন যে জ্ঞানের জোরে সাহেবরা উপনিবেশ গড়েছে সেই জ্ঞানের উৎসে রয়েছে যে ইহজাগতিকতা ও দেশপ্রেম তাকে জানবার জন্য। একটি পথ পিতৃতান্ত্রিকতার, অপরটি মাতৃদুর্দশায় কাতর হওয়ার।
বলাবাহুল্য রামমোহনের পথটিই প্রশস্ত হয়েছে, সেখানে যাত্রী অনেক বেশি। ঠেলাধাক্কাও। বিদ্যাসাগরের পথ তেমন প্রশস্ত নয়, সেটি আবার বিপদসঙ্কুলও বটে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকে রামমোহন নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, পাছে রক্ষণশীলরা বিরূপ হয়ে উদ্যোগের ক্ষতি ঘটায়; বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছেন লাঞ্ছনার সকল হুমকিকে উপেক্ষা করেই। স্মরণীয় যে বিদ্যাসাগর বাস্তবজীবনে যা ঘটিয়েছেন পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র তাঁদের সাহিত্যেও তেমনটা ঘটনা ঘটাতে সাহস করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তো শেষ পর্যন্ত চলে গেছেন ধর্মের কাছে। শরৎচন্দ্রও প্রশ্রয় দিয়েছেন সামন্তবাদকে। উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগর রামমোহনের কাজকে যে তেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়। ১৮৪৮ সালে লেখা তাঁর ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে রামমোহনকে একজন অসাধারণ মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাজের প্রতি তেমন একটা সমর্থন জানানো হয় নি। সতীদাহ নিবারণের উল্লেখ পর্যন্ত সেখানে নেই।
৪
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) সম্পর্কে আমরা তেমন একটা জানি না। তিনি বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক, একই বছরে তাঁদের জন্ম। একই মাত্রায় দরিদ্র ছিলেন, এবং ছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযাত্রী। তবে তিনি অতটা প্রবল নন। তাঁর কাজ তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান; কিন্তু একই ধারায় কাজ করতেন তাঁরা। বিশেষ করে ইহজাগতিকতার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ও নারীশিক্ষার প্রশ্নে ছিলেন একই রকম স্পষ্ট ও দৃঢ়।
কেবল ইহজাগতিক নন, অক্ষয়কুমার অনেকটা বস্তুবাদী; বিদ্যাসাগরের মতোই। মানুষের জীবনে প্রার্থনার মূল্য সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরিষ্কার সমীকরণটি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। সহজভাবে তিনি দেখাচ্ছেন যে পরিশ্রম করলে শস্য পাওয়া যায়, পরিশ্রমের সঙ্গে প্রার্থনা যোগ করলেও ফল সেই শস্যই, তার বেশি কিছু নয়। তাহলে প্রার্থনার মূল্য কী? মূল্য তো শূন্য। শস্যের এই উপমাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। অক্ষয়কুমার কৃষক ও কৃষি বিষয়ে সচেতন ছিলেন, জমিদারের উৎপীড়ন, নীলচাষিদের দুর্দশা এসব বিষয়ে লিখেছেন, এবং এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করে গেছেন তিনি। তাঁর সময়েই বেকারত্ব দেখা দিয়েছিল। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকাতে তিনি লিখেছেন, ‘যেমন একটি শব দৃষ্ট করিলে শত শত শকুনি তদ্পরি আক্রমণ করে, সেইরূপ কোনো স্থানে একটি পদ শূন্য হইলে ভূরি ভূরি ব্যক্তি তদর্থে লালায়িত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে।’ (‘হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সংবাদ’)
‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা তিনি একটানা বারো বছর সম্পাদনা করেছেন। এটি ছিল সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার মালিক ছিল ব্রাহ্ম সমাজ, যার প্রধান ছিলেন রামমোহনের পথানুসারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পিতা। অক্ষয়কুমার একটি বই লিখেছিলেন, নাম ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।’ সেটি পাঠে দেবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, ‘আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল তফাৎ।’ তফাৎটা শেষ পর্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়েছিল; দেবেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ‘কতগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এপদ বইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।’
মাতৃভাষার অনুশীলন না হলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের যে উপায় নেই এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের বক্তব্য বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের মতোই স্পষ্ট। শিক্ষা ভিন্ন যে উন্নতি অসম্ভব এবিষয়েও দুই বন্ধুর মত অভিন্ন। অক্ষয়কুমার দেখাচ্ছেন যে মাতৃভাষার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক দুটি। ‘প্রথম প্রতিবন্ধক শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ কর্তৃক সমধিক ইংরাজি ভাষার চর্চা ও আলোচনা; এবং বঙ্গভাষানুশীলনে অবহেলা এবং তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন।’ দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, ‘বাঙালীদিগের স্বাধীনতা শূন্যতা।’ ইংরেজের শাসন যখন মধ্যগগনে, তার অবসানের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী যখন নিশ্চিত, সেই সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশে, অক্ষয়কুমার দত্ত লিখছেন,
আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহার যেরূপ মনের অবস্থা তাহার ভাষাও সেইরূপ হইয়া থাকে।...বর্তমান সময়ে বঙ্গবাসীরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন। সত্য বটে সুসভ্য স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি আমাদের রাজা, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে সকল প্রকার স্বাধীন অধিকারে অধিকারী করেন নাই। সম্প্রতি আবার তাঁহারা প্রেস এ্যাক্ট আইন বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের স্বাধীন আলোচনার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছেন।...যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে। (‘বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক’)
অক্ষয়কুমার অনেক দূর এগিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তবু ধর্ম যে তাঁর পিছু ছাড়ে নি সেটাও সত্য, এবং সেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের সাথে থাকতে পারেন নি। অক্ষয়কুমার একসময়ে ভেবেছিলেন খ্রিস্টান হয়ে যাবেন; খ্রিস্টান হন নি ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। অপর দিকে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম হবেন এমনটা কখনোই ভাবেন নি। ধর্মের ব্যাপারে তিনি উদাসীনই রয়ে গেছেন। অক্ষয়কুমার এরকম কথা বলেছেন যে, ‘যেসকল প্রচলিত ধর্মের সহিত জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্তব্য’। (‘বিদ্যা ও ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধবিচার’) কিন্তু ধর্ম বিষয়ে উদাসীন হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু তাই নয়, পরাধীনতার দরুন মাতৃভাষার জায়গাতে ইংরেজি ভাষার চর্চার ক্ষতিকর প্রবাহ লক্ষ্য করে তিনি আশঙ্কা করেছেন যে ওই তোড়ে মানুষ হয়তো বিধর্মী হয়ে পড়বে। অক্ষয়কুমার লিখেছেন, ‘আমরা পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়।’ (‘বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থান’)
অক্ষয়কুমারের আরেক সীমা এই যে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের কথাই শুধু ভেবেছেন, মুসলমানরা তাঁর চিন্তায় আসে নি। উঁকিঝুঁকিও দেয় নি। যেমন তাঁর প্রবন্ধের নাম, ‘হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা’ এবং ‘হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখ মোচনীয় সংবাদ’। এর আগে কলকাতার বিদ্যোৎসাহী মানুষেরা নিজেদের উদ্যোগে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটির নাম তাঁরা রেখেছিলেন হিন্দু কলেজ; জাতীয় মেলা নামে যার শুরু তার পরিণতি ঘটেছে ‘হিন্দু মেলা’তে। অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল যে পত্রিকা তার নামকরণেও বাঙালিত্ব প্রকাশ পায় নি; সেটির নাম ছিল ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’।
এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িক-বিভাজনকে উৎসাহিত করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ধারণাতে ইংরেজরা জোরেশোরে হাওয়া দিয়েছে; এবং বিরোধের ওই বোধ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করে দেশবাসীকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ভাষা বলছিল পরিচয়টা হওয়া চাই ভাষাভিত্তিক, ধর্ম এসে ভাষার কাঁধে চেপে বসল।
ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষয়কুমারের উপস্থিতিটি ছিল অত্যন্ত শান্ত; প্রবল হয়ে উঠেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)। ১৮৫৭-তে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। অচিরেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দেন। আগে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, বিধবাবিবাহের পক্ষে নাটক প্রযোজনা করেছেন, তাতে অভিনয় করেছেন, বিদ্যাসাগর সে প্রযোজনায় উপস্থিত ছিলেন। নারীশিক্ষার বিস্তারে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খুলেছেন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে ত্রাণের আয়োজন করেছেন, শ্রমিকদের ভেতর গিয়ে কাজ করেছেন; ‘সুলভ সমাচার’ নাম দিয়ে একপয়সা দামের পত্রিকা বের করেছেন। মনে হচ্ছিল উদারনীতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক অবস্থান নেবেন। কিন্তু আসলে ছিলেন ধর্মের ওই বন্ধনের ভেতরেই। তবে বিভাজন দেখা দেয়। কেশব সেন উপবীত ত্যাগের ওপর জোর দিয়েছিলেন, তাঁর চাপে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ছাড়তে রাজি না হয়ে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐক্য ধরে রাখা গেল না, ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’ থেকে কেশব সেনের ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ আলাদা হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।
কেশবচন্দ্র সেনের ছিল প্রবল আবেগ ও অপরিমেয় কর্মোদ্দীপনা। ব্রাহ্ম ধর্মকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রচারের জন্য ইংল্যান্ডেও গেছেন। সেখানে ডিজরেইলী ও গ্লাডস্টোন উভয়ের সঙ্গেই দেখা ও আলাপ করেছেন। মহারানীর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিলেতে তিনি কয়েকমাস মাত্র ছিলেন, কিন্তু বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ব্যঙ্গবিদ্রুপের পত্রিকা Punch লিখেছিল ‘Big as a lion or small as a wren/ who is this Chunder sen?’ তাঁকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি Indian Reform Association গঠন করেন। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলরা মনে করতেন তিনি ছদ্মবেশী খ্রিস্টান। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন ‘Thunderbolt of Bengal’-এর।
কেশব সেন চেয়েছিলেন ধর্মান্দোলনে পুরুষদের পাশে মেয়েরাও থাকবে। এককথায় সবদিক থেকেই তিনি আধুনিক। কিন্তু রইলেন না। আবেগ যুক্তির বিশ্বস্ত মিত্র হয় না; দেখা গেল কেশব সেন যুক্তির চাইতে আবেগকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাঁর ক্ষেত্রে অহমিকায় পরিণত হলো, তিনি অবতারবাদের দিকে ঝুঁকলেন, এবং ভক্তদের নিরুৎসাহিত করলেন না যখন তারা তাঁকে অবতার হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করল। প্রগতিশীলতার মুখপাত্রের ভেতর দেখা দিল রক্ষণশীলতা। হিন্দু প্রথায় নিজের অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দিলেন কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ আছর করল তাঁর ওপরে। শেষ পর্যন্ত হাত ধরে ফেললেন তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের।
এরকমটা ঘটাটা বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষ করে আত্মবিশ্বাস যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয় তাহলে বিদ্যা ও বুদ্ধি তার কাছে পরাজয় মানে, হৃদয় কার্যক্ষমতা হারায়, এবং আত্মম্ভরিতা কর্তৃত্ব পেয়ে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা গেছে। সশস্ত্র পথে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার ব্রত নিয়ে এসেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হলেন। ‘বন্দেমাতরম’ নাম দিয়ে ইংরেজি দৈনিক বের করলেন, জেলে গেলেন, কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে মাথা নত করে চলে গেলেন প-িচেরীতে, আশ্রম গড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। অধ্যাত্ম সাধনার নতুন পথ খুলে বসলেন। বিপ্লবের পথে অস্থির ছিলেন এম এন রায়। অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন চিন্তায় ও কাজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন মার্কসবাদকে সংশোধন করে নতুন মতাদর্শের জন্ম দেবেন, তার নাম দিলেন বিপ্লবী মানবতাবাদ এবং একপর্যায়ে ঠিক করলেন রাজনৈতিক দলেরই প্রয়োজন নেই। উদারমনা ব্যক্তিদের সমাবেশই যথেষ্ট। অসাধারণ উঁচু মাপের বুদ্ধিজীবী ছিলেন ট্রটস্কি; রুশ বিপ্লবের অগ্রগণ্য নেতাদের ভেতর তিনি একজন। বই লিখেছেন, সংগঠন গড়েছেন, বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু অবশেষে নিজের দেশেও তাঁর থাকা হলো না, নির্বাসিত অবস্থায় প্রাণ হারালেন। ধরা যাক আমাদের কাছের সময়ের একজন মেধাবান ফরাসি বুদ্ধিজীবীর কথা। একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে তিনি এসেছিলেন সাংবাদিক হিসেবে, তাঁর বয়স তখন ২৩, আসল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধটিকে জানা, পারলে সাহায্য করা। এই বুদ্ধিজীবী—বের্নার-অঁরি লেভি—বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকাটা অনুধাবন করতে। তাঁদের সঙ্গে থাকাটাই পছন্দ করতেন। যুদ্ধের পরেও কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন, সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে কাজও করেছেন কয়েক মাস; তারপর চলে গেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকেছে সরকারের কছে। দুবছর পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন ফরাসি ভাষায়, যার বিষয়বস্তু, তাঁর ভাষায়, ‘বিপ্লবের ভেতর জাতীয়তাবাদ’ (বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে ‘বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল’ নামে, অনুবাদ ও সম্পাদনা শিশির ভট্টাচার্য)। কিন্তু তাঁর বয়স যত বেড়েছে বামপন্থায় আস্থা তত কমেছে; শেষ পর্যন্ত তাঁর মতাদর্শিক অবস্থানটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কসবাদবিরোধী তথাকথিত গণতন্ত্রীর। লেভি ধনী পরিবারের সন্তান, আলজেরিয়াতে তাঁর পিতার কাঠের ব্যবসা ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রভূত বিত্তের মালিক হয়েছিলেন তিনি। ধারণা করা অন্যায় নয় যে অতিরিক্ত আবেগ ও আত্মবিশ্বাস তাঁকে অস্থির করে ফেলেছিল, সঙ্গে ছিল শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য এবং চারদিকে বিরাজমান হতাশার চাপ। সব মিলিয়ে বিপ্লবী থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত তো সর্বজনবিদিত। তাঁর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল, সাম্যও চাইতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সম্ভব নয় এবং সাম্য শ্রেণিস্বার্থের জন্য বিপজ্জনক, এই উপলব্ধিতে পৌঁছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের কাছে, এবং উৎসাহ যোগালেন সাম্প্রদায়িকতাকে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা বহুবিস্তৃত। সংজ্ঞায়িত করা প্রায় অসম্ভব। তিনি রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার উত্তরাধিকারকে সমন্বিত করেছেন, এবং উদারনীতিকতাকে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ ও অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন, নিজের অসামান্য সব কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর সময়ে পুঁজিবাদ আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নিয়েছেন। ১৯২৬-এ রচিত ‘রক্তকরবী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন দুর্ধর্ষ পুঁজিবাদ কীভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করছে। মানুষকে উৎপাটিত করছে, তার ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। নির্মম নির্যাতনে প্রকৃতির প্রাণশক্তি নিঙড়ে নিচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদীদেরকে তিনি পুঁজিবাদী বলছেন না, বলছেন আকর্ষণজীবী। যাদের অবস্থান কর্ষণজীবীদের বিরুদ্ধে। কর্ষণজীবীরা কৃষিজীবী।
রুশ দেশ ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে ১৯৩২ সালে লেখা নাটক ‘রথের রশি’তে রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন যে ইতিহাসের অগ্রগতি নির্ভর করছে মেহনতী মানুষদের শ্রমের ওপর। রাজা, পুরোহিত, সৈনিক, বণিক, ধনিক সকলের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে, রথ এখন অচল, সে অপেক্ষা করছে মেহনতী মানুষ কখন এসে তার রশি ধরে টান দেবে সেই শুভ ক্ষণটির জন্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাদের মেহনতী বলছেন না, বলছেন শূদ্র। দ্বিধা এখানেও ছিল। তবে মানবজাতির ভরসা যে আপাতত কৃষক ও শ্রমিকের মেহনতের ওপরই সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। রাষ্ট্রশাসকের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লিখেছেন তিনি তাঁর ‘তাসের দেশ’ নাটকে। তার কত আগে, সেই ১৯২২-এ, এসত্য ধরা পড়েছিল তাঁর চোখে যে পানি নিয়ে পৃথিবীতে ভীষণ বড় সমস্যা দেখা দেবে। তাঁর ‘মুক্তধারা’ নাটকে দেখা যাচ্ছে উত্তরকূটের শাসকেরা নদীর ওপর বাঁধ বানিয়ে নিচের এলাকার বাসিন্দাদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন বলবৎ রাখতে চাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করাটা কেবল অন্যায় নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনকও।
বিশেষভাবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কৃষকের ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা। কৃষকের জীবনে শরিক হতে না-পারা নিয়ে নিজের ওপরে তাঁর অসন্তোষ ছিল। জমিদারি ব্যবস্থার তিনি অবসান চেয়েছেন, কৃষকের উন্নতির জন্য ভেবেছেন ও কাজ করেছেন; সমাজে মৌলিক পরিবর্তন তাঁর কাক্সিক্ষত ছিল, রাশিয়ার বিপ্লব তাঁকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল, মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণ না ঘটলে ইতিহাস যে এগুবে না এ বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল না। যদিও সহিংস বিপ্লবে তাঁর সমর্থন ছিল না। বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ‘না’ বলার আবশ্যকতা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল, যদিও তিনি উদারনৈতিক ধারাতেই ছিলেন, সেই ধারার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের একজন হিসেবে।
রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন আনবার প্রধান উপায় হিসেবে শিক্ষাকেই বিবেচনা করেছেন। আর শিক্ষার মাধ্যম যে হবে মাতৃভাষা সেই কথাটা তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন। বলেছেন যে মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষা কিছুতেই যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না। ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি বলতেন বুদ্বুদ; বাইরে শোভা আছে, ভেতরে সারবস্তু নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের চাইতেও দৃঢ়ভাবে বলেছেন।
৫
তুলনায় বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল অনগ্রসর। শিক্ষায় তারা প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে ছিল। এর প্রধান কারণ দারিদ্র্য। মুসলমানরা অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং দরিদ্র। এই দুই বাস্তবতা তাদের এগুতে দেয় নি, টেনে ধরে রেখেছে। এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯২২)। তিনি ‘জমীদার দর্পণ’ নামের একটি নাটক লিখে দেখিয়েছেন যে জমিদার হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, সে প্রজার শত্রু। জমিদারী ব্যবস্থার তিনি অবসান চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকটির সাহিত্যিক গুণের প্রশংসা করলেও, এ বইয়ের প্রচার কামনা করেন নি, পাছে কৃষক অসন্তোষের আগুনে ঘি ঢালা হয়। ‘গো-জীবন’ নামের বইতে মশাররফ গরু কোরবানির বিরুদ্ধে বলেছেন এবং বলার ফলে তাঁকে মুসলমান সমাজের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ জীবনে মীর মশাররফ হোসেনকেও আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে ধর্মের কাছে, লিখতে হয়েছে ‘মৌলুদ শরীফ’ নামে কবিতার বই। শ্রেণি ও পরিবেশ এতটাই অসহিষ্ণু ছিল।
বিস্ময়কর প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। শ্রেণির বন্ধন ও সম্প্রদায়ের নিষেধ দুহাতে সরিয়ে দিয়ে তিনি যেভাবে এগিয়ে গেছেন বাংলা ভাষায় ও বঙ্গদেশে তার তুলনা বিরল। তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ্য। প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতা। তাঁর কালে অসাম্প্রদায়িক হওয়াটাই কঠিন ছিল; নজরুল অসাম্প্রদায়িকতার স্তর পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার স্তরে। দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেম। দেশ বলতে অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যেখানে ভারতবর্ষকে বুঝতেন, নজরুল সেখানে বুঝতেন বাংলাকে। আমরা জানি যে রামমোহন চেয়েছিলেন উন্নত ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক, পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ উভয় দলই স্বাধীনতা বলতে বুঝেছে ‘ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস’। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই তারা পেয়েছে, দেশকে দুটুকরো করতে সম্মত হয়ে। নজরুল চেয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং ১৯৩১ সালে ‘ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস’ পাওয়া যাবে বলে যখন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছিল সেই সময়ে তিনি ‘ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস’ নামে একটি অসামান্য কবিতায় দেশবাসীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন,
আজ তবু কেন বিস্কুট খাস
হয়েও গেলি প্রায় রাজাই।
গাল বাজাই আয় কানাডা আর
অস্ট্রেলিয়ার ভায়রা ভাই
[...]
বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে।
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি,
মা হবেন আজ ডোমনী রে।
নজরুলের বইগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; ‘ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস’ কবিতাটি ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপের কবিতার বই ‘চন্দ্রবিন্দু’র অংশ। ব্রিটিশ সরকার ওই বই-ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। স্মরণীয় যে তারা কেবল বইকেই আটক করে নি, বইয়ের লেখককেও বন্দী করেছিল, কারাগারে। বই ও বইয়ের লেখকের এমন একত্র নির্যাতন ব্রিটিশের বর্বর ঔপনিবেশিক নিপীড়নের কালেও কমই ঘটেছে। নিজের দেশ ‘ডোমনী’ হবে এবং দেশবাসী হবে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ভায়রা ভাই এমন সম্ভাবনা এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের প্রীত করতে পারলেও নজরুলের চিন্তায় তা ঘৃণা ভিন্ন অন্য কিছুর উদ্রেক করে নি।
তৃতীয় ক্ষেত্রটি ছিল সাম্যবাদে আস্থা। রুশ বিপ্লবের মতাদর্শকে বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টিশীল উপায়ে তাঁর মতো করে অন্য কেউ আনতে পারেন নি। এখানে এসে তিনি আর নিছক জাতীয়তাবাদী থাকেন নি, তাঁর জাতীয়তাবাদ পৌঁছে গেছে আন্তর্জাতিকতায়, যে জন্য কলকাতার রেল স্টেশনে কুলিমজুরটির দুঃখকে তিনি একজন ব্যক্তির মারখাওয়া হিসেবে দেখেন নি, দেখতে পেরেছেন জগৎজুড়ে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হাতে বিশ্বমানুষের অপমান হিসেবে। মেহনতী মানুষের দুঃখে তাঁর কান্না পেয়েছে, কিন্তু সেই কান্না তাঁর দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয় নি। দুটি সত্য তিনি একসাথে দেখতে পেয়েছেন। প্রথমটি হলো পুঁজিবাদী সভ্যতার ভিত্তিতে মেহনতী মানুষের শ্রমশক্তির শোষণের বাস্তবতা; দ্বিতীয়টি হলো ওই শোষণই শেষ কথা নয়, শোষণেরও শেষ আছে। এবং রুশ বিপ্লব সেই মুক্তির আশ্বাসই দিচ্ছে। তবে মুক্তি এমনি এমনি আসবে না, আসবে মহা-উত্থানের মধ্য দিয়ে। সে-উত্থান সকল দেশের সকল নিপীড়িত মানুষের। তাঁর অঙ্কনে পুঁজিবাদী শোষণের ছবিটা অবিস্মরণীয় :
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্।
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল রেলে,
বল ত এ-সব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান না ক’, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকা মানে!
পুঁজিবাদী সভ্যতার ভেতরের বাস্তবতার এমন মর্মস্পর্শী উন্মোচন বাংলাভাষায় বিরল। সর্বহারা ও সাম্যবাদী নাম দিয়ে কবিতার বই লেখার কথা নজরুলের আগে কেউ ভাবেন নি।
নজরুল রামমোহনের নয়, বিদ্যাসাগরের ধারার লোক, রুশ বিপ্লবের পরের লেখক এবং শ্রেণিচ্যুত বুদ্ধিজীবী। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা প্রায় সবাই ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক; তাঁদের আধুনিকতা ছিল পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দলিল। যে জন্য নজরুলকে তাঁদের মনে হয়েছে, উচ্চকণ্ঠ এবং অভদ্র। নজরুলের তুলনায় তাঁরা যে খাটো ছিলেন সে শুধু মেধার মাপে নয়, দৃষ্টিভঙ্গির মাপেও; দৃষ্টিভঙ্গিটাই বরঞ্চ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এরিয়েল যারা সাজতে পছন্দ করে ক্যালিবানরা তাদের কাছে অসহ্য বটে।
নারীর অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা এসব প্রসঙ্গ ও প্রশ্নের বিবেচনা সাহিত্যে নানাভাবে এসেছে। নজরুল বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর ‘নারী’ কবিতা সূচনা-পঙ্ক্তি দুটি আমাদের সবারই জানা; ‘সাম্যের গান গাই—/ আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।’ নারীমুক্তির যে ভবিষ্যতটি তিনি দেখছেন সেটিও বৈষম্যহীনতারই। ‘সেদিন সুদূর নয়—/ যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।’ এই ঘটনাটা এমনি এমনি ঘটবে না, এর জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন হবে, সাম্যবাদী বিপ্লবের। করুণা, বদান্যতা বা সংস্কারে সেটা আসবে না, আসবে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, আর সে-সংগ্রামে পুরুষ যেমন থাকবে তেমনি থাকবে নারীও,
ভেঙে যমপূরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি।
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে।
আশপাশের আধুনিক কবিরা যখন যৌবনের কারাগারে বন্দী অবস্থায় নানা সুরে হাহাকার ও নারীবন্দনা করছেন, করতে গিয়ে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত পর্যন্ত হচ্ছেন, নজরুল তখন প্রতিষ্ঠা চাইছেন নারী-পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের। তফাৎটা নিতান্ত সামান্য নয়।
সমসাময়িক মুসলিম সমাজে নজরুলের তুলনায় অধিক বিদ্বান অনেকেই ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কারও পক্ষেই নজরুলের অনন্যতার নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় নি। যেমন ঢাকায় ছিলেন ‘বুদ্ধির মুক্তি’ গোষ্ঠীর সদস্যরা। নজরুলের কাছে তাঁরা হার মেনে গেছেন আরম্ভতেই, এবং সেটা এক দিক থেকে নয়, একাধিক দিক থেকে। তাঁরা তাঁদের সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’, অপরদিকে নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক, এবং অন্তর্গতচেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, ঘোষিত রূপেই তাঁরা মনস্থ করেছেন চর্চা করবেন বুদ্ধির; নজরুল ছিলেন যেমন বুদ্ধির তেমনি হৃদয়ের। এই সত্যটা তাঁদের তরুণ হৃদয়ে ধরা পড়ে নি যে বুদ্ধির চর্চা যথেষ্ট নয়, হৃদয়ের অনুশীলনও অত্যাবশ্যক। তৃতীয়ত, তাঁরা কেউই রুশ বিপ্লবের চিন্তাকে সেভাবে ধারণ করেন নি, নজরুল যেভাবে করেছেন।
আশ্চর্য ব্যতিক্রম হচ্ছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। নজরুলের চেয়ে উনিশ বছর আগে তাঁর জন্ম; পরিবেশ ছিল পুরোপুরি বৈরী। প্রথমত নারী, দ্বিতীয়ত অভিজাত মুসলিম পরিবারের সদস্য; তাঁর পরিবারে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক চর্চা ছিল প্রায় নিষিদ্ধ, অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বিপত্নীক উর্দুভাষী সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে। নজরুল তবু স্কুলে গেছেন, গৃহত্যাগ করে নানা জায়গায় ঘুরেছেন, যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে, চলে গিয়েছিলেন করাচি পর্যন্ত, অবাধ মেলামেশা ছিল বহু ধরনের মানুষের সঙ্গে। বেগম রোকেয়ার জন্য সকল দরজাই ছিল বন্ধ, ছিলেন তিনি অবরোধবাসী, তাঁর নিজের বর্ণনায় ‘লোহার সিন্দুকে’ বন্দী। কিন্তু যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের ধারার সঙ্গেই। বিদ্যাসাগরের মতোই স্বচেষ্টায় নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন, এবং সকল নিষেধ অমান্য করে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করছেন। আবার বিদ্যাসাগরের মতোই, যতটা না তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছেন শিক্ষাবিস্তারের জন্য তার চেয়ে বেশি সাহিত্যচর্চার কারণে, যে সাহিত্যের অনেক চিন্তাই ছিল আধুনিক এবং প্রায় বৈপ্লবিক। ধরা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান। বিদ্যাসাগর ধর্মকে সামাজিক ব্যবস্থা বলেই জানতেন, রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সেরকমেরই। নিজে তিনি ধর্মপালন করতেন, কিন্তু ধর্মীয় বিধানকে প্রশ্ন করতে ছাড়েন নি। ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ নামে প্রবন্ধে তাঁর উক্তিটি তো সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধ; ‘তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।’ তাঁর কল্পকাহিনী ‘সুলতানার স্বপ্ন’-তে এমন এক দেশের কথা বলা হচ্ছে যেখানে সবকিছু সুশৃঙ্খল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিরুপদ্রব এবং যেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার পর্যন্ত রয়েছে। এর কারণ হলো দেশটিতে কর্তৃত্ব পুরুষের নয়, নারীর। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে বেগম রোকেয়া তাঁর কল্পনার সমাজটিকে আরও সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, সেখানে স্বামী কর্তৃক অন্যায়ভাবে পরিত্যক্ত নায়িকা সিদ্দিকা আশ্রয় পেয়েছে তারিণী ভবন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে। তারিণী ভবনে বিপন্ন নারীরা আশ্রয় পায়; বড় ব্যাপার যেটা তা হলো প্রতিষ্ঠানটি একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ। মেয়েরাই কর্তা। এবং সকল ধর্মের মেয়েরাই এখানে নির্বিঘেœ থাকে এবং সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত হয়। সিদ্দিকার সাবেক স্বামী তার সন্ধান পেয়েছে, সে এখন তাকে ফেরত নিতে চায়। সিদ্দিকা যাবে না, ব্যারিস্টার লতিফকে সে যে ঘৃণা করে তা নয়, ভালোই বাসে, কিন্তু ভালোবাসা আর বিবাহ যে সমার্থক নয় সেটা সে বুঝে নিয়েছে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে; তদুপরি সিদ্দিকা পেয়েছে নতুন জগতের সন্ধান, সে জানিয়ে দিতে চায় যে বিয়ে করা ছাড়াও মেয়েদের জন্য অনেক কাজ আছে করবার।
বেগম রোকেয়ার সঙ্গে নজরুলের সামনাসামনি দেখা হয় নি। হওয়ার কথা নয়, তাঁকে থাকতে হতো পর্দার আড়ালে, কিন্তু তিনি নজরুলের অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’তে লিখেছেন। মেহনতীদের দুঃখ তিনিও জানতেন। তাদের ব্যাপারে সরব ছিলেন। ‘চাষার দুক্ষু’ নামের প্রবন্ধে রোকেয়া লিখছেন যে কলকাতায় পাটকলের কর্মচারীরা বেশ ভালো বেতন পাচ্ছে, তারা নবাবি হালেই চলে; আর তার বিপরীতে পাটচাষিদের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় সেটা রোকেয়ার বক্তব্য এবং প্রশ্ন,
যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের অবস্থা এই যে ‘পাছায় জোটে না ত্যানা’ ইহা ভাবিবার কথা নহে কি? আল্লাহ তা’লা এত অবিচার কি রূপে সহ্য করিতেছেন?
কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতির সম্মেলনে তাঁকে সভানেত্রী করা হয়েছিল। সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেছেন যে তাঁকে ওই পদে আসীন করাটা মোটেই ঠিক হয় নি, কারণ ‘আমি আজীবন কঠোর সামাজিক পর্দার অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এমন কি সভানেত্রীকে হাসিতে হয় না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না।’
তিনি মন্তব্য করেছেন,
পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবাসিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূ ভারতে নাই।
আলীগড়ের শিক্ষাবিদ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ’র একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে রোকেয়া বলছেন যে পর্দ্দা ‘সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক’ এই কথাটা তিনি মানেন না। কারণ “যন্ত্রণাদায়ক হইলে অবলাগণ ‘বাবারে! মা’রে! মলুম রে! গেলুম রে!’ বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বলিক এসিডের সহিত তুলনা করা যায়। তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের অবসর পায় না। অন্তপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে তিল-তিল করিয়া মরিতেছে।”
এই মৃত্যুতে সমাজের যে কোনো লাভ নাই, এমন বক্তব্য এতটা পরিষ্কারভাবে সেকালে মুসলমান সমাজের আর কেউ বলেন নি। কিন্তু রোকেয়া কেবল যে মুসলমান সমাজের কথা ভাবছিলেন তা নয়, তাঁর ভাবনা ছিল গোটা বাঙালি সমাজ নিয়ে।
৬
অক্ষয়কুমার দত্ত আশাবাদী মানুষ, তিনি ধারণা করেছিলেন যে ইংরেজ যখন চলে যাবে তখন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার যে আগ্রহ তারও অবসান ঘটবে। আশার সুরে এবং ভরসা করে লিখেছেন,
এইক্ষণে যদিও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসীর অনেক যুবক ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করিতেছেন তথাপিত ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজী বিদেশী লোকদের ভাষা, সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবে? (‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’)
তা বিদেশি ইংরেজ তো বিরল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইংরেজির কদর কি কিছুমাত্র কমেছে? নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে? ইংরেজের প্রস্থান এবং ইংরেজি ভাষার কদর বৃদ্ধি এই দুই আপাত বিপরীত ঘটনার ব্যাখ্যাটা অবশ্য কঠিন নয়, সেকালের বুদ্ধিজীবীরা সেটা না বুঝলেও একালের বুদ্ধিজীবীরা তা বোঝেন। সেটা হলো এই যে ইংরেজি ভাষা অনেক গভীরে চলে গিয়েছে। তদুপরি ইংরেজ শাসনে যে সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধালোভী শ্রেণি তৈরি হয়েছিল সেই শ্রেণি এবং তাদের উত্তরাধিকারীরাই পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর। ওই শ্রেণি ইংরেজিতে কেবল অভ্যস্ত নয়, এই অভ্যাস নিয়ে তারা বিলক্ষণ গৌরব বোধ করে। সেকালে করত একালেও করে। আরও বড় সত্য এই যে ইংরেজের শাসনের অবসান ঘটেছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজে তো কোনো বিপ্লব ঘটে নি। রাষ্ট্র সেই আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদীই রয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা একটি বিশ্বব্যবস্থারই অংশ, যেখানে ইংরেজি কেবল প্রতিষ্ঠিতই নয়, সর্বাগ্রগণ্য বটে। তৃতীয়ত, ভাষা শিক্ষা তো কেবল বিদ্যাশিক্ষা নয়, ভাষা চিন্তাকে প্রভাবিত করে, চিন্তাশক্তির অংশ হয়ে দাঁড়ায়, এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাড় দেয় না। সে ঘটনাই ঘটেছে বাংলাদেশে।
বাংলাদেশে তো আমরা একবার নই, দুবার স্বাধীন হয়েছি। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, কিন্তু ভেতরে বাইরে ইংরেজির দাপট আরও বেড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’-এর ‘পত্র-সূচনা’ রচনাটিতে ইংরেজির রমরমা ব্যবসা দেখে পরিহাস করে লিখেছিলেন, ‘আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজীতে পঠিত হইবে।’ সেটা ঘটে নি, তবে বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাদান চালু হয়েছে, এবং আগামীতে তার হ্রাস না-ঘটে বৃদ্ধি ঘটবে এমন ধারণা মোটেই অমূলক নয়। সেকালের বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে অভিন্ন শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে বলেছেন; বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাতেই কার্যকর ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার স্বপ্ন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাওয়া গেছে, বাংলা তার রাষ্ট্রভাষাও হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের শাসকদের ভাষা হয় নি।
পাঠশালা, টোল ও মক্তব—এই তিনধরনের শিক্ষা ইংরেজদের আগমনের আগে এদেশে ছিল; বাংলাদেশে এখন ইংরেজি, বাংলা ও মাদ্রাসা এই তিনধারা সমানে চলছে, এবং বিভাজনের ভিত্তিতে সম্প্রদায় নেই, রয়েছে শ্রেণি। শ্রেণিবিভাজন দূর না করলে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম হওয়ার কোনো আশাই নাই। স্বাধীনতা শ্রেণিবিভাজন দূর করবে কি, সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রূপকথার মতো উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু রূপকথা দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য যে নরকের সৃষ্টি করেছে সেটা মিথ্যা নয়, রূপকথাবাদীরা যদিও তাকে ঢেকে রাখতে চায়। এদের পরিচয়ও দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবী হিসেবেই। রূপকথাবাদীরা সবকিছুকেই রূপকথায় পরিণত করেন, উন্নতিকে যেমন, বিজ্ঞানকেও তেমনি। এঁরা আর যা-ই হোন বুদ্ধিজীবী নন।
অক্ষয়কুমারের আরেকটি বক্তব্য স্মরণীয়। সে-বক্তব্যটির ভিত্তি আশা নয়, ভিত্তি বাস্তবতা।
বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা একসঙ্গে চলিতেছে, কিন্তু ইংরাজি ভাষার যেরূপ আত্যন্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজি ভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির বিশেষ হানিকর হইতেছে এবং ঐ ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক উদিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। বর্তমান সময়ে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহারা প্রায় সমস্ত জীবন ইংরাজি ভাষানুশীলনে, ইংরাজি পুস্তক অধ্যয়ন ও ইংরাজি বিদ্যা পর্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। বঙ্গভাষায় বিশেষ অনুশীলনে তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোককেই তৎপর দেখা যায়। (‘বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক’)
অক্ষয়কুমার এদের ধিক্কার দিয়েছেন ‘স্বদেশবিদ্বেষী’ বলে। তাঁর ওই ধিক্কারধ্বনির পরে একশ’ পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে, অনেক দিক দিয়েই আমরা দৃশ্যমান উন্নতি করেছি, কিন্তু ক্ষমতাবানদের ‘স্বদেশবিদ্বেষ’ কি কমেছে, নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে? আমরা প্রথমে বিদেশি ও বিজাতীয় ইংরেজ এবং তার পরে বিজাতীয় পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি, কিন্তু দেশি স্বদেশবিদ্বেষীদের নিয়ে এখন কী করি?
দোষ ব্যক্তির নয়, দোষ ব্যবস্থার। পুঁজিবাদ এখন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। ভেতরের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এবং বাইরের সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মুখে পড়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দিশেহারারা বেপরোয়া হয়। দিশেহারা পুঁজিবাদ তার শেষ অবলম্বন ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজের সর্বত্র ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন চলছে। ওদিকে মানুষকে সে ব্যস্ত রাখছে ব্যক্তিগত উন্নতির অস্থির প্রতিযোগিতায়। তথাকথিত অবাধ তথ্যপ্রবাহের বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে পৃথিবীটাকে বড় করার নাম করে ছোট করে ফেলেছে। পুঁজিবাদের পক্ষের লোকদের ভাষায় macro নয়, micro-ই, গুরুত্বপূর্ণ; grand narrative-এ কাজ হবে না, ক্ষমতার দ্বন্দ্বগুলো দেখতে হবে। সেগুলো অসংখ্য। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রে ও সমাজে আছে; আছে অফিস কাছারিতে, শিক্ষালয়ে, হাসপাতালে, গৃহে, কোথায় নেই? ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এইসব দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মূল শত্রুর খুব সুবিধা হয়, সে আড়ালে থেকে তার তৎপরতা চালাতে পারে।
কিন্তু পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠছে। সংশোধন করে, ছাড় দিয়ে, পকেটে ঘুষ গুঁজে দিয়ে তাকে আর রক্ষা করার উপায় নেই। উদারপন্থীরা তাই ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, দুইপক্ষেই দুই কট্টরপন্থীরা দাঁড়িয়ে গেছে। একদিকে ফ্যাসিবাদীরা, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীরা। ফ্যাসিবাদী ডোনাল্ড ট্রাম্পদের মোকাবিলা এখন উদারনীতিক হিলারী ক্লিন্টনকে দিয়ে হচ্ছে না, হবে না, প্রয়োজন হবে সমাজতন্ত্রী বার্নি স্যান্ডোর্সের। লেবার পার্টির নেতা হিসেবে টনি ব্লেয়ারকে এখন হাস্যকর ঠেকে, তাঁর সঙ্গে টোরিদের নৈকট্য বিবেচনা করলে। এখন তাই জেরিমি করভিন এসে গেছেন। যিনি ব্যক্তি মালিকানার বিপক্ষে সামাজিক মালিকানার পক্ষে বলছেন, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। লন্ডন শহরে কেনসিংটন এলাকাতে ২৪ তলা টাওয়ারে আগুন লেগে বহু মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আগের দিনে হলে বলা হতো নিছক দুর্ঘটনা, এখন আসল সত্য লুকানো যাচ্ছে না, ধরা পড়ছে যে দুর্ঘটনার ভেতরেও আরেক ঘটনা আছে, সেটা হলো অবহেলা। ওই টাওয়ারে কম আয়ের মানুষেরা থাকে, টাওয়ারের তাই যত্ন নেওয়া হয় নি, আগুনের আসল কারণ অযতœ ও অবহেলা। পাশেই আছে বড়লোকদের বড় বড় বাড়ি, সেগুলো খালি পড়ে থাকে, সেগুলোর যতœ নেওয়া হয় এবং সেখানে আগুন লাগে না। প্রতিবাদীরা তাই বলছেন এটা শ্রেণির ব্যাপার, এবং জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁদের প্রতিবাদ শ্রেণিসংগ্রামেরই অংশ। আমেরিকার হোয়াইট হাউজে একজন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ বসবাস করবেন এমন কথা রক্ষণশীল আমেরিকানরা কল্পনাও করে নি; লন্ডন শহরের মেয়র হবেন একজন উপমহাদেশীয় বংশোদ্ভূত এ ছিল ইংরেজদের ধারণার অতীত। সেসব ঘটেছে। কিন্তু তাতেও কুলাচ্ছে না, আরও এগুতে হবে। দাঁড়াতে হবে সমাজ-পরিবর্তনের পক্ষেই। এবং সে জন্য দরকার হবে শ্রেণিচ্যুতির। আমাদের দেশে যার পথ বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন।
বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়াবার লোকের অভাব নেই। ব্যবস্থার পক্ষে মিডিয়া আছে। মিডিয়া মালিকের পক্ষ হয়ে কাজ করে। মালিকেরা সকলেই পুঁজিবাদী। এটা প্রত্যক্ষ সত্য যে মিডিয়া এখন যতটা শক্তিশালী আগে কখনো ততটা ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকে গেছিলেন জবরদখল করার জন্য; অজুহাত ছিল সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। জানতেন সেসব নেই, খোঁজাখুঁজি করে তাই পেলেন না; তবু বলতে থাকলেন যে আছে। বলতে পারলেন মিডিয়ার সাহায্যে। আসলে মিডিয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র। মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করার চেষ্টার ক্ষেত্রে সে মারাত্মক রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার বিশেষ উপযোগিতা এজন্য যে তাকে শত্রু মনে হয় না, মনে হয় সে মিত্র। এমন বিশ্বাসঘাতকতা আসলেই বিরল।
পুঁজিবাদী অসুস্থ সমাজে মিডিয়াসহ বহুবিধ উৎপাতের ভেতর বসবাস করে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি। শারীরিকভাবেও সুস্থ থাকা কঠিন। মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে তিন গুণ—জ্ঞান, বুদ্ধি ও হৃদয়ানুভূতি—তাদের দমিত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। সমাজ সেটাই চায়, রাষ্ট্র ওই দমনকে উৎসাহিত করে।
অসুখ হলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে সাধারণ চিকিৎসায় কাজ হবে না, তাকে বদলাতে হবে, যাতে সে স্বাভাবিক হয়, এবং মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে ‘না’ বলা চাই, নতুন ‘হ্যাঁ’ যাতে আসতে পারে সেই প্রয়োজনে। আসার পথ তৈরির চেষ্টা সারা বিশ্বে চলছে; সে চেষ্টায় আমাদেরও যুক্ত হওয়া চাই, সুস্থ থাকার জন্য।
একাজে বিদ্যা, বুদ্ধি ও হৃদয়, এই তিনটিরই একত্র অনুশীলন দরকার পড়বে। এ কেবল বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপার না, ব্যাপার সকল নাগরিকের। বাংলাদেশে বিদ্যার প্রসার ঘটছে বলে আমাদের ধারণা; কিন্তু সে-বিদ্যার অন্তরে কী আছে তা নিয়ে সন্দেহের কারণ রয়েছে। বিশেষত মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা না দেওয়া হলে সে শিক্ষা যথার্থ হবে এমন কথা কেউ বলবেন না। ওদিকে দেশে বুদ্ধিমান মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বুদ্ধির চর্চাটা আত্মস্বার্থনির্ভর। এই রকম বুদ্ধিকে নির্ভয়ে কূটবুদ্ধি বলা চলে। এমন বুদ্ধির বিকাশ মোটেই আশার খবর নয়। এবং খুবই অভাব রয়েছে হৃদয়ানুশীলনের। হৃদয়ের শিক্ষার স্বল্পতার দরুন আবেগের আকস্মিক প্লাবন পাওয়া যায়, কিন্তু তার প্রবহমানতা দেখা যায় না। ভুললে চলবে না যে যাকে বিবেক বলি তার আশ্রয় ওই হৃদয়ই, এবং সেখানেই তার নিরাপদ লালনপালন।
মূল কাজটা বিদ্যমান দুষ্ট ব্যবস্থাকে ‘না’ বলা, এবং নতুন ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো। সে-ব্যবস্থাটা হবে সমাজতান্ত্রিক। মালিকানা ব্যক্তিগত থাকবে না, হবে সামাজিক, এ কাজের জন্য প্রয়োজন, বার বার বলতে হয় কথাটা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও হৃদয়ানুভূতির একত্র অনুশীলন। এ সত্যটা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা মস্তবড় একটা দুঃসংবাদ, যদিও গণমাধ্যমে তা আসে না। বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুটি বিশেষ মিত্র হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা। তারাও তৎপর রয়েছে। তাদেরও যেন না ভুলি।
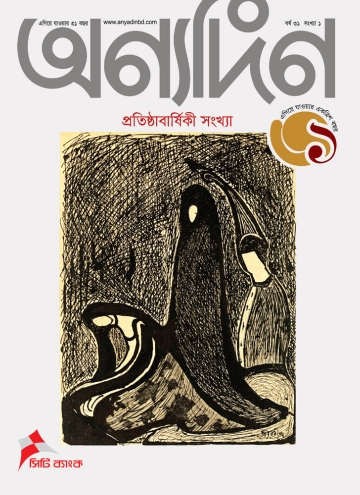




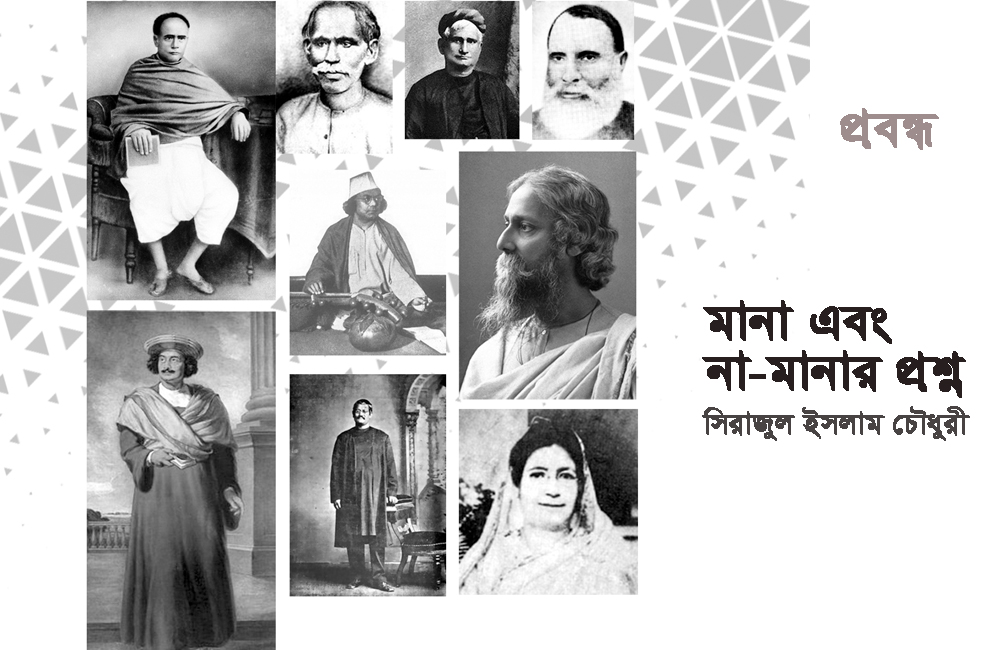

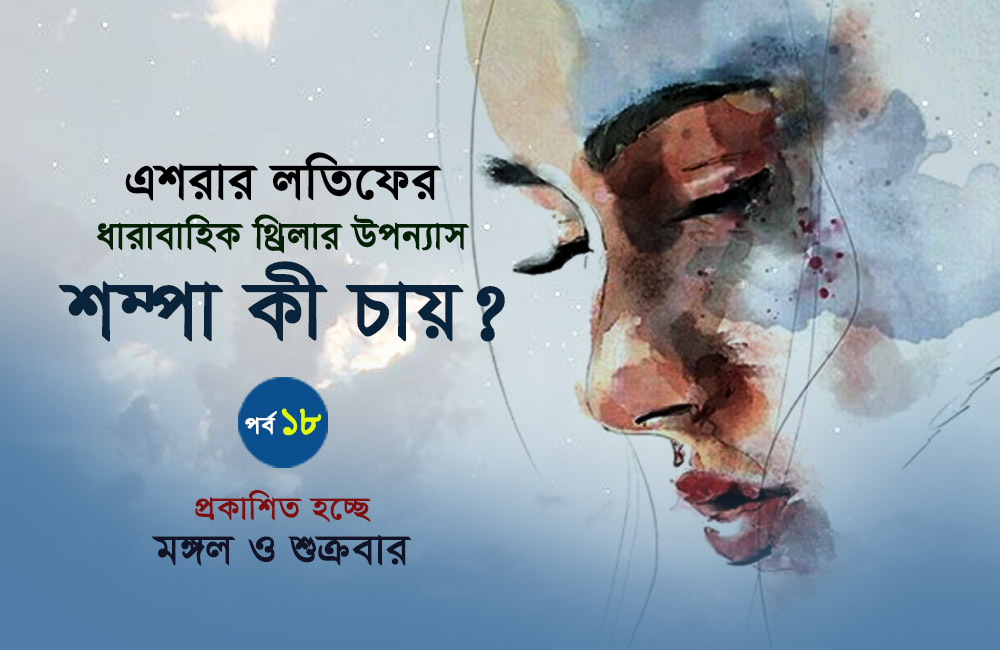







Leave a Reply
Your identity will not be published.