[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার স্মরণীয় নারী
বাংলার রেনেসাঁস আর রাজনীতি এই দুটো প্রক্রিয়ায় বাংলার নারীর অংশগ্রহণ (ধারা) প্রায় একই সঙ্গে শুরু হয়ে কখনো পাশাপাশি, কখনো জড়োজড়ি করে চলতে থাকে। প্রধানত তিন কারণে নারীরা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। প্রথমত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নারী পরাধীনতার গ্লানিতে বিদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নারীর এই অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেগবান হতে শুরু করে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে। দ্বিতীয় যে কারণ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায়, সেটা হলো আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে যখন নারী সমাজের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে গিয়ে বৃহত্তর জগতের জন্যে কিছু করার ব্যাপারে মনস্থির করে। ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির এক সহোদরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিয়ে করে অল্প কিছুদিনের জন্যে বিবাহিত থেকে বাকি জীবন বৈধব্য পালন (সেই সময় স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক বেশি; বিশেষ করে কুলীন সম্প্রদায়ের পাত্র হলে) করার চাইতে আজীবন কুমারী থাকা শ্রেয়। আর সেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি কখনো বিয়ে করেন নি। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ব্যক্তিগত জীবনের একটি সিদ্ধান্ত হলেও এটি একটি সামাজিক এবং নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। তৃতীয় যে কারণে অনেক নারী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, সেটা হলো, গতানুগতিক রাজনীতির (এক্ষেত্রে প্রধানত কংগ্রেস দল কেন্দ্রিক) কোন্দল ও স্বার্থপরতা এবং সন্ত্রাসী/বিপ্লবী দলের (যেমন যুগান্তর) দূরদৃষ্টিতার অভাব। কমিউনিজমের সঙ্গে পরিচয় ও জানাশোনা এই নতুন ও তৃতীয় পথের সন্ধান দেয়। মানবতার জয়গানমুখর শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন নিয়ে অনেক তরুণী রাজনীতিতে আশার আলো দেখতে পান এবং তা অর্জন করার জন্যে রাস্তায় নামেন। এঁরা কৃষক, শ্রমিক, প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার্থে সংগ্রাম করার জন্যে তাদের সাহস ও প্রেরণা যোগান এবং সকলকে একত্রিত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এই শেষোক্ত দল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাদের সাধারণ লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের এই বন্দি দশা থেকে মুক্তির পরিকল্পনাকেও যোগ করে নেন।
নারীদের দুই ধারার রাজনীতিতেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়— পার্লামেন্টারি রাজনীতি এবং বিপ্লবী বা সংঘাতময় রাজনীতি। তবে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের আগে যেহেতু মেয়েদের ভোটাধিকারই ছিল না এই অঞ্চলে, তখন পার্লামেন্টারি রাজনীতি করার সুযোগ ছিল খুবই অল্প। বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে মুক্তিকামী রাজনৈতিক নেত্রী ও কর্মীরা হয় অহিংস ও অসহযোগী আন্দোলন করেছেন অথবা করেছেন সন্ত্রাসী বিপ্লবী আন্দোলন।
সুনীতি চৌধুরী (১৯১৭-১৯৮৮) ও শান্তি ঘোষ (১৯১৬-১৯৮৯) প্রথম দুই নারী যাঁরা মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে ‘যুগান্তর’ দলের সদস্য হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করার দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন (১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর)। সেই সময় শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নবাব ফয়েজুন্নেসা স্কুলে কেবল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করার পরে তাঁরা হাতেনাতে ধরা পড়ে যান। সাবালিকা না হওয়ায় তাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে গান্ধীর আন্দোলনের মুখে সকল রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি পাওয়ার সময় শান্তি-সুনীতিও মুক্তি পান।
বীণা দাস তাঁর স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বড়বোনের কারাদণ্ড জনিত দুর্দশা আর লাঞ্ছনা দেখে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে যখন বাংলার অত্যাচারী গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে খুন করার কথা চলছে, বীণা দাস অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজটি গ্রহণ করেন। বীণার বড় বোন কল্যাণী দাস ও তার বান্ধবী কমলা দাসগুপ্ত ছিলেন বিপ্লবী বীণা দাশের অনুপ্রেরণা। বীণার জন্যে রিভলভারটি কমলাই যোগাড় করেন। মিশনের দিন বীণার জন্যে রিভলভার বহন করে তাঁর সঙ্গে ঘটনাস্থল অবধি হেঁটে যান কমলা দাসগুপ্ত। আর গভর্নরের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত নিজেই শাড়ির নিচে বন্দুকটি লুকিয়ে রাখেন। বীণার সঙ্গে দৃপ্ত পদক্ষেপে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সভাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বীণা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সামান্য আহত গভর্নর বেঁচে গেলেন। বীণা গ্রেফতার হলে কোর্টে গিয়ে এক নির্ভীক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন এবং রাজনৈতিক বন্দি তার বড় বোনের ওপর নির্দয় ব্যবহারের নিন্দা জানালেন। থানায় বহু অত্যাচার করলেও কে তাকে এই মিশনে সহায়তা করেছে এ ব্যাপারে কোনো নাম উচ্চারণ করেন নি। মুখ বুঁজে কারাদণ্ড মেনে নেন। এই দুই বোনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর প্রবল অত্যাচার নেমে আসে।
এর ঠিক পরেই ঘটে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, যেখানে মাস্টারদাকে সাহায্য করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। প্রীতিলতাদের বন্দুকের ট্রেইনিং দেন দীপালী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ। এর পরে ইউরোপিয়ন ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়লে প্রীতিলতা আত্মহত্যা করে পরিত্রাণ পান।
চল্লিশ শতকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে কৃষক বিদ্রোহ। জমিদারদের অন্যায্য ভাবে ফসলের অংশ দাবি ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা, যেমন ময়মনসিং অঞ্চলে মনি সিং, উত্তরবঙ্গে রানীমা ইলা মিত্র ও তাঁর স্বামী। এর ভেতর ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনার টংক বিদ্রোহে আটককৃত সহযোদ্ধা কুমুদিনী হাজংকে দলবল নিয়ে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সর্বপ্রথমে সাহসী নারী নেত্রী ও বীর যোদ্ধা রাসমণি হাজংসহ বেশ কয়েকজন হাজং সম্প্রদায়ের কৃষক। অন্যদিকে ইলা মিত্রকে ১৯৫০ সালে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় বন্দি অবস্থায় অতি হীন পদ্ধতিতে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার করে। তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চলানো হয় কথা বের করে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু তবু একটি কথাও বের কতে পারে না ইলা মিত্রের কাছ থেকে।
কলকাতা ও হাওড়ায় ধাঙড় ও পাটকল বিদ্রোহে সফল নেতৃত্ব দেন সন্তোষকুমারী, সাকিনা বেগম, দুখমৎ দিদি ও প্রভানতী দাসগুপ্ত। আইন অমান্য আন্দোলনে ও ব্রিটিশ ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন বহু নারী, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মনিকুন্তলা দেবী, অরুণা আসফ আলী, সরোজনী নাইডু, সরলাবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা, স্বর্ণকুমারী দেবী। গরিব কৃষক পরিবারের বিধবা নারী মাতঙ্গিনী অগাস্ট বিপ্লবে তমলুক থানা অভিযানে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ৭২ বছর বয়সে শহীদ হন। ননীবালা দেবী নিজে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও পার্টির কাজের খাতিরে শাখাসিঁদুর পরে এক সহযোদ্ধার স্ত্রী সাজতে দ্বিধা করেন নি। জেলখানায় তাঁর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার জন্যে ননীবালা একজন বিদেশি জেল কর্মকর্তার গালে চড় মেরেছিলেন। এসব সত্ত্বেও ননীবালাই বাংলার প্রথম নারী যিনি স্টেট প্রিজনারের মর্যাদা পেয়েছেন।
সন্ত্রাসী ও বিপ্লবী দল কিংবা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ছাড়াও গান্ধীর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন অনেক বিখ্যাত নারী নেত্রী—যেমন সরোজিনী নাইডু, সুচেতা কৃপালনী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী ও ভগ্নী যথাক্রমে বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দাশ, নেলী সেনগুপ্ত, দৌলতেন্নেসা, কাদম্বিনী বসু ও কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের সুযোগ্য কন্যা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। সরোজিনী নাইডু নারীদের ভোটাধিকারসহ আরও কিছু দাবি নিয়ে একদল নারী নেত্রীসহ সোজা ইংল্যান্ড গিয়ে নিজেদের দাবি সরাসরি পেশ করে এসেছেন ১৯১৯ সালে। বাংলার মেয়েরা ভোটের অধিকার পান ১৯২৯ সালে। ভোটের অধিকার না থাকায় সাংবিধানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারীরা বিংশ শতকের আগে কম আগ্রহী ছিলেন। আর তাই বিপ্লবী ও চরমপন্থীদের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিলেন তরুণ নারী সমাজ।
কাদম্বিনী বসু ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম কংগ্রেসের নারী সদস্য। ১৮৮৯ সালে তাঁরা প্রথম বাঙালি নারী যাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন বোম্বেতে। এর আগে অন্য কোনো অধিবেশনে কোনো নারী যোগ দেন নি। শুধু তাই নয় পরের বার, ১৮৯০ সালে, কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হলে সেখানে কাদম্বিনী বসু ইংরেজিতে চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে কোনো নারীর দেওয়া সেটাই প্রথম বক্তৃতা। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে সকলের অনুরোধে দেশাত্মবোধক ‘বন্দে মাতরম’ গানটি গেয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন সরলা দেবী চৌধুরানী। গানের প্রথম দুটি লাইনের সুর করেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বাকি পুরো গানটির সুর সরলা দেবী নিজেই করেন। আরেক কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ‘জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে’, দেশাত্মবোধক গানটি দ্বৈতকণ্ঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বোন অমলা দাশ ও সরলা দেবীর নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। স্বাধীনতার পরে এই গানটি জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুর দিতে সাহায্য করেন, বিশেষ করে যেগুলোতে বিদেশি গানের সুর ভেঙে বাংলা গানের নতুন সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। গানের ওপর প্রভূত দখল থাকায় সরলা রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানের স্বরলিপি করে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন।
১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড় আন্দোলনে’ সর্বভারতীয় ভূমিকা পালন করেন দুই বঙ্গললনা, অরুণা আসফ আলি ও সুচেতা কৃপালনী। ইতোমধ্যে হালিমা খাতুন ও রাজিয়া খাতুন নামে দুই গ্রামের মেয়ে ময়মনসিংহ থেকে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন, এবং আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর সাহসী ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার জন্যে স্বাধীন ভারতে অরুণা আসফ আলীকে দিল্লির প্রথম নারী মেয়র করা হয় এবং শান্তির জন্য তিনিই প্রথম নারী যিনি লেনিন পুরস্কার পান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে অরুণার মাথার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার্য করে ইংরেজ সরকার জানাতে বাধ্য হয়েছিল অরুণা গা ঢাকা দিলে তাঁকে খুঁজে বের করে জেলে পোরা কত কঠিন। স্বাধীনতাসংগ্রামে অভূতপূর্ব নেতৃত্ব দানের জন্যে স্বাধীন ভারতে সরোজিনী নাইডুকে প্রথম নারী রাজ্যপাল করা হয় উত্তরপ্রদেশে। সরোজিনীই প্রথম ভারত উপমহাদেশের নারী, যিনি ১৯২৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রথম নারী যিনি একটি রাজ্যের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। আরেকজন কংগ্রেস নেত্রী সুচেতা কৃপালনী স্বাধীনতার পরে প্রথম উত্তর প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী হন। কিন্তু পরে (১৯৬৩-১৯৬৭) তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই ভারতের কোনো রাজ্যের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী। ওদিকে সিলেটে এবং ঢাকায় সাতচল্লিশের আগে ও পরে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী ও দৌলতুন্নেসা। দৌলতুন্নেসা আবার একজন দক্ষ লেখক ও কবিও ছিলেন। এদিকে হেনা দাস শিক্ষকদের ও নারীর সুযোগ-সুবিধার জন্যে সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। সাতচল্লিশের স্বাধীনতাসংগ্রামে দেশী পণ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাবার জন্যে আশালতা সেন ও তাঁর সহকর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খদ্দর বিক্রি করেছেন। এ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে আশালতা সেন গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাশীল ছিলেন তাঁর কাজের ব্যাপারে।
ভাষাআন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ মাতৃভাষার জন্যে জীবন দান করেছেন। বায়ান্নর সংগ্রামে কোনো নারীকে আত্মাহুতি দিতে না হলেও সেই সংগ্রামে নারীরা চুপ করে বসে ছিলেন না। যাঁরা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, রাজিয়া খান আমিন, কুলসুম হক, মমতাজ বেগম, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, ইলা বকশী উল্লেখযোগ্য।
এ ছাড়া পূর্ব বাংলায় সামরিকতন্ত্র, স্বৈরশাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও তাদের দোসর ঘাতক-দালালদের নির্মূলের আন্দোলনে অনেক নারীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে অংশগ্রহণ করে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, বেগম ফজিলাতুন্নেসা, বেগম মুস্তারি শফি, নূরজাহান মুরশিদ, মনোরমা বসু, নীলিমা ইব্রাহিম, হামিদা হোসেন উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য নারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষ অবদাবের জন্যে কাউকে কাউকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। যেমন নারী ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ও গণবাহিনীর তারামন বিবি।
নিচে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন এমন নারীদের একটি তালিকা দেওয়া হলো। এর বাইরেও অনেক নারী রয়ে গেলেন বাংলায় যাঁরা রাজনীতিতে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। এই তালিকা তাই সম্পূর্ণ না হলেও অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করে তখনকার রাজনীতি-সচল নারীবৃন্দের।
১. অরুণা আসফ আলী (১৯০৯-১৯৯৬)
২. আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৭২)
৩. ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)
৪. ঊর্মিলা দাশ (১৮৮৩-১৯৫৬)
৫. কমলা দাসগুপ্ত (১৯০৭-২০০০)
৬. কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫)
৭. কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) (১৮৬১-১৯২৩)
৮. জাহানারা ইমাম (১৯২০-১৯৯৪)
৯. জোবেদা খাতুন চৌধুরানী (১৯০১-১৯৮৬)
১০. জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৪৫)
১১. দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯১৮-১৯৯৭)
১২. নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩)
১৩. নেলী সেনগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭৩)
১৪. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২)
১৫. বদরুন্নেসা আহমেদ (১৯২৭-১৯৭৪)
১৬. বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪)
১৭. বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬)
১৮. বেগম ফজিলাতুন্নেসা রেণু (১৯৩০-১৯৭৫)
১৯. ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৫-১৯১১)
২০. মনিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭)
২১. মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২)
২২. মেহেরুন্নেসা (১৯৪০-১৯৭১)
২৩. রানী রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১)
২৪. রাশমণি হাজং (১৮৯৮-১৯৪৬)
২৫. লীলা (লীলাবতী) নাগ (রায়) (১৯০০-১৯৭০)
২৬. শান্তি ঘোষ (১৯১৬-১৯৮৯)
২৭. সন্তোষকুমারী (১৮৯৭-১৯৮৯)
২৮. সরলা দাশ (রায়) (১৮৬১-১৯৪৬)
২৯. সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)
৩০. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)
৩১. সারা তৈফুর (১৮৮০-১৯৭১)
৩২. সুচেতা কৃপালিনী (১৯০৮-১৯৭৪)
৩৩. সুনীতি চৌধুরী (১৯১৭-১৯৮৮)
৩৪. সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)
৩৫. সেলিনা পারভীন (১৯৩১-১৯৭১)
৩৬. সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩)
৩৭. হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮-১৯৬২)







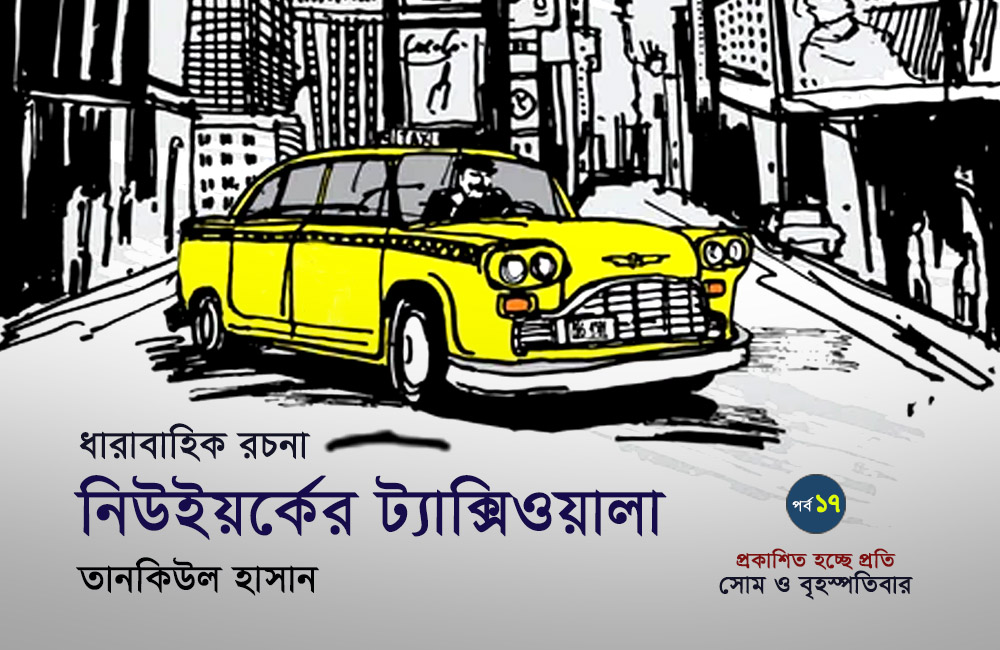

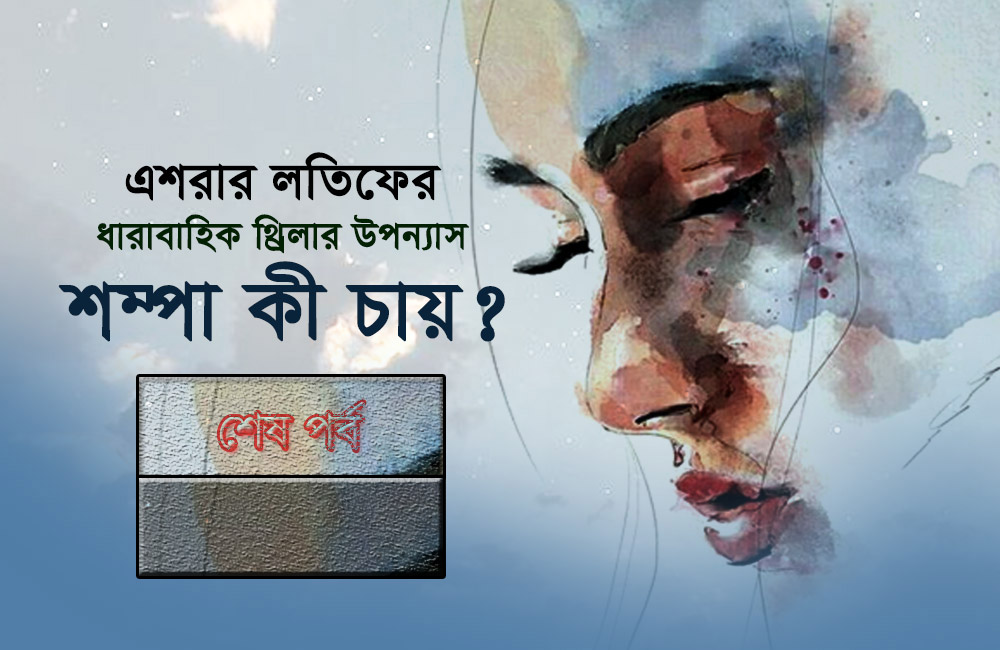





Leave a Reply
Your identity will not be published.