[বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। তাঁর আগমনে বাংলা চলচ্চিত্র হয়েছে সমৃদ্ধ, পেয়েছে নতুন ঘরানা। আগামীকাল ১৪ মে তার ১০২তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এই বিশেষ রচনাটি পত্রস্থ হলো।]
চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন সম্পর্কে চলচ্চিত্র সমালোচক সোমেন ঘোষের ভাষ্য হচ্ছে, “আধুনিক সিনেমার নানা টেকনিক মৃণাল সেনের ছবিতে বহুল পরিমাণে দেখা গেছে। সেই সঙ্গে টেকনিকের রীতি লঙ্ঘনেও মৃণাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারেন।”
মৃণাল সেন ১৯২৩ সালের ১৪ মে বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ট্রেড ইউনিয়জম করে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। শব্দগ্রাহক হিসেবে কাজ শেখার মধ্য দিয়ে এই মাধ্যমটিকে বোঝার চেষ্টা করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে নিমার্ণ করেন ‘রাতভোর’। মৃণাল সেনের এই প্রথম চলচ্চিত্রকর্মটি শৈল্পিক ও ব্যবসায়িক উভয় দিক থেকে নিদারুণভাবে ফ্লপ করে।
‘রাতভোর’ (১৯৫৫)-এর পরে মৃণাল সেন চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ‘নীল আকাশের নিচে’ (১৯৫৮)-র চিত্রনাট্য লেখার সূত্রে আবার পা রাখেন এখানে এবং শুধু চিত্রনাট্য লেখকই নয়, ছবি পরিচালনার সুযোগও লাভ করেন। অবশ্য ‘নীল আকাশের নীচে’-তেও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে নানা ক্রুটি ছিল। যদিও ছবিটির একটা রাজনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। যাহোক, ‘নীল আকাশের নিচে’ ব্যবসায়িকভাবে সফল হলে পায়ের নিচে মাটি খুুঁজে পান মৃণাল সেন এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তৈরি করেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৯৬০)। এটি তাঁর প্রথম আদ্যন্ত শিল্পচেতনায় জারিত ছবি। বস্তুত, এ ছবি থেকেই এক নতুন মৃণাল সেনের যাত্রা শুরু। চলচ্চিত্র ভাষায় যাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য।
প্রায় চল্লিশ বছরের চলচ্চিত্রজীবনে ছাব্বিশটি কাহিনিচিত্র, একটি প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যরে ছবি এবং টিভি ফিল্ম নির্মাণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে : বাইশে শ্রাবণ (১৯৬০), পুনশ্চ (১৯৬১), আকাশ কুসুম (১৯৬৫), ভুবন সোম (হিন্দী) [১৯৬৯], ইন্টারভিউ (১৯৭০), কলকাতা ৭১ (১৯৭২), পদাতিক (১৯৭৩), কোরাস (১৯৭৪), মৃগয়া (১৯৭৬), একদিন প্রতিদিন (১৯৭৯), আকাশের সন্ধানে (১৯৮০), চালচিত্র (১৯৮১), খারিজ (১৯৮২), খান্ডাহার (হিন্দী) [১৯৮৩], মহাপৃথিবী (১৯৯১), অন্তরীণ (১৯৯৩) প্রভৃতি।
সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ থেকে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র নির্মাণ। এজন্যেই তিনি বক্তব্য প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন।
চলচ্চিত্রকার হিসেবে মৃণাল সেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয় কিংবা আঙ্গিকে এক জায়গায় তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। “ক্রমশ ছড়িয়ে দেন নিজেকে তবে সর্বদাই ব্যক্তি ও মানুষের মুক্তির কথা বলেন। কখনো অভ্যাস থেকে, বদ্ধ খাড়ী থেকে মুক্তি, কখনো ইতিহাস পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। কখনো প্রত্যক্ষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তি—নির্বিশেষ মানবিকতার সঙ্গে তিনি শ্রেণিগত মানবিকতাকে মেলান বলেই, মৃণাল সেন যান্ত্রিক হয়ে পড়েন না”।১ শুধু তাই নয়, বিষয়ের দিক থেকে মৃণাল সেন কখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। “সরকারি ব্যুরোক্রাট, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে আদিবাসী পর্যন্ত তাঁর অবাধ যাতায়াত। আর সবক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখেন অব্যর্থভাবে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে ফিল্মের গঠনে অঙ্কিত করেন সামাজ্যবাদ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব সবই উঠে চলচ্চিত্রের ফ্রেমে। ব্যক্তিকে চিত্রায়িত করেও বোঝেন ব্যক্তির মৃত্যু হবে, কিন্তু মানুষের মৃত্যু নেই। এই মানুষের জয় ঘোষণা মাঝে মধ্যে তিনি নাটুকেভাবেই করেন, কিন্তু নাটক তো মানুষেরই অংশ”।২ এ প্রসঙ্গে ‘ভুবন সোম’ (১৯৬৯), ‘কলকাতা ৭১’ (১৯৭২) ও ‘মৃগয়া’ (১৯৭৬)—এই তিনটি ছবি বিশেষভাবে স্মরণীয়।
মৃণাল সেনের নির্মিত ছবিগুলোকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে মৃণাল সেন একটা বিশেষ যুদ্ধোত্তর অবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন, ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৯৬০), ‘পুনশ্চ (১৯৬১) ছবি দুটিতে যথাক্রমে গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে পুরুষশাসিত সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। ‘প্রতিনিধি’-তে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ, সন্তান ও বি-পিতার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ওপর প্রভাব প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে।
দ্বিতীয় পর্বে মৃণাল সেন অনেক বেশি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছবি করেছেন। সত্যি বলতে কী, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের অগ্রপথিক তিনি। ‘কলকাতা ৭১’-এর মাধ্যমে এ ধারা চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু। অবশ্য এর আগে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে গণমানুষের রাজনৈতিক জীবন স্থান পায় নি, এ কথা বলা যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে সচেতন ও সার্থকভাবে ধারণ করে প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কৃতিত্ব মৃণাল সেনের। ‘কলকাতা ৭১’, ‘পদাতিক’, ‘কোরাস’-এ ক্রমশ মৃণাল সেনের রাজনৈতিক ভাবনার গভীরতা ধরা পড়ে।
তৃতীয় পর্বে আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর চারপাশের মানুষজনকে দেখেছেন। ‘একদিন প্রতিদিন’ (১৯৭৯), ‘চালচিত্র’ (১৯৮১), ‘খারিজ’ (১৯৮২)-এ কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা ও মানসিকতা প্রকাশে মৃণাল সেনের গভীর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন দক্ষ সার্জনের মতো কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ-দেহের ব্যবচ্ছেদ করে এর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।
চতুর্থ পর্বে প্রবেশ করেছেন মৃণাল সেন ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৯১),-র মধ্য দিয়ে। এখানে তিনি তখনকার দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর চেহারা তুলে ধরেছেন, মানুষের বিচ্ছিন্নতা, অস্থিরতা, পরস্পরের প্রতি একটা প্রচণ্ড বিশ্বাসহীনতা—সমগ্র টালমাটাল বিশ্বের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।
এবার নির্মাণশৈলীর প্রসঙ্গ। এ ক্ষেত্রে মৃণাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের সচেতন ও নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্রকার। “যে এক্সপেরিমেন্ট তিনি আঁকড়ে ধরেন, তার মূলকথা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। কখনো গল্প বোনেন, প্রচলিত ন্যারেশনকেই অবলম্বন করেন, আবার প্রয়োজনে গল্প ত্যাগ করেন। ফর্মের চাপে বিষয়কে ফেরান—কখনো একটি ব্যক্তি তাঁর থিম, কখনো সমূহ, কখনো আদ্যন্ত একটি বিষয়ের ফ্রেমে ফিল্মকে ধরেন, কখনো এপিসোডের আপাত বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বিন্দুকে মেলান কোলাজ পদ্ধতিতে। কেবল বৃদ্ধি নয়, হৃদয়কে সংযত করা নয়, গভীরভাবে অনুভূত আবেগকেও তিনি ফিল্মের শুদ্ধ পরিবেশ গঠনে প্রয়োজনীয় মনে করেন”।৩
চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলীর ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রথাসিদ্ধ নিয়মকে প্রথম ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন ফ্রান্সের নবতরঙ্গের নির্মাতারা (যেমন, ক্রফো. গদার), বাংলা চলচ্চিত্রে মৃণাল সেনও এক সময় ধ্রুপদী ঢং থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, প্রথাসিদ্ধ নিয়মকে ভেঙেছিলেন। কেননা তাঁর মতে, “সিনেমা এমন একটা মিডিয়াম যার সবকিছুই, তার ভাষা, তার ব্যকরণ, সবকিছুই নির্ভর করে যা দিয়ে তা তৈরি হয় তার ওপর। অক্ষর দিয়ে যে সাহিত্য তৈরি হয় তার যেমন পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ আগে যেভাবে উপন্যাস লেখা হতো এখন সেভাবে লেখা হয় না, তার রং ঢং সবই পাল্টেছে, চিরকালই পাল্টেছে। আজ যখন জেমস জয়েস পড়েন তখন তার সঙ্গে ডিকেন্সের কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবা ডারেল যখন পড়েন চসারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মার্গারেট ডুরাসের সঙ্গে কিংবা নাতালি সারোদের সঙ্গে কিংবা ভার্জিনিয়া উলফের সঙ্গে টমাস মানের মিল পাবেন না। তারাও যেমন নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন...ফিল্মে এই পরিবর্তন আরও বেশি আসতে পারে”।৪ তাই তো বাংলা চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে পরিবর্তন এসেছে, মৃণাল সেন নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। “ফ্রিজের একাধিক ব্যবহারে কাট-এর অধিক গুরুত্বে ‘আকাশকুসুম’ আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা সিনেমায় অনেকটা নতুন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যন্তরে উপনীত হওয়ার সময়কে মৃণাল সেন এ ছবিতে নানা কৌশলে ভেঙে নিয়েছেন ব্যক্তিগত শিল্পভাবনায়”।৫ ‘ইন্টারভিউ’-এর আঙ্গিক আরও পরীক্ষামূলক, ফর্মের যে যাতায়াত দেখা গেল এবং “গদার যেমন প্রতি মুহূর্তে তাঁর দর্শকের অনুভূতির ওপর আঘাত করেন, মৃণাল সেন অনুরূপভাবে তাঁর দর্শকদের চেতনাকে বিপর্যস্ত করেছেন। এমনকি তাঁর আধুনিক ছবি সত্তরের অন্যতম রাজনৈতিক নির্মিত ‘পদাতিক’-এ তিনি বিভিন্ন জীবিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষকে ছবির পর্দায় এনে সরাসরি ওহঃবৎারবি করেছেন ছবিরই একটি চরিত্রের মাধ্যমে। বাংলা চলচ্চিত্রে এই রীতি ভাঙার ব্যাপারটা তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন গদার থেকে”।৬ অবশ্য শুধু গদারই নয়, ক্রুফো (‘আকাশ কুসুম’-এর কয়েকটি ফ্রিজশট ক্রুফোর ‘জুল এন্ড জিম’ ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়), আন্তনিও (‘প্রতিনিধি’তে চরিত্রের অন্তর্লীন সংকট আন্তনিওয়নির ‘লা নোত্তে’ বা ‘লাভেন্তরা’-র প্রধান চরিত্রসমূহের কথা মনে করিয়ে দেয়—যারা সকলেই অন্তর্মুখিনতার দ্বন্দ্বে পীড়িত) এবং এ্যান্ডারসনের দ্বারাও মৃণাল সেন প্রভাবিত হয়েছেন এবং ‘আকালের সন্ধানে’ ছবিটিকেও আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন ধরনের ছবি বলা যায়, কেননা এটি হচ্ছে সিনেমার ভেতরে সিনেমা—যা ভারতীয় ছবি (যদিও এই ফর্মে বিশ্ব চলচ্চিত্রে দুটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র রয়েছে—একটি ফেলিনির ৮১/২, অন্যটি ক্রফোর ‘ডেজ ইন নাইট’)।
মৃণাল সেন এমন একজন সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার—যিনি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাঙালি চলচ্চিত্রকারের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা ভারতীয়, কেননা তিনি বাংলা ছাড়াও—ওড়িয়া, হিন্দী, তেলেগু—এই তিনটি ভাষায় ছবি নির্মাণ করেছেন।
রাজনৈতিক ধারার ছবি নির্মাণের অগ্রপথিক মৃণাল সেন। চলচ্চিত্রে তিনি গল্প বলার চেয়ে প্রবন্ধধর্মীতা আনার চেষ্টা করেছেন। যদিও পুরোপুরি সার্থক ও সফল হন নি। পাশাপাশি আবার এটাও উল্লেখ্য, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বরূপ উন্মোচনে তাদের স্ববিরোধীতাকে আঘাত করার ব্যাপারে মৃণাল সেনের ভূমিকা স্মরণীয়।
সহায়ক রচনা
১. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : ভুবন সোম থেকে মৃগয়া / সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল, কলকাতা, পৃ. ১২৪
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০-১২১
৪. চিত্রবীক্ষণ, মৃণাল সেন সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল-মে ১৯৯৩, পৃ. ২০
৫. সোমেন ঘোষ, বাংলা সিনেমার পালাবদল, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
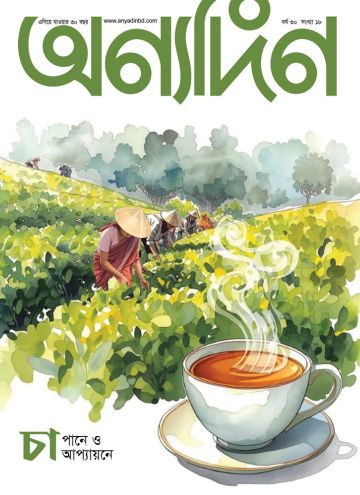











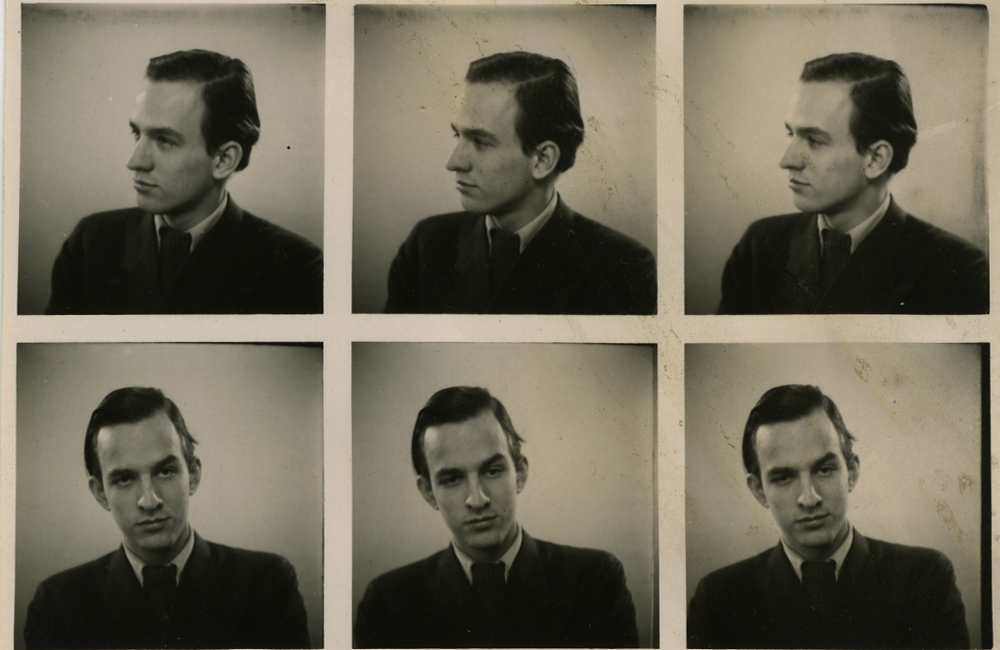


Leave a Reply
Your identity will not be published.