[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
বাংলার নবজাগরণে সক্রিয় সহোদরা
বাংলার নবজাগরণের সময় দেখা গিয়েছে প্রগতিশীল পিতামাতার কেবল একটি কন্যা নয়, দুটি বা ততধিক কন্যাই কোনো সৃজনশীল কাজে অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনে কিংবা নারীকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অনেক সময় পরিবারের এক মেয়ে অন্য মেয়ের কাছে প্রেরণা বা আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। যেমন, অবলা বসুর কাছে সরলা রায় (দাশ), বেগম রোকেয়ার কাছে করিমুন্নেসা খানম, বীণা দাসের কাছে কল্যাণী দাস।
অরু দত্ত ও তরু দত্ত : খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন পিতা গোবিন্দ চন্দ্র। দুই বোন অরু ও তরু দত্ত। সুশিক্ষা, উন্নত রুচি ও শাণিত মানসিকতা গঠনের জন্যে তাদের পিতা দুই কন্যাকে খুব অল্পবয়সে (১৮৬৯ সালে) ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে দেন। তাঁরাই সম্ভবত প্রথম বাঙালি নারী উচ্চশিক্ষার্থে যাঁরা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে যান। তাঁরাই বাঙালি নারীদের ভেতর প্রথম যাঁরা ইংরেজি ও ফরাসি কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তরু দত্ত অনেক ফরাসি কবিতা ও লেখার অনুবাদ করেন। দুজনেরই অকাল মৃত্যু হয়। তরুর অধিকাংশ মৌলিক কবিতা ও ফরাসি থেকে অনূদিত কবিতা ও রচনা তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তরু দত্তের লেখা Le Journal de Mademoiselle d’Arvers (1879) ফরাসি ভাষায় কোনো বাঙালির লেখা প্রথম উপন্যাস এবং Bianca, or the Young Spanish Maiden (1879) ইংরেজিতে লেখা কোনো বাঙালি নারীর প্রথম উপন্যাস।
চন্দ্রমুখী বসু ও বিধুমুখী বসু : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে নারী প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন, তাঁর ছোট দুই বোন বিধুমুখী ও বিন্দুবাসিনী পরে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেন। তাঁদের পিতার নাম ভুবনমোহন বসু। এঁরা দেরাদুন প্রবাসী বাঙালি। চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৮১ সালে পাস করেন এফএ, ১৯৯৩ সালে বেথুন কলেজ থেকে বিএ ও ১৮৮৪ সালে এমএ ডিগ্রি করেন। তারপর বেথুন কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। বেথুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হলে তিনি কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। ১৯০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম যে দুজন নারী ১৮৮৮ সালে যে এমবি ডিগ্রি লাভ করেন, তাঁদের একজন বিধুমুখী বসু, অপরজন ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। প্রকৃতপক্ষে ভার্জিনিয়া পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯০৪ সালে মেরীর বিয়ে হয় পূর্ণচন্দ্র ননীর সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি তাঁর স্বামীর নারী রোগীদের পরীক্ষা করতেন, চিকিৎসাও করতেন। কিন্তু তিনি নিজে স্বতন্ত্রভাবে প্র্যাকটিস করতেন না। তখনকার দিনে নারীরা সাধারণত কেউ তা করত না। বিধুমুখীও করেন নি।
অবলা বসু (দাশ) ও সরলা রায় (দাশ) : বিক্রমপুরের প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাশের দুই কন্যা সরলা ও অবলা দাশ। দুজনেই নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণে বহুমাত্রার কাজ করে গেছেন। সরলা দাশ কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে ভারতের নারীদের মধ্যে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে অনুমতি পান। ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। সমাজসংস্কারক, নারী-প্রগতির পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উইলিয়াম মার্কবি কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাশকে (বিবাহের পরে সরলা রায়) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি হন শর্তসাপেক্ষে। যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পপ নিলেন ইংরেজির, অধ্যাপক রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিলেন ইতিহাসের, অধ্যাপক গ্যারেট নিলেন গণিতের আর পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিলেন বাংলার পরীক্ষা। দুজনেই যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সরলা দাশ শেষ অবধি আর প্রবেশিকা পরীক্ষাটি দিতে পারেন নি। পরীক্ষার ঠিক আগে আগেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ প্রসন্ন কুমার রায়ের সঙ্গে সরলার বিয়ে হয়ে যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না সরলার। অল্পবয়সেই সরলা বিধবা হন। ভারতের প্রথম বিমান বাহিনী প্রধান সুব্রত মুখার্জী, যাঁকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনক বলা হয়, সরলা ও প্রসন্নের দৌহিত্র (কন্যর পুত্র)। স্বামীর মৃত্যুর পর কারও মুখেপেক্ষি না হয়ে সরলা তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের তত্ত্বাবধান করে আর ওই স্কুলের হোস্টেলে বসবাস করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন, আর নারীদের বিশেষ করে বিধবাদের নানাবিধ সমস্যার বাস্তব সমস্যা খুঁজে বেড়ান। স্ত্রী-শিক্ষার জন্যেও তিনি অনেক আত্মত্যাগ করেন। নিজের গয়না বিক্রি করে স্কুলের ঋণ পরিশোধ করেন। সরলা প্রথম বাঙালি নারী যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য হন। সরলা রায়ের অনুরোধে সখীসমিতির জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ‘মায়ার খেলা’ নৃত্যনাট্যটি লিখেছিলেন। বেথুন কলেজে ‘মায়ার খেলা’ মঞ্চস্থ করে সরলা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখীসমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।
সরলাকে অবলা সব সময় তাঁর জীবনের আদর্শ ও কর্মের প্রেরণা মনে করতেন। অবলা বসুকে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করল না নারী বলে, তখন অবলা ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে মেডিকেলে প্রথমে ভর্তি হন। সেই হিসেবে অবলাই পুরো উপমহাদেশের প্রথম নারী, যিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ অসুস্থতার জন্যে তিনি মেডিকেলে পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি। ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি। জগৎদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রবসু অবলাকে দেখে পছন্দ করলেন, এবং তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। জগদীশ চন্দ্র যত দিন বেঁচে ছিলেন এবং দেশে বিদেশে যখন যেখানে যেতেন ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে থাকতেন অবলা। জগদীশ চন্দ্র বসু ও অবলার ঘনিষ্ঠ দুই পারিবারিক বন্ধু হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিস্টার নিবেদিতা। শিলাইদহের পদ্মার ওপরে বোটে বা কলকাতায় জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়িতে কিংবা জোড়াসাঁকোয় এই আসর বা আড্ডাগুলো হতো। এখানে আরও আসতেন চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমলা দাশ, সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা চৌধুরানী, সাহানা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য লেখা কোনো রচনা বা কবিতা পড়তেন, আর সকলে তার ওপর আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে গান শোনাও হতো। কথা ও সুরের ওপর বিভিন্ন বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রধানত হালকা ঢঙের হাস্যরসাত্মক গানই বেশি গাওয়া হতো। উল্টোটাও যে হতো না, তা নয়। এইসব সাহিত্য-সংগীত আড্ডা প্রথমে ‘ডাকাতের দল’, পরে ‘খামখেয়ালী সভা’ বলে আখ্যায়িত ছিল। আড্ডাস্থলের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, কলকাতার রাস রোডের চিত্তরঞ্জনের বাড়ি, জগদীশচন্দ্রের কলকাতার বাড়ি বা শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কিংবা পদ্মার ওপরে বড় নৌকা, কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের কলকাতার বাড়ি কিংবা ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আসতেন তাঁর বাসায়।
কল্যাণী দাস ও বীণা দাস : নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রিয় শিক্ষক ছিলেন বীণা ও কলাণী দাসের পিতা বেণীমাধব দাস। দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী পিতার ঘরে জন্ম নেওয়া এই দুই কন্যা প্রথমে গান্ধীর অহিংস পথেই রাজনীতির দীক্ষা নেন। কিন্তু পরে বিপ্লবী পার্টির সদস্য হিসেবে আস্তে আস্তে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কল্যাণী দাসকে পুলিশ যখন গ্রেফতার করে, তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁর হাতব্যাগে বিপ্লবী পার্টির একটি গোপনীয় মিটিংয়ের লিফলেট ছিল। এই লঘু অপরাধের জন্যে কল্যাণীকে ধরে নিয়ে গিয়ে, একজন স্নাতক পাস, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে সাধারণ কয়েদির চাইতেও দুঃসহ খারাপ অবস্থায় রাখে। তাঁকে প্রতিবার দেখতে গিয়ে ক্রোধে, প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে বীণা। অবশেষে ১৯৩২ সালে বীণা দাস তাঁর জীবনের সবচাইতে দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করার। তাঁকে বন্দুক দিতে এবং পাশে থেকে এই কাজে সাহায্য করতে রাজি হন বীণার বড় বোন কল্যাণীর বন্ধু কমলা দাসগুপ্ত। কিন্তু বীণা স্ট্যানলিকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লেও টার্গেটমতো গুলি ছুড়তে ব্যর্থ হন এবং কারাবন্দি হন। কোর্টে যে সাহসিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তৃতা দেন, তা অভাবনীয় দৃঢ় ও শক্তিশালী একটি বক্তৃতা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলেও ১৯৩৯ সালে গান্ধীর মধ্যস্থতায় অন্য অনেকের সঙ্গে ছাড়া পান। শেষ বয়সটা হরিদ্বারে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন।
শান্তা দেবী ও সীতা দেবী : সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘প্রবাসী’ যা এলাহাবাদ থেকে বেরুত, এখানে শুধু রবীন্দ্রনাথই নন সমসাময়িক সকল প্রথিতযশা ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের লেখা ছাপা হতো। সেই পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি প্রথম লেখকদের রচনা প্রকাশের জন্যে সম্মানীবাবদ অর্থ দিতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ রচনা তিনি ধারাবাহিকভাবে ‘প্রবাসী’তে ছাপাতেন এবং নিয়ম করে সব লেখার জন্যে সম্মানী পাঠিয়ে দিতেন। রামানন্দের দুই কন্যা শান্তা দেবী ও সীতা দেবী। রবীন্দ্রনাথ তাদের দুজনকেই খুব স্নেহ করতেন এবং তাদের গান শেখাবার চেষ্টা করেছেন। দুই বোনই স্কুলে থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তারা দুজনে মিলে হিন্দুস্তানী উপকথার অনুবাদ করেন এবং সংযুক্তা দেবী এই ছদ্মনামে তাঁদের উপন্যাস ‘উদ্যানলতা’ রচনা করেন। অতঃপর শান্তা দেবী প্রচুর গল্প লিখেন আর সীতা দেবী সেই গল্পগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এই অনুবাদ গল্পগুলো ‘টেলস অব বেঙ্গল’ নামক গ্রন্থে প্রকাশ করে। ১৯১৭ সালে সীতা শান্তিনিকেতনে থেকে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ সালে ইনি ‘কল্লোল যুগ’ ও ‘প্রবাসী যুগের’ বিখ্যাত লেখক সুধীর কুমার চৌধুরীকে বিয়ে করেন। সীতাদেবী সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম ‘মঁটির বাসা’, ‘ক্ষণিকের অতিথি’ ও ‘মাতৃঋণ’।
বেগম রোকেয়া ও করিমুন্নেসা খানম : রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম দুই সহোদরার। করিমুন্নেসা তাঁর অনুজা রোকেয়ার মতো অত জনপ্রিয় না অলেও জানা যায়, তিনি একজন কবি ও সমাজসেবী হিসেবে তৎকালীন জনপদে পরিচিত ছিলেন। উর্দুভাষী পরিবারে লালিতপালিত হলেও নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বিপুল দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন টাঙ্গাইলের জমিদার। ‘বিষাদসিন্ধু’খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন এই এস্টেটের ম্যানেজার। মীর মশাররফ ‘বিষাদসিন্ধু’র প্রথম সংস্করণটি করিমুন্নেসার নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। করিমুন্নেসা আহমদী’ বলে একটি পত্রিকা বের কতেন। ‘দুঃখতরঙ্গিনী’ ও ‘মানস বিকাশ’ নামে তাঁর দুটি কবিতার গ্রন্থ রয়েছে। বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলমান মেয়েদের নারী জাগরণের পথিকৃৎ, নারীর প্রতি বৈষম্য অবিচারের বিরুদ্ধে বহু সাহসী লেখার রচয়িতা। মুসলমান মেয়েদের জন্যে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমরিয়াল স্কুল খোলেন এবং তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র জোগাড় করার চেষ্টা করেন। বেগম রোকেয়া তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মতিচুর’ অগ্রজা করিমুন্নেসাকে উৎসর্গ করেন।
সরলাবালা দেবী চৌধুরানী ও হিরন্ময়ী দেবী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন সুসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, নারীনেত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই সুযোগ্যা কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী চৌধুরানী। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা তাঁরা। সরলা বারো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রথমে মায়ের সঙ্গে এবং পরে দুই বোন মিলে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। স্বর্ণকুমারীর প্রতিষ্ঠিত সখীসমিতির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হিরন্ময়ী দেবী। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সখীসমিতি সক্রিয় ছিল। তারপর হিরন্ময়ী বিধবা আশ্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হিরন্ময়ী দেবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরে একটি বিধবা আশ্রম চালু করেন। এই আশ্রমের নাম ছিল ‘মহিলা বিধবা আশ্রম’। হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর এই আশ্রমটিরই নতুন নামকরণ হয় ‘হিরন্ময়ী বিধবা আশ্রম’। জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ১৮৮৭ সালে হিরন্ময়ী ও সরলা দেবী চৌধুরানী, দুই বোন, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সর্বপ্রথম ঘটা করে পালন করেন ৪৯ নম্বর পার্কস্ট্রিটে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে। এই অনুষ্ঠানেই জন্মতিথির সংখ্যা অনুসারে মোমবাতি জ্বালাবার প্রথা চালু করেন হিরন্ময়ী। সরলাদেবী চৌধুরানী একসময় সর্বভারতীয় নেত্রী হিসেবে সারা দেশে পরিচিতি পান। সংগীতে তাঁর পারদর্শিতা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রসংগীতের বেশ কয়েকটির সুরসংযোজনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করেন, বিশেষ করে যেগুলো বিদেশি গানের সুর থেকে রূপান্তরিত করা। রবীন্দ্রসংগীতের সুর পিয়ানোতে ধরতেও সাহায্য করেন সরলা। তিনি বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি রচনা করে দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ায় তিনি ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ পুরস্কার পান। ১৯২৫ সালে তিনি নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতির সভানেত্রী হয়েছিলেন। ‘জীবনের ঝরাপাতা’ তাঁর লেখা আত্মজীবনী।
প্রচারবিমুখ, কাজপাগল বড়বোন হিরন্ময়ী সরলার কর্মজীবনে ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রেরণা। ১৯৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ‘ভারতী’ পত্রিকায় সরলা অকপটে লিখেছেন, ‘কাশিয়াবাগানগৃহে পল্লীর গৃহস্থ মেয়েদের জড় করিয়া তিনি (হিরন্ময়ী) একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। তিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমি হইলাম তাঁর সহকারিণী। তখন তাঁহার বয়স পনেরো, আমার বয়স এগারো। আমরা নিজেরা তখন দিনেরবেলা বেথুন স্কুলে পড়ি, সকালে সন্ধ্যায় বাড়িতে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত ওস্তাদ ও মেমের কাছে ইস্কুলের পড়া ছাড়া সংস্কৃত, গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি, আর ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই অপরাহ্ণে সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা রীতিমতো ইস্কুল চালাই। বাঙ্গলা, ইংরাজি, অঙ্ক ও সেলাই এই চারটি বিষয়ই শেখানো হইত। প্রায় গুটি কুড়িক মেয়ে আসিত, কেহ কুমারী, কেহবা বাল্যবিধবা। চাঁদনির সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে বসিত। জায়গাটি ছিল শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে। খিড়কি দুয়ার দিয়া পাড়ার বৌ-ঝিরা মল ঝুমঝুম করিয়া পুকুরে জল তুলিতে নিত্য আনাগোনা করিত। তাই বোধ হয় হিরন্ময়ীর মনে তাদের জড় করিয়া পড়ানোর কল্পনা উদয় হয়। জোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের প্রতিদিন সমাগম হইত। আমরা তাঁহাদের কারও কারও দ্বারা মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করাইতাম, প্রাইজ দেওয়ার সমারম্ভেরও ত্রুটি হয় নাই। দিদির বিবাহের পর আমি একলা কিছুকাল সে স্কুল চালাইয়াছিলাম। যখন আমার এন্ট্রান্স পরীক্ষার সময় ঘনীভূত হইল তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইল।’
কুলসুম হুদা ও রাজিয়া খান আমিন : রাজিয়া খান আমিন, দুর্দান্ত প্রতাপশালী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ফ্যাশনদুরস্ত এই নারীর ববকাটা চুল, হাতকাটা ব্লাউজ, পরিধানে, দামি সিল্কের শাড়ি, অল্প মেকআপ। বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পের বই লিখেছেন। তিনি চার বড় নগরের কন্যা। কলকাতা মহানগরে স্কুলজীবন, করাচি মহানগরে কলেজজীবন, ঢাকা মহানগরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, ঢাকা ও লন্ডন শহরে কর্মজীবন। ’৭৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। রাজিয়া খান আমিন ‘দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার’ পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৯৫৭-৫৮ সালে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের নামকরা ছাত্রী ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজিতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ‘পাকিস্তান অবজারভার’ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন রাজিয়া খান ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬৫ থেকে ২০০২ সাল প্রায় ৩৮ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দখল ছিল অসাধারণ।
কুলসুম হুদা, প্রাক্তন এমপি ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য। রাজিয়া খান ও তার বড় বোন কুলসুম হুদা ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষাআন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আন্দোলন, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতা ও মিছিল করেছেন। রাজিয়া খান ও কুলসুম হুদা, দুজন সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমতী নারী, ১৯৫২-৫৪ সালে বাংলা ভাষার সমর্থনে ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন। টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের ৪০ বছরের বেশি সময় সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি মুকুল বলেছেন, ‘রাজিয়া খান ও কুলসুমের ভাষাআন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ ও যুক্তফ্রন্টের জনসভায় বক্তৃতা শুনে আমরা তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি।’ রাজনৈতিক আন্দোলন বা নারী জাগরণের বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি রাজিয়া খান আমিন সাহিত্য রচনার মাধ্যমেও সুনাম অর্জন করেন। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে ‘বটতলার উপন্যাস’, ‘হে মহাজীবন’ উল্লেখযোগ্য।
ঊর্মিলা দাশ, অমলা দাশ ও তরলা দাশ : বিক্রমপুরের ভুবনমোহন দাশের আট সন্তানের মধ্যে তিন বিখ্যাত কন্যা—ঊর্মিলা, অমলা ও তরলা। ভুবনমোহনের অপর সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সংগীত ও সাহিত্যামোদী তরলা দাশের স্বামী ডক্টর প্যারিমোহন গুপ্ত, যিনি সংগীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ সেনের আপন মামা। তরলা ও প্যারিমোহনের কন্যা বিখ্যাত গায়িকা সাহানা দেবী, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং নিজে গান শিখিয়েছেন। ঊর্মিলা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিখ্যত নেত্রী, যিনি চরকাকে নারীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ‘নারী কর্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গান্ধীর অসহযোগ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ঊর্মিলা ভাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ভ্রাতৃবধূ বাসন্তী দেবীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ও তাঁদের নিবিড় সান্নিধ্যে দেশের জন্যে কাজ করে গেছেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে দেশি জিনিস ক্রয়ে উৎসাহ দিতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দর বিক্রি করার সময় গ্রেফতার করা হয় ঊর্মিলাকে। এ ছাড়াও স্বদেশি আন্দোলনে মিটিং মিছিল করে, বিভিন্ন আইন অমান্য করে বহুবার কারাবরণ করেন ঊর্মিলা। এদিকে চিরকুমারী অমলা দাশ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন গানের ভুবনে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের খুব ভক্ত ছিলেন। অমলা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে অন্যদের সামনে একাধিকবার গানও গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা দেশাত্মবোধক গান ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবেত সুরে গাওয়ার জন্যে দ্বৈতকণ্ঠে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অমলা দাশ ও সরলা দেবী চৌধুরানী।







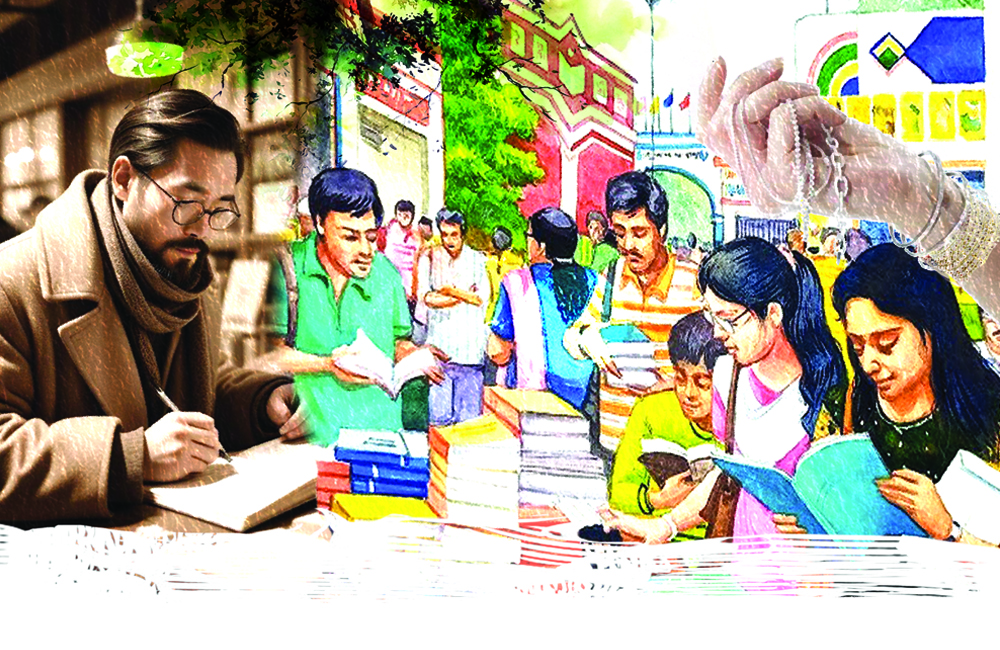
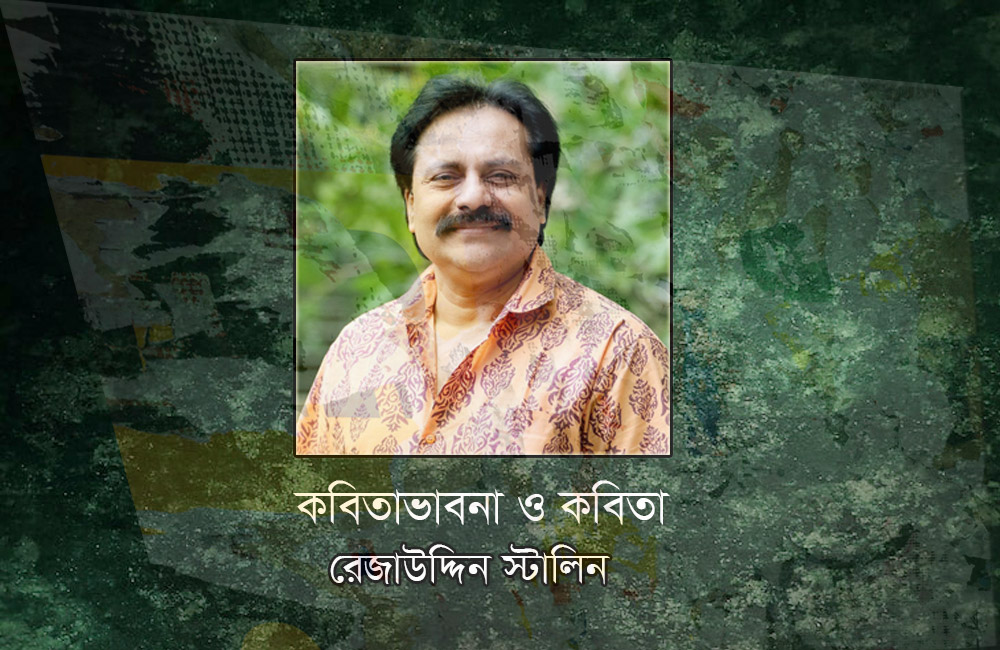



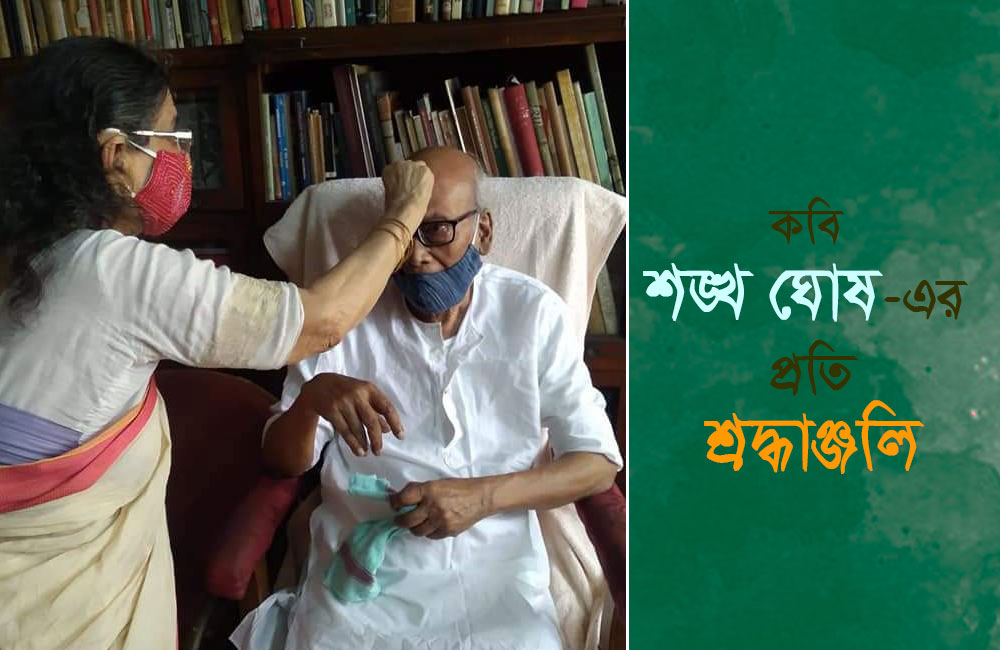
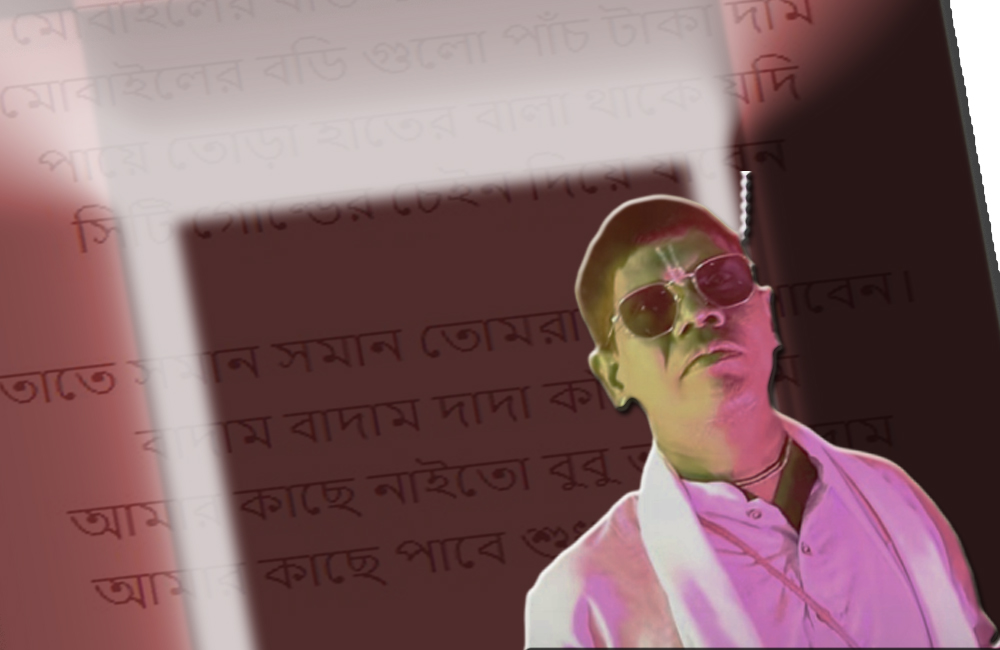

Leave a Reply
Your identity will not be published.