পশ্চিমবঙ্গের নতুন ধারার বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ছিলেন প্রয়াত উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। ধীমান দাশগুপ্ত তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলছেন যে, “ন্যাচারালিজম ও অতি নাটকীয়তার জীবনমুখী সংমিশ্রণ। মধ্যবিত্তের কাছে আদিবাসী হলো একটা থিম, আর স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের কাছে চোখ হলো একটি আর্কিটাইপ, এসবের মধ্য থেকে তিনি তাঁর ছবির থিম বা মোটিফ বেছে নেন। ব্যক্তিগত সমস্যা সমষ্টিগত সমস্যার যে ছাতা তার একটা শিক মাত্র হয়ে ওঠে। লোকায়ত জীবন ও লোক সংস্কৃতির প্রতি টান, আবেগ ও রহস্যময়তা এবং তাত্ত্বিক অসঙ্গতি কিন্তু আবেগগত অভিঘাত সমস্ত বিচারে উৎপলেন্দু ঋত্বিকের অনুগামী।” গত ২০ আগস্ট ছিল উৎপলেন্দুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এই রচনাটি পত্রস্থ হলো।
১৯৪৮ সালে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর জন্ম। চলচ্চিত্রে আসার আগে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও শিক্ষকতা করেছেন। সাহিত্য রচনা করেছেন ‘স্বর্ণ মিত্র’ নামে। একাধিক গ্রন্থের লেখক ছিলেন।
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। প্রথম চলচ্চিত্র ‘মুক্তি চাই’। এরপর প্রথম কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেন ‘ময়না তদন্ত’ (১৯৮০)। নতুন ধারার এ ছবির মাধ্যমে এই চলচ্চিত্রকার ভারতীয় সমাজের একটা অবহেলিত শ্রেণিকে তুলে ধরেছেন। ছবিটির নায়ক একজন শবর। উড়িষ্যা ছোট নাগপুর কিংবা বাংলাদেশে শবর এক কর্ষণজীবী তরুণ দাস জাতীয় আদিবাসী। চাষবাস তারা একদা করত, যখন জমিতে তাদের স্বত্ব ছিল। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এখন তারা ক্রীতদাস। তারা ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়, চরমতম দারিদ্র্য তাদের গ্রাস করে। তারা বাবুদের সেবা করে, সেবা করতে বাধ্য থাকে, বাঁধাও থাকে। দারিদ্র্যই তাদের বাবু শ্রেণির কাছে একমুঠো অন্নের বিনিময়ে বন্ধক রাখে। সমাজে তারা থাকে অস্পৃশ্য হয়ে। এই আদিবাসী শ্রেণির ছেলেটি, ভোলা, জোতদারের অনুগত ভৃত্যেও পরিণত হয়, বন্দুক চালানো শিখে। কিন্তু যখন তার প্রভু সাঁওতালদের বিরুদ্ধে বন্দুক চালাতে বলে, তখন সে অবাধ্য হয়। তার ভালোবাসার মানুষের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে সে জেলে যায়। জেল থেকে ফিরে ভোলা কোথাও কাজ পায় না। তারপর একদিন বনের মধ্যে পড়ে থাকে তার মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়—আত্মহত্যা নয়, অনাহারে এই মৃত্যু।
উৎপলেন্দুর দ্বিতীয় কাহিনিচিত্র ‘চোখ’। নতুন ধারার এই চলচ্চিত্রে শুধু বিষয়বস্তুর জোর নয়, সঙ্গে রয়েছে সাউন্ড ও ইমেজের দ্বারা একটা কাহিনি বর্ণনা, একটা জোরালো বক্তব্যের প্রকাশ। একজন শ্রমিকের দান করা চোখের মাধ্যমে সরাসরি শ্রেণিদ্বন্দ্ব উন্মোচন। মানুষের মৌলিক সৌভ্রাত্রের সঙ্গে শাসক শ্রেণির স্বার্থের মরিয়া সংঘাতের এক সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত চিত্রণ। তাদের স্বস্ব শ্রেণির শ্রেণিমানসিকতাসহ পরিচালক তুলে ধরতে চেয়েছেন। একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছবি উঠে এসেছে গোটা ছবিতে। প্রত্যেকটি লোক তার শ্রেণির অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে।
‘চোখ’ ছবিতে দেখা গেছে এমন এক শ্রমিক নেতার চরিত্র, মালিক পক্ষ যাকে কিনতে পারে নি, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিপদের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে গেছে। এই শ্রমিক নেতা যগুনাথ, বলা বাহুল্য, মালিক পক্ষের কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুক্ষীণ হয় এবং এক সময় পুঁজিপতি জেঠিয়ার ভাইকে হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলে। যদুনাথের অন্তিম ইচ্ছে ছিল, তার চোখ দুটো যেন তারই শ্রেণির কোনো মজুর পায়। যদুনাথের দান করা এই চোখের দুজন প্রার্থী দেখা যায়, একজন শ্রমিক ছেদীলাল, অন্যজন জেঠিয়ার ছেলে। এবং স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী পক্ষেরই জয় হয়। হাসপাতালের সুপারকে অর্থের জোরে কিনে নিয়ে জেঠিয়াই চোখ দুটি লাভ করে। কিন্তু যখন জেঠিয়া জানতে পারে, চোখ দুটি যদুনাথের, তখন সে তার ছেলের চোখে ওই চোখ লাগতে রাজি হয় না। শুধু তাই নয়, চোখ দুটো নষ্ট করে ফেলল। জেঠিয়ার লোকেরা যদুনাথের চোখ দুটিকে—দুটি কর্নিয়াকে মাটির নিচে পুঁতে জুতো দিয়ে মাড়ালো। কিন্তু কেন এই চোখ নষ্ট করার প্রয়াস ? পরিচালক কি এটা বলতে চান যে, ওই চোখটা থেকে গেলে, যদুনাথ যে চোখে স্বপ্ন দেখেছিল, মজুরদের মুক্তির স্বপ্ন, বিপ্লবের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটা তো থেকে যায়। জেঠিয়ারা শুধু চোখটাকেই নষ্ট করে না, চোখটাকে নষ্ট করতে গিয়ে যদুনাথের বিপ্লবের স্বপ্নটাকেই নষ্ট করে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে, আর এই বিপ্লবী স্বপ্ন নষ্ট করার জন্য আগামী দিনের নেতারা, মন্ত্রীরা, এখন যারা যুবনেতা, তারাই সাহায্য করছে জেঠিয়াদের। এদিক থেকে দেখলে একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে চোখ নষ্ট করার অশৈল্পিক দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সস্তা সিনেমার সেন্টিমেন্ট ছাড়া আর কিছু নেই। তাছাড়া ছবির শেষ সিকোয়েন্সের দরুন এই চোখ নষ্ট করার বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা সেখানে চলচ্চিত্রকার পজিটিভ বক্তব্যই রেখেছেন, সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামে দৃপ্ত পদক্ষেপই তুলে ধরেছেন। ফ্রেমের একেবারে নিচ থেকে উঠে আসে কিছু কালো কালো বিন্দু। সেই বিন্দুগুলি যে মানুষের মুখ, সেখানে যে মানুষেরই পদক্ষেপ, কে জানত ? ধীরে ধীরে অসংখ্য মানুষের মুখে ছেয়ে যায় ছবির পর্দা।...এগিয়ে চলেছে যদুনাথের বিধবা স্ত্রী, এগিয়ে চলেছে অন্ধ ছেদীলালরা। কোনো বাস্তব অবস্থাকে এখানে আর পরিচালক বিশ্বাস করতে চান নি। তিনি একটি প্রতীকী স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রশক্তি, হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সংঘবদ্ধ সর্বহারা।
উৎপলেন্দুর চলচ্চিত্র হলো ন্যাচারালিজম ও অতি নাটকীয়তার জীবনমুখী সংমিশ্রণ এবং অবশ্যই প্রতিবাদী চলচ্চিত্র। তৃতীয় কাহিনিচিত্রে (দেবশিশু) তিনি ধর্মের বুজরুগি আর কুসংস্কারকে আঘাত করেছেন। তারপর ‘রং’, ‘অপরিচিতা’ এবং ‘বিকল্প’—এই চলচ্চিত্রগুলো একের পর এক লক্ষ করলে দেখা যাবে—সেখানে কান্না, নীরব প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদই ফুটে উঠেছে। এই তিনটি ছবিই অবশ্য টেলিফিল্ম। এর পরে তিনি বড়পর্দার জন্যে নির্মাণ করেন ‘ছন্দনীড়’। এখানে একজন নৃত্যশিল্পীর জীবন এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আপসহীন মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে চিত্রভাবনার অসংলগ্নতা ছবিটিকে কোনো একটি জায়গায় পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়। তবে হ্যাঁ, উৎপলেন্দু যে একজন বড় মাপের সুরকার ছিলেন—তা তিনি এখানে প্রমাণ করতে পেরেছেন।
উৎপলেন্দুর চলচ্চিত্রের আবেদন শুধু দর্শকদের হৃদয়ের কাছে নয়, মস্তিষ্কের কাছেও। তাঁর চলচ্চিত্রে রাজনীতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রমিক, মালিক, মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মানসিকতা চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে।
বাংলা চলচ্চিত্রের ভাষাটা যারা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তাদের একজন। বিশেষ করে ‘চোখ’-এ চলচ্চিত্র ভাষার চমৎকার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—পরস্পর বিরোধী চিত্রভাষাকে একটি চলচ্চিত্রে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা...ক্যামেরা এডিটিংয়ের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে ঘটনাবলির নাট্যরস মূর্ত হয়ে ওঠা ইত্যাদি।
প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও উৎপলেন্দু সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রই ছিল প্রামাণ্য চলচ্চিত্র—‘মুক্তি চাই’ । সত্তর দশকের উত্তপ্ত রাজনীতিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ‘দেবব্রত বিশ্বাস’-এ আপসহীন এক কণ্ঠশিল্পীর জীবনকে সেলুলয়েডে বন্দি করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সংগীত—এই বিষয়টিকে নিয়েও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন উৎপলেন্দু।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রগতিতে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর অবদান অবশ্যই গুরুত্বের সাথে উল্লেখের দাবি রাখে।
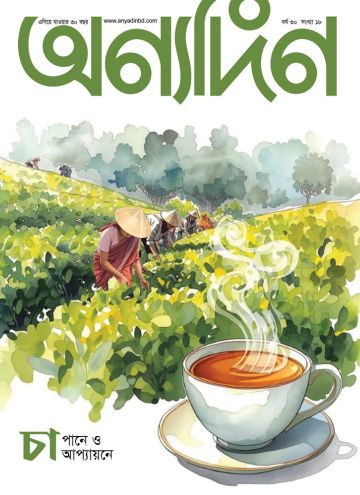




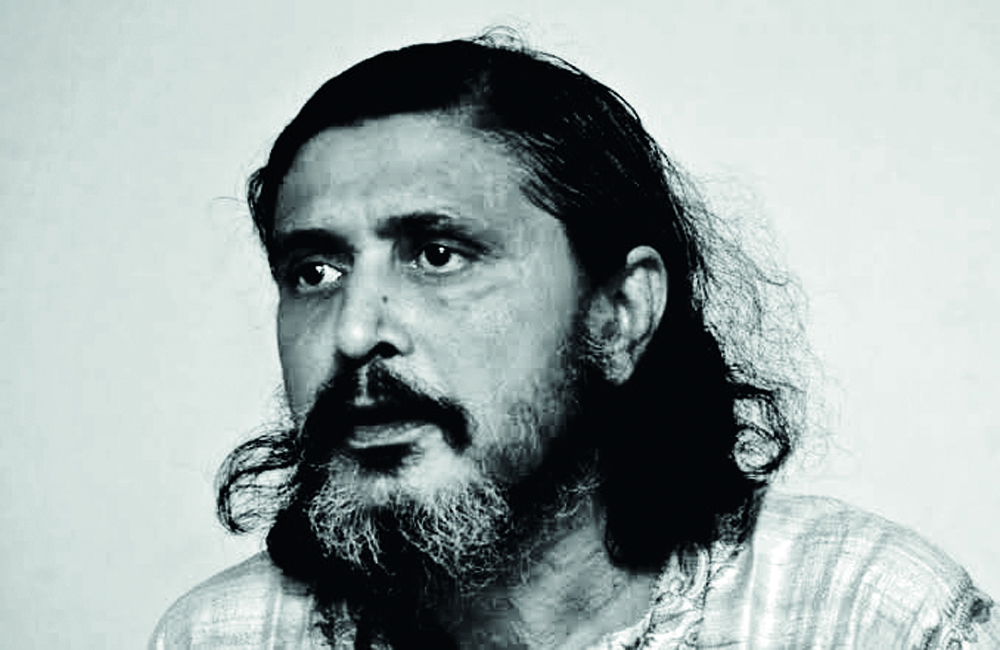





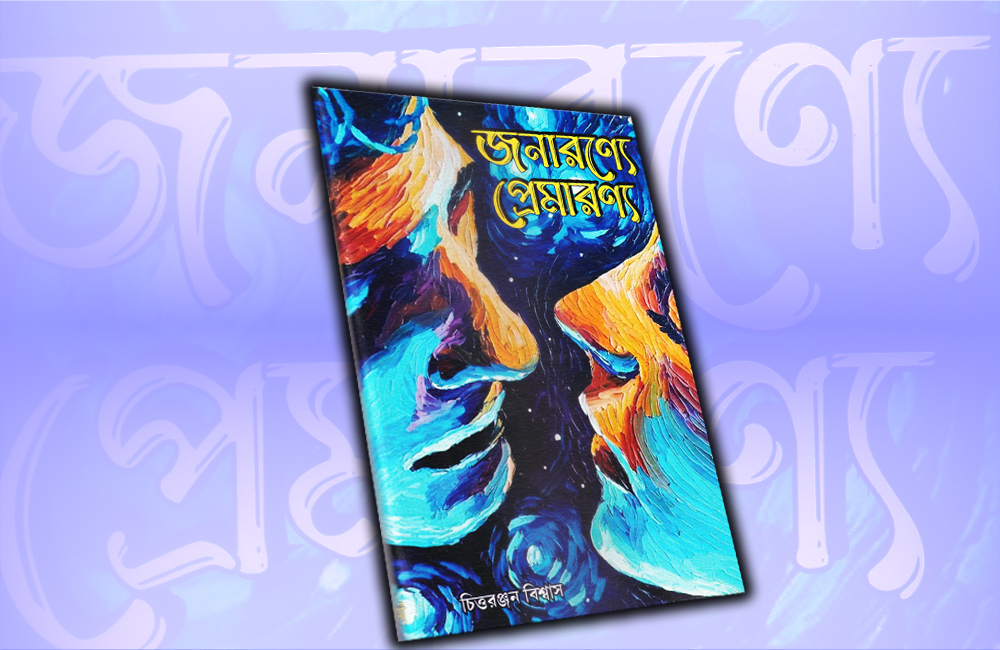


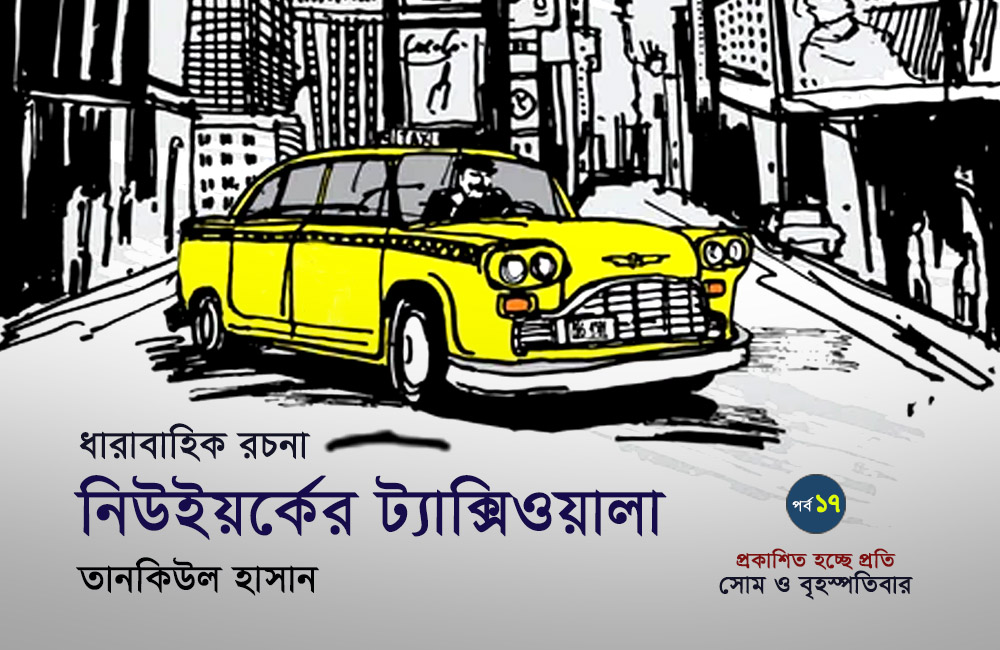
Leave a Reply
Your identity will not be published.