ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন নিয়ে নানা তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ১৬১০ সালে ইসলাম খান চিশতি ঢাকায় সুবাহ বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেন ‘জাহাঙ্গীরনগর’। তখন থেকেই ঢাকা শহরটির আধুনিক নগর হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ঢাকা ১৪৩০ সাল থেকে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।
একটি প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, ইসলাম খান যখন ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন আনন্দের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তিনি শহরে ‘ঢাক’ বাজানোর নির্দেশ দেন এবং এই ‘ঢাক’ বাজানোর ঘটনা থেকেই শহরটির নাম ঢাকা হয়ে যায়।
প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও ঢাকার প্রাচীনত্ব
পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ১৪৩০ সালে একটি বিশাল প্রাসাদ ও দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, ঢাকা একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে আধুনিক নগরীর রূপ নেওয়ার অনেক আগেই বিদ্যমান ছিল।
ঢাকা নগরী বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হাসেম সূফীর মতে, জনপদ হিসেবে ঢাকার গোড়াপত্তন হয় প্রায় ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে এবং শহর হিসেবে এর গোড়াপত্তন হয় প্রায় ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে। বলা যায়, যদিও ১৬১০ সাল থেকে ঢাকার আধুনিক নগর জীবনের সূচনা হয়, তবে ঢাকা একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে অনেক প্রাচীন।
সুদীর্ঘ চার শত বছরের পথচলায় এই ঢাকা শহরে রয়েছে অসংখ্য পুরাকীর্তি স্থাপনা। যদিও আমাদের ঢাকা শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে তবুও মোগলদের হাত ধরেই যে মূলত ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। লালবাগের কেল্লা, পরীবিবির মাজার, বড় কাটরা, ছোটো কাটরা, শাঁখারী বাজারের অসংখ্য শতবর্ষী দালানকোঠা, মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ, ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ, বাহাদুর শাহ পার্ক, নারায়ণগঞ্জের নৌ-দুর্গ, কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা প্রাসাদ, নারিন্দার প্রাচীনতম মসজিদ বিনত বিবি মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলের ভূতত্ত্ব বিভাগের পাশে বাংলার বারো ভূঁইয়া খ্যাত ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁর কবর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন সংলগ্ন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের ৫০০ বছরের পুরোনো গুরু দুয়ারা নানক শাহী উপাসনালয়, বলধা গার্ডেন, ঢাকেশ্বরী মন্দির, টিকাটুলির রোজ গার্ডেন, ফরাশগঞ্জের নর্থব্রুক হল, শঙ্খনিধি হাউস, রূপলাল হাউস, হোসেনী দালান ইত্যাদি স্থাপনার কথা বলা যায়। তা ছাড়া ঢাকার নবাবদের আমলে নির্মিত আহসান মঞ্জিল, বেগম বাজারে অবস্থিত নবাব স্যার সলিমুল্লাহর কবর, নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত শায়েস্তা খানের কন্যা মরিয়ম বিবির কবর সংলগ্ন তিন গম্বুজ মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মুর্শিদ কুলি খানের আমলে তৈরি ঢাকা তোরণ, এইসব কিছুই ঢাকা শহরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে এখনো কোনোভাবে টিকে আছে।
পুরান ঢাকার ওয়ারীর টিপু সুলতান রোডের শতবর্ষী একটি স্থাপনার নাম শঙ্খনিধি হাউস। চার দশক আগে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত হয় স্থাপনাটি। নিয়ম অনুযায়ী, সংরক্ষণের কথা থাকলেও ভবনটি ভাঙার কাজ চলছে। সর্বশেষ ২০১১ সালে ভবনের একাংশ ও ছাদ ভাঙেন দখলদারেরা।
শঙ্খনিধি হাউসের মতো শতবর্ষী অনেকগুলো স্থাপনা রয়েছে পুরান ঢাকায়। দেশের পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এইসব স্থাপনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঢাকার অতীত ইতিহাস। তবে দখল, অপরিকল্পিত ব্যবহার ও সংস্কারের অভাবে হারাচ্ছে এই ঐতিহ্য। নিদর্শন চিহ্নিত করতেই যাচ্ছে বছরের পর বছর।
রূপলাল হাউসের ভেতরের অংশ
সম্প্রতি পুরান ঢাকার অন্তত ২৫টি শতবর্ষী ভবন ঘুরে দেখা যায়, ঐতিহাসিক এসব স্থাপনার অনেকগুলো গুদাম ও কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনোটিতে রয়েছে ৩০টির বেশি পরিবার। সংরক্ষিত হিসেবে তালিকাভুক্তির পরও ঘটছে ভবন ভাঙার ঘটনা।
স্থাপনা নিয়ে কাজ করে আরবান স্টাডি গ্রুপ নামের একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। তারা ২ হাজার ২০০টি বাড়িকে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ উল্লেখ করে উচ্চ আদালতে রিট করেছিল। এসব বাড়ি অক্ষত রেখে সেগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য নির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে ২০১৮ সালে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। মাঠপর্যায়ে জরিপ করে সেই চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঁচ বছরেও দাখিল করতে পারে নি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
২০০৯ সালে পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারসহ চারটি অঞ্চল ও মোট ৯৩টি স্থাপনাকে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। বিধি অনুযায়ী এইসব স্থাপনা ও এইসব এলাকায় অবস্থিত ইমারত, উন্মুক্ত জায়গা, রাস্তা ও গলির প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার, অপসারণ ও ধ্বংসের ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়। অথচ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এসব ভবনের সংস্কার করে কাঠামো বদলে দেওয়া হচ্ছে। স্থাপনাগুলো সংরক্ষণে নীতিমালার কোনো প্রয়োগ নেই। অপর দিকে তা বর্তমান ব্যবহারকারীদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ।
শঙ্খনিধি হাউসের নিচতলায় আছে মোটর সারাই কারখানা। ছাদে হয়েছে নতুন ঘর। পুরোনো নকশা মুছে লাগানো হয়েছে টাইলস। ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলী বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে শঙ্খনিধি হাউস। তবে শতবর্ষী এই স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেই।
শঙ্খনিধি হাউসের মতোই অবস্থা রাজধানীর অন্যতম পুরোনো অধ্যায়ের নিদর্শন ‘রূপলাল হাউসের’। ফরাশগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীর কোলঘেঁষা ২০০ বছরের পুরোনো এই স্থাপনাটিও তালিকাভুক্ত প্রত্নতত্ত্ব।
সংস্কারের সময় অলংকরণ মুছে ফেলার উদাহরণ কম নয়। লাল মোহন সাহা স্ট্রিটের ২২৪ নম্বর বাড়ির সামনের দিকের ইন্দো-ইউরোপীয় রীতির সব অলংকরণ মুছে সম্প্রতি প্লাস্টার করা হয়েছে। একই অবস্থা বি কে দাস লেনে লক্ষ্মী ভিলা ও পূর্ণ চন্দ্র ব্যানার্জি রোডের ৬ থেকে ১০ নম্বর বাড়ির।
বি কে দাস লেনের মঙ্গলালয়ের ছাদে বাঁ দিকের নির্মাণ সময়কাল ১৯১৫ লেখা তোরণটি সম্প্রতি ভাঙা হয়। দোতলার সামনের দিকের বারান্দার দেয়ালও আটকে দেওয়া হয়েছে ইটের গাঁথুনিতে।
ইতিহাসবিদ ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভের সাবেক পরিচালক শরীফ উদ্দিন আহমেদ ‘প্রথম আলো’ক বলেন, সব উন্নত দেশে প্রত্নতত্ত্ব রক্ষার দায়িত্ব নেয় সরকার। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই কাজ করতে হবে। সব স্থাপনা প্রত্নতত্ত্ব না-ও হতে পারে। আগে সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
লাল মোহন সাহা শাহ স্ট্রিটের একটি বাড়িও সংরক্ষণের তালিকায় নেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের। মোড়ের এই বাড়িটি শতবর্ষী বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বড় কাটরা পুরান ঢাকার চকবাজারের দক্ষিণে, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি আয়তাকারে নির্মিত ইমারত এবং এতে মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বড় কাটরা ঐতিহাসিক মুঘল আমলের সরাইখানা, যা সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪৪-১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ান মীর আবুল কাসিম কর্তৃক নির্মিত হয়। এটি মূলত মুসাফিরখানা (পথিকদের থাকার জায়গা) হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং বর্তমানে জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম, বড় কাটরা মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে এর সংরক্ষণ জরুরি হলেও কালের পরিক্রমায় এর আদি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
ছোট কাটারা শায়েস্তা খানের আমলে তৈরি ঢাকার একটি ইমারত। আনুমানিক ১৬৬৩-১৬৬৪ সালের দিকে এ ইমারতটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তা ১৬৭১ সালে শেষ হয়েছিল। এটির অবস্থান ছিল বড় কাটরার পূর্বদিকে হেকিম হাবিবুর রহমান রোডে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। ইমারতটি দেখতে অনেকটা বড় কাটরার মতো হলেও এটি আকৃতিতে বড় কাটরার চেয়ে ছোট এবং এ কারণেই হয়তো এর নাম হয়েছিল ছোট কাটারা। তবে ইংরেজ আমলে এতে বেশ কিছু সংযোজন করা হয়েছিল। ১৮১৬ সালে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক লিওনার্দ এখানে ঢাকার প্রথম ইংরেজি স্কুল খুলেছিলেন। বর্তমানে ছোট কাটারা বলতে কিছুই বাকি নেই, শুধু একটি ভাঙা ইমারত ছাড়া। যা শুধু বিশাল তোরণের মতন সরু গলির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে অসংখ্য দোকান এমনভাবে ঘিরে ধরেছে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে মুঘল আমলের এমন একটি স্থাপত্য ছিল। ছোট কাটরার সাথে বিবি চম্পার স্মৃতিসৌধ অবস্থিত ছিল। এক গম্বুজ, চার কোণা, প্রতিপাশে ২৪ ফুট দীর্ঘ ছিল স্মৃতিসৌধটি। তায়েশ লিখেছেন, “পাদ্রি শেফার্ড ওটা ধ্বংস করে দিয়েছেন।” শেফার্ড বোধহয় কবরটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিবি চম্পা কে ছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি। তবে কারও মতে তিনি শায়েস্তা খাঁর মেয়ে।
জিঞ্জিরা প্রসাদ রাজধানী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ এই মোঘল আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাটি প্রায় ৩৫০ বছরের পুরোনো। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবনটি বর্তমানে জিঞ্জিরা প্রাসাদের একটি ভঙ্গুর অংশ। বাংলার মোগল সুবাদার দ্বিতীয় ইবরাহিম খান (১৬৮৯-১৬৯৭) প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন তাঁর প্রমোদকেন্দ্র হিসেবে। ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলী খান বাংলার দেওয়ানি মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিলে জিঞ্জিরা প্রাসাদের গুরুত্ব কমে যায়। জিঞ্জিরা প্রাসাদটি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার কারণ হলো, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারকে এখানেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মীর জাফরের পুত্র মীরনের চক্রান্তে সিরাজের মা আমেনা, খালা ঘষেটি বেগম, সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেছা ও তার শিশুকন্যাসহ সবাই বন্দি হয় এ প্রাসাদে। ইতিহাসবিদ নাজির হোসেনের ‘কিংবদন্তি ঢাকা’ গ্রন্থে বলা হয়, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারকে দীর্ঘ ৮ বছর জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। মুঘল শাসকদের অনেককে এ দুর্গে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।
জিঞ্জিরা প্রাসাদকে স্থানীয়রা হাভেলি বা হাওলি বলে থাকেন। প্রাসাদটির নির্মাণশৈলীতে রয়েছে বেশ নান্দনিকতা। প্রাসাদটির নির্মাণশৈলী বড় কাটরার আদলে হলেও কক্ষ ও আয়তন অনেক কম। প্রাসাদের পশ্চিম অংশে দুটি সমান্তরাল গম্বুজ রয়েছে। আর মাঝ বরাবর রয়েছে ঢাকনাহীন আরেকটি গম্বুজ। প্রাসাদের পূর্বাংশে দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে রয়েছে ছাদ। এ ছাদ থেকে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।
এ প্রাসাদের তিনটি বিশেষ অংশ আজও টিকে আছে। প্রবেশ তোরণ, পৃথক দুটি প্রাসাদ। কয়েক একর জমির ওপর এ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল মূলত অবকাশ যাপনের জন্য। চারদিকে জলরাশির মাঝখানে একখণ্ড দ্বীপ জিঞ্জিরা। নারিকেল-সুপারি, আম-কাঁঠালসহ দেশীয় গাছ ও সবুজের সমারোহ দ্বীপজুড়ে। মুঘল স্থাপত্যশৈলীর অনুপম এক নিদর্শন ছিল জিঞ্জিরা প্রাসাদ। প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জেমস টেইলর তার ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’ গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে জিঞ্জিরা প্রাসাদের নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। জায়গাটির আশেপাশে গড়ে উঠেছে পাঁচতলা-ছয়তলা অসংখ্য ভবন। তাই কাছে না গেলে প্রাচীন ভবনটির অস্তিত্ব বোঝা বড় কঠিন কাজ। এই ভবনের প্রতিটি ইটের গায়ে লেখা রয়েছে টুকরো টুকরো ইতিহাস। সেই খবর ক’জনই-বা রাখেন! এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। অথচ ভবনটির গায়ে কোথাও তার উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি রয়েছে, নবাব মীর জাফর আলী খানের পুত্র মীর সাদেক আলী খান ওরফে মীরনের নির্দেশে জমাদার বকর খান মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে ঘষেটি বেগম ও আমেনা বেগমকে প্রাসাদ থেকে নৌকায় তুলে ধলেশ্বরী নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করে। বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এ প্রাসাদের যতটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে, সেটুকুই রক্ষা করা এখন সময়ের দাবি।
নারিন্দার বিনত বিবি মসজিদ রাজধানী ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ। এটি ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নারিন্দা এলাকায় হায়াৎ বেপারির পুলের পাশে নির্মিত হয়েছিল এবং এটিকে ঢাকার প্রথম মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন ও প্রথম মসজিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে (৮৬১ হিজরি সনে) মারহামাতের কন্যা মুসাম্মাৎ বখ্ত বিনত এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাঁর নামানুসারেই মসজিদটির নামকরণ করা হয় ‘বিনত বিবি মসজিদ’। প্রাচীন এই মসজিদটি পুরান ঢাকার নারিন্দা রোডের ৬ নম্বর সড়কের হায়াৎ বেপারীর পুলের উত্তর পাশে অবস্থিত। বিনত বিবি মসজিদ প্রাক-মুঘল আমলের স্থাপত্যশৈলীর উদাহরণ। এর মূল ভবনটি অবিকৃত রেখে এখানে একটি নতুন ভবন ও সুউচ্চ মিনার যুক্ত হয়েছে। গুরুত্বের বিবেচনায় এটি ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন টিকে থাকা মসজিদ। ঢাকা শহরের প্রথম মসজিদ এবং প্রাচীনতম মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।
হোসেনী দালান ইমামবাড়া বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরান ঢাকার এলাকায় অবস্থিত একটি শিয়া উপাসনালয় এবং কবরস্থান। বিকল্প উচ্চারণ হুসনি দালান এবং ইমারতের গায়ে শিলালিপিতে ফারসি ভাষায় লিখিত কবিতা অনুসারে উচ্চারণ হোসায়নি দালান। এটি মোগল শাসনামলে ১৭শ শতকে নির্মিত হয়। ইমারতটি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পৌত্র হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর কারবালার প্রান্তরে শাহাদাৎ বরণ স্মরণে নির্মিত। প্রতি বছর ১০ই মহররম এখান থেকে তাজিয়া মিছিল বের করা হয়।
ঢাকার সবচেয়ে পুরোনো এবং সর্ববৃহৎ খ্রিস্টান কবরস্থান নারিন্দায় অবস্থিত, যা ‘ঢাকা খ্রিস্টান কবরস্থান, ওয়ারী’ নামে পরিচিত। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মী থেকে শুরু করে ওলন্দাজ, আর্মেনিয়ান এবং চীনা নাগরিকদের কবর ছাড়াও আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হওয়া শত ইংরেজ সৈনিকের গণকবর।
প্রায় চার শ বছরের বেশি বয়স এই সমাধিক্ষেত্রের। মূল গেট দিয়ে ঢুকে কেয়ারটেকারের রুমের পাশ ঘেঁষে পায়ে চলা সোজা একটি রাস্তা, সামনেই সাদা বিশাল তোড়ন। দুপাশে সারি সারি অনেকগুলো প্রাচীন সমাধি। কিছু সমাধির বয়সকাল ইউরোপিয়ানদের বাংলা দখলেরও পূর্বের। সমাধি ফলকগুলোর এপিটাফ মুছে গিয়েছে। সন-তারিখ কোনোকিছুই ভালো বোঝা যায় না। জরাজীর্ণ ফলকে শ্যাওলার আস্তরণ। নারিন্দা সমাধিক্ষেত্রটির পাশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য ঢাকার প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কালের পরিক্রমায় ক্ষয়ে যাওয়া কবর ফলকগুলো দেখে জানা যায়, এখানে শায়িত আছেন কলকাতার মন্ত্রী রেভারেন্ড জোসেফ প্যাজেট, যিনি ১৭২৪ সালে ২৬ বছর বয়সে মারা যান। আরও রয়েছেন ১৭২৫ সালে মারা যাওয়া ইংরেজ কুঠির প্রধান ন্যাথানিয়েন হল।
সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিও বহন করছে এই সমাধিক্ষেত্র। সিপাহী বিদ্রোহে নিহত দুই সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে এখানে, সদর দরজার বাঁ দিকে, একদম পথের শুরুতেই। এর মধ্যে এখনো বেশ চেনা যায় হেনরি স্মিথের সমাধি, ২২ নভেম্বর বিদ্রোহের দিন তিনি নিহত হন। এছাড়াও যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত সেনা নেইল ম্যাকমুলেন ও জেমস মুরস ২৩ নভেম্বর এবং উইলিয়াম এসডেন ও রবার্ট ব্রাউন ২৪ নভেম্বর মারা যান। এই সমাধিক্ষেত্রেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পোগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার নিকোলাস পোগোজ। যিনি ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ব্যাংকের একজন পরিচালক ছিলেন। পরবর্তীসময়ে। ১৮৭৪ সালে, তিনি ঢাকা পৌরসভার কমিশনারও হন। তাঁর পাশাপাশি এই সমাধিক্ষেত্রেই সমাধিস্থ হয়েছেন তাঁর ছেলে পল।
আরও আছে প্রিয় ডাক্তার সাহেব ইউরোপিয় চিকিৎসক আলেকজান্ডার সিম্পসনের সমাধি। তিনি ১৮৫৮ সালে যাত্রা শুরু করা মিটফোর্ড হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পরলোকে চলে যান।
বছর চার-পাঁচ আগে এক বিকেলে কৌতূহলবশত: আমার এক বন্ধুকে নিয়ে ওয়ারী কবরস্থানটি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে বিশাল কবরস্থানের ভেতরে সুনসান নীরবতা , কয়েক শ বছরের পুরোনো জরাজীর্ণ নামফলক লাগানো অসংখ্য কবর ও ভেঙে পড়া বেশকিছু প্রাচীন সমাধিগুলো দেখে মনে একরকম ভয় সৃষ্টি হয়েছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমরা কবরস্থান থেকে বের হয়ে আসি।
আমার ছাত্রজীবনে মাঝেমধ্যে পুরান ঢাকার ওয়ারীতে অবস্থিত বলধা গার্ডেনে বেড়াতে যেতাম। তৎকালীন ঢাকা বর্তমান গাজীপুর জেলার বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ১৯০৯ সালে দেশবিদেশের অসংখ্য গাছ এনে মনোরম এই উদ্ভিদ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অসংখ্য দেশবিদেশের নামি-দামি মানুষ অতীতে এই বলধা গার্ডেন পরিদর্শন করেছেন। ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলধা গার্ডেনে বসে লিখেছিলেন। এই উদ্ভিদ উদ্যানটি যে কত সুন্দর তা ঠিক বলে বুঝানো যাবে না। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীদের কারণে বলধা গার্ডেনের ভেতরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
শায়েস্তা খাঁ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬৬৪-১৬৮৮) বাংলার সুবেদার নিযুক্ত ছিলেন। লালবাগের কেল্লার নির্মাণ কাজ চলাকালে ১৬৬৮ সালে তাঁর কন্যা পরীবিবি'র অসময়ে মৃত্যু ঘটলে পরীবিবিকে কেল্লা প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। পরীবিবি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র ভবিষ্যৎ মোঘল সম্রাট শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের স্ত্রী। শায়েস্তা খাঁ তাঁর কন্যা পরীবিবির কবরের উপরে একটা সমাধি নির্মাণ করেন এবং দুর্গের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। লালবাগ দুর্গ ঢাকা শহরের অন্যতম দর্শনীয় একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। নির্দিষ্ট বন্ধের দিন ছাড়া বাকি প্রতিদিন অসংখ্য দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী এখানে এসে বেড়িয়ে যান। আমার কাছে লালবাগ দুর্গে পরিবার-পরিজন নিয়ে শীতের বিকেলে বেড়াতে অনেক ভালো লাগে। আমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের বাসা লালবাগ দুর্গের পূর্ব পাশের একটি ছয়তলা ভবনে। গভীর রাতে সেই বাড়ির ছাদ থেকে লালবাগ দুর্গের রাতের দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত ভালো লাগে। কল্পনায় হারিয়ে যাই চার শ বছর আগে ঠিক কেমন ছিল এই মোঘল আমলের স্থাপনাটি ?
লালবাগ দুর্গে একটি রহস্যময় সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, এ সুড়ঙ্গ পথে যে একবার যায়, সে আর ফিরে আসে না। এই সুড়ঙ্গ পথটির প্রবেশমুখ জননিরাপত্তার স্বার্থে লোহার গেইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।
১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লবের সময়, ২২ নভেম্বর, ইংরেজ মেরিন সেনারা ঢাকার লালবাগের কেল্লায় দেশীয় সেনাদের নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালায়। কিন্তু সিপাহীরা বাধা দিলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। ইংরেজদের সঙ্গে এই সম্মুখযুদ্ধে মোট ৪০ জন সিপাহী নিহত হয়। আহত ও পালিয়ে যাওয়া সিপাহীদের ধরে এনে সংক্ষিপ্ত প্রহসনমূলক কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিচারের পর ১১ জন সিপাহীকে আন্টাঘর ময়দানে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) এনে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে লাশগুলো বহুদিন ধরে এখানকার বিভিন্ন গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মানুষ তখন ভয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় নি। এরপর বহুদিন পর্যন্ত এই ময়দানের চারপাশ দিয়ে হাঁটতে ঢাকাবাসী ভয় পেত। কারণ জায়গাটি নিয়ে বিভিন্ন ভৌতিক কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৭৪ সালে পরীবিবির সমাধি ও লালবাগ দুর্গকে প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা হিসেবে ঘোষণা করে। শায়েস্তা খাঁর অপর মেয়ে তুরান দখত, স্থানীয়ভাবে পরিচিত মরিয়ম বিবির মৃত্যুর পরে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় কেল্লারপুল, হাজীগঞ্জে সমাহিত করা হয়। মেয়ের কবরের উপরে একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। শায়েস্তা খাঁ সমাধির পশ্চিম পাশে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মরিয়ম বিবি মসজিদ ও স্কুল নির্মাণ করেন। মরিয়ম বিবির স্মৃতিসৌধটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মরিয়ম বিবি স্মৃতিসৌধটির বাইরের আস্তরণ , ইট, সুরকি খসে পড়ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পুরাকীর্তিটি সংস্কারের কোনো রকম উদ্যোগ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নেই। শায়েস্তা খান ( ১৬৬৪-১৬৬৮) এই স্মৃতিসৌধটির চারপাশে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এই স্মৃতিসৌধ সীমানার সামনে স্থাপিত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ডে উল্লেখিত নির্দেশ অমান্য করে স্মৃতিসৌধ ঘেরা উঁচু দেয়াল প্রাচীর ঘেঁষে অসংখ্য অবৈধ দোকানপাটের স্থায়ী স্থাপনা গড়ে উঠেছে ।
নারায়ণগঞ্জে মোঘলদের নির্মিত প্রধান নৌ দুর্গগুলোর মধ্যে হাজীগঞ্জ দুর্গ এবং সোনাকান্দা দুর্গ অন্যতম, যা শীতলক্ষ্যা নদীর দুই তীরে অবস্থিত এবং ঢাকা শহরকে নৌ-দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। হাজীগঞ্জ দুর্গ (খিজিরপুর দুর্গ নামেও পরিচিত) শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, আর সোনাকান্দা দুর্গ শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এই দুর্গগুলো ঢাকার নৌপথের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং মোগল আমলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।
ঐতিহাসিক সাতমসজিদ রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত মুঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ। এই মসজিদটি চারটি মিনারসহ তিনটি গম্বুজের কারণে মসজিদের নাম হয়েছে ‘সাতমসজিদ’। এই মসজিদটি মুঘল আমলের অন্যতম নিদর্শন। ১৬৮০ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করান। এই মসজিদটির পশ্চিম দিক দিয়ে একসময় বুড়িগঙ্গা নদী বহমান ছিল। জলদস্যুর আক্রমণের হাত থেকে ঢাকা শহরবাসীদের রক্ষা করতে মসজিদটির চারটি মিনার মূলত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো বলে এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পরবর্তী সময়ে গাবতলী থেকে মোহাম্মদপুর হয়ে সোয়ারিঘাট পর্যন্ত বেড়িবাঁধ নির্মিত হওয়ায় সাতমসজিদের পেছনে ও দুই পাশের জমি ভরাট করে সেখানে অসংখ্য বহুতল ভবন নির্মিত হওয়ায় কারণে দেখে বুঝার উপায় নাই যে, একসময় সাতমসজিদ এলাকার তিন দিকে জলাশয় ছিল। আমি ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা, এইসব কিছুই আমার নিজ চোখে দেখা।
মোঘল শাসন আমলের পরে ঢাকার নবাবরা ছিল ব্রিটিশ বাংলার সবচেয়ে বড় মুসলিম জমিদার পরিবার। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় ব্রিটিশদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য ব্রিটিশ রাজ এই পরিবারকে ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করে। নবাবদের আদি নিবাস ছিল কাশ্মীরে। তাঁদের ভাষা ছিল উর্দু ও পারসী। পরিবারটির বাসস্থান ছিল আহসান মঞ্জিলে। পরিবার ও জমিদারির প্রধানকে নবাব বলা হতো। ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ভূষিত ঢাকার প্রথম নবাব ছিলেন খাজা আলীমুল্লাহ। ঢাকার নবাবদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পুরান ঢাকাবাসীদের জন্য ব্যয়বহুল পাঁচ তলা উঁচু ওভারহেড পানির ট্যাংক নির্মাণ করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে আসাম-বাংলার সচিবালয় ঢাকায় স্থাপন করা, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমান বুয়েট) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান এদেশের জনগণ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।
আহসান মঞ্জিল পুরান ঢাকার ইসলামপুরের কুমারটুলী এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারির সদর কাচারি। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসারে এর নামকরণ করেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে আহসান মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে এখানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। আহসান মঞ্জিল কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে।
আমাদের পুরান ঢাকা প্রত্ন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি বিশাল জনপদ। এখানকার পুরাকীর্তিগুলো আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের পরিচায়ক। এগুলোর বিলুপ্তির অর্থ হচ্ছে রাজধানী শহরের পুরোনো ইতিহাস ও অতীত গৌরবকে ধ্বংস করা। একটি দেশের সমৃদ্ধি ও খ্যাতির ক্ষেত্রে তার পুরাকীর্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই অমূল্য পুরাকীর্তিগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে শুধু সরকারকেই নয় সর্বস্তরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। বাড়াতে হবে এ বিষয়ে জনসচেতনতা। দেশীয় ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হলো, প্রত্ন ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা। প্রত্ন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ছাড়া আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে অতিদ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।
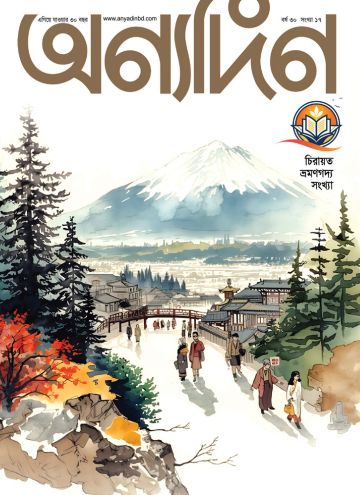





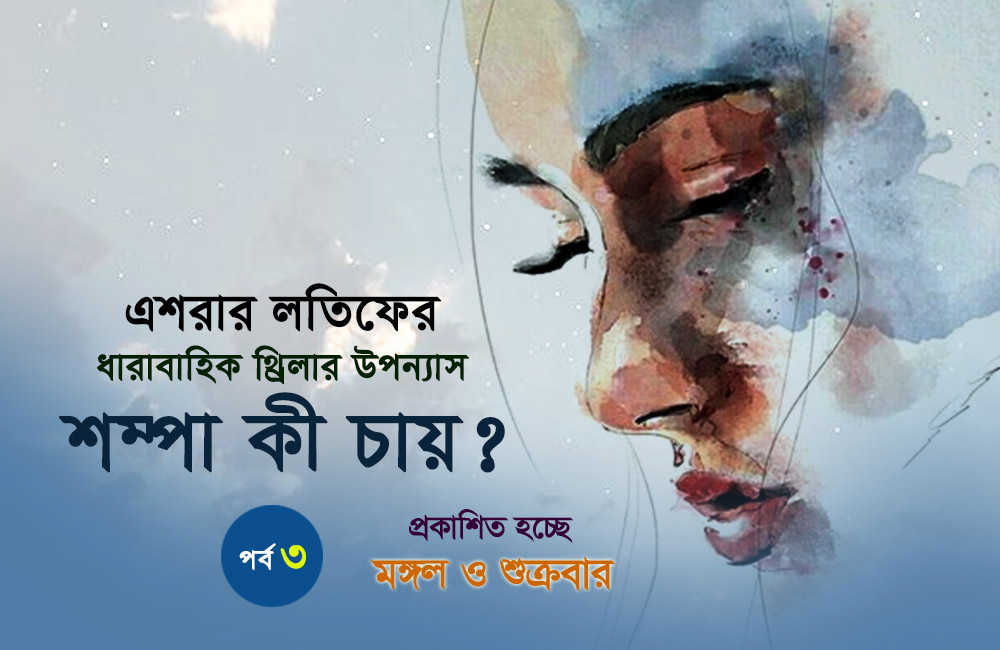




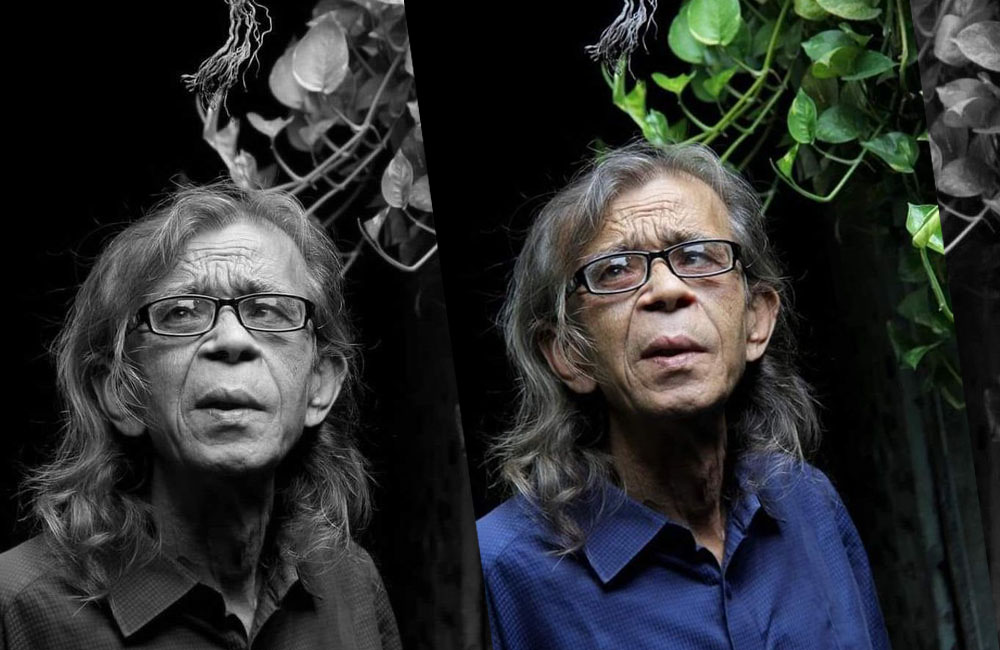

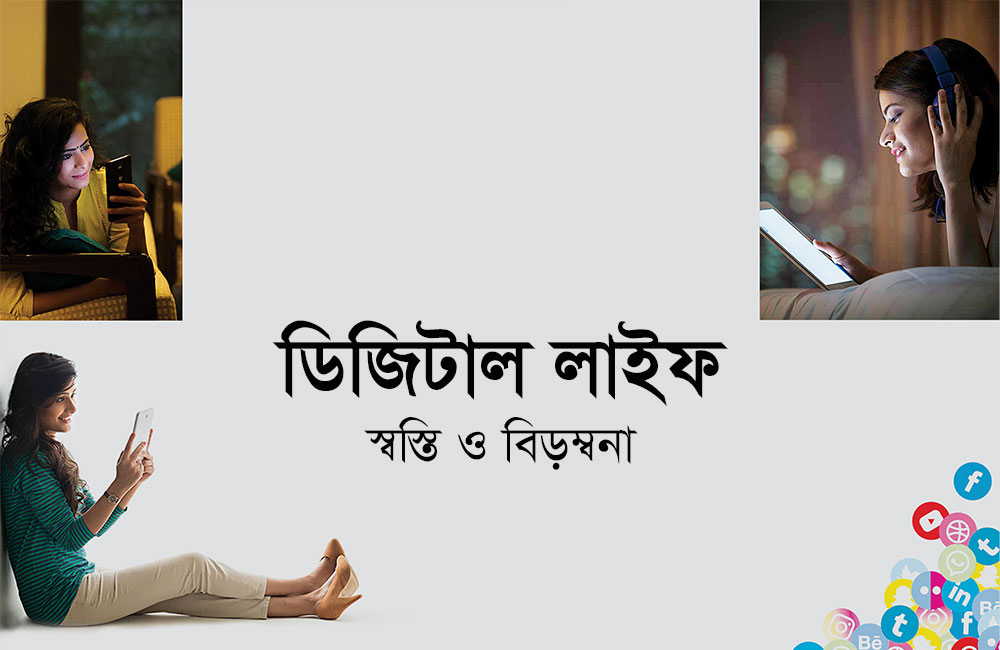

Leave a Reply
Your identity will not be published.