তাঁর কণ্ঠে লালনগীতি বাক্সময় হয়ে উঠত। এখানে তিনি ছিলেন অনন্যা। তুলনাহীন। কেননা গানের ভেতর থেকে গেয়ে উঠতেন তিনি; গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিবেদন করতেন আমাদের সামনে। আমরাও সেই গানের ভাবসম্পদের গভীরে ডুবে যেতে যেতে মগ্ন হয়ে যেতাম, যাই; সম্মোহিত হয়ে পড়ি। গান শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তার রেশ রয়ে যায় বহুক্ষণ।
তিনি ফরিদা পারভীন। লালনগীতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠশিল্পী। যাঁর গানের জন্য আমরা কান পেতে ছিলাম, থাকি। মগ্ন চৈতন্যের গভীরে ডুবে যাই। গান যে শুধু শোনার বিষয় নয়, উপলব্ধিরও বিষয়—সেটি ফরিদা পারভীনের গান শুনলে আমরা বুঝতে পারি। জগৎ-সংসার, চারদিকের বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমরা অন্যলোকে বিচরণ করি।
এই অনন্যসাধারণ কণ্ঠশিল্পীর মুখোমুখি হয়েছিল অন্যদিন ২০২৩ সালের এপ্রিলের এক সন্ধ্যায়। নানা প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোমিন রহমান। এই সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ঈদসংখ্যা অন্যদিন ২০২৩-এ। এখানে আবার তা তুলে ধরা হলো। ধারণযন্ত্র থেকে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন তানিয়া আক্তার।
মোমিন রহমান: শৈশবে গান সম্পর্কিত বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে ?
ফরিদা পারভীন: আমার জন্ম নাটোরে। তারপর মাগুরার ভাড়াবাড়িতে বেড়ে ওঠা। গানের সাথে যোগ তৈরি হয় মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে। মা বান্ধবীদের নিয়ে সিনেমা হলে যেতেন। আমি যেহেতু বাবা-মায়ের এক সন্তান, তাই মায়ের সিনেমা দেখার সঙ্গী ছিলাম আমিও। সেসময় দিলীপ কুমারকে চিনতাম না, নার্গিসকে চিনতাম না। সেই সময় সিনেমায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শুনতাম। সেই গানগুলো আমাকে কোলে নিয়ে মা গুনগুন করে গাইতেন। ওই যে সুরের অনুরণন, শুনতে শুনতে আমার অবচেতন মনে প্রভাব ফেলেছে। তারপর একদিন পড়ার টেবিলে বসেছি, এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে হারমোনিয়ামের সুর ভেসে এল কানে। পড়া বাদ দিয়ে দিলাম দৌড়। কারণ এই সুর আমাকে শুনতে হবে। সেই বাড়ির কপাট ধরে গানের সুর শুনেছিলাম সেদিন। মা ঘুম থেকে সজাগ হয়ে উঠে তার একমাত্র মেয়েকে না দেখতে পেয়ে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখে, পাশের বাড়ির কপাট ধরে সুর শুনছি। সেই সুর আমাকে এতটা আন্দোলিত করেছে যে বাবাকে এসে বলার পর মিস্ত্রি ডেকে এনে হারমোনিয়াম বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি এখনো আছে। আমার চেয়ে হারমোনিয়ামের যত্ন বেশি করেছেন আমার মা। আবার আমার বাবাও গান করতেন। আমার জন্মের আগে দুর্ভিক্ষ লেগেছিল। বাবা গান গেয়ে গেয়ে অর্থ জোগাড় করে অন্নহীনদের জন্য অন্ন জোগাড় করতেন। এজন্যই বোধহয় তাদের একমাত্র সন্তান গানের অনুরাগী হোক এই প্রত্যাশা বাবারও ছিল। বাবার পাশাপাশি মায়েরও বেশ আগ্রহ ছিল। বাবা-মায়ের যুগল প্রত্যাশা আর আমার আগ্রহ মিলিয়ে গানের ভুবনে যাত্রা।
মোমিন রহমান: গানের গুরু কারা ছিলেন এবং তাঁরা কেমন ছিলেন ?
ফরিদা পারভীন: গানের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে বাবা নানা জনের কাছে আমাকে গান শিখিয়েছেন। আমার সেইসব গুরু বাড়িতেই এসেছেন। মনে পড়ে, আমার প্রথম গুরু কমল চক্রবর্তী আমাকে কোলে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়ে একহাতে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখতে সাহায্য করেছেন। বাবা যেহেতু চিকিৎসা পেশায় ছিলেন তাই বদলির চাকরি ছিল। সেই সুবাদে বিভিন্ন জেলাতে থাকার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু কুষ্টিয়াতে থাকার সময় আমার আদি-অন্ত যাই বলি না কেন সেখান থেকেই আমার উৎপত্তি। আমি তখন এত হালকা গড়নের ছিলাম যে হাত দিয়ে হারমোনিয়ামের পুরোটা ধরার সুযোগ হতো না। তানপুরার সাথে ক্ল্যাসিকালের তালিম নিয়েছি ইব্রাহিম খান, রবীন্দ্রনাথ রায়, মোতালেব বিশ^াস, ওসমান গণি এই গুরুজনদের কাছ থেকে। নজরুলসংগীতের তালিম নিয়েছি ওস্তাদ আব্দুল কাদেরের কাছে। মীর মোজাফফর আলী মেহেরপুরে থাকতে স্বরলিপি দিয়ে আমাকে গান শেখাতেন। সবাই সুরের সাধক ছিলেন। আমাকে গান শেখানো একেক গুরুর শেখানোর ধরন ছিল একেকরকম। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটি বিষয় বেশ মিল ছিল তা হলো আন্তরিকতা। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রত্যেকেই আমাকে শিখিয়েছিলেন।
মোমিন রহমান: বেতারে গাওয়া প্রথম গান কোনটি ?
ফরিদা পারভীন: ‘মুসাফির মোছ রে আঁখি-জল’...এই নজরুলসংগীতটি প্রথমবারের মতো বেতারে গেয়েছিলাম। সেই সময় কুষ্টিয়ায় নজরুল, রবীন্দ্রনাথের গানের অনেক অনুষ্ঠান হতো। এদিকে আমি যেহেতু নজরুলের গান করতাম, তাই যখনই শিলাইদহে কোনো অনুষ্ঠান হতো আমাকে ডাকা হতো। অবশ্য অন্যদেরও ডাকা হতো। তবে আমি বয়সে তাদের তুলনায় ছোট বলে আমাকে বেশি ডাকা হতো। আমিও সাড়া দিতাম। এরপর বঙ্গবন্ধু তখন মাত্র দেশে ফিরে এসেছেন। সেই সময় ১৯৭২ সালে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস শুরু হয়। যা দেশের সর্ববৃহৎ অডিও আর্কাইভ। এর মাধ্যমে অন্য বিষয়ের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। ফলে তখন সাতদিনব্যাপী সারা রাতব্যাপী সারা বাংলাদেশের বেতার থেকে যে লোকসংগীতের উৎসব হলো, সেখানে আমাকে ‘লালন’-এর গানের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। রাতজেগে জেগে বেতারের জন্য অনেক গান রেকর্ড করেছি।
মোমিন রহমান: নজরুলসংগীত সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?
ফরিদা পারভীন: নজরুলের উপমা তিনি নিজেই। নজরুল তাঁর গানের জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করেছেন তা অন্য কারও গানে নেই। একজন সংগীত সমালোচকের অভিমত—সুরকার হিসেবে নজরুল হলেন পঞ্চগীতি কবির মধ্যে সেরা—এই কথাটার সঙ্গে আমি একমত। নজরুল নিজেই তাঁর বেশিরভাগ গানে সুর দিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। সেই কারণে নজরুলসংগীতের উৎকর্ষতা অনেক বেশি। এছাড়াও নজরুলের গানে বৈচিত্র্য বেশি। তাই শ্যামা সংগীত, প্রেম সংগীত, ইসলামী সংগীত কিংবা উদ্দীপনামূলক সংগীত একেকটা থেকে অন্যটা ভীষণ আলাদা। তাই দেশ ও জাতির জন্য যতটুকু প্রজ্ঞা হওয়ার দরকার এটা নজরুলের গান না শুনলে কেউ উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না।
মোমিন রহমান: লালনগীতির প্রতি ভালোবাসা তৈরির গল্পটা জানতে চাই
ফরিদা পারভীন: ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন/ সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন’...এই গানটি দিয়ে শুরু হয়েছিল আমার লালনগীতির পথচলা। এই গানটি শিখতে সহায়তা করেছিলেন আমার গুরু মোকসেদ আলী সাঁইজী। লালনের গান শুরু করার পর থেকে আজ সারা পৃথিবীতে আমার যে নাম ও সম্মান তৈরি হয়েছে, তার মূলে রয়েছেন আমার এই গুরু। এছাড়া জীবনজুড়ে বাবা-মা তো আছেনই। তবে লালনগীতির শুরু হয়েছিল অনেকটা অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো। তখন ১৯৭২ সালের দিকে কুষ্টিয়াতে লালন সাঁইজীর আখড়াতে ভারতের পুণ্যদাস বাউল এসেছিলেন। ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন’ এই লালনগীতির জন্য প্রথম একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আমাকে অনুরোধ করছিলেন। তারপর আমার গুরু অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমি তখন আমার গুরুকে জানিয়ে দেই যে, ‘এসব ফকির-ফাকরার গান আমাকে দিয়ে গাওয়াবেন না। আমার পছন্দ হয় না।’ তখন আমার গুরু বললেন, ‘তুই একটা গান করে দেখ, যদি ভালো লাগে পরে আবার করিস।’ সেই রাতে আমি ঘুমঘোরে উপলব্ধি করছিলাম যে কেউ একজন আমাকে বলছে, ‘সাঁইজীর গান করলে তোর ভালো হবে। তোর সত্যি সত্যি ভালো হবে। তুই সাঁইজীর গান কর।’ এই বিষয়টা আমার ভেতরে লালনগীতির প্রতি অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিল। যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম আমার মায়ের কোলে মাথা রেখে তখন আমার মা দেখেছিলেন যে এপাশ-ওপাশ করছি। ঘুম আসছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী রে তোর গান গাওয়া ভালো হয় নি আজ ?’ কারণ মা জানতেন গান ভালো না হলে আমার মধ্যে অস্থিরতা কাজ করে। তখন মাকে আমি জানালাম ‘গান গাওয়া নিয়ে তো সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। কিন্তু এখন তো দেখছি গান আমাকে আরও শিখতে হবে।’ এই কথা শুনে মা বলেছিলেন, ‘যদি ইচ্ছা হয় আরও গান শিখবি। সব গানই অল্প অল্প করে শিখে রাখতে হয়।’ মায়ের উৎসাহ পেয়ে নতুন উদ্যমে আমার গুরুর সহায়তায় শুরু হয় লালনের গান শেখা। এভাবেই শুরু হলো লালনকে ধারণ করা, লালনকে লালন করা।
মোমিন রহমান: লালন ফকিরের বিষয়ে বলা হয়, গানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে পেতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।
ফরিদা পারভীন: লালন ফকিরের গান হচ্ছে ভাববাদী গান। বলা হয়, গানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে পেতে চেয়েছেন তিনি। এটি বেশ সত্য কথা। প্রথমত, লালন সাঁইজী তার দীর্ঘ ১০৬ বছরের জীবনে বিভিন্ন আঙ্গিকের এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় করেছেন তাঁর গানে। যেমন দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব, আল্লাহ-নবী তত্ত্ব...এভাবে সবই সমন্বয় করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, লালন সাঁইজি মানবাত্মা ও পরমাত্মার সাথে মিলনের যে আকুতি সেখানে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাঁর গান যাকে বলে মূলত আত্মসমর্পনী গান অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে নিজেকে নিবেদন করা। ‘নিগূঢ় প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে, যে প্রেমেতে আল্লাহ নবি মেরাজ করেছে’ এটা হলো প্রেমতত্ত্ব গান। এখানে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার প্রেম বোঝানো হয়েছে। এই গানটির মাধ্যমে যেমন ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে তেমনি সনাতনী ধর্মের কথা রয়েছে—‘সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে,/ ও সে বাজিয়ে বাঁশি ফিরছে সদাই,/ কুলবতীর কুলনাশে, মজবি যদি কালার পিরিতি,/ আগে জান গে যা তার কেমন রীতি’ এই গানটিতে। অথবা ‘লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন, চলো গোকুলবিহারী, গোষ্ঠে চলো হরিমুরারি।’ অথচ কিছু মানুষ লালনকে নানা ধরনের ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে ফেলতে চায়। কিন্তু তিনি সব ধর্মের সমন্বয় করেছেন। সেজন্য তিনি গেয়েছেন ‘বিধাতা স্বর্গের রাজা আমায় করে রাখলেন প্রজা,/ ‘দেয় গো সাজা, কারও দোহাই মানে না।’ আবার ‘পারে কে যাবি নবির নৌকাতে আয়’...এখানে নিজ নিজ কাজের জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে। আবার লালন যখন বলছেন, ‘বে-সরা নেয় যারা তুফানে যাবে মারা একই ধাক্কায়’—এখানে তিনি জানাচ্ছেন ব্যক্তিটির ইমান শক্ত নয়। জাগতিকভাবে অনেকে পীর ধরে যাতে তিনি পারে নিয়ে যেতে পারেন। অথচ লালন তার গানে বলেছেন ‘পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়, রূপকাঠের নৌকাখানি নাই ডুবার ভয়, নবী না মানে যারা, মোয়াহেদ কাফের তারা, যে মুর্শিদ সেই তো রাসুল, তাহাতেই নাই কোনো ভুল, খোদাও সে হয়’—এই গানে লালন বলেছেন নবী হলেন সব ধর্মের পথপ্রদর্শক। এভাবে খুব সাধারণ কথার মধ্যে এত গভীরতা রয়েছে যে আমি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। এছাড়া ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়’ এটা বিশুদ্ধভাবে দেহতত্ত্বের গান। আবার দেহতত্ত্বের গানে বলেছেন, ‘চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি, ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়’—নিজেকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করো। ‘মন তুই রৈলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে’—এটাও দেহতত্ত্বের গান। একসময় দেহটা খসে পড়বে। এদিকে দৈন্য গান বা প্রার্থনা গানের মধ্যে রয়েছে—আমার মনের বাসনা, আশা পূর্ণ হলো না, বাঞ্ছা করি যুগল পদে, সাধ মেটাব ওই পদ সেধে, বিধি বৈমুখ হলো তাতে, দিলো সংসার যাতনা, বিধাতা সংসার রাজা, করে রাখলে আমায় প্রজা, ও সে কর না দিলে দেয় গো সাজা, কারও দোহাই মানে না, পড়ে গেলাম বিধির বামে, ভুল হলো মোর মূল-সাধনে, লালন বলে, এই নিদানে মুরশিদ, ফেলে যেও না—এখানে তিনি প্রার্থনা করেছেন। ‘আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে, তারে জমন-ভর একবার দেখলাম নারে’—এটাও প্রার্থনা। এছাড়াও নিজেকে চেনার জন্য যে গানগুলো আছে এরমধ্যে ‘আপন ঘরের খবর নে না, অনা’সে দেখতে পাবি, কোনখানে সাঁইর বারামখানা।’... আবার ‘মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে’ এখানে পরমেশ^রের সাথে মিলনের আকুতি জানিয়েছেন। কারণ লালনের সব গানের মাঝে একটা মিলনের বিষয় আছে। সেখানে সুরের সাথে, গানের অর্থের সাথে মিল কিংবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সব মহাজনরাই যেমন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, পাগলা কানাই, কাঙ্গাল হরিনাথসহ সবাই তাঁদের নিজস্ব ভাষায় রচনা করেন। তবে মূল বিষয়টাই হলো আধ্যাত্মবাদ। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সমর্পণ। একটা খাতাতে আমরা রুটিনমাফিক ভালো কাজগুলো লিখতে পারি কিন্তু খারাপ কাজগুলো লুকিয়ে রাখি। সেজন্য ইসলাম ধর্মে বলা আছে, ‘এমন কোনো ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করবে না যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যক্তিও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে।’ তেমনি হিন্দু ধর্মেও উল্লেখ আছে, ‘তুমি আগে নিজেকে শুধরাও। নিজের আত্মাকে দোষারোপ কোরো না বরং তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো।’ লালন সাঁইজি নিজেও আত্মাকে শুদ্ধ করে পরমাত্মার প্রতি নিজেকে নিবেদন করেছেন। আমার গুরু লালন সাঁইজি সব ধর্ম থেকে বেরিয়ে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর গানগুলোও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই রচনা করে গেছেন।
মোমিন রহমান: লালনের গানে ‘মানুষ’ শব্দটি এসেছে অনেকবার। এই শব্দগুলো দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করেন ?
ফরিদা পারভীন: লালন ফকির একজন মানবতাবাদী সাধক। তিনি জীবনভর মানবতার গান গেয়েছেন। ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ এই গানে ‘মানুষ’ শব্দটি দিয়ে মানুষরূপী মানুষ নয় বরং মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর এমন অনেক গান আছে যেমন, ‘এই মানুষে সেই মানুষ আছে, কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বী তারে খুুঁজে বেড়াচ্ছে’ বা ‘মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার,/ সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার’ কিংবা ‘কেন কাছের মানুষ ডাকছো শোর করে’ আবার ‘সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে’, ‘মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে’ এবং ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন, সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন’, ‘যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জাতি গোত্র নাহি রবে,/ এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে’, ‘এমন মানব জনম আর কি হবে,/ মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে’, ‘কত লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে, আমরা পেয়েছি এই মানব জনম’—এমন অনেক মানবতাবাদী গান গেয়েছেন লালন সাঁইজী। কারণ এই মানুষ সেই মানুষ নয়। রাস্তাঘাটে যে মানুষ গামছা বিছিয়ে শুয়ে থাকে। সেই হলো সহজ মানুষ। আর কঠিন হওয়া অনেক সহজ। তবে সহজ হওয়া অনেক কঠিন। এটা আমি আমার জীবদ্দশায়ও দেখছি। লালন সাঁইজী জীবনভর মানবতাকে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। তাই তার গানে ‘মানুষ’ শব্দের এত ব্যবহার হয়েছে। তিনি তাঁর গানে ‘ফানা’ শব্দটাও ব্যবহার করেছেন। এই ফানা মানে হলো, নিজেকে যখন কেউ পরমাত্মার লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে তখন তার ভেতরটা অস্থিরতায় ভরে ওঠে। আবার লালন সাঁইজির গানে ‘মারেফত’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। সেখানে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফত-এর মধ্যে ‘মারেফত’ শব্দটি হচ্ছে নিগূঢ়তত্ত্ব। আমি লালন ফকিরের সেই নিগূঢ়তত্ত্বে যাই নি। আমি তাঁর ভাবতত্ত্ব নিয়ে আছি। সেই ভাবে ভাব মেলানো এবং উচ্চারণ করা অর্থাৎ গান নিয়ে আছি। কারণ গান করতে গেলে সঠিক উচ্চারণ জানতে হবে। এছাড়াও সুরের অবয়বটা সঠিকভাবে গলায় আনতে হবে। উপস্থাপনাও ঠিকভাবে করতে হবে। তালযন্ত্রের সাথে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাই আমি লালনের আধ্যাত্মবাদের দিকে না গিয়ে তাঁর ভাবতত্ত্বটাই বুঝি এবং মেনে চলি।
মোমিন রহমান: লালনের গানে কিছু আলো-আঁধারি ভাষা আছে যা শুধু বাউলদের বোধগম্য হয়। এই বিষয়ে কিছু বলুন।
ফরিদা পারভীন: আমি লালন ফকিরের সব গান গাই না। কারণ তাঁর ভাবতত্ত্ব বিষয়ে বুঝি কিন্তু আধ্যাত্মবাদ নিয়ে আমার তেমন ধারণা নেই। তাই সেই আলো-আঁধারি ভাষাটা নিজেও বুঝে উঠতে পারি না। তবে অনেকে এই কাজ করে থাকে। লালনের গান না বুঝলেও গেয়ে থাকে। অনেকে চমকও লাগিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে লালনের একটি গান আছে যে, ‘দেখনা মন ঝাক মারি এই দুনিয়াধারি’—এখানে লালন ফকির নিজেই বলেছেন, তাঁর গান নিয়ে নানারকম ধ্বজা ধরছে। কিন্তু আমি তা করি না। কারণ আমি তাঁর বাণী দ্বারা প্রভাবিত। সুর দ্বারা প্রভাবিত। যতটা তার বাণী বুঝি ততটাই গেয়ে থাকি। তাই সব সময় লালন ফকিরের ভাবের গানগুলোই ভালো লাগে।
মোমিন রহমান: আপনার দেশাত্মবোধক গানগুলোও মন ছুঁয়ে যায়। এই সম্পর্কে কিছু বলুন।
ফরিদা পারভীন: খুলনা বেতার থেকে প্রথম দেশাত্মবোধক গান গাই। এটি মূলত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ‘এই পদ্মা, এই মেঘনা; এই যমুনা সুরমা নদী তটে,’ এই গানটি প্রথম গেয়েছিলাম। গানটির গীতিকার ও সুরকার হলেন আবু জাফর। তখন সদ্য কুষ্টিয়াতে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুলনা বেতারের জন্য গানটি করব কি না ? প্রথমত গানটি ভালো লাগে নি আমার। পরে যখন বাংলা একাডেমিতে, রাজশাহী বেতারে এবং বিটিভিতে গাইলাম তখন গানটির প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। তবে গানটি নিয়ে কষ্টদায়ক স্মৃতিও রয়েছে। যখন এই গানটি বেতারে দেওয়া হলো তখন চিঠি পাঠিয়ে জানাল ‘আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, এই গানটি আমাদের মনপুঃত হয় নি। তবে আপনি চেষ্টা করে যান।’ অথচ এই গান, বিশে^র যতগুলো দেশে আমাদের দেশের অ্যাম্বেসি আছে সবাই এই গানটি ভালোবাসে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ যেমন চীন কিংবা জাপানের লোকেরা এই গানটি ভালোবেসে এদেশে আসে এবং বাংলা শিখে গানটি করে থাকে। যাহোক, এক পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গান শুরু করি। এর সাথে কিছু আধুনিক গানও করেছি। তবে আধুনিক গান বেশি গাওয়া হওয়া নি। সেগুলো অনেক পুরোনো কথা। পরেও গাইতাম। ভালো লিরিক্স পেলে অবশ্যই গাইতাম। এখন রফিকুজ্জামান, অনুপ ভট্টাচার্য যদি গান রচনা বা সুর করেন আমি সেই গান নিশ্চয় গাইব। আমি গানের সংখ্যা বাড়াতে চাই নি বরং গুণগত মান বাড়াতে চেষ্টা করেছি।
মোমিন রহমান: শিল্পীদের মধ্যে অন্যরাও লালনের গান গাইছেন। অন্যদের এবং আপনার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বলে মনে করেন ?
ফরিদা পারভীন: সংগীত হলো গুরুমুখীবিদ্যা। তাই প্রথমেই সঠিক গুরু নির্বাচন করতে হবে। সঠিক গুরু ছাড়া সংগীত যথাযথ শেখা যায় না। দ্বিতীয়ত পর্যায়ক্রমে সংগীতের উপকরণগুলো শিখতে হবে। লালনগীতি যারা গায় সেই ফকিরদের গানের কণ্ঠ ভালো থাকায় তারা একতারার সাথে মিলিয়ে একই তালের গান করে থাকেন। অন্য তালের গান তারা গাইতে পারেন না। পরিশীলিত গলায় যখন একটি গান গাওয়া হয়, তখন সেটির আবেদন এক ধরনের হয়। আবার খালি গলায় গান গাওয়ার আবেদনটা আরেক রকম হয়ে থাকে। তবে ফকিরেরা এক গানের কথা অন্য গানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। কারণ তারা শিক্ষিত না। ফলে গানের মানে বুঝে না। তাই লালন ফকিরের গান গাইতে গেলে তাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। আমি প্রায় সময়ই একটা কথা বলি যে, পাঁচটা বই পড়ে নোট করা যায় কিন্তু সাতটা স্বরে গলা মেলাতে হয়। সাগরের যেমন তলদেশ আছে তেমনি লালনের বাণী এবং সুরের তলদেশ সারাজীবন তালাশ করতে হয়। লালন বলে গেছেন, ‘ভক্তি দ্বারা বান্ধা আছে সাঁই।’ ভক্তি না থাকলে পরমাত্মা কাছে আসবে না। প্রথমে গানের প্রতি প্রেম থাকতে হবে। কারণ প্রেমই সব।
মোমিন রহমান: বর্তমানে টেলিভিশনকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে কোনো অভিমত থাকলে বলুন।
ফরিদা পারভীন: আমি খুব স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, মাত্র একটা গান করে কারও মঞ্চে উঠা উচিত নয়। আমি নিজেও এই কাজটি করি নি। কিন্তু এখন টেলিভিশনগুলোতে এটাই হচ্ছে। একটা গান শিখেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। লালনকে নিয়ে জাপানে, আমেরিকায় এমনকি ভারতবর্ষেও গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু ভারতে পরিস্থিতি ভিন্ন। সেখানে বাংলা টেলিভিশনগুলোতে প্রতিযোগিতার নামে লালনের গানগুলো নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। সেখানকার একটা গণমাধ্যম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের দেশের লালনচর্চা এবং আমাদের দেশের লালন চর্চার মূল পার্থক্য কী ? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমাদের লালনচর্চা যথাযথ হয় কিন্তু আপনাদের লালনচর্চা যথাযথ হয় না। কারণ গান নিয়ে যত্রতত্র যা খুশি তা করা যায় না। বিশেষ করে সাঁইজির গান নিয়ে তো নয়ই। নিজের মতো করে গাওয়া যায় না। যা সেখানকার জী বাংলার সংগীতের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে গাওয়া হচ্ছে। লালনের বাণীগুলো এলোমেলো করে দিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। এভাবে আকাশ মিডিয়াগুলো গানের চর্চাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখনকার সংগীত এবং এখনকার সংগীতের মধ্যে পার্থক্যটা হলো, এখন সস্তা বাহবা পাওয়ার সংগীত। সস্তাভাবে মানুষকে বশীভূত করে কিছু টাকা পাওয়া হচ্ছে এখনকার সংগীত। একদম তৃণমূলের কিছু মানুষ দুয়েকটা গান শিখে প্রতিযোগিতায় এসে জিতে গিয়ে বাড়ি-গাড়ি তৈরি করছে।
মোমিন রহমান: একজন মরমী কবি এবং সংগীতসাধক হিসেবে লালনকে বর্তমান সময়ে কি যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় ?
ফরিদা পারভীন: কুষ্টিয়াতে লালনের আখড়ার পাশেই একটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। সেখান থেকে থুতু, কাশিসহ ময়লা ফেলা হয় আখড়ায়। একজন মরমী কবি এবং সংগীতসাধক হিসেবে লালন ফকিরকে মোটেই সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে আমরা প্রতিবাদও জানিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। ন্যূনতম সম্মান যদি না দেখাতে পারি তবে সুসংস্কৃতি গড়ে উঠবে না। এছাড়া লালন ফকিরের মতো এত উঁচু মানের মানুষের কাজ নিয়ে গবেষণাও বেশ অপ্রতুল। অথচ এই দেশের মাটিতে একজন লালনের জন্ম হয়েছে। এই দেশের জন্যই নয় সারা পৃথিবীতেই লালন ফকির একজন মহাজন। তাঁর সৃষ্টি নিয়ে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন। এদেশের বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভেতরে লালনের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করতে হবে। নতুন প্রজন্ম নতুনভাবে আবিষ্কার করবে লালনকে। এটা বেশ জরুরি।
মোমিন রহমান: লালনের সুর ও ভাবাদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ‘অচিন পাখি সংগীত একাডেমী’ নামে আপনার একটি বিদ্যায়তন রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানি সম্পর্কে জানতে চাই।
ফরিদা পারভীন: ‘অচিন পাখি সংগীত একাডেমী’র মাধ্যমে মূলত আমার গুরুর ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাই ফরিদা পারভীন ফাউন্ডেশনের পক্ষে এই সংগীত শিক্ষালয় গড়ে তুলেছি। আমি এই শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তেজগাঁওয়ের তেজকুনিপাড়ায় এর ভবন। এখানে শেখানো হয় সংগীত, বাঁশি, তবলা, চিত্রাংকন ও গিটার। আমরা যে সময়টায় গান শিখেছি তখন গুরুদের যতটা ভক্তি করতাম তেমনি গুরুরাও আমাদের স্নেহের ছায়ায় রেখে শিক্ষা দিতেন। গুরু-শিষ্যের চমৎকার বন্ধনে সংগীতবিদ্যা শেখা হয়ে যেত। আমি আমার শিক্ষালয়েও শিক্ষার্থীদের মাঝে সেই হৃদয়াঙ্গম পরিবেশ দিয়ে শেখাতে চাই। যা আমি শিখেছি তা যেন আমার বিদ্যার্থীদের ছড়িয়ে দিতে পারি সেই চেষ্টাই থাকবে। ফলে আমার হৃদয়ের গভীরে যেমন আমার গুরু এবং লালন ফকির বিরাজমান তেমনি শিক্ষার্থীদের হৃদয়েও লালন ফকির, আমার গুরু এবং আমি যেন রয়ে যাই।
মোমিন রহমান: দেশের বাইরে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা বলুন।
ফরিদা পারভীন: বিদেশে আমাকে সুফি আর্টিস্ট হিসেবে গণ্য করে। জাপানের কয়েকজন নাগরিক আমার কাছ থেকে লালনের গানের তালিম নিয়ে যায়। কিওকতাগাদা আমার ছাত্রী। তাঁর স্বামীর নাম তাগাদা। আরেক শিক্ষার্থী ফুপুজাওয়া। তিনি জাপানের একটি বিশ^বিদ্যালয়ের পেইন্টিংয়ের শিক্ষক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় তিনি এদেশে ছিলেন। এই দেশের প্রতি তাঁর অবদানও রয়েছে। তিনি গামছা ও লুঙ্গি পরেন। তার ছেলের নাম সোনার এবং মেয়ের নাম বাংলা। এই যে বাংলাদেশের প্রতি প্রীতি, এটি তার মধ্যে রয়েছে। একবার তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জাপান যাব কি না ? আমি রাজি হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছেন সম্মানীর কথা। কত টাকা নেব আমি। আমি তখন বলেছি, যেখানে ভালোবাসা জড়িত, সেখানে অর্থ দিয়ে সরিয়ে রাখছেন কেন ? পরে তারা ২০০২ সালে আমাকে জাপানে নিয়ে গিয়ে একটা প্রোগ্রাম করিয়েছেন। জাপানে যখন আমি ‘সময় গেলে সাধন হবে না’ গেয়েছি, তখন দেখেছি দর্শক-শ্রোতারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমিও কাঁদছি এবং তারাও কাঁদছে। সেখানের সাংবাদিকেরা তাদের কান্নার কারণ জানতে চেয়েছে। তখন তাদের উত্তর হলো, ‘তাঁর যে গায়কী, তাঁর মুখের যে অভিব্যক্তির সেটি আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা আমাদের আবেগ আটকে রাখতে পারি নি।’ এমন ঘটনা সুইডেনেও ঘটেছে। সুইডেনের রানি তাঁর গ্রামের বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। তখন সাংস্কৃতিক দল হিসেবে আমরা গিয়েছিলাম। ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানটি যখন গেয়েছিলাম তখন রানিও আবেগাপ্লুত হয়ে একই কথা বলেছেন। আর বলেছেন, ‘আমার তো ভাষা বোঝার দরকার নেই। কারণ সুর হচ্ছে সর্বজনীন।’ এছাড়া আমাদের ওপার বাংলায়ও আমাকে ভীষণ সম্মান দেখিয়েছে। একটা হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার পা ছুঁয়ে সালাম করেছিলেন। সেখানে সিস্টার নিবেদিতা বিশ^বিদ্যালয়ে লালনের ওপর একটি কোর্স করিয়ে এলাম। বিশ্লেষণ করে করে চারটি গান শিখিয়ে এসেছি। তারা বেশ সম্মান করেছে। প্রথমবার যখন পশ্চিমবঙ্গে গেছি মোহাম্মদ রাফি হলে গান গেয়েছি। আমি ছিলাম সাথে ছিলেন সৈয়দ হাদি ভাই, শবনম মুস্তারিসহ অন্যরা। সেখানে লালনের গান গাওয়ার পর—তখন একটা পত্রিকা বের হতো যেখানে ভারতীয় একজন নৃত্যশিল্পী, নৃত্য পরিকল্পক ও অভিনেতা উদয়শঙ্কর আমাকে নিয়ে লিখেছিলেন, ‘ফরিদা পারভীনের কণ্ঠস্বরটা ভারতবর্ষে যদি ফ্রেম করে বাঁধিয়ে রাখা যেত তাহলে আমরা বেশ উপকৃত হতাম।’ এমনকি আশা ভোঁসলের স্বামী রাহুল দেববর্মন, পঞ্চমদা, তিনি তাঁর ম্যানেজার দিয়ে হন্য হয়ে আমাকে খুঁজেছেন—যে বাংলাদেশের আর্টিস্টরা গান গাইতে এসেছে তারা কারা। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে খুঁজে পেলেন না। সেখান থেকে চলে এলাম। ফলে পঞ্চমদা আমাকে আর পেলেন না। যদি তিনি পেতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর সুর করা গানে আমাকে গাওয়াতেন। কারণ বাংলাদেশের লোকজ সুরের যে ঐতিহ্য সেটি তো তাঁর মধ্যে আছে। এরপর ২০০৮ সালে জাপানে ফুকুয়াকা অ্যাওয়ার্ড, যা এশিয়ার নোবেল বলে খ্যাত, সেটি পেয়েছি। সেসময় এই পুরস্কারটি আমরা তিন নারী পেয়েছিলাম। হংকংয়ের একজন চলচ্চিত্রকার, শ্রীলংকার একজন আইনজীবী আর আমি সংগীতের। এছাড়াও মালয়েশিয়ার একজন শিক্ষক এই পুরস্কার পেয়েছেন। সেসময় রাজা আমাকে যখন মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন তখন তিনি বললেন, ‘আমাদের প্রাসাদে তোমাদের যেতে হবে।’ কিন্তু রাজপ্রাসাদে নেওয়ার মতো কী নেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু আমাদের হৃদয়টা তো আকাশের মতো। তাই হাতের কাজ করা একটি কটি, ওড়না ও সালোয়ার নিয়ে গেছি। তারা বেশ খুশি হয়েছেন। আমি হিরোশিমা বিশ^বিদ্যালয়েও গেছি। তাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা জেনেছি। জাপানের প্রতিটা রাজ্যে বেড়িয়েছি এবং গান করেছি। সম্প্রতি আমেরিকায় লালনের তিরোধান উৎসব উদ্বোধন করে এলাম। তারপর সেখানকার অন্য স্টেট থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা হয়েছে।
মোমিন রহমান: বর্তমানে কোন কাজগুলো করছেন এবং কোন কাজগুলো বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা রয়েছে ?
ফরিদা পারভীন: ‘মরিলে সব হবে মাটি, ত্বরায় এই ভেদ লও জেনে’, এই গানটি দিয়ে লালন সাঁইজি বলেই দিয়েছেন, ‘তাড়াতাড়ি ভেদটা জেনে নাও।’ তাই আমার ইচ্ছে রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজও করে যাচ্ছি, এটা হলো স্টাফ নোটেশন। এই কাজে সহায়তা করছেন ইদ্রিস আলী। তিনি শুদ্ধ নজরুল সংগীতের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। নজরুল একাডেমিতে ছিলেন। তিনি মূলত নজরুলের স্বরলিপির কাজগুলো করেন। লালনের গানের গবেষণার কাজ করার জন্য আদি-অন্ত নতুন প্রজন্মকে জানানো ও শেখানো প্রয়োজন। যেখানে তাদের থাকার জন্য হোস্টেল থাকবে। সবাই সেখানেই থাকবে এবং শিখবে, এমন দশ কাঠা জায়গা দরকার। সরকারের অনেক পতিত জমি আছে, সেখান থেকে যদি পেয়ে যা, আমি আমার মতো গড়ে তুলব। এছাড়াও আমার গানগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে ভালোভাবে রেখে যেতে চাই। একটা ভালো খবর হলো, নরসিংদীতে লালন সাঁইজীকে নিয়ে একটি বিশ^বিদ্যালয় করা হচ্ছে। সেখানে আমাকে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই বিশ^বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে। তখন হয়তো লালনকে নিয়ে কিছু কাজ করা সম্ভব হবে। তখন সংগীতের একটি ঘরানা থাকবে। এভাবেই লালনকে ধারণ করতে চাই, লালনকে লালন করতে চাই।






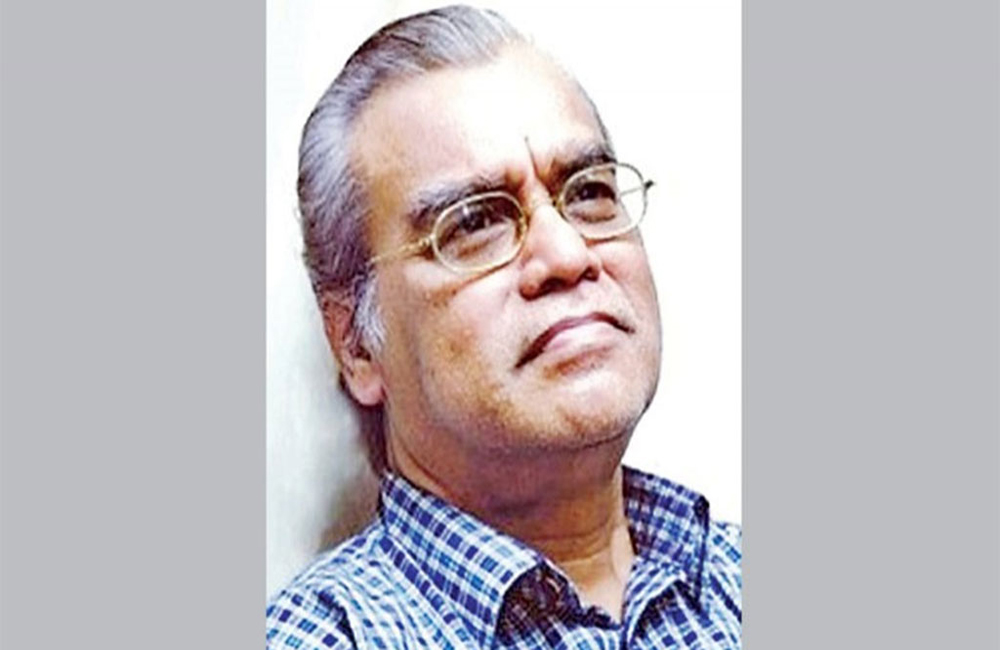
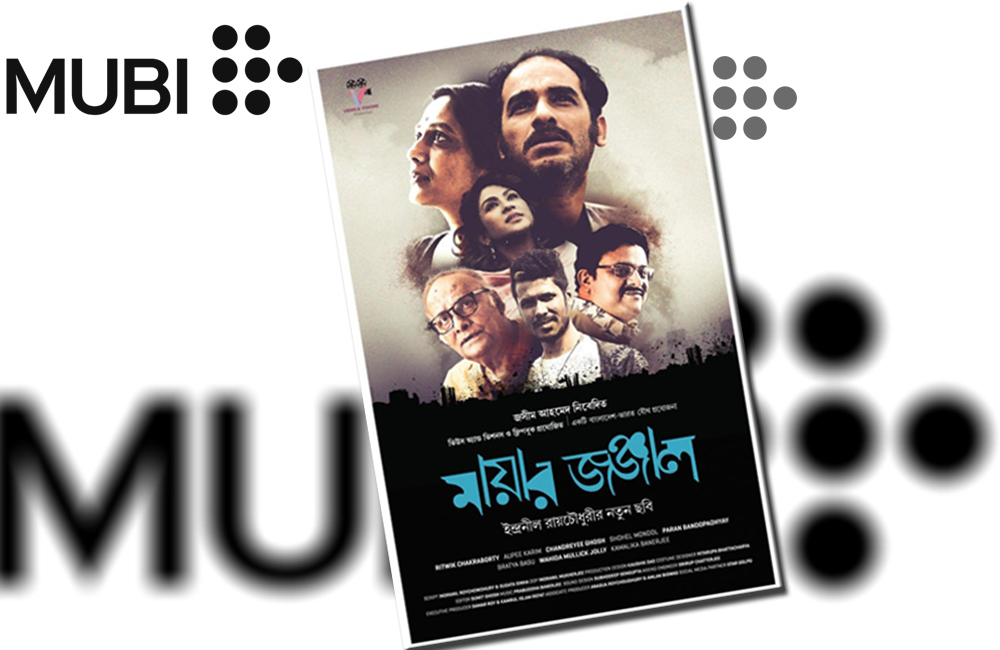
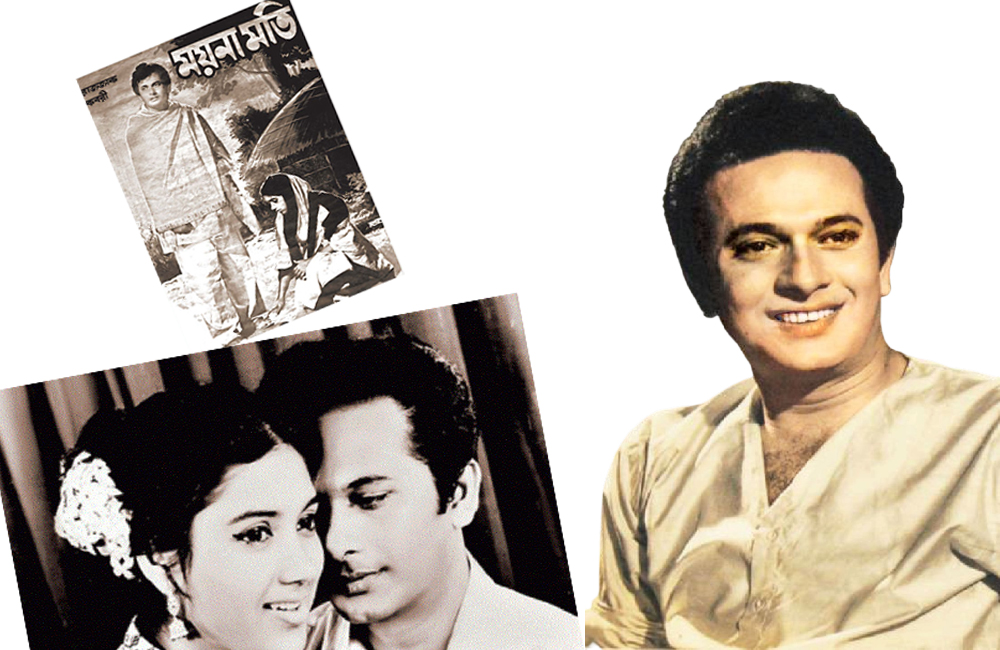

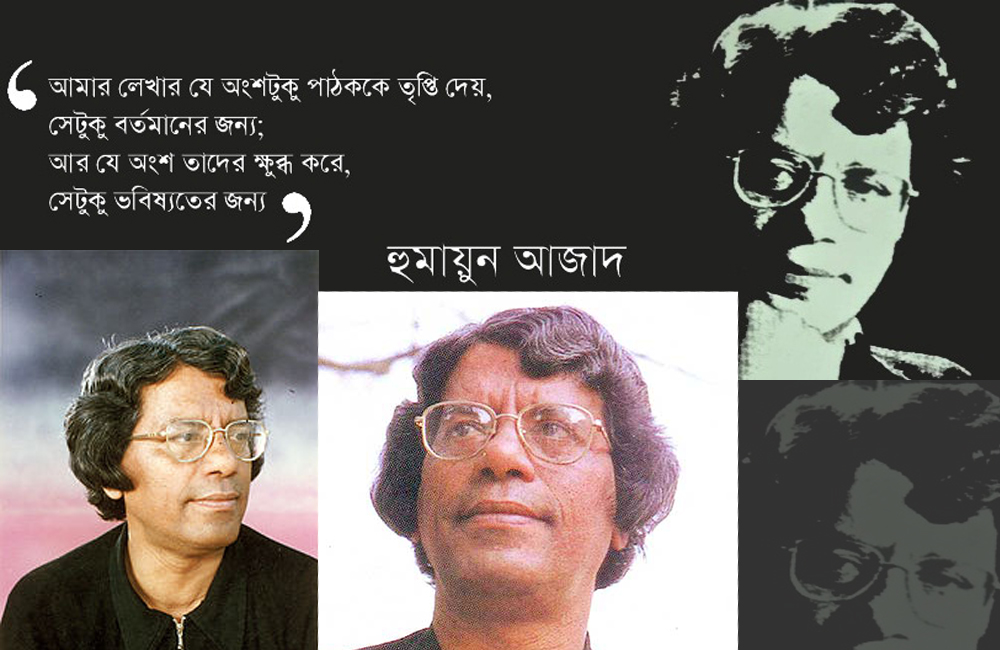




Leave a Reply
Your identity will not be published.