সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম—অর্থাৎ অনেকের কাছে পরিচিত নাম এস. এম. আই.—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমার এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। সাধারণত এমন ক্ষেত্রে যেমন ঘটে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে চলাফেরা করতাম। পরে যখন আমরা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত হই, তখনই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ঘটে। একদিন জানতে পারলাম, তিনি আমার চেয়ে মাত্র দুই দিন বড়—তখন থেকেই আমি তাঁকে মজা করে ডাকতাম ‘দুই দিনের দাদা’ বলে। বিষয়টি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৃত্তের কাছে বেশ আনন্দের ছিল; এই বৃত্তে আমার সহপাঠী ফকরুল আলমও ছিলেন। আমাদের তিনজনকে—মনজুর, ফকরুল আর আমি—অনেকে একসঙ্গে চিনত। তবে অধ্যাপক নিয়াজ জামান (আমাদের শিক্ষক, পরবর্তীসময়ে সহকর্মী ও পরামর্শদাতা) একবার বলেছিলেন, ‘তিনজনেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, তবুও খুব ভালো বন্ধু।’
আমাদের বন্ধুত্ব শুধু আড্ডায় সীমাবদ্ধ ছিল না; সাহিত্য নিয়েও ছিল গভীর আগ্রহের মিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবুল খায়ের লিটু ভাই আমাদের টেনে নিলেন তাঁর বেঙ্গল ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন প্রকাশনা উদ্যোগে—যেগুলোর পরিসর ছিল জনপ্রিয় থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যন্ত। একদিকে ছিল ঝকঝকে ম্যাগাজিন ICE Today (নামটি দিয়েছেন লিটু ভাই) এবং ‘চারবেলা চারদিক’ (নামটি দিয়েছেন মনজুর ভাই)। অন্যদিকে ছিল উচ্চমানের শিল্পবিষয়ক পত্রিকা Jamini, পরে ‘কালি ও কলম’ এবং Six Seasons Review সব মিলিয়ে মনজুরই ছিলেন এসব উদ্যোগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ‘চারবেলা চারদিক’ সম্পাদনা করতেন এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুর পর ‘কালি ও কলম’-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। পাশাপাশি তিনি অন্য পত্রিকাগুলোর সম্পাদকমণ্ডলীরও সদস্য ছিলেন। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বাইরে তিনি ছিলেন সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন কমিটিতে। ‘অন্যদিন’ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবেও যুক্ত ছিলেন। আমি আশঙ্কা করছি, তাঁর বিকল্প খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে।
মনজুরের সাহিত্যিক জীবনব্যাপী সময় অর্ধশতাব্দীরও বেশি। অনেকেই জানেন না—তাঁর প্রথম সাহিত্য প্রকাশ ছিল কিছু কবিতা। তিনি নিজেই বলেছিলেন, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে কবি হিসেবে খুব দূর এগোনো সম্ভব নয়; তাই তিনি গদ্যে মন দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে একজন শিল্পসমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন—বিভিন্ন পত্রিকায়, প্রদর্শনীর ক্যাটালগে এবং সংকলনে লিখতে শুরু করেন। তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে Routledge Handbook of Bangladeshi Literary Culture-এ, যা আমি অধ্যাপক শামসাদ মোর্তুজার সঙ্গে সম্পাদনা করছি।
শিল্পসমালোচক ও সাহিত্যসম্পাদক হিসেবে তাঁর কাজগুলো ছিল বিশেষায়িত। তবে জনপরিসরে তিনি পরিচিতি পান একজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে—পত্রিকার কলাম, টেলিভিশনের টকশো এবং সামাজিক মন্তব্যের মাধ্যমে। এই অংশটা আমি তেমনভাবে অনুসরণ করি নি, তবে শুনেছি তিনি পাঠক ও দর্শকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর কলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’ সাহিত্যকেন্দ্রিক হলেও তরুণ পাঠকদের জন্য ছিল শিক্ষণীয় ও প্রভাবশালী।
যাঁরা আজকের জেন-জি বা আলফা প্রজন্মের, তাঁদের জন্য কল্পনা করাও কঠিন—ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন আসার আগে সাহিত্যজগৎ কেমন ছিল! সেই সময়ে কোনো লেখক নোবেল পুরস্কার পেলে খবরটি আসত টিভিতে, আর পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকেরা তড়িঘড়ি করে তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে লেখা খুঁজতেন। অচেনা লেখক হলে বই জোগাড়ের জন্য হন্যে হয়ে যাওয়া, কষ্টে-সৃষ্টে একটা পড়ার মতো লেখা তৈরি করা—সবই ছিল সেই যুগের অংশ। মনজুর ভাইও এমন অনেক পাঠযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সমাজের নানা বিষয় নিয়েও তিনি মন্তব্য করতেন—সব সময় ভারসাম্যপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গিতে।
তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মনজুরকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখা হবে কথাসাহিত্যিক হিসেবে। আমার বিশ্বাস, তিনি মূলত গল্পকার, যদিও কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছেন সফলভাবে। মনজুরের কথাসাহিত্যিক রূপের জন্ম আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন আমরা তরুণ শিক্ষক, নিয়মিত পরীক্ষার দায়িত্বে থাকতাম। পরীক্ষা চলাকালে ফাঁকে ফাঁকে তিনি বসে কয়েকটি লাইন লিখতেন—বলতেন, ‘একটা খবর দেখেছি বা একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি, সেটার ওপর গল্প লিখছি।’ এ ছিল এক অভিনব পদ্ধতি, যদিও আমি মনে করতাম এতে গল্প মাঝপথে ‘শ্যাগি ডগ’ স্টোরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর দক্ষতা ছিল, তিনি নিয়ন্ত্রণ রাখতেন বয়ানে—ফলে গল্পগুলো হয়ে উঠত আকর্ষণীয়। পরবর্তীসময়ে এই একই পদ্ধতিতে তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন এবং পাঠকমহলে প্রশংসা পেয়েছিলেন।
সাহিত্যিক প্রভাবের ক্ষেত্রে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস নিঃসন্দেহে মনজুরের লেখায় সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছেন। তিনি মার্কেসের প্রতি এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে গিয়ে স্প্যানিশ ভাষা কোর্সও করেছিলেন। আরেকজন প্রভাবশালী লেখক ছিলেন আমেরিকান পোস্টমডার্নিস্ট কার্ট ভনেগাট। মনজুর হয়ে ওঠেন লাতিন আমেরিকান ম্যাজিক রিয়ালিজম ও আমেরিকান পোস্টমডার্নিজম-এর প্রবক্তা, এবং তিনি আনন্দ নিয়ে এসব বিষয় পড়াতেন।
এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বিতর্কও হতো। কখনো কখনো তিনি চরম পোস্টমডার্ন ধারার ‘Anything goes’-এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। আমি বলতাম, এই দর্শন জীবনের অস্তিত্বমূলক ভিত্তিকেই নড়িয়ে দেয়। ভনেগাটের সাহিত্য আমি তাঁর মতোই উপভোগ করতাম, কিন্তু মনে করিয়ে দিতাম—ভনেগাটের কাছে পোস্টমডার্নিজম শুধু একটি সাহিত্যিক কৌশল, যার অন্তরালে রয়েছে এক নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি।
এখন মনজুর নেই—আর কখনো সেই বিতর্কে ফিরব না। তাঁর ছাত্ররা হারিয়েছে এক উদার শিক্ষককে; পাঠকেরা হারিয়েছে তাঁর নতুন রচনার অপেক্ষা। সহকর্মীরা হারিয়েছে তাঁর হাস্যরস আর প্রাণবন্ত উপস্থিতি। তাঁর মৃত্যুর খবর ছিল আকাশ থেকে পড়া বজ্রপাতের মতো। স্টেন্ট বসানোর পর যে আশাব্যঞ্জক উন্নতির কথা জানা গিয়েছিল, তা খুব দ্রুত উল্টে গেল—আমরা অবিশ্বাস নিয়ে সেই পতন দেখেছি।
সৌভাগ্যক্রমে, তাঁর স্ত্রী সানজীদা (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী) তখন বোস্টনে ছিলেন; তিনি তাঁদের ছেলে—যিনি সেখানে আইনজীবী—তাকে সঙ্গে নিয়ে সময়মতো দেশে ফিরতে পেরেছিলেন। শেষ মুহূর্তে কিছু কথা বলতে পেরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে। আমি ভেবেছিলাম, এই সামান্য সুযোগ হয়তো তাঁদের মনে কিছুটা সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু সানজীদা আমাকে বললেন, আমাদের প্রিয় রসিকতার ভঙ্গিতে—“দোস্ত, ক্লোজার বলে কিছু নেই, ওটা শুধু একটা শব্দ।” কথাটা শুনে হৃদয় ভেঙে গেল।
এখন কেবল সেই চিরচেনা প্রার্থনাটাই বলা যায়—আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।
আকস্মিক ও অকালপ্রয়াণে এস.এম.আই-কে স্মরণ
কায়সার হক ০২ নভেম্বর ২০২৫ ০ টি মন্তব্য
Related Articles
প্রকাশিত হলো ড. এম. মারুফ হোসেনের গ্রন্থ AI Success Beyond Perfect Data...
অন্যদিন০৭ ডিসেম্বর ২০২৫অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেখক ড. এম. মারুফ হোসেন। যিনি ইউনিভার্সিটি অব মেলর্বোন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা এআই-এর ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
৩ জনের হাতে জেমকন সাহিত্য পুরস্কার
অন্যদিন০৮ জানুয়ারি ২০২৩বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে জেমকন সাহিত্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজনে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে চেক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র তুলে দেওয়া হয়।
শম্পা কী চায়? (পর্ব ১৭)
এশরার লতিফ১৯ জুলাই ২০২২সাদিয়া চৌধুরী প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে হেডস্কার্ফ আর চশমা খুলে টেবিলে রাখতেই মিলি অস্ফুট স্বরে বলল, শম্পা তুই? ইন্সপেক্টর লাবণি সাদিয়া চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তাহলে কুখ্যাত শম্পা সোহানি?
স্ট্যামফোর্ডে ‘বাংলা টেলিভিশনের ৫০ বছর’ নিয়ে পাঠ আলোচনা
অন্যদিন০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬‘বাংলা টেলিভিশনের ৫০ বছর’ বইকে ঘিরে আয়োজিত পাঠ আলোচনায় উঠে আসে টেলিভিশনের দীর্ঘ পথচলার স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও প্রভাবের কথা।





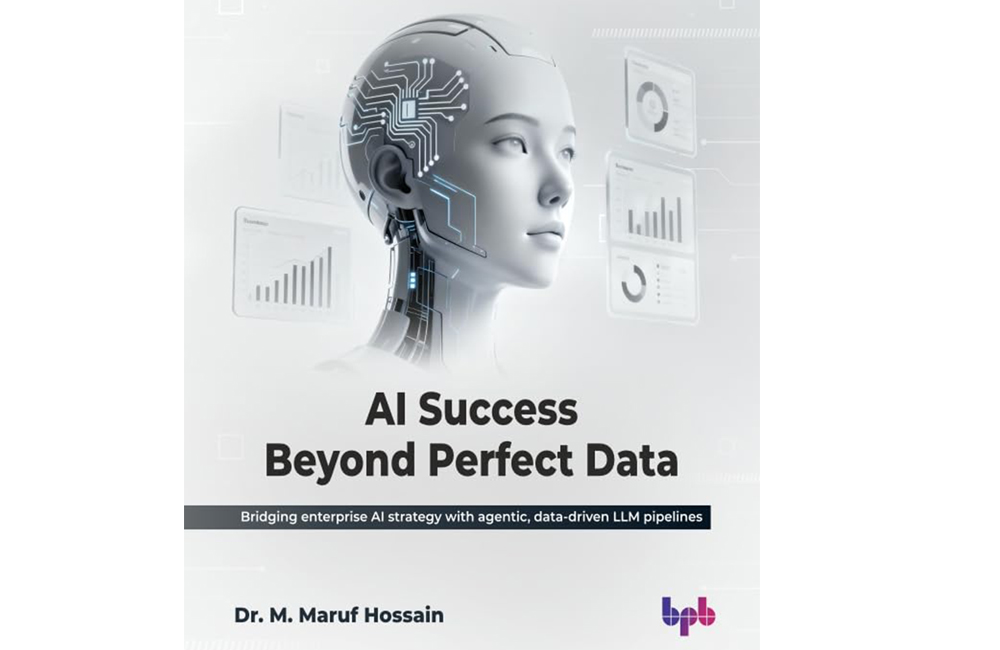
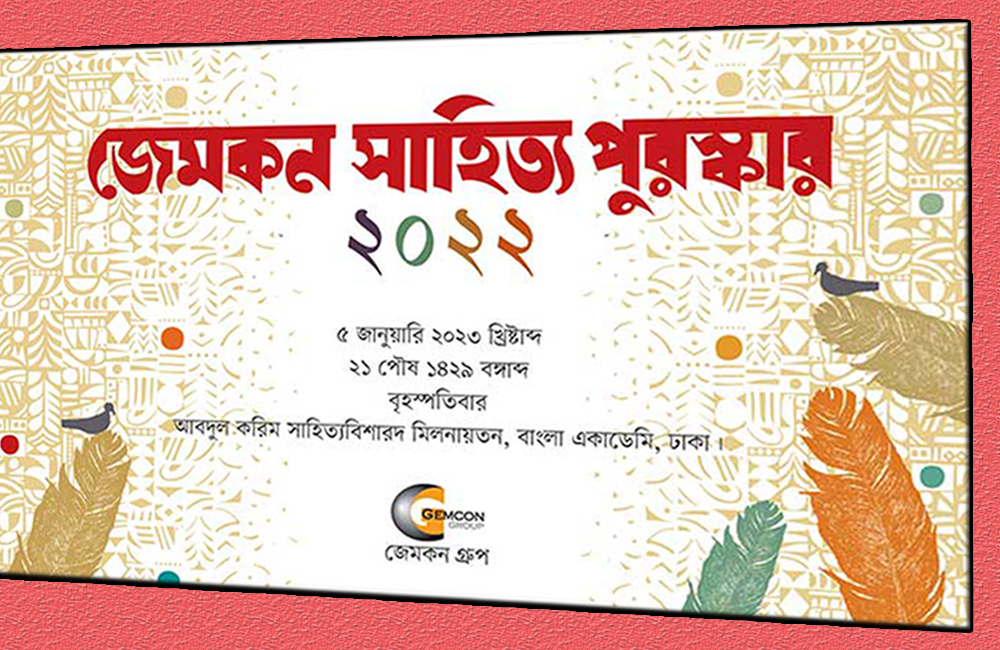
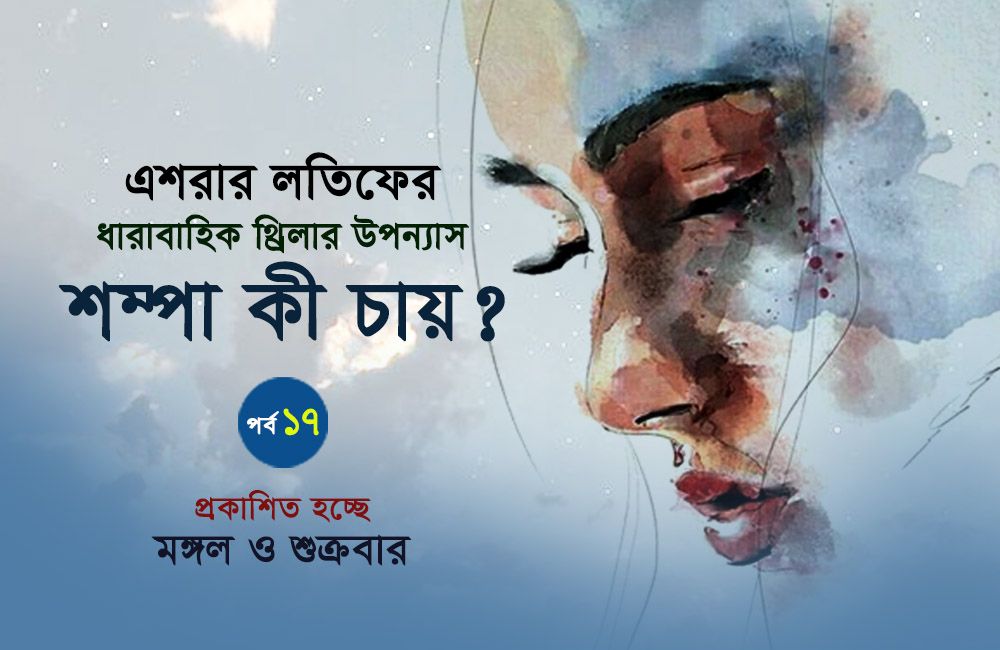

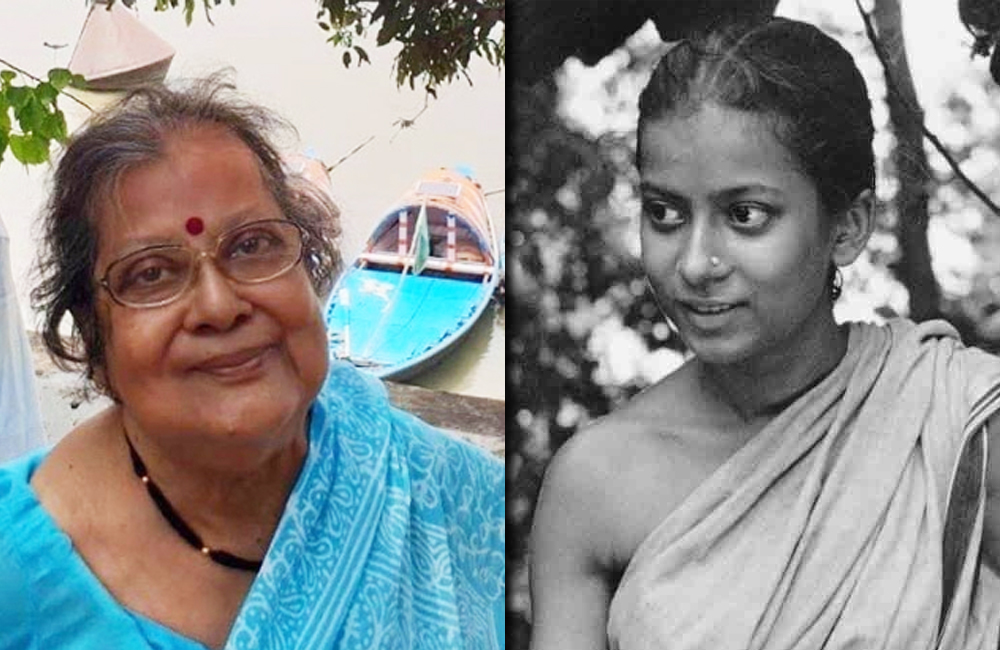

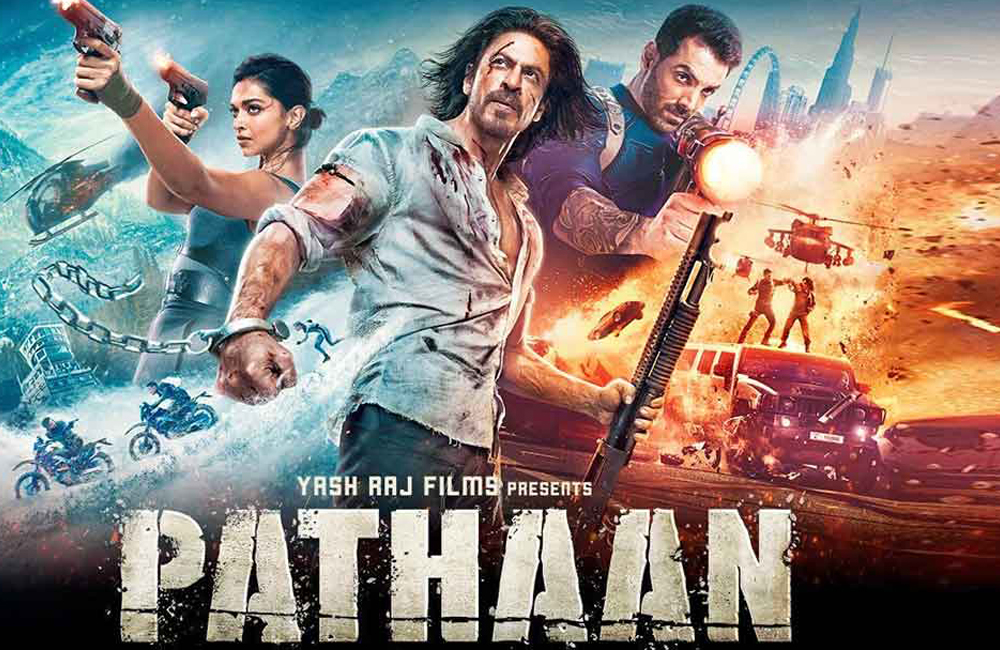

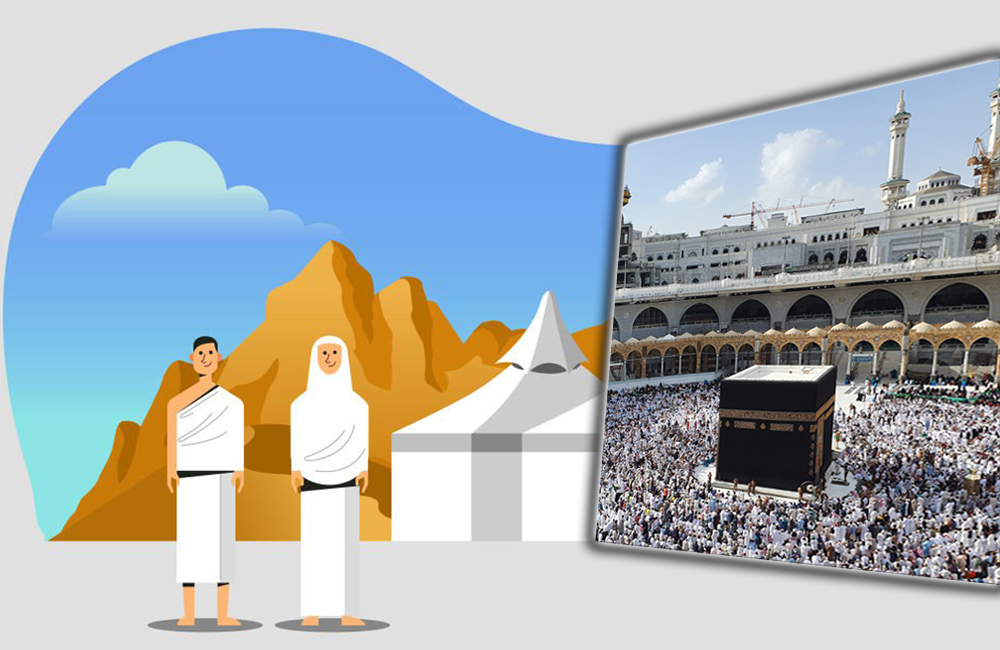
Leave a Reply
Your identity will not be published.