মলাটের অভ্যন্তরে
কেমন হবে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একজন লেখক যদি আপনার আুশপাশের জীবনধারণ করা অতি সাধারণ কিছু মানুষের নিত্যদিনের টুকরো অংশ বা জীবনের হাইলাইটেড কিছু গল্প বা হাসি-কান্নার কিছু আলাপ প্রতিদিন পড়ন্ত বিকেলে এসে আপনার ছাদবাগানের পাশে বেঞ্চে বসে চায়ের কাপের ধোঁয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে অসাধারণ সাহিত্যমানে শোনানোর প্রস্তাব দেন ? ঠিক এই অনুভূতিই আমি পেয়েছিলাম হুমায়ূন আহমেদের ‘আনন্দ বেদনার কাব্য’ বইটি পড়ার সময়।
ব্যক্তিগত বার্তা
বলা বাহুল্য, এই বইটি হুমায়ূন আহমেদের একটি আন্ডাররেটেড বই। সৌভাগ্যক্রমে, আমার দুই বড় বোনের দুজনেই উঁচু লেভেলের সাহিত্যানুরাগী। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল আপুদের অবারিত কালেকশনের তাকে-তাকে ঘুরে বেড়ানোর গ্রিন কার্ড। তাই এই বইটি আমি পড়তে পারি। বইটি সম্বন্ধে আমার রিডিং এক্সপেরিয়েন্স ১০-এ ১০। প্রতিটি ছোটগল্প যেন একেকটা ফ্লেভারের ক্যান্ডি। শীতবিকেলের আদুরে রোদের মতো মিষ্টিসুখে উপভোগ করেছি বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা।
বইটিতে নয়টি গল্প রয়েছে :
আনন্দ বেদনার কাব্য
এইসব দিনরাত্রি
ঊনিশ শ একাত্তর
জলছবি
খেলা
শিকার
পাখির পালক
অসুখ
কবি
লেখনশৈলীর আদ্যোপান্ত
হুমায়ূন আহমেদের লেখনশৈলী সব সময় সহজ-সরল, কিন্তু বাক্যের গভীরে বহুমাত্রিক স্তর লুকায়িত থাকে। ফলে পাঠকের দৃষ্টিতে সারফেস লেভেল থেকে বেশ সহজ-সরল প্রতীয়মান হলেও মননে তা প্রকাশিত হয় এক আপাদমস্তক শৈল্পিক, সাইকোলজিক্যাল গভীরতা এবং সাংস্কৃতিক অনুরণন হিসেবে। এমন বৈশিষ্ট্য খুব কম বাঙালি লেখকের লেখায়ই খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের সাথে সাথে ছোটগল্পগুলোতেও হুমায়ূন আহমেদ কলমের কারুকাজ সমান ধারায় চালিয়ে যেতে এতটুকু ব্যর্থ হন নি। আলোচ্য বইজুড়ে হুমায়ূন আহমেদের লেখনশৈলীর বেশ কাঠখোট্টা পর্যবেক্ষণের এক সরলতম অনুলিপি তুলে ধরা হলো :
১. ভাষার সরলতা, অনুভূতির গভীরতা
তার বাক্যগুলো বেশ সংক্ষিপ্ত, চলিত এবং টু দ্য পয়েন্ট। ক্লাসিক্যাল শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোর মতো জটিল-যৌগিকের সমন্বয়ে সৃষ্ট কোনো রচনা নয়। নেই কোনো কয়েক টন ওজনের মেটাফোর, অভিধান-ঘাঁটা শব্দাবলি। তিনি সরলতার মুখোশে পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক জগতে তোলপাড় তৈরি করে দেন। এর দরুন তাঁর ন্যারেটিভ সকল শ্রেণির পাঠকের বুকশেলফে সজ্জিত থাকে —শহুরে থেকে গ্রাম্য, স্কুলপড়ুয়া থেকে বুদ্ধিজীবী। পাঠক ভাবে লেখক তাকে লিখে নয়, বরং সাক্ষাৎ কথোপকথনে বলছেন।
যেমন ‘আনন্দ বেদনার কাব্য’ গল্পের শুরুর দিকে—
এবং একসময় দেখি গ্রন্থাকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধ হয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না।
হুমায়ূন স্যার ব্যবহার করেন ‘সরলতার বিভ্রম’—প্রতিটি সরল বাক্যও আসলে সূক্ষ্মভাবে নির্বাচিত, যা কোরেসপন্ডিং চরিত্রের সুর ও মানসিকতার ইঙ্গিত বহন করে।
২. কাব্যিক সংলাপ
তাঁর সৃষ্ট অতি সাধারণ ক্যারেক্টারগুলোও যেন বাস্তবতায় ডুব দিয়ে আসা। তাদের সংলাপগুলো মনে হয় আমার চেনা-জানা কারও মুখের কথা। প্রতিটি বাক্যে গেঁথে আছে হাসি, কান্না, ক্রোধ, ভালোবাসা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বা চাপাকথা। কোনো কথা অসম্পূর্ণ, কোনো কথা সাধারণ, কোনো কথায় অযত্ন, কোথাও দ্বিধাবোধ। তিনি সংলাপ দ্বারা ইনফরমেশন প্রদান করেন নি, বরং ক্যারেক্টারের পারসোনালিটি প্রকাশ করেছেন। এর প্রভাবে পাঠক আর তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যে যে ক্ষণিকের জন্য হলেও একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, একথা কোন হুমায়ূনপড়ুয়া অস্বীকার করবে ?
যেমন ‘পাখির পালক’ গল্পে জরী এবং আনিসের ফোনালাপ—
আপনার কি ঠান্ডা লেগেছে ?
না তো।
গলার স্বর ভারী।
আমি ছোট্ট একটি নিশ্বাস গোপন করলাম। আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে, কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙা ভাঙা। কোনোদিন চিনতে পারে না।
নাটক ও চিত্রনাট্যের অভিজ্ঞতা তাঁর সংলাপকে দিয়েছে নিখুঁত ছন্দ ও অন্তর্নিহিত অর্থ। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন ধীর, মোলায়েম এক সিনেমার পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে।
৩. বর্ণনাধারায় মিনিমালিজম
তিনি কোনো ব্যক্তি বা স্থান বা পরিস্থিতি ওভার-ডিসক্রাইব করেন না। তাঁর বর্ণনাশৈলিতে আতিশয্য নেই। তিনি চাকচিক্যময় প্যারাগ্রাফে পাঠককে দৃশ্য অনুধাবন না করিয়ে, মিনিমালিস্ট ধাঁচে সিলেক্টিভ ডিটেইলে প্লটের গভীরে প্রবেশ করান। পাঠকমস্তিষ্ক আপনা-আপনিই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নেয়। ফলে কাহিনির ঘোর পাঠকের মন থেকে কখনো পালাতে পারে না।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘জলছবি’ গল্পের প্রারম্ভিক সিনারিও—
ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতার তলাটা খুলে পড়ে গেল। বাসে উঠবার উত্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন না। শুধু মনে হলো দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না।
তিনি ব্যবহার করেন এক ধরনের ‘শূন্যস্থান-নির্মাণ’ স্ট্র্যাটেজি—যেন একজন চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে কিছু অংশ ফাঁকা রাখলেন, যাতে দর্শকের মন সেটুকু পূর্ণতা দেয়।
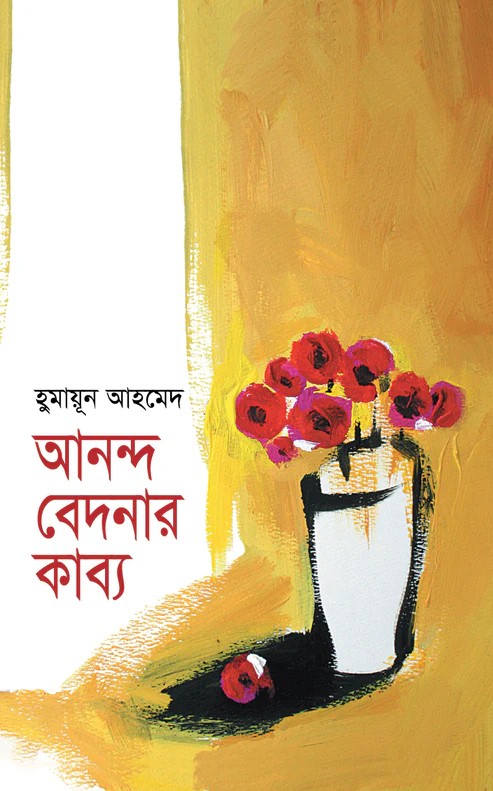
৪. সাইকোলজিক্যাল লেয়ারস
তাঁর ক্যারেক্টারগুলো মোটাদাগে বললে কোনো দিগি¦জয়ী হিরো নয়; তারা সাধারণ, ভালোমন্দ মিশেলে বাস্তবজীবনের পরিস্থিতি থেকে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা নম্বরের ক্রমবৃদ্ধিতে উঠে আসে তাদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, ইতিহাস বা ব্যক্তিত্ব। ফলে পাঠকেরা পরিশেষে প্রত্যেক ক্যারেক্টারকে দুইভাবে নিজের মানস-আয়নায় রিলেটেবল হিসেবে দেখতে পায়—হয় নিজের ভেতরে, নয়তো চেনা-জানা কারও ভেতরে। এভাবে খুব কম লেখকের লেখাই পাঠকমনে কো-এক্সিস্ট করার সক্ষমতা রাখে।
যেমন ‘অসুখ’ নামক গল্পে বিতর্কিত ঘরানার প্রধান ক্যারেক্টার রঞ্জু একসময় নিজের ব্যাপারে আত্মকথার স্বরে বলে—
আমি অন্য দশ জন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। একটি ছোট্ট ঘর। একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশি তো কখনো চায় না।
তার চরিত্র এভাবেই সময়ের ব্যবধান এক লাফে ডিঙিয়ে পাঠকদের রোমাঞ্চিত করে যাচ্ছে।
৫. আনন্দ ও বেদনা-দ্বৈত আবেগের টানাপোড়ন
তাঁর হাস্যরস সব সময় আইরনি নয়; বরং কখনো আসে বিদ্রূপ থেকে, কখনো অদ্ভুত যুক্তি থেকে, কিংবা মানবিক অদ্ভুত বিষয় থেকে। অথচ মুহূর্তেই আনন্দের দৃশ্য ঘুরে যায় গভীর বেদনায়, অথবা ভাইস-ভার্সা। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পাঠকদের পাঠ-অভিজ্ঞতা হয় একদিকে সাবলীল ও বিনোদনমূলক, অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী নস্টালজিয়া।
এক্ষেত্রে আলোচ্য গল্পগ্রন্থ থেকে কয়েকটি কোটেশন উল্লেখ করা যায়—
“মাসের বিশেষ বিশেষ ফুর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি বাদলা হয় কেন, এই রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন না।” (গল্প ‘কবি’)
“সে ইদানীং উর্দুতে বাতচিত করছে। কখন যে পাবলিকের হাতে মার খাবে। দিনকাল খারাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।” (গল্প ‘পাখির পালক’)
“কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সব সময় আগের মতো থাকে। পর্দার রং পাল্টায় না। কিংবা হয়তো সব সময় একই রঙের পর্দা কেনা হয়।” (গল্প 'অসুখ’)
এই তাঁর ট্র্যাজি-কমিক দৃষ্টিভঙ্গি—জীবন একইসঙ্গে হাস্যকর এবং ভঙ্গুর।
সুতরাং হুমায়ূন আহমেদের লেখনশৈলী জনপ্রিয়, কারণ তা প্রাঞ্জল; আর সমাদৃত কারণ তা গভীরভাবে আলোড়নকারী। তিনি একটি শিল্পে পাকা-হাত গড়ে তুলেছিলেন যে, আমার বাক্যবাগীশ ভঙ্গিমায় লিঙ্গুইস্টিক এক্সিবিশন করবার প্রয়োজন নেই, না দরকার একাডেমিক নলেজের ঘনত্বে লেখা মেরিনেট করার। পাঠক ঢাকার জ্যামে বসে বা ঝুম বর্ষায় একাকী পার্কে বসে থেকেও যেন অবচেতন মনে হঠাৎদৃষ্ট কোনোকিছুতে আমার সৃষ্ট কোনো কথাসাহিত্যের প্লট, ক্যারেক্টার বা এক্সার্প্ট খুঁজে পায়।
একটুখানি রিসার্চফুল ইনসাইট
বইটি পড়ে সর্ব প্রথমে যে ধারণা আমার নিউরনগুলোতে জেঁকে বসেছে তা হলো, হুমায়ূন আহমেদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের যুগান্তকারী ডেফিনেশনকে বেশ শক্তবাহুতে আলিঙ্গন করেছেন। প্রায় প্রত্যেক গল্প শেষেই মনে ছন্দিত হয়—
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যায়, ‘শিকার’ গল্পের নাম। স্পয়লার এড়াতে কেবল এতটুকুই বললাম।
এছাড়াও আমি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিশারদগণের সার্থক ছোটগল্পের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দ্বারা আলোচ্য বইয়ের গল্পগুলো পরখ করে দেখেছি, কোনোভাবেই একটিও নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে না।
O. Henry বলেন—
A short story is something you can hold in your hand, and it will cut you, or warm you, or leave you wondering.এ প্রসঙ্গে ‘এইসব দিনরাত্রি’ গল্পের শেষাংশ যদি বলি—
প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, কিছুই ঠিক হয় না রে। তার কথা সমর্থন করেই ঘরের ভিতর থেকে একটি তক্ষক ডেকে উঠল। চারদিকে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।
Edgar Allan Poe-এর মতে—
“A short story must have a single mood and every sentence must build towards it.”
বইয়ের ‘খেলা’ গল্পটি আগাগোড়া হাইস্কুলের থার্ড স্যার বাবু নলিনী রঞ্জন-কে ঘিরেই আবর্তিত।
V. S. Pritchett সংজ্ঞায়িত করেন : “Something glimpsed from the corner of the eye, in passing.”
‘পাখির পালক’, ‘কবি’, ‘জলছবি’ গল্পগুলো এমন ভাইব—এই সারাঘর ভরে দেয়।
সংক্ষেপে পাঠপ্রতিক্রিয়া
কেন পড়বেন ?
হরেক রকম ভারী বইয়ের ভিড়ে রিডিং হ্যাবিটে একটুখানি স্লো ডাউন। একটু জানতে জীবনকে কীভাবে দেখে আরও কত কেউ।
কারা পড়বেন ?
সব ধরনের পাঠক, সব বয়সের, সব শ্রেণির। আর হ্যাঁ, রিডিং ব্লকের প্যারায় থাকা পাঠকগণের প্যারাসিটামল হতে পারে এই নাতিদীর্ঘ, সহজপাঠ্য, হৃদয়স্পর্শী গল্পগ্রন্থ।
সমালোচনা ?
বেশ খানিকক্ষণ ভাবলাম কী বলা যায়। কিন্তু সরি, কিছুই পেলাম না। এই ছিল আমার খুব দামি এক পাঠ্যানুভূতিকে অক্ষরায়িত করার প্রাণপণ প্রয়াস।
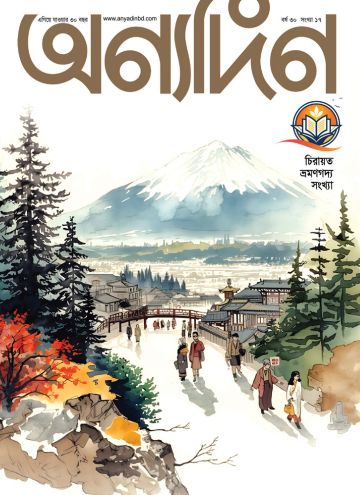





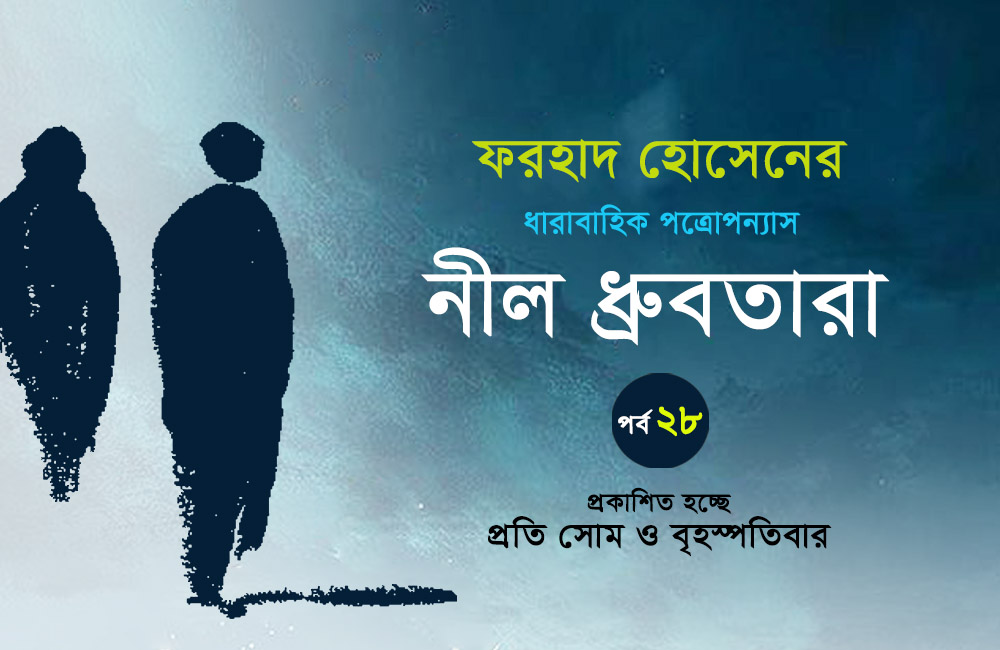
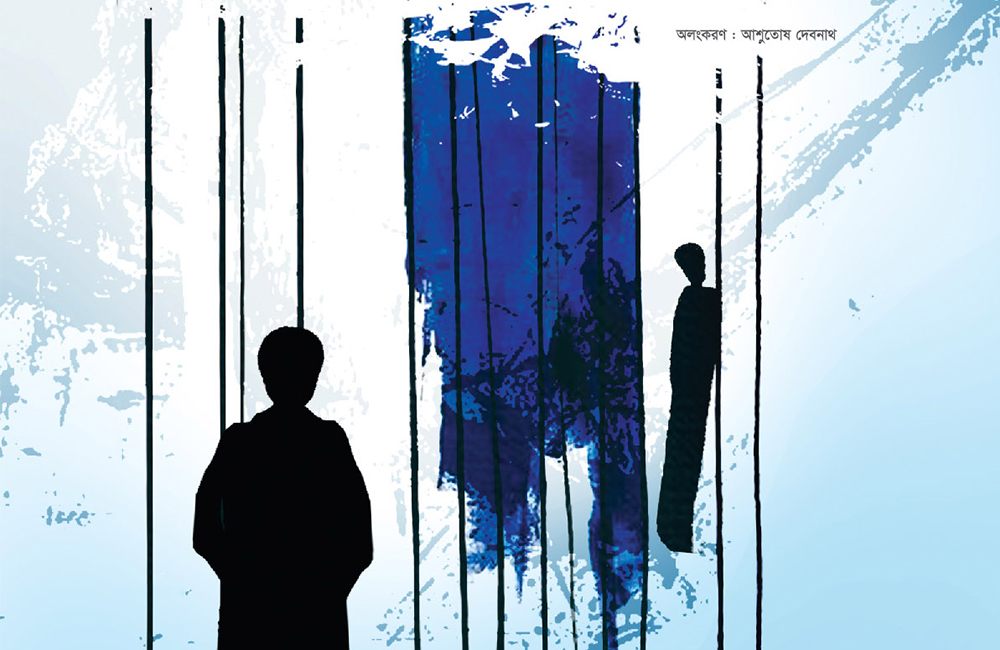





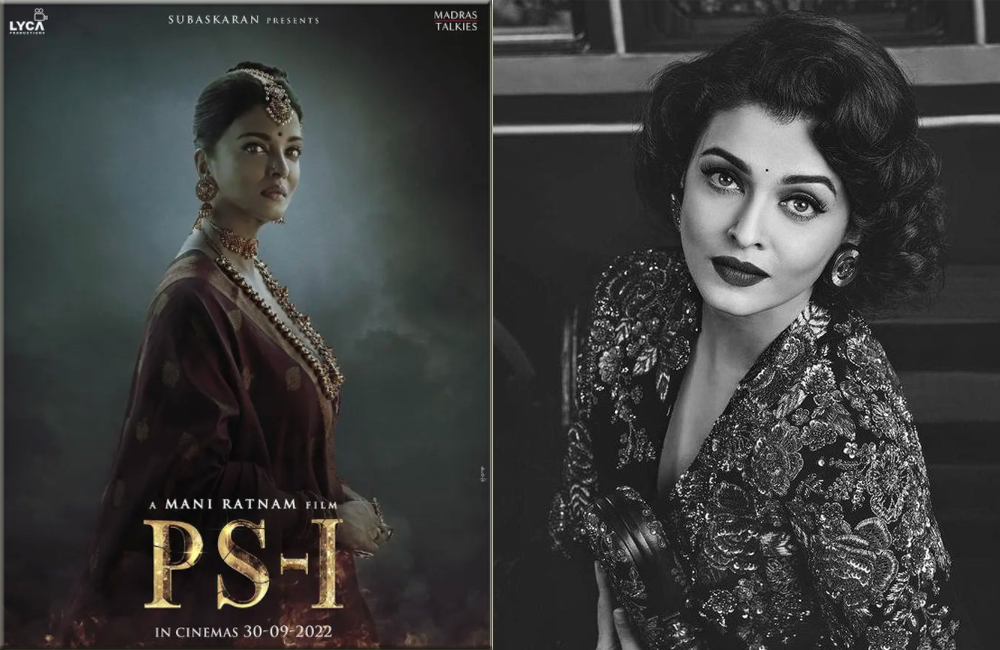

Leave a Reply
Your identity will not be published.