বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ, হ্রদ আর তুষার গলা পানি থেকে ছোট ছোট ধারার সৃষ্টি হয়- তারই মিলিত রূপ নদী। এবং আমরা জানি নদীর সাথে মানুষের রয়েছে আত্মিক যোগাযোগ, গভীর সম্পর্ক। বলা যায়, মানুষের ইতিহাস রচনা করেছে নদী। হরপ্পা সভ্যতার পেছনে সিন্ধুনদ, মেসোপেটেমিয়ান সভ্যতায় টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, মিশরীয় সভ্যতার অন্তরালে নীলনদ এবং পুরনো চৈনিক সভ্যতাতে হোয়াং হো ও ইয়াংসি নদীর অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।
অন্যদিন-এর নতুন ঈদ ম্যাগাজিন পড়তে এখানে ক্লিক করুন...
যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই ভূ-খণ্ডের মানুষের সাথেও নদীর নিবিড় সম্পর্ক। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা- এই চারটি প্রধান নদী ছাড়াও মাথাভাঙা, ইছামতি, কুমার, গড়াই মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, তিস্তা, ধলেশ্বরী, করতোয়া, আত্রেয়ী, সুরমা, কুশিয়ারা, তিতাস, গোমতিসহ বিভিন্ন উপনদী ও শাখা-প্রশাখা বাংলাদেশের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পার্বত্য নদী কর্ণফুলী, সাংগু, মাতামুহুরী, হালদা আর নাফ।
আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ নদীর ভাঙা-গড়ার খেলার সাথে একাত্ম। সর্পিল নদীর জলের আঘাতে একদিকে পাড় ভাঙে তো অন্যদিকে জেগে ওঠে নতুন জমি। নদীকে কেন্দ্র করে যাদের জীবিকা তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। বাঙালির জীবনের সাথে নদীর সম্পৃক্ততার কারণেই সাহিত্য, শিল্প আর সংস্কৃতিতে এর প্রবল উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসে, ছোটগল্পে, পত্রসাহিত্যে, স্মৃতিকথাতে, কবিতা আর ছড়াতে, গানে এবং চলচ্চিত্রে নদী আপন মহিমায় ভাস্বর।
বাংলা উপন্যাসে নদী কখনো প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, কখনো তার রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’এবং অদ্বৈত মল্ল বর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ নদীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পাঠক যখন পড়ে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র ‘দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, নদীর বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে নতুন চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।... এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়ি-ঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও-পাড়ায় যাইতে হয় নৌকায়। কয়েকদিন পর জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আরো এক মাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না’— তখন প্রমত্তা পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপ, বর্ষার বেগবান প্রকৃতি তার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ উপন্যাস পাঠে সে উপলব্ধি করতে পারে, পদ্মাকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম। এ ছাড়া হুমায়ূন কবিরের ‘নদী ও নারী’, তারাশংকার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতি’, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, অমর মিত্রের ‘সুবর্ণ রেখা’, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ এবং ইমদাদুল হক মিলনের ‘নদী উপাখ্যান’ উপন্যাসেও নদীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা চোখে পড়ে। পাশাপাশি আবার কোনো কোনো উপন্যাসে নদী কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে নির্জন চরের দৃশ্য শচীনের ধ্যানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আবার কয়েকটি উপন্যাসে নদীকে বিশেষ শিল্প কৌশলের প্রয়োজনে আনা হয়েছে, এখানে নদী উপন্যাসের বহিরঙ্গ গুণ হিসেবে পরিমণ্ডলে অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ বা ‘কপালকুণ্ডলা’র কথা বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি গল্পে নদীর নান্দনিক উপস্থিতি চোখে পড়ে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’, ‘অতিথি’, ‘সমাপ্তি’, ‘নিশীথে’; কাজী নজরুল ইসলামের ‘জিনের বাদশা’, নব্যেন্দু ঘোষের ‘নাগিনী’, সমরেশ বসুর ‘লড়াই’, মনীন্দ্রলাল বসুর ‘মালতী’প্রভৃতি গল্পে নদী কোথাও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, কোথাও গল্পের বহিরঙ্গ গুণ হিসেবে পরিমণ্ডলে অবস্থান করেছে, আবার কোথাও বিশেষ শিল্প কৌশলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। সমরেশ বসুর ‘পাড়ি’ গল্পে, যেখানে একজন পুরুষ একজন নারী- দুজন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম দেখানো হয়েছে, এখানে নদীর পটভূমিকা অত্যন্ত জোরালো। ‘আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো ঠেক করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস করে। বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তরতর করে’— এখানে গঙ্গা যেন স্বয়ং একটি চরিত্র, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কঠিন জীবনের নদীর চমৎকার উপস্থিতি বলা যায় তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের নদীর রূপ পরিস্ফুটিত রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্নপত্র’-এ এবং বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথাতে। ‘আমার ছেলেবেলা’তে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: ‘নোয়াখালির মেঘনার মতো এমন হতশ্রী নদী পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখি নি। রুক্ষ পাড়ি, ঘাট নেই কোথাও, কেউ নামে না স্নান করতে, কোনো মেয়ে জল নিতে আসে না। তরণীহীন, রঙিন পালে চিহ্নিত নয়, জেলে ডিঙ্গির সঞ্চরণ নেই- একটি মাত্র খেয়া-নৌকা দেহাতি ব্যাপারিদের নিয়ে সকালে-সন্ধ্যায় পারাপার করে। শহরের এলাকাটুকু পেরোলেই নদীর ধারে-ধারে বনজঙ্গল, নয়তো শুধু বালুডাঙ্গা, মাঝে মাঝে চোরাবালিও লুকিয়ে আছে- শীতে গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ চরের ফাঁকে-ফাঁকে শীর্ণ জলধারা বয়ে যায়। বর্ষার স্ফীত হয়ে ওঠে নদী- বিশাল অন্য তীর অদৃশ্য। কিন্তু তখনো চোখ খুশি হতে পারে না, বরং আমার ভয় করে সেই কালচে-ব্রাউন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে তাকাতে- যার উপর দিয়ে বর্ষায় ক-মাস, একটি নিঃসঙ্গ স্টিমার যাতায়াত করে হাতিয়া-সন্দ্বীপে, পৃথিবী ত্যক্ত দুই দ্বীপ, যেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসে সর্পদংশনের ভীষণ সব কাহিনী।
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঝড়ের সংকেত আসে মাঝে মাঝে, ঘূর্ণি হাওয়ায়, এঁকে-বেঁকে পাতলা বৃষ্টি পড়ে সারাদিনÑ বারোশো ছিয়াত্তর বা অন্য কোনো দূর বছরের বন্যার স্মৃতি লোকদের বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে। আর এইসব কিছুর উপরে আছে ভাঙন, অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ভাঙন। প্রতি বর্ষায় নদী এগিয়ে আসে শহরের মধ্যে- প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে- বিরাট বুড়ো গাছ, বটগাছ আর অগুনতি পাখির বাসা নিয়ে মস্ত বড়ো মাটির চাঁই ধ্বসে পড়ে হঠাৎ। ধোঁয়া ওঠে জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই নদী আবার নির্বিকার’।
নদীকে কেন্দ্র করে বাঙালি কবিরা স্মরণীয় পংক্তিমালা রচনা করেছেন। ‘সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;/সতত (যেমন লোক নিশার স্বপনে/ শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে/জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!’ (কপোতাক্ষ নদ/ মধুসূদন দত্ত); ‘যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি/ আমি তবে এক্ষণি হই ইছামতী নদী/ বইবে আমার দখিন ধারে সূর্য-ওঠার পার/ বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায় নামবে অন্ধকার/ আমি কইব মনের কথা দুই পাড়েরই সাথে-/ আধেক কথা দিনের বেলায় আধেক কথা রাতে’ (ইছামতী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); ‘ওগো ও কর্ণফুলী/ উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।/ যে লোনা জলের সিন্ধু-সিরুতে নিতি তব আনাগোনা/ আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশি লোনা’(কর্ণফুলী/ কাজী নজরুল ইসলাম); ‘রাইসর্ষের খেত সকালে উজ্জ্বল হলো- দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল/ তারি পাশে নদী;/ নদী, তুমি কোন্ কথা কও?/ অশত্থের ডালপালা তোমার বুকের’পরে পড়েছে যে;/ জামের ছায়ায় তুমি নীল হলে/ আরো দূরে চলে যাই/ সেই শব্দ- সেই শব্দ পিছে পিছে আসে/ নদী নাকি? নদী, তুমি কোন কথা কও?’ (নদী/ জীবনানন্দ দাশ) ইত্যাদি পংক্তিমালা সেই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। এরপর চল্লিশ থেকে এই নব্বই দশকের কবির কবিতায়ও নদী চিরকালীন আবেদনের ভাস্বর।
বাংলা গানে নদী এসেছে নানাভাবে। লোকসঙ্গীত থেকে আধুনিক গান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নদীর বিচিত্র অবস্থান। ‘নদীর কূল নাই কিনার নাইরে’, ‘সর্বনাশা পদ্মা নদী’, ‘রুপালি নদীরে, ও তোর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল’, ‘এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা’, ‘ও কূল ভাঙা নদীরে’, ‘গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই, ‘ও নদীরে/ একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে’, ‘গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা’, ‘আমায় ডুবাইলিরে আমার ভাসাইলিরে’, ‘বিস্তৃত প্রান্তরের হাহাকার শুনেও হে গঙ্গা তুমি বইছো কেন’, ‘কত না নদীর জন্ম হয় আর একটা কেন গঙ্গা হয় না’, ‘ওগো মা গঙ্গা’, ‘এই তো নদী যায় সাগরে’, ‘কত যে ধীরে বহে মেঘনা/শান্ত তবু সুপ্ত সে নয়’, ‘এই পদ্মা এই মেঘনা’ ইত্যাদি গানগুলিতে নদীর মধুর রূপের পাশাপাশি ভয়ঙ্কর রূপ যেমন পরিস্ফুটিত, তেমনি নানাভাবে নদীর সমান্তরালে বাঙালি জাতি সত্তার প্রকাশ- বাংলা গানে বিচিত্র রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে নদী।
শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্রেও নদীর নান্দনিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। ‘গঙ্গা’র মাধ্যমে সেলুলয়েডের রুপালি ফিতায় নদীকে প্রথম নিয়ে আসেন রাজেন তরফদার। এতে গঙ্গার বিচিত্র রূপের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জেলেদের জীবনের নানা দিক, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন অঙ্গগুলি চিত্রায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, নদীর প্রতি রাজেন তরফদারের প্রবল টান সবসময় লক্ষ করা গেছে। তাই তো ‘পালঙ্ক’-এ কুমার নদী এবং শেষ চলচ্চিত্র কর্ম ‘নাগপাশ’-এ রায়মঙ্গল নদী সেলুলয়েডে মূর্ত হয়ে ওঠে।
সাম্প্রতিক সময়ে আরেক বাঙালি চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষের মধ্যেও রয়েছে নদীর প্রতি প্রবল অনুরাগ। ‘দখল’(১৯৮১), ‘অন্তজর্লী যাত্রা’ (১৯৮৯), ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৯২) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে জীবনের সমান্তরালে নানাভাবে নদীকে ব্যবহার করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে গৌতম ঘোষ বলেন, ‘নদীর যে প্রবাহ সেটা শৈশব থেকে আমাকে আলোড়িত করেছিল। পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছিল নদী হচ্ছে সমস্ত সভ্যতার প্রতীক। যেহেতু আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। একে কেন্দ্র করে সব জীবন। এই রকম অবচেতন মনে নদীটা বারবার আমার ছবিতে ফিরে এসেছে’।
এ ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের ‘অপুর সংসার’, ‘জলসা ঘর’, তপন সিংহের ‘অতিথি’, ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণ রেখা’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ‘নদী ও নারী’, ‘চিত্রা নদীর পারে’, ‘মাটির ময়না’, ‘হালদা’য় অপূর্ব চলচ্চিত্রিক ব্যঞ্জনায় নানাভাবে নদী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।
আদিকাল থেকে নদীর সঙ্গে বাঙালির নিবিড় সম্পর্ক। তাই সঙ্গত কারণেই বাঙালির সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতেও নদীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলোর অবস্থা খুবই করুণ, শুষ্ক মৌসুমে পানি বলতে গেলে থাকেই না, তখন ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র উপন্যাসের ‘পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে! সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটি বুক কেহ কোনোদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে’— এই কথাগুলো পরিহাসের মতো শোনায়। অন্যদিকে বৃষ্টির মৌসুমে এই ভাটির দেশে বন্যার পানিতে ভাসে মানুষ, গৃহপালিত পশু, ঘরবাড়ি আর গাছপালা।
আগামীতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলো স্বরূপে আবার আত্মপ্রকাশ করবে কি?
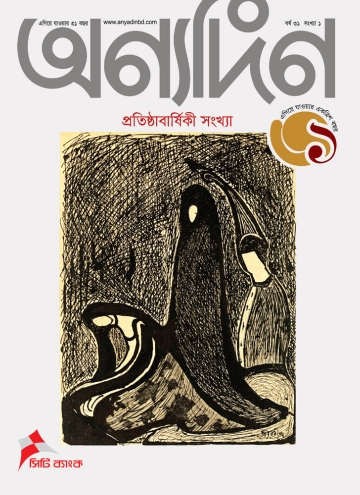














Leave a Reply
Your identity will not be published.