স্বনামধন্য ভ্রমণলেখক, গল্পকার, অনুবাদক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক ফারুক মঈনউদ্দীন। তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণগদ্য ‘মরু গুহা ও দ্বীপের গল্প’-এর দ্বিতীয় পর্ব 'প্রিয়ার গালের তিল ও সমরকন্দ' প্রকাশ হলো আজ।
প্রথম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন...
সুফি কবি হাফিজের সেই বিখ্যাত বহুল আলোচিত পংক্তিদ্বয় ছাড়াও কবি ও কথাশিল্পী এডগার এলান পো যে নগরী সম্পর্কে বলেছিলেন ‘এবার তাকাও সমরকন্দের দিকে/ সে কি রানী নয় পৃথিবীর?/ সকল নগরী ছাপিয়ে ওঠে নি কি গৌরব তার?/ তার হাত কি দেখিয়ে দেয় নি নিয়তির পথ?/ বিশ্বের জ্ঞাত সব মহিমার পাশে/ একাকী অভিজাত দাঁড়ানো নয় কি সে?’ কিংবা ‘শরীরের মাংস থেকে আত্মা বিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত’ যে নগরীর পথে পথে ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে চেয়েছিলেন ইংরেজ কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলো, বুখারা থেকে বের হয়ে ন্যাড়া ফসলকাটা মাঠের মধ্য দিয়ে সেই সমরকন্দের দিকে হাইওয়ে ধরে ছুটতে থাকা গাড়ির দুপাশে পত্রহীন গাছগুলো দেখি পেছন দিকে দৌড়াচ্ছে। নীল দিগন্তের কাছাকাছি কিছু অনুচ্চ ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। কোনো ছোট শহরের কাছে এলে রাস্তার পাশে ইতস্তত কিছু ভবন বা অন্য স্থাপনা দেখা যায়, তবে সেগুলোর কোনোটিই উঁচু দালান নয়। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার রাস্তায় কোথাও বহুতলবিশিষ্ট ভবন চোখে পড়ে নি। চোখে পড়ে নি কোনো মানুষজনও। যে ফসলকাটা মাঠের মাঝের হাইওয়ে ধরে আমাদের যাত্রা, সেই মাঠ মানে আমাদের ধানখেত নয়, গমখেতও নয়, তুলাখেত। আমরা জানি তুলা উজবেকিস্তানের মূল অর্থকরী ফসল। বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারী দেশটিতে বছরে প্রায় দশ লাখ টন তুলা উৎপাদিত হয়। বিশ্ব রপ্তানির ১০ শতাংশ তুলা আসে উজবেকিস্তান থেকে। আমাদের দেশে পাটকে যেমন আমরা সোনালি আঁশ বলে ডাকি, উজবেকিস্তানেও তুলাকে বলা হয় ‘সফেদ স্বর্ণ’।

তবে এই সাদা স্বর্ণ উৎপাদনের পেছনে রয়েছে জবরদস্তিমূলক শিশুশ্রমের কলঙ্কতিলক। সরকার প্রতিবছর লাখ লাখ কর্মীকে বলপূর্বক তুলা চাষের কাজে পাঠায়। কৃষকদের নির্দিষ্ট কোটায় তুলা সরবরাহে বাধ্য করা হয়, অন্যথায় জরিমানা, জমির স্বত্ব হারানো, চাকরিচ্যুতি, নাগরিক সুবিধা হরণ, ছাত্রদের শিক্ষালয় থেকে বহিষ্কারের মতো বিভিন্ন মাত্রার শাস্তির বিধান রয়েছে। তুলা আহরণের কাজটি মূলত করানো হয় কিশোর শ্রমিকদের দিয়ে, যদিও কীটনাশকের সংস্পর্শে আসার কারণে কাজটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিবছর গরমে, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং নানান দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটা মানবাধিকার সংস্থার চাপে উজবেকিস্তান থেকে তুলা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। যা-ই হোক, দেশভ্রমণের আনন্দের মধ্যে এসব নিরানন্দ প্রসঙ্গের অবতারণা ঠিক নয়।
সমরকন্দ বহু মানুষের স্বপ্নের দেশ। সুফি কবি হাফিজ তাঁর ভালোবাসার রমণীটির গালের কালো তিলের বিনিময়ে যে শহর তাঁকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন, সেই সমরকন্দ আমাদেরও যেন সেই তিলটির মতো ডাকে। হাফিজের সেই বহুল আলোচিত কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করলে এ রকম হবে:
শিরাজের তুর্কি রমণী যদি নিজ হাতে তুলে নেয় আমার হৃদয়
তার গালের কালো তিলের সাথে বুখারা সমরকন্দ হবে বিনিময়।
কবিতার এই ভাষ্য কারো কাছে যেন রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। হাফিজের বিরুদ্ধবাদীদের কেউ সম্রাট তৈমুর লংকে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানালে তিনি কবিকে দরবারে তলব করে বলেন, ‘আমার সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে আমি আমার বাসভূমি রাজধানী বুখারা ও সমরকন্দকে সাজানোর জন্য বিশ্বের বিরাট অংশ জয় করেছি, আর আপনি তুচ্ছ এক মানুষ সেই শহর বিনিময় করতে চান শিরাজের কোনো এক নারীর গালের তিলের জন্য!’ এর জবাবে হাফিজ কী বলেছিলেন, তার দুই ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। এক ভাষ্যমতে তিনি বলেছিলেন, “হে বিশ্বের প্রবল প্রতাপশালী মহামহিম, জাহাঁপনা, আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে, শেষের চরণের ‘সমরকন্দ বুখারার’ জায়গায় হবে ‘দো মণ কন্দ ও সি খোর্মারা’। অর্থাৎ আমি বলেছি, ‘আমি তার গালের তিলের বদলে দুই মণ চিনি ও তিন মণ খেজুর দান করব’।” অন্য ভাষ্যমতে তিনি বলেছিলেন, ‘হে বিশ্বের প্রবল প্রতাপশালী মহামহিম, নিজের এই অমিতব্যয়িতার জন্যই আজ আমার এমন দৈন্যদশা।’ বলা হয়, তাৎক্ষণিক এই জবাবে খুশি হয়ে তৈমুর লং তাঁকে কোনো শাস্তি না দিয়ে বরং উপঢৌকনে ভূষিত করেছিলেন।
এখানে উল্লেখ করা যায়, হাফিজের অনেক কবিতা ‘শাখণ্ডই-নবাৎ’ নামের কোনো এক ইরানি সুন্দরীর উদ্দেশে নিবেদিত। কারও মতে, ‘শাখণ্ডই-নবাৎ’ হাফিজের দেওয়া আদরের ছদ্মনাম। কে এই ভাগ্যবতী রমণী কবির মানসপ্রিয়া, তা নিয়ে বহু জল্পনাকল্পনা রয়েছে। কারও মতে, হাফিজ যখন এক রুটির কারখানায় কাজ করতেন, তখন তাঁর কাজের মধ্যে ছিল নগরীর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে রুটি পৌঁছে দেওয়া। সেখানেই তিনি দেখা পান অপরূপ সুন্দরী শাখণ্ডই-নবাতের। তিনি জানতেন তাঁর এই একতরফা ভালোবাসার প্রতিদান তিনি পাবেন না, তাই তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে সেই রমণীর স্তবগাথা।
ওপরের গল্পটির মতো হাফিজকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে। তাঁর মৃত্যু নিয়েও এ রকম একটা গল্প আছে। তাঁর জীবনীকারদের কয়েকজনই এটির উল্লেখ করেছেন। হাফিজের মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর জানাজা পড়তে ও কবর দিতে অস্বীকার করে। হাফিজের ভক্তদের সঙ্গে এ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় একটা রফা হয় যে হাফিজের সমস্ত কবিতার মধ্য থেকে কেউ একজন তাঁর যে-কোনো কবিতার প্রথম দুই চরণ পড়ে যদি হাফিজের ধর্ম কী ছিল তা বুঝে নিতে পারে, তাহলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর যে কবিতাটি এই প্রক্রিয়ায় উঠে আসে সেটি ছিল এ রকম:
হাফিজের এই শব হতে গো তুলো না চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশতে যাবে তবু।
এরপর আর কারও মধ্যে কোনো মতানৈক্য থাকে না, তখন সবার সম্মতিতে কবিকে এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁকে হাফিজ নামে চিনলেও তাঁর নাম খাজা শামস-উদ-দিন মুহাম্মদ হাফেজ-ই-শিরাজি। অল্প বয়সে তিনি কোরানে হাফেজ হয়েছিলেন বলে হাফিজ নামেই তাঁর পরিচিতি।

সমরকন্দের গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে যখন খুব ভোরে সকাল দেখতে বের হয়েছিলাম, তখন তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। নাশতা সারার পর একটু বেলা করে আমরা বের হই ইমাম বুখারির মাজারের উদ্দেশে। যাত্রাপথ খুব দীর্ঘ নয়, প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। পথের দুপাশে সেই পরিচিত দৃশ্য, ছাড়া ছাড়া অনুচ্চ ঘরবাড়ি, আর শূন্য মাঠ। মাজার কমপ্লেক্সের বেশ দূরে মূল রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে যে হাঁটাপথ ধরে যেতে হয়, তার দুপাশে নানান ধরনের পণ্য দিয়ে সাজানো অস্থায়ী দোকানের সারি। সেসব পসরার মধ্যে তসবিহ, জায়নামাজ, ব্যাগ, গালিচাসহ বেশির ভাগই ধর্মচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত।
গার্ডপোস্ট পেরিয়ে কমপ্লেক্সের সীমানায় ঢুকলেই পোড়া ইটের তৈরি দেয়ালের টানা একতলা ভবন, তার গায়ে ইসলামি স্থাপত্যের চিরাচরিত নিদর্শন শিখরাকার জানালার ঘুলঘুলি। সামনে এগিয়ে গেলে প্রশস্ত মূল ফটক, তার ওপর তিনটি ফিরোজা রঙের গম্বুজ। ফটকে পরপর দুটো দরজা, দরজার ওপর ইসলামি স্থাপত্যরীতির বাঁকানো খিলান, তার গায়েও ঘুলঘুলি। দুই মূল দরজার মাঝখানে বেশ প্রশস্ত একটা করিডর। সেই ফটক থেকে সোজা সামনের দিকে তাকালে একটা উঁচু চতুষ্কোণ স্তম্ভাকার স্মারক। স্তম্ভের গায়ে দরজার মতো উঁচু ধনুকাকৃতি খিলান, তার মাথায় মিষ্টিকুমড়োর ফালির মতো ওপর-নিচ খাঁজ কাটা ফিরোজা রঙের গম্বুজ। সেটির ওপর ফুলের নকশা আঁকা, চূড়ায় পিতলের দণ্ডের মাথায় আটকানো একফালি চাঁদ। কাছে গেলে বোঝা যায় স্তম্ভাকৃতি কাঠামোটির গায়ে চারদিকে মোট চারটি বাঁকানো খিলানের দরজা। কাঠামোর দেয়াল মোজাইক, গ্রানাইট, মার্বেল আর অনিকস পাথরের তৈরি। নীল, সাদাসহ বিভিন্ন রঙের সমাহারে সূক্ষ্ম ফুল আর জ্যামিতিক নকশায় পুরো স্তম্ভটি ঝকঝক করে। চারটি দরজা দিয়েই দেখা যায় ভেতরে আয়তাকার মার্বেলের নিরেট সমাধি পাথর। বিশাল উঁচু সেই দরজার ওপরে ও পাশে নানান নকশার পাশাপাশি আরবি ক্যালিগ্রাফিতে কোরানের আয়াত উৎকীর্ণ। মাজার স্তম্ভের ডান পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা বদ্ধ দরজার সামনে। দরজার পেছনে ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে রয়েছে মূল সমাধি। ওপরের পাথরটি মূল কবরের একটা প্রতীকী উপস্থিতিমাত্র।
আজ আমাদের সঙ্গে সকাল থেকেই রয়েছে শাহরুখ নামের এক তরুণ গাইড। শাহরুখ আমাদের শোনায় ইমাম আল বুখারির জীবনকাহিনি। ইমাম বুখারির প্রকৃত নাম আবু আবদাল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে আল-মুগিরাহ ইবনে বারদিজবাহ আল জুফি আল বুখারি। তাঁর জন্ম হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় পৌনে তিন শ বছর পর ৮১০ খ্রিষ্টাব্দে। ছোটবেলা থেকে তাঁর ছিল বিস্ময়কর স্মরণশক্তি। ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে তিনি প্রায় ৭০ হাজার হাদিস মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তারপর মা ও ভাইয়ের সঙ্গে হজ পালন করতে যান তিনি। মা ও ভাই বুখারায় ফিরে এলেও তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীগুলো সংগ্রহ করার জন্য মক্কা নগরীতে থেকে যান, যাতে সেসব হাদিস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও উপস্থাপন করতে পারেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিশটির মতো দেশে ভ্রমণ করে হাজারখানেক আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছয় লক্ষাধিক হাদিস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহুবার তিনি ভ্রমণ করেছেন সিরিয়া, মিসর, আল-জাজিরা (বর্তমান কাতার), ইরাকের বসরা, কুফা ও বাগদাদ এবং সৌদি আরবের হেজাজ। সেসব নগরীতে বছরের পর বছর অবস্থান করে বিভিন্নজনের কাছ থেকে অবিকৃত অবস্থায় সংগ্রহ করেছেন হাদিস।
এভাবে হাদিসের খোঁজে বিভিন্ন দেশ ঘুরে প্রায় চল্লিশ বছর পর ইমাম বুখারি বুখারায় ফিরে এসে হাদিস শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু সকল মহান ব্যক্তির কিছু শত্রু ও বিরুদ্ধবাদী থাকে। তাঁর বেলায়ও এটি ঘটে, তারা তাঁর নামে বিভিন্ন ধরনের অসত্য কথা বলে বুখারার আমির আহমদ আজ-জুখালির কান ভারী করে। এটির সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি কারণ। আমির চেয়েছিলেন ইমাম বুখারি যাতে আমিরের দরবারে গিয়ে তাঁকে হাদিস শিক্ষাদান করেন। বুখারি এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, ‘আমি জ্ঞানকে আমিরের বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে জ্ঞানের অসম্মান করতে পারব না। যার জ্ঞান দরকার, তাকে সেটা খুঁজে নিতে হবে। খোদার কসম, আমি কখনোই আমার জ্ঞানকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি না’। বলা বাহুল্য, এমন জবাব আমিরের পছন্দ হয় নি। এ কারণে তাঁকে বুখারা থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি সমরকন্দের কাছে খরতাং গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এই গ্রামের গোরস্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শেবানি শাসনামলে ইমাম বুখারির কবরটিকে মাজারের রূপ দেওয়া হয়।

আমাদের গাইড শাহরুখ জানায়, ইমাম বুখারির অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান, মূলত মা-ই তাঁকে মানুষ করেছেন। তাঁর বয়স যখন ১২, সে সময় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বহু হেকিম ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েও কোনো লাভ হয় নি। তাঁর মা ক্রমাগত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে তাঁর ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাতে থাকেন। অবশেষে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখা পান হজরত ইব্রাহিমের (আ.)। তিনি ইমাম বুখারির মাকে জানান যে তাঁর চমৎকার একাগ্র নিবেদনের কারণে আল্লাহ তাঁর ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরদিন সকালেই ঘুম থেকে উঠে ইমাম বুখারি বুঝতে পারেন তাঁর দৃষ্টি ফিরে এসেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর অন্ধত্ব ছিল চার বছর, সেই সময়ের মধ্যে তাঁর মায়ের পড়ে শোনানো প্রায় ৫ লাখ হাদিস তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।
সোভিয়েত যুগে পবিত্র এই মাজারটি প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়ে, বছরের পর বছরের অবহেলায় এটির তখন জরাজীর্ণ অবস্থা। সোভিয়েত সরকারও যেন এই স্থাপনাটি সম্পর্কে অবহিত ও আগ্রহী নয়। এই অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যখন এক রাষ্ট্রীয় সফরে তাসখন্দ আসেন। তিনি ইমাম বুখারির মাজার জিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করলে সরকারি মহলে তোলপাড় ঘটে যায়, কারণ, সরকারের মধ্যে অনেকেই জানতেন না ইমাম বুখারির মাজারটা কোথায়। সুকর্ণর অনুরোধ সোভিয়েত সরকারের পক্ষে উপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। কারণ, মুসলিম দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কোন্নয়নে ক্রুশ্চেভের যে উদ্যোগ ছিল, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের প্রেসিডেন্টের একটা অনুরোধ রক্ষা করতে না পারলে সে উদ্যোগ ব্যাহত হতে পারত। তাই রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায় থেকে তড়িঘড়ি করে সমরকন্দে একটা কমিশন পাঠানো হয়। এই কমিশন মাজার প্রাঙ্গণে গিয়ে মসজিদ আর মাজারের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, এমনকি কবরের একটা সমাধিফলকও ছিল না। কমিশনের পক্ষে তাড়াহুড়া করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকু মেরামত করে মসজিদ ও মাজারের একটা চলনসই অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এমনকি মূল সড়ক থেকে একটা অ্যাসফল্টের রাস্তাও তৈরি করে ফেলা হয়। সুকর্ণর পর সোমালিয়ার প্রেসিডেন্টও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে এসে ইমাম বুখারির মাজার জিয়ারতের ইচ্ছা জানালে তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হয়। তারপর একটা পৃথক প্রশাসনিক বিভাগকে ইমাম বুখারির মাজার ও সংলগ্ন মসজিদ দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাতে মুসলিম বিশ্বের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়।

সমাধির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে শাহরুখ আমাদের ইমাম বুখারি ও এই সমাধি সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে থাকে। ভূগর্ভস্থ কবরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি না, জানতে চাইলে শাহরুখ জানায়, ইমাম বুখারিকে কবরস্থ করার পর তাঁর কবর থেকে সুঘ্রাণ বের হতো। এমনকি কবরের চারপাশ থেকে বিচ্ছুরিত হতো আলো। ও জানায়, এই মাজারের ভূগর্ভস্থ কবরে আগে দর্শনার্থীদের যেতে দেওয়া হতো, কিন্তু নিচে নামলে একধরনের সুঘ্রাণ এবং একটা জোর হাওয়া বইত সেখানে। বহু মানুষ এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নিচে যাওয়ার দরজাটা সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।
মূল সমাধি থেকে ডান দিকে গেলে মাজার কমপ্লেক্সের জাদুঘর। জাদুঘর মানে অনেক গ্যালারিসংবলিত কিছু নয়, একটা দীর্ঘ করিডরের ভেতর সার বাঁধা কাচঢাকা কিওস্কের ভেতর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দান করা কোরান রাখা আছে। এখানে কাবা শরিফের একটা গিলাফ আছে যেটা ১৯৯২ সালে সৌদি বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ উপঢৌকন দিয়েছিলেন উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইসলাম করিমভকে। সেই গিলাফে ছাপা আছে কোরানের সূরা আল ইমরানের আয়াত। প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া গেল ১৮৪১ সালে মিসর থেকে প্রকাশিত ইমাম বুখারির সহিহ হাদিসের কপি, ১৮৯০ সালে প্রকাশিত সহিহ হাদিসের ওপর একটা আলোচনাগ্রন্থ। বাকি যেসব কোরানের কপি প্রদর্শিত রয়েছে, সেসব হাল আমলের।
কমপ্লেক্সের চত্বরে কয়েকটা শতবর্ষী চিনার গাছের সারি। প্রায় ছয় শ বছরের প্রাচীন এই গাছগুলো পুরো চাতালকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। চাতালের এক পাশে কয়েকটা ট্যাপ থেকে ক্রমাগত ঝরে যাচ্ছে জল, সেই পানি পানে রোগ সারে জানার পর আমাদের সফরসঙ্গীদের সবাই সাগ্রহে বোতলের কৃত্রিম পানি ফেলে দিয়ে সংগ্রহ করে মাজারের পবিত্র জল।

সমরকন্দ শহরে ফিরে এসে কফি হাউসে সময় কাটানোর ফাঁকে নগরীটি নিয়ে কিছু পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমরকন্দ ছিল সগদিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। সগদিয়া হচ্ছে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানজুড়ে প্রাচীন এক ইরানি সভ্যতা। চিনের তাং রাজত্বের সময় সেখানেও সগদিয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, বাকিরা বাইজেন্টাইন (মধ্যযুগীয় গ্রিকভাষী রোমানদের পরিচালিত সা¤্রাজ্য) সা¤্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিল। সিল্ক রুটের বাণিজ্যে এই জনগোষ্ঠীর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মধ্য এশিয়া জয় করার পর বিজয়ী মুসলমানরা সগদিয়াদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করে। সে সময় থেকে এখানে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং কালক্রমে নগরীটি ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। রোম ও ব্যাবিলনের সমসাময়িক সময়ে প্রতিষ্ঠিত সমরকন্দের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লংয়ের মতো বিশ্ববিজেতাদের নাম। সিল্ক রুট নামে পরিচিত চীন থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বাণিজ্যপথের ওপর থাকার কারণে সমরকন্দ পরিণত হয়েছিল এক সমৃদ্ধ নগরীতে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বণিকেরা এই শহরে এসে মিলিত হয়ে নিজ নিজ পণ্য বেচাকেনা করত।
সমরকন্দের নামটি এসেছে দুই শব্দের সংমিশ্রণে। ফারসি ভাষার ‘আসমারা’ (পাথর বা পাষাণ), আর সগদিয়া ভাষার ‘কন্দ’ (কেল্লা বা শহর) থেকে সমরকন্দ নামটির উদ্ভব, অর্থাৎ পাথরের কেল্লা বা পাথরের শহর। ৩২৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার শহরটি যখন জয় করেন, সে সময় গ্রিকদের কাছে এই নগরীর নাম ছিল ‘মারাকান্দা’। সমরকন্দ জয় করার পর তিনি বলেছিলেন, ‘এই শহরের সৌন্দর্য সম্পর্কে যা শুনেছি, তা অবিকল সত্য। তবে পার্থক্য হলো, এটি আমার শোনা বর্ণনার চেয়েও বেশি সুন্দর।’
আব্বাসীয় শাসনামলে সমরকন্দ পরিণত হয় মধ্য এশিয়ার রাজধানীতে। এই নগরী তখন মধ্য এশিয়ার মুসলিম সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। চেঙ্গিস খান সমরকন্দ দখল করেন ১২২০ সালে, সেই আগ্রাসনে শহরটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। চেঙ্গিস খানের বিজয়ের ২০০ বছর পর তৈমুর লং সমরকন্দকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করলে এই নগরী লাভ করে নতুন জীবন, আবার গড়ে ওঠে এক সমৃদ্ধশালী নগর হিসেবে।
কফি পান শেষে আমরা যখন গুর-ই-আমির দর্শনে যাই, তখন সূর্য প্রায় মধ্যগগনে, কিন্তু শীতের মিষ্টি রোদে মনে হচ্ছিল যেন সকালবেলা। গুর-ই-আমির মানে তৈমুরের সমাধি। কমপ্লেক্সের বাইরে দূর থেকেই দেখা যায় সমাধির নীল গম্বুজ আর দীর্ঘ মিনারের মাথা। কমপ্লেক্সে ঢোকার আগে একটা বাগিচা, সেটিতে সাইপ্রেস, পবনঝাউসহ নাম না জানা গাছগাছালির পরিকল্পিত বিস্তার। তার মাঝে একটা বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ‘আমির তিমুর মাকবারাসি’। মাকবারা অর্থ সমাধি। একবার দিল্লি গিয়ে গাড়ির চালককে বললাম, হুমায়ুনস টুম্ব চলো। সে কিছুতেই বোঝে না, হুমায়ুনস টুম্ব কোথায়। অনেক কষ্টে ওকে বোঝানোর পর ও বলে, ‘আভি সমঝা, হুমায়ুন মাকবারা’। এই মাকবারাই উজবেক ভাষায় ‘মাকবারাসি’।
মূল সমাধিসৌধে ঢোকার মুখে গেরুয়া রঙের পোড়া ইটে তৈরি উঁচু ফটক। তার গায়ে মোজাইকের কারুকাজ। বাঁকানো খিলান থেকে স্টেলেকটাইটের মতো ঝুলে আছে কারুকাজ করা সুষম নকশাদার পাথর। মোজাইকের মধ্যে ময়ূরকণ্ঠী নীলের প্রাধান্য। সেই গাঢ় আর হালকা নীলের সঙ্গে সাদায় মেশানো লতা আর ফুলের মোটিফ। তোরণের চাঁদওয়ারিতে কোরানের আয়াত লেখা। তৈমুরের নাতি উলুগ বেগের শাসনামলে এই তোরণটি বানানো হয়। তোরণটি উচ্চতায় যত লম্বা, তার বাঁকানো খিলানের দরজাটি তত ছোট, ফটকের মোট উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একখণ্ড বাগান পেরিয়ে সামনে মূল সমাধি ভবন। তার মাথায় লম্বালম্বি খাঁজকাটা ফিরোজা রঙের গম্বুজ। এই গভীর খাঁজের কারণে গম্বুজটি পেয়েছে এক অসাধারণ চপলতা, সাদামাটা সাধারণ গম্ভীর গম্বুজের মতো মনে হয় না। বুখারা ও সরকন্দের আরও বহু স্থাপনায় দেখা গেছে একই ঘরানার স্থাপত্য। গায়ে জ্যামিতিক নকশা করা গম্বুজটা ছাদের ওপর সরাসরি বসানো নয়। বৃত্তাকার লম্বাটে গেরুয়া ইটের ভিতের ওপর বসানো বলে ওটাকে গোল মনে হয় না। সেই ভিতের গায়ে আরবি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা বাক্যগুলোকে নকশার অংশ বলে ভ্রম হয়। মূল ভবনের টেরাকোটার দেয়ালের গায়ে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা। তার ছাদের দুপাশে দুটো উঁচু মিনার, ওগুলোর গায়েও জ্যামিতিক নকশা লতার মতো পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। মূল সমাধিতে ঢোকার তোরণটিও বাইরের মূল ফটকের মতো প্রায় একই ধরনের নীল-সাদা মেশানো টাইলসের। তার মধ্য দিয়ে ঢোকার যে নিচু দরজাটি রয়েছে, সেটি আয়তাকার, বাঁকানো খিলানের নয়। দরজাটির এই আকার ও আকৃতি মূল স্থাপত্যের সঙ্গে বিসদৃশ ঠেকে। সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে তৈমুরের বিশাল এক পেইন্টিং। ক্যামেরা আবিষ্কারের চার শ বছর আগের মানুষটির এই চেহারা কীভাবে পাওয়া গেল, তার জবাব পাওয়া যাবে আরও কিছুদূর গেলে।
সমাধির মধ্যে ঢোকার আগে একটা বড় ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে গাইড শাহরুখ আমাদের তৈমুর লংয়ের জীবনী এবং তাঁর যুদ্ধাভিযানের ফিরিস্তি শোনায়। বহু আলোচিত ও সমালোচিত এই শাসকের জন্ম ১৩৩৬ সালে বর্তমান উজবেকিস্তানের শাহরিসাবজ শহরে। তাঁর নাম তিমুর হলেও ইউরোপীয়রা সেটিকে বিকৃত করে বলে, ‘তেমারলেন’, যার উৎপত্তি ফারসি ‘তিমুর-ই ল্যাং’, বা ‘খোঁড়া তিমুর’ থেকে। অপরিণত বয়সে তৈমুর ছিলেন একটা ছিঁচকে চুরি-রাহাজানি করা দলের নেতা। এই দলের কাজ ছিল কৃষকদের গরু-ভেড়া চুরি কিংবা বণিক আর পর্যটকদের কাছ থেকে টাকাপয়সা ছিনতাই করা। সহজাত নেতৃত্বের গুণে তৈমুর দ্রুত সামরিক অধিনায়কে পরিণত হয়ে চেঙ্গিস খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হন। তাঁর বিজয়াভিযানের বলি হয়েছিল ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, আজারবাইজান, জর্জিয়া, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, তুরস্ক ও সিরিয়া। ধারণা করা হয়, তাঁর সামরিক আগ্রাসনে প্রায় এক কোটি সত্তর লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যা তখন বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ।
তিনি যখন দিল্লি আক্রমণ করেন, তখন দিল্লির সুলতান নাসিরউদ্দিন তুঘলকের সেনাদল তৈমুরের বাহিনীকে ভয় দেখানোর জন্য হাতির বহর ব্যবহার করেছিল। কিন্তু চতুর যুদ্ধবাজ তৈমুর তাঁর বাহিনীর সঙ্গে থাকা উটের পিঠে খড়ের গাদা বেঁধে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে হাতি বাহিনীর দিকে ছুটিয়ে দেন। আগুনের তাপে ক্রুদ্ধ উটের বহর আক্রমণ করে হাতির দলকে। ধাবমান অগ্নিকুণ্ড দেখে হাতিগুলো ত্রাসে পেছন দিকে ছুটতে শুরু করে। অস্থির এই হাতির দলের পায়ের নিচে দলিত হয়ে মারা পড়ে সুলতানের বাহিনীর অনেক সৈন্য। ফলে দিল্লির দখল পেতে তৈমুরের বাহিনীকে কোনো বেগ পেতে হয় নি। দিল্লি অধিকার করে নগরীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় তৈমুরের বাহিনী। সে ইতিহাস অনেকেরই জানা।

তৈমুর ছিলেন কুশলী সমরনায়ক, নিষ্ঠুর শাসক, নির্দয় নৃপতি। কিন্তু সমরকৌশলে তিনি এক বিশাল ভুল করেছিলেন চীন জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে সময় চীনে মিং বংশের রাজত্বকাল। এমন একটি বিশাল দেশ দখলের উদ্দেশ্যে দুই লাখ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে তিনি যখন সমরকন্দ থেকে তিন হাজার মাইল দূরের চীন অভিমুখে অভিযান শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স সত্তরের ঘরে। সেটা ছিল ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, প্রচ- শীতের মৌসুম। তাঁর বাহিনী যখন কাজাখস্তান পৌঁছায়, তখন ঘন তুষারে ঢাকা সেই দেশ, নদীর জলও জমে বরফ। বাধ্য হয়ে তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। এ সময় প্রচ- ঠান্ডায় কাবু তৈমুর আক্রান্ত হন জ্বরে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকেরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও অবস্থার উন্নতি করতে পারেন না। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর মৃত্যুর অনিবার্যতা। তিনিও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁর স্ত্রী ও পদস্থ সমর নেতাদের ডেকে প্রায় অস্ফুট দুর্বল স্বরে একটা বক্তব্য দেন। তাঁদের বলেন কেউ যাতে কান্নাকাটি করে নিজেদের জামাকাপড় ছিঁড়ে মাতম না করেন, সবাই যাতে কেবল তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি মারা যান ১৪০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ফলে চীন অভিযান বাতিল হয়ে যায়। তাঁর মরদেহ সমরকন্দে ফিরিয়ে নিয়ে এই গুর-ই-আমিরেই সমাহিত করা হয়।
মূল সমাধিতে ঢোকার পর দেখা যায় অনেক উঁচু ছাদের নিচে শান্ত, স্তিমিত আলোয় সাতটা সমাধি পাথর। সমাধির চারপাশ ঘিরে নিচু মার্বেল পাথরের জাফরি কাটা রেলিং। কালচে সবুজ পাথরটিই যে তৈমুরের কবর, সেটা আর বলে দিতে হয় না। ভেতরে অনিকস পাথরের দেয়ালের গায়ে নকশা কাটা, তার ওপরের অংশে মার্বেল আর জেসপারের গায়ে কোরানের আয়াত খোদাই করা। গম্বুজের ঘেরের নিচের প্রান্তেও উৎকীর্ণ রয়েছে কোরানের আয়াত। ওপরের প্যানেলের গায়ে মার্বেল পাথরের কার্নিশ। রঙিন প্লাস্টারের ওপর সূক্ষ্ম কাজ করা জ্যামিতিক নকশা এমন স্বল্পালোকেও ঝলমল করে যেন। দেয়ালের ওপরের অংশে এবং গম্বুজের গায়ে বাঁকানো দরজার আকারের কুলঙ্গি সোনালি কিংখাবের মতো উজ্জ্বল। অনেক উঁচুতে জাফরি কাটা জানালা গলে ঢোকা রোদ তৈরি করেছে এক আলো-আঁধারি পরিবেশ।
এমন এক শান্ত, সমাহিত নীরবতায় ছয়টি সাদা মার্বেল পাথরের সমাধির মাঝখানে কালচে সবুজ পাথরটি যেন এক অলিখিত ব্যতিক্রম। এই ইয়াশম (জেড) পাথরটি নাকি সে সময় পাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইয়াশমের খণ্ড। একসময় এটা চীন সম্রাটের প্রাসাদের মন্দিরে রক্ষিত ছিল, ১৪২৫ সালে মঙ্গোলিয়া থেকে এটা সংগ্রহ করে সমরকন্দে নিয়ে আসেন উলুগ বেগ। মঙ্গোলিয়াতে এই পাথরের ওপর সিংহাসনে বসতেন চেঙ্গিস খানের বংশধরদের একজন, সম্রাট দুয়া (মৃত্যু ১৩০৭)। উলুগ বেগের ইচ্ছাতেই পাথরটি বসানো হয় তাঁর পিতামহের কবরের ওপর। তৈমুরের কবরের মাথার দিকে আরেকটি কবর, কিংবা সেই কবরটির পায়ের কাছে তৈমুরের সমাধি। এটি একদা শক্তিমান এই শাসকের ধর্মীয় শিক্ষক মির সাইয়িদ বারাকার কবর। সেই কবরের মাথার দিকে মসজিদের মেহরাবের মতো দরজা আকৃতির কুলুঙ্গি, ওপরে জাফরি কাটা গবাক্ষ। তার পরের কবরগুলো তৈমুরের দুই দৌহিত্র মুহাম্মদ সুলতান ও উলুগ বেগের। তার পর রয়েছে তাঁর পুত্র শাহরুখ ও মিরন শাহের, বাকি দুটিও তাঁর দুই ছেলের। তৈমুরের এক ছেলের নাম শাহরুখ জেনে আমরা গাইড শাহরুখকে কিঞ্চিৎ খোঁচানোর চেষ্টা করি, সে সলজ্জ হাসিতে সেইসব খোঁচা কবুল করে নেয়।
তৈমুর লংয়ের সমাধির সঙ্গে জড়িত রয়েছে রহস্যময় ঘটনার একাধিক ইতিহাস। নাদির শাহ যখন সমরকন্দ দখল করেন, তখন পাথরটি উঠিয়ে পারস্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে দুর্ঘটনাবশত পাথরটি ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায়। বলা হয় তার পর থেকে বিভিন্ন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাড়া করে ফিরতে থাকে তাঁকে, তাঁর পুত্রও এক দুরারোগ্য রোগে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মীয় উপদেষ্টারা মনে করেন তৈমুরের সমাধি পাথরটাই এসব দুর্যোগের মূল উৎস। তাঁদের পরামর্শে পাথরটি আবার সমরকন্দে পাঠিয়ে দিয়ে গুর-ই-আমিরে বসিয়ে দেওয়া হয়। নাদির শাহের ছেলেটিরও রোগমুক্তি ঘটে। পরের ঘটনাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুটো অধ্যায়।
ইতিহাসবিদ আলেকজান্দার মিশকভের লেখা থেকে জানা যায় সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্তালিন ১৯৪১ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী মিখাইল গেরাসিমভকে তৈমুরের কবর থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে তাঁর সত্যিকারের চেহারার ছবি আঁকার নির্দেশ দেন। কঙ্কাল থেকে মৃত ব্যক্তির ছবি আঁকার বিশেষ কায়দাটি সে সময় রাশিয়ায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। তৈমুরের কবর চিহ্নিত করার পর গেরাসিমভের দল কবর খোঁড়ার কাজ শুরু করে। এ রকম সময়ে তাঁর কাছে খবর আসে, তিনজন বুজুর্গ মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। কাছেই ছিল চাইখানা নামে পরিচিত মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত বিশেষ ধরনের জনপ্রিয় এক চায়ের ক্যাফে। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন তিন বৃদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয়, তিনজন ঠিক যেন যমজ ভাই। তাঁরা দোভাষীর সাহায্যে গেরাসিমভকে তৈমুরের মৃতদেহ তুলতে নিষেধ করেন। কিন্তু স্তালিনের হুকুমের বরখেলাপ করা যাবে না। তবু তিনি তাঁদের এই অনুরোধের কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, ‘স্তালিনের চেয়ে আরও বড় ক্ষমতাধর শাসক তৈমুর লংয়ের মৃতদেহ এটি।’ মারাত্মক কিছু ঘটে যাওয়া থেকে বাঁচতে চাইলে তাঁর উচিত হবে এই ভয়াবহ কাজ থেকে বিরত থাকা। তারপর তাঁরা তাঁকে আরবিতে বা ফারসিতে লেখা প্রাচীন এক পুঁথি দেখান, ওটার এক জায়গায় লেখা ছিল ‘তৈমুর লংয়ের ঘুম ভাঙালে পৃথিবীতে এমন একটি রক্তাক্ত ও ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হবে, যা মানবজাতি আগে কখনো দেখে নি’।
বলা বাহুল্য, গেরাসিমভ এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করার মানুষ নন। তাই নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে তিনি ফিরে যান তাঁর খননকাজে। সেদিন ছিল ১৯৪১ সালের ২০ জুন। কবর খুঁড়ে তাঁরা দেখেন সমাধির গায়ে ফারসি ও আরবি ভাষায় লেখা, ‘আমি যেদিন জাগব, সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হবে’। এই লেখা দেখেও গেরাসিমভ বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। সমাধির পাটাতন সরিয়ে কফিন ওঠানো হয় ২২ জুন তারিখে। গভীর আগ্রহ নিয়ে কফিনের ডালা খুললেন গেরাসিমভ। সঙ্গে সঙ্গে কর্পূর, ধূপ, গোলাপ আর লোবানের মিলিত গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে সমাধিগৃহ। গবেষণায় জানা যায়, এই গন্ধ মৃতদেহ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত তেলের। কফিনে শায়িত পাঁচশ বছর আগে পরপারে চলে যাওয়া মহাশক্তিধর তৈমুরের নিথর-নীরব দেহ। মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা আরেকটা ফলক দেখে প্রায় চমকে ওঠেন গেরাসিমভ। সেটিতে লেখা, ‘যে-ই আমার কবর খুলুক না কেন, সে আমার চেয়ে ভয়াবহ এক আগ্রাসীকে পৃথিবীতে ডেকে আনবে’।
গেরাসিমভের ভেতর ভর করে কিছুটা সংশয়। তবু তৈমুরের দেহাবশেষ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান তিনি। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, তৈমুর ছিলেন ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা। কোনো এক যুদ্ধে আঘাত পাওয়ার কারণেই হয়তো তাঁর এক পা খোঁড়া।
গেরাসিমভ যেদিন তৈমুরের মৃতদেহ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, ঠিক সেদিনই জার্মানির নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিমুখে হামলা চালায়, ঐতিহাসিক এই অভিযানের নাম ‘অপারেশন বারবারোসা’। তিন হাজার ট্যাংক, সাত হাজার কামান আর আড়াই হাজার যুদ্ধবিমান নিয়ে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার অঞ্চলজুড়ে জার্মানির সেই আচমকা আক্রমণ অপ্রস্তুত সোভিয়েত বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছিল।
খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন গেরাসিমভ। তাঁর মনে পড়ে যায়, কবরের গায়ের লেখা সাবধানবাণীটির কথা। তিন বৃদ্ধের নিষেধের কথা ভেবে তিনি ছুটে যান সেই চাইখানায়। দোকানের মালিক জানান, রহস্যময় তিন বৃদ্ধকে আর কখনোই দেখে নি কেউ, আগেও কখনো নয়। এবার গেরাসিমভের মনে হলো তিন বৃদ্ধের সাবধানবাণী, কবরের গায়ে এবং কফিনের ভেতর ফলকের লেখা—এসব গ্রাহ্য করলে হয়তো রাশিয়ার এত বড় বিপর্যয় ঘটত না। স্তালিনকে ফোন করে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেন তিনি। স্তালিন কোনো কথা শুনতে চান না, তিনি দেখতে চান তৈমুরের মুখচ্ছবি। অগত্যা মনের ভেতর প্রবল দ্বিধা নিয়ে কাজ চালিয়ে যান গেরাসিমভ। তাঁর সফল কাজের শেষে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলো লৌহমানব তৈমুরের কঠোর চেহারা। উল্লেখ্য, চাঘতাই ভাষায় তৈমুর, শব্দের অর্থ লোহা।
এদিকে অপারেশন বারবারোসার ধারাবাহিকতায় নাৎসি বাহিনীর কাছে ক্রমাগত পরাজিত হচ্ছিল সোভিয়েত বাহিনী। স্তালিন তখন হয়তো নিজের অজান্তেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তৈমুরের দেহাবশেষ তোলার অভিশাপেই রুশ বাহিনীর এমন পরাজয় ঘটছে। তাই পূর্ণ মর্যাদায় ইসলামি রীতি মেনে তৈমুরের কফিন ফের দাফনের আদেশ দেন তিনি। ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর তৈমুরের মৃতদেহ আবার দাফন করা হয় গুর-ই-আমিরে। দাফনের পরপরই স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে অপারেশন ইউরেনাসে হিটলারের বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় সোভিয়েত বাহিনী। ইতিহাসবিদ আলেকজান্দার মিশকভের মতে এটিই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট। বিষয়টির সকল আনুষঙ্গিক তথ্য সঠিক, তৈমুরের দেহাবশেষ কবর থেকে ওঠানো এবং আবার সমাহিত করার তারিখের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের দুটি ঘটনা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে বটে, কিন্তু এটির কোনো গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের রাশিয়ান প্রোপাগান্ডা এরকমই হতো।
লৌহমানব তৈমুরের সমাধিগৃহ থেকে বের হয়ে পেছন দিকে গেলে দেখা যায় বহু প্রাচীন ইটের দেওয়ালের ভগ্নস্তূপ। এখানে ছিল খানকা ও মাদ্রাসা। মূল সমাধিগৃহের সংস্কার হলেও এগুলো এখন কেবলই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে টিকে রয়েছে ধ্বংসস্তূপের মতো। সামনের দিক থেকে দেখলে হুমায়ুনের সমাধি, তাজমহল—এসব স্থাপত্য একই ঘরানার বলেই মূল সমাধিভবনটাকে খুব পরিচিত মনে হয়। সামনের প্রশস্ত বাগানের এক কোণে নিরেট পাথরের একটা বিশাল চতুষ্কোণ খণ্ড রাখা। তার গায়ে লতাপাতার নকশা খোদাই করা। কারও মতে, এটি তৈমুরের সিংহাসনের বেদি। তার সামনে একখণ্ড মার্বেল পাথরের মধ্যে বড়সড় একটা চৌবাচ্চা। সেটিতে ফাটল ধরেছে, ভেঙে গেছে একটা প্রান্ত। ধারণা করা হয়, এটি ছিল তৈমুরের অজু করার পানির গামলা। গাইড শাহরুখ জানায় আরেক নতুন তথ্য। এটি দিয়ে নাকি বিভিন্ন অভিযানে যাওয়া সৈনিকদের মৃতের সংখ্যা নিরূপণ করা হতো। কোনো যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রত্যেক সৈন্য ডালিমের রস চিপে এটি ভর্তি করে যেত। দিন শেষে ফেরার পর সেই রস পান করত ওরা। রসের অবশিষ্টাংশ থেকে নিরূপণ করা হতো কতজন সৈন্য যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে আসে নি। ধারণাটার মধ্যে কতখানি বাস্তবতা আছে, বোঝা যায় না। তবে এ ধরনের ঐতিহাসিক নিদর্শনের সঙ্গে সব সময় কিছু ধারণাপ্রসূত কাহিনি প্রচলিত থাকে বলে সেসব অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।
গুর-ই-আমির থেকে বের হয়ে পিছু ফিরে তাকালে উজ্জ্বল গম্বুজ আর দুই সুউচ্চ মিনারের সৌন্দর্যের পেছনে আড়াল হয়ে যায় তৈমুরের যাবতীয় নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস। বিশ্বাস হতে চায় না, নিষ্ঠুর এই নৃপতির নাকি ছিল শিল্পের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের নিয়ে এসে তাদের দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে স্থাপত্যশিল্পের মাধ্যমে তিনি সাজিয়ে তুলেছিলেন সমরকন্দ নগরীকে। তৈমুরের এই বিপরীত চরিত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র হয়তো এটি নয়।

গুর-ই-আমির থেকে বের হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। আমাদের লাঞ্চে সব সময়ের মতোই ছিল বিভিন্ন ধরনের বনরুটি, সালাদ ও কাবাব। ঘোড়ার মাংসও ছিল, অনেকের আপত্তি থাকলেও আমরা কয়েকজন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অপরিচিত সেই মাংস খাই। ঘোড়ার মাংস খাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল মঙ্গোলিয়ায়। সালামির মতো ঈষৎ লোনা শুঁটকির মতো এই খাবারটি আমাদের গরু-ভেড়া খাওয়া জিহ্বায় তেমন সুস্বাদু মনে হয় না। যা কিছু রোচে, সেটুকু বোধ হয় ভদকার গুণে। বলে রাখা উচিত, দখলদার আমলে ভদকার বীজটা রাশিয়ানরা বেশ ভালোভাবেই পুঁতে দিয়ে গেছে উজবেকিস্তানে। আমাদের টেবিলে বসিয়ে রেখে আলিশের ও শাহরুখ কিছুক্ষণ পরপর ফোনে কারও সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলে যাচ্ছে, ওদের সেই ভাষা না বুঝলেও কণ্ঠের উৎকণ্ঠা চাপা থাকে না।
বিষয়টা খোলাসা হয় লাঞ্চের পর বাইরে এসে। আমাদের সঙ্গের মাইক্রোবাসটি বিকল হয়ে গেছে, ওটা চালু করার চেষ্টা চলছে। এটা ট্যুর কোম্পানির মাথাব্যথা বলে আমাদের মধ্যে কোনো উদ্বেগ সংক্রমিত হয় না। ওরা দ্রুত কয়েকটা ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে গন্তব্য বলে আমাদের রওনা করিয়ে দেয়। সামান্য দূরত্বে গিয়ে যেখানে নামতে হয়, সেটি হচ্ছে রেগিস্তান স্কোয়ার। মসজিদ, খানকা ও মাদ্রাসার সমন্বয়ে গঠিত রেগিস্তান এক বিশাল কমপ্লেক্স। ঢোকার মুখেই কয়েকজন কিশোরী ও মহিলা ভিখিরি আমাদের দেখে ছুটে আসে। তবে শাহরুখ তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সামনের রেলিংঢাকা উঁচু মঞ্চের মতো বেদির ওপর দাঁড়ালে চোখে পড়ে নিচের প্রশস্ত চত্বরের তিন পাশে তিনটি বিশালাকার উঁচু ফটক। একসময় এই চত্বরই ছিল নগরীর মূল জনসংযোগের জায়গা। সব ধরনের রাজকীয় ফরমান ঘোষণা, বিচার-আচার, শাস্তি—সব এখানেই ঘটত। আমরা যখন সেই মঞ্চের মতো বেদির ওপর দাঁড়িয়ে রেগিস্তানের ভাস্কর্য সৌন্দর্য উপভোগ করি, তখন সদ্য বিবাহিত কয়েক যুগল ফটো সেশনের জন্য আসে সেখানে। কনের নিষ্কলঙ্ক সাদা ব্রাইডাল গাউনের আভা রেগিস্তানের বৈকালিক আবহে যোগ করে এক শ্বেতশুভ্র শুদ্ধতা। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী মহিলাদের দেখে স্থানীয় উজবেক রমণীদের মধ্যে ওদের সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। এ যেন মডেলদের সঙ্গে ছবি তোলার প্রতিযোগিতা। অথচ এই অনন্যসুন্দরী উজবেক তরুণীদের সঙ্গে বরং ছবি তোলা উচিত ছিল আমাদের।
ছবি তোলার এই মচ্ছব শেষ হলে মনোযোগ দিয়ে সামনের তিনটি স্থাপনার দিকে ভালো করে তাকানোর সুযোগ মেলে। আমাদের গাইড শাহরুখ জানায়, এগুলোর তিনটিই মাদ্রাসা, হাতের ডানে শের দোর মাদ্রাসা, সোজা সামনে তিল্লা করি মাদ্রাসা এবং বাঁয়ে উলুগ বেগ মাদ্রাসা। শাহরুখের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরা বেদি থেকে নিচের চত্বরে নেমে আসি। শের দোর মাদ্রাসার সামনের উঁচু ফটকের চাঁদওয়ারির দুপাশে দুটো বাঘসদৃশ প্রাণীর পিঠের ওপর শজারুর কাঁটার মতো কাঁটা, তার নিচে দুটো মানুষের মুখের চেহারা। সেই প্রাণীর সামনে দুটো হরিণ। সপ্তদশ শতাব্দীর এই স্থাপনায় মানুষের চেহারা এবং প্রাণীর ছবি কীভাবে আসে, মাথায় ঢোকে না। ইসলামে যে-কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। সেই ফটকের মাথায় স্বস্তিকা চিহ্ন দেখেও কোনো হিসাব মেলে না। প্রাচীন কাল থেকে স্বস্তিকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচুর্য আর উর্বরতার প্রতীক হিসেবে। জার্মান নাৎসি বাহিনীর প্রতীক এবং হিন্দু মন্দিরের স্বস্তিকা চিহ্নের সঙ্গে এই মাদ্রাসার ফটকের চিহ্নটির কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায় না। দৃশ্যত শের দোর মাদ্রাসার এই ফটক যেন উল্টো দিকের উলুগ বেগ মাদ্রাসার প্রতিবিম্ব। পার্থক্য কেবল ফটকের ওপরের স্বস্তিকা ও প্রাণীদের ছবি। শের দোর মাদ্রাসার ফটকে এ দেশের অন্য স্থাপত্যগুলোতে ব্যবহার করা নীল রং অনুপস্থিত। অনুপস্থিত লতাপাতার নকশাও। এটির নকশাগুলো সবই জ্যামিতিক। তার সঙ্গে রয়েছে আরবি ক্যালিগ্রাফি। ফটকের দুপাশে ছাদের ওপর দুটো ফিরোজা রঙের খাঁজকাটা গম্বুজ, তার দুপাশে দুটো মিনার। গম্বুজের গায়ের নকশা, নিচের অংশের উৎকীর্ণ আরবি ক্যালিগ্রাফি—সবই গুর-ই-আমিরের গম্বুজটির মতো, মিনার দুটোও। যেন একই কারিগরের হাতে তৈরি দুটোই।
উলুগ বেগ মাদ্রাসার প্রতি একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল আমার। তৈমুর লংয়ের নাতি চৌদ্দ শতকের শাসক উলুগ বেগ ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ। তাঁর মূল আগ্রহের বিষয় ছিল জ্যামিতি। বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদার এই মাদ্রাসায় তিনি তাঁর বাছাই করা পণ্ডিতদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা এখানে এসে গবেষণা করেন। এই কাজে সহায়তা করার জন্য তিনি একটা মানমন্দিরও তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র বিশ বছর পর একদল ধর্মান্ধ মানুষ মানমন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, সব যুগে সব ধর্মের কট্টরপন্থী মানুষেরা যাবতীয় প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের জানা আছে কোপার্নিকাস, জোহান কেপলার, গ্যালিলিও—যাঁরাই বলার চেষ্টা করেছেন যে সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তাদেরকেই হয় তাঁদের মতবাদ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে, কিংবা সইতে হয়েছে সামাজিক ও ধর্মীয় ভর্ৎসনা ও গঞ্জনা। ক্লেমেন্ট ব্রুনোর কথা আমাদের মনে আছে, যিনি ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে এই মহাবিশ্বের মতো আরও মহাবিশ্ব আছে, পৃথিবী গোলাকার, সূর্য এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়, বরং একটি নক্ষত্রমাত্র। তাঁর এই ধর্মদ্রোহী বিশ্বাসের কারণে তাঁকে জনসমক্ষে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।
উলুগ বেগের জীবদ্দশায় এই মাদ্রাসায় শ খানেক শিক্ষার্থী ছিল। নীলপ্রাধান্যের নকশাখচিত মূল ফটক দিয়ে ভেতরের আঙিনায় ঢুকলে চারপাশজুড়ে দোতলা ভবন। ফটকের চাঁদওয়ারিতে সৌরমণ্ডলের তারকারাজির নকশা। ভেতরের আঙিনার চারপাশজুড়ে তীব্র ময়ূরকণ্ঠী নীল আর হালকা গেরুয়া রঙের টেরাকোটার ওপর সিরামিকে লতাপাতার জটিল নকশা করা পরিচিত বাঁকানো খিলানের সারি, প্রতিটি খিলানের পেছনে আছে আরেক প্রস্থ খিলান, সেগুলোর নিচে লম্বা চতুষ্কোণ দরজা। ধারণা করা যায়, এগুলো ছিল শিক্ষার্থীদের হোস্টেল। সেই দ্বিতল ভবন আর মূল ফটকের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে জ্যামিতিক ক্যালিগ্রাফিতে খোদিত কলেমা। ভেতরের আঙিনায় অনুচ্চ গাছের নিরাভরণ বাগান। সেসব গাছের কোনোটি পাতাঝরা শীতের প্রভাবে উলঙ্গ শাখা-প্রশাখা নিয়ে দাঁড়ানো। উলুগ বেগের নাম খচিত এই স্থাপনার সঙ্গে বাকি দুই স্থাপত্যের একটা প্রায় অলক্ষ পার্থক্য চোখে পড়ে। তিল্লা করি ও শের দোর মাদ্রাসার মতো দৃষ্টিনন্দন চোখে পড়ার মতো কোনো গম্বুজ নেই উলুগ বেগ মাদ্রাসার ওপর। একটা গম্বুজ আছে বটে, সেটা চোখেও পড়ে না, বাকিগুলোর মতো বর্ণিলও নয়। দূর থেকে দেখলে কেবল তার জৌলুসহীন বিনম্র উত্থান দেখা যায়। এখানে বলে রাখা ভালো, এই মাদ্রাসাটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছিল প্রাচ্যের মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। বিখ্যাত পার্সি কবি, মরমি সাধক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আবদুল রহমান জামি এখানেই পড়াশোনা করেছেন। উলুগ বেগ স্বয়ং পাঠদানের অংশ হিসেবে এখানে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর শাসনামলে এই মাদ্রাসা ছিল শিক্ষাবিস্তারের এক প্রধান কেন্দ্র।
উলুগ বেগ মাদ্রাসার তীব্র নীল নকশার আবহ থেকে বের হয়ে আমরা যাই তিল্লা করি মাদ্রাসাসংলগ্ন মসজিদটিতে। মসজিদের ভেতর ঢুকে কিছুক্ষণ আগে দেখা বৈকালিক আলোয় উলুগ বেগ মাদ্রাসার গাঢ় নীল আবহ থেকে তীব্র সোনালি আলোকচ্ছটা সয়ে নিতে আমাদের খানিক সময় লাগে। নীল আর সোনালি রঙের সঙ্গে আরও বিভিন্ন রঙের সমাহারে মেহরাবের অনুজ্জ্বল আলো ক্ষণিকের জন্য আমাদের প্রায় চন্দ্রাহত করে রাখে। মেহরাবের পাশে মার্বেল পাথরের মিম্বার দশ কি এগারোটি সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ভেতরের দেয়ালে ও গম্বুজের ছাদের নিচে সোনালি গিল্টি করা সূক্ষ্ম নকশার কারুকাজ উজ্জ্বল, নিখুঁত ও সুষম। ‘তিল্লা করি’ অর্থ ‘সোনার গিল্টি করা’ জানার পর মসজিদটির নামের এই সোনালি উদ্ভাসের মাহাত্ম্য পরিষ্কার হয়। মসজিদের ভেতরের সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস নিচ থেকে দেখা এটির ছাদের গোলাকার সূক্ষ্মতম নকশার কারুকাজ। ঘাড় বাঁকিয়ে ওপরের দিকে দেখলে কখনো মনে হয় এটি গম্বুজের নিচের সমতল ছাদ, আবার কখনো মনে হয় সমতল ছাদের তলায় কেবল নকশার কারণেই এই দৃষ্টিভ্রম। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী ‘যেন নহে এ-ই সে-ই’ মতবাদে বিশ্বাসী কবি সিদ্ধার্থ হক মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করে এটি কি সমতল নাকি অবতল, অর্থাৎ ভেতরের দিকে বাঁকা। কিন্তু আজ অবধি বুঝতে পারি নি আসলেই সেই অবিশ্বাস্য চিত্রকলা সমতল কি অবতল। তিল্লা করি মাদ্রাসার ভেতরের স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে বুখারার দিভান বেগি মাদ্রাসা কিংবা পাশের উলুগ বেগ মাদ্রাসার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সেই চারপাশ ঘেরা দোতলা ভবনের বাঁকানো খিলানের সারি, তার পেছনে বিভিন্ন কক্ষের দরজা। প্রতিটি কক্ষের জন্যই খিলানযুক্ত একখণ্ড বারান্দা। তার সামনের দেয়ালে সাদা পটে নীলের আবহে লতানো নকশার সূক্ষ্ম কারুকাজ।
দীর্ঘ সময় তিল্লা করি মাদ্রাসার ভেতরের চমৎকার পরিবেশ উপভোগ করে নিচতলার স্যুভেনিরের দোকানের সুন্দরী উজবেক তরুণীদের সঙ্গে স্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে নানান খুনসুটি করে আমরা সুবোধ বালকের মতো ভেতরের আঙিনায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়ার জন্য বসি। আমাদের এ রকম আয়েশি ভঙ্গি দেখে আলিশের উশখুশ করে, কারণ, আমাদের আজই তাসখন্দে পৌঁছাতে হবে, সেটি আলিশেরের দায়িত্ব।
কিছুক্ষণ আগে শেরদোর মাদ্রাসার ফটকের ওপর মনুষ্যমূর্তি, বাঘ ও হরিণের ছবি দেখে যতখানি বিস্মিত হয়েছিলাম, ততখানি বিস্মিত হই তিল্লা করি মাদ্রাসার ভেতরের চাতালঘেরা বারান্দার নিচতলায় স্যুভেনিরের দোকানগুলোর সামনে প্রমাণ সাইজের মনুষ্যমূর্তি দেখে। মনে হয়, এসব বেদাতি কাজ রাশিয়ানরাই শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এমনকি বুখারার দিভান বেগি মাদ্রাসার মূল ফটক আর শের দোর মাদ্রাসার ফটকের অনৈসলামিক চিত্রগুলোও হয়তো রাশিয়ান যুগের কাজ। তবে এসব নিয়ে কিছু বলা বিপজ্জনক। বের হয়ে এলে মূল চত্বরের এক পাশে শের দোর মাদ্রাসার ফটকের সামনে হাতের বাঁয়ে একটা বেমানান সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। সযত্নে সংরক্ষিত এই সমাধি হচ্ছে এক কসাইর কবর। সেই কসাই প্রতিদিন রেগিস্তান নির্মাণে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বল্প মূল্যে কিংবা বিনা মূল্যে খাবার সরবরাহ করতেন। এই খাবারের বিনিময়ে তাঁর কোনো বাড়তি দাবি ছিল না, তাঁর একমাত্র দাবি ছিল তাঁকে যাতে রেগিস্তানের মূল চত্বরে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রেগিস্তানের চত্বরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।
দীর্ঘ বিশ্রামের পর আমরা যখন তিল্লা করি মাদ্রাসা থেকে বের হই, তখন রেগিস্তানের সামনের চত্বরে বৈকালিক ছায়ার দীর্ঘ অবয়ব প্রলম্বিত হয়েছে। সেই ছায়াচ্ছন্ন বিকেল ছিল শীতবিকেলের মতো বিষণ্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান সাঁঝবেলা। সেই ছায়াময় বিকেল কি সন্ধ্যায় আমরা তাসখন্দের পথে যাত্রা শুরু করি। পেছনে পড়ে থাকে সমরকন্দের আরও বহু দর্শনীয় জায়গা, এক জীবনে পৃথিবীর সবকিছু কি দেখা সম্ভব?
চলবে...
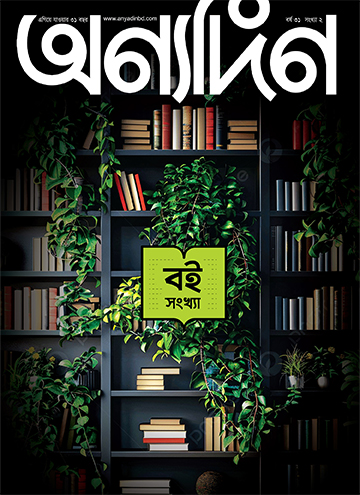









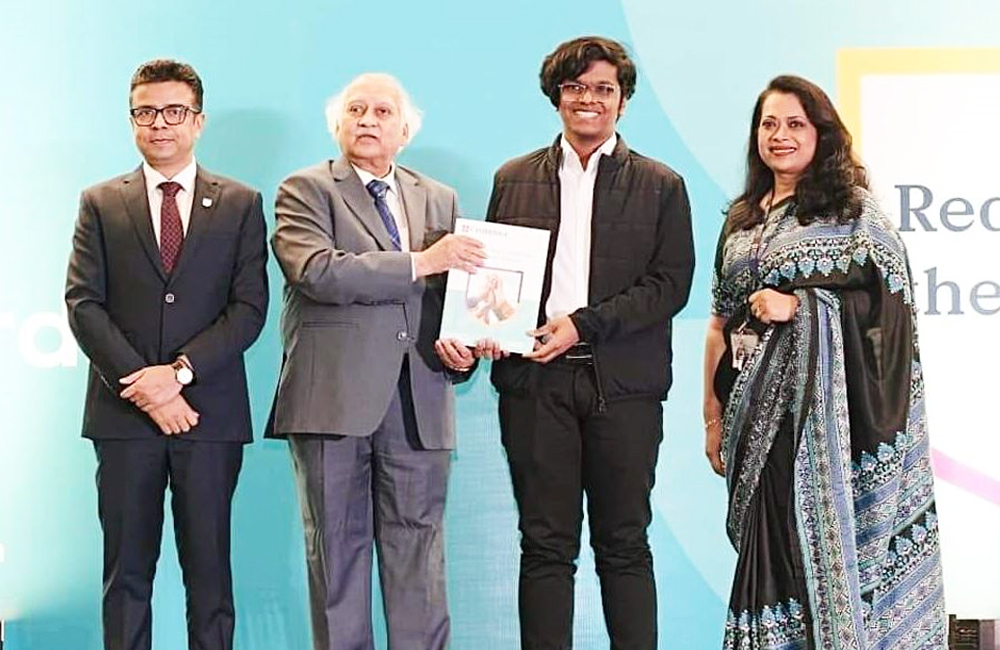




Leave a Reply
Your identity will not be published.