শোয়েবের কথা
লহরি, আমার মেয়ে, তাকে আমি খুন করতে চাই। রোজ রাতে ভাবি। ঠিক কীভাবে মারলে পুলিশ সন্দেহ করবে না, সেটা ভেবে পাই না দেখে মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে আর আমি মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি ক্রমশ।
আজও সকাল থেকে মেজাজ প্রচণ্ড বিগড়ে আছে আমার।
বৃষ্টি নেই পঁচিশ-ত্রিশ দিন। ৪১ ছাড়িয়েছে তাপমাত্রা। এই অস্থির গরমে মাথার ওপরে ফ্যানটিও বোধ হয় মানুষের মতোই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত। ক্লান্তির ছাপ তার ঘূর্ণনেই টের পাওয়া যাচ্ছে। আর বিরক্তির ব্যাপারটা ধারণা করছি।
সরকারি হাসপাতাল এমন জায়গা, যেখানে ডাক্তার থেকে শুরু করে আয়া পর্যন্ত সবাই বিরক্ত থাকে। হাসপাতালের আসবাবইবা এর ব্যতিক্রম হবে কেন! দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বড় অনীহা নিয়ে ঘুরছে ফ্যানটা। বিরক্ত না হলে নতুন ফ্যান অমন ধীরে ঘুরবে কেন, অমন শব্দই করবে কেন?
ফ্যানটির একটি ব্যাপার আমার চোখে পড়ছে, এতে ডানা চারটি। এর আগে চার ডানার সিলিং ফ্যান দেখি নি আমি। সারা জীবন দেখে এসেছি, ফ্যানে তিনটি ডানা হয়। চার ডানার কারণেই কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না, বাতাসের চেয়ে শব্দ বেশি হচ্ছে। মনে হয়, এই ফ্যান কিনেই আনা হয়েছে শব্দ সৃষ্টির জন্য, যাতে রোগীরা বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তাতে ডাক্তারদের কষ্ট কমবে, অন্য কর্মচারীরাও বেঁচে যাবে। পাঁচ বছর ধরে হাসপাতালে হাসপাতালে দৌড়াচ্ছি, সব ডাক্তার চেনা আছে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারেরা মনোযোগ দিয়ে একটি মাত্র সময়েই রোগী দেখে, যখন সে বেসরকারি হাসপাতালে বসে। কিন্তু আমার পক্ষে আর বেসরকারি হাসপাতালে দৌড়ানো সম্ভব নয়।
আমি উঠে গিয়ে কান্তার পাশে গিয়ে বসলাম। সব রাগ, বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, আরও সময় লাগবে মনে হচ্ছে। মাত্র ১৫ নম্বর সিরিয়াল চলে। আমরা ৩৪-এ। তুমি এক কাজ করো, লহরিকে আমার কোলে দাও।
কান্তা আমার কোলে মেয়েকে দিতে যাচ্ছিল, সাথে সাথে লহরি, আমার মেয়ে, চেঁচিয়ে উঠল। এমন চিলচিৎকার যে প্রতিটা মানুষ আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। আমার মনে হতে লাগল যেন চিড়িয়াখানার কোনো একটা দরজা খুলে বসে আছি স্ত্রীকন্যাসমেত। মেজাজ আরও বিগড়াল। আমি জোর করে নিতে গেলাম এবার লহরিকে, দুহাত দিয়ে খামচে দিল সে। এক লাফে সরে গেলাম। হাতের চামড়া তুলে নিয়ে গেছে অনেকখানি। রক্ত বেরোচ্ছে।
আমার চোখ দেখে কান্তা বুঝতে পারল যে প্রচণ্ড রেগে আছি। মিহি স্বরে সে বলল, থাক, আমার কোলেই থাক। যাবে না ও।
আমি বললাম, তোমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘেমে নেয়ে গেছ।
কান্তা বলল, থাক। বাসায় গিয়ে রেস্ট নেব।
আর রেস্ট! এই জীবনে কোনো রেস্ট নেই আমাদের।
কান্তা বলল, মন খারাপ কোরো না। দেখো, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।
বিড়বিড় করে বললাম, কিচ্ছু ঠিক হবে না কান্তা। কিচ্ছু না।
দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে রাখায় আমার গায়ে হাত রাখতে পারল না কান্তা। শুধু আমার শরীরের আরও কাছে ঘেঁষে এসে বলল, মন খারাপ কোরো না। আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।
আমি তো কোনো ভালো খুঁজে পাচ্ছি না। তবু কান্তাকে আমি অবিশ্বাস করি কীভাবে! সে কখনো মিথ্যে বলে না।
আমার মেয়ে লহরি, জন্মানোর পরপর ধার করে আড়াই মণ মিষ্টি কিনে বিলিয়েছিলাম কাছের মানুষদের। বিয়ের চার বছর পর কনসিভ করেছিল কান্তা। লহরির জন্মের দেড় বছর পর টের পাই, সে স্বাভাবিক বাচ্চাদের মতো নয়। প্রথম সন্দেহটা হয় মূলত তার ছমাস বয়সে। মনে হচ্ছিল, ও বোধ হয় কানে শুনতে পায় না।
খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন ভোরবেলা থেকে। অফিসে যাব কি যাব না ভাবছি, হঠাৎ ধড়াম-ধড়াম করে দীর্ঘ এক বজ্রপাত হলো কাছে কোথাও। ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। অথচ লহরি দেখলাম একমনে আঙুল চুষছে। কী ব্যাপার! জন্মের পর লহরির এই প্রথম বৃষ্টি। শিশুরা প্রথম যা দেখবে-শুনবে, তাতেই বিস্মিত হবে। অথচ সামান্যও বিকার নেই তার। তখনই সন্দেহ হলো।
কান্তা উড়িয়ে দিয়েছিল আমার কথা। বলল, ছ-মাসের বাচ্চার কাছ থেকে তুমি কি ছ-বছরের বাচ্চার এক্সপ্রেশন আশা করো? আশ্চর্য!
আমাকে ধমকালেও কান্তা যে আসলে মোটেও উড়িয়ে দেয় নি ব্যাপারটা, সেটা বুঝতে পারলাম বেশ। প্রায়ই আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে পরীক্ষা করতে শুরু করল সে। কখনো কানের কাছে হাতের চুড়ি বাজাত রিনঝিন করে। কখনো হয়তো জোরে ডাক দিল, লহরি! লহরি!
মেয়ে সেদিকে ফিরেও তাকাত না। নিজের মতো একমনে খেলত।
পারতপক্ষে আমার সামনে কান্তা এসব করত না। হঠাৎ হঠাৎ আমার সামনে পড়ত। দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যেতাম। শেষমেশ লহরির প্রথম জন্মদিনের দিন কান্তাই বলল, চলো তো, মেয়েকে কানের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। সাহিক সেন্টার খুব ভালো এসবের জন্য।
কোনো লাভ হলো না। ওরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল, তারপর ঘোষণা দিল যে লহরি কানে শুনবে না। তার কানে শোনার ক্ষমতাই নেই একদম।
তবু একের পর এক ডাক্তারদের কাছে দৌড়াতে লাগলাম। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতাল। শুরুতে সরকারি, তারপর বেসরকারি। লাভের লাভ এই হলো যে সরকারি ডাক্তারদের ওপর থেকে আমার ভক্তি আর বিশ্বাস উঠে গেল। আর বেসরকারি ডাক্তারদের ওপর থেকে উঠে গেল সম্মান।
এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই বুঝতে পারলাম, লহরি কথা বলতে পারবে না। যেহেতু সে কানে শোনে না, তাই ভাষা শেখার কোনো কারণই নেই। এভাবে সতেরো-আঠারো মাসে এসেও যখন দেখলাম যে মেয়ে আমার শুয়েই থাকে, উঠে বসে না পর্যন্ত, তখন সন্দেহ আরও গাঢ় হয়। আত্মীয়স্বজনেরা সান্ত্বনা দেয়, অনেক বাচ্চাই দেরিতে হাঁটা শুরু করে। নিশ্চয়ই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
কিচ্ছু স্বাভাবিক হলো না।
আমরা নতুন করে আবিষ্কার করলাম, লহরির হাজারটা সমস্যা। তার হাইড্রোকেফালাস নামে ভয়াবহ এক অসুখ আছে। মাথায় পানি জমা। এই অসুখ হলে মাথা বিকট রকম বড় হয়ে যায়। দেখতে ভয়ংকর লাগে, দানবের মতো। লহরির মাথায় পানির পরিমাণ সামান্য দেখে তার মাথা অতটা বড় নয়। কিন্তু সেটাও একধরনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। মাথায় এত কম পরিমাণ পানি থাকায় ডাক্তারেরা তার অপারেশন করতে রাজি নয়।
ফলে আড়াই-তিন বছরেও লহরি বিছানায় জগদ্দল পাথরের মতো শুয়ে থাকে। হাতে কোনো একটা খেলনা ধরিয়ে দিলে বুঁদ হয়ে খেলতে থাকে।
তিন বছর তিন মাসে এসে দেখা দিল নতুন উপসর্গ।
সারা দিন খুব শান্ত-শিষ্ট থাকে লহরি। নিজের মতো খেলে। কিন্তু রাত হলেই পাল্টে যায় তার চেহারা। বিশেষ করে, ঘুমানোর পর। ঘুমিয়ে পড়লেই শুরু করে ত্রাহি চিৎকার। সেই চিৎকার থামানোর একটাই উপায়, মেয়েকে পায়ের ওপর শুইয়ে ক্রমাগত পা নাড়ানো। একটুও থামা যাবে না। থামলেই চিৎকার শুরু।
আমার সকালে অফিস থাকে, ফলে জেগে জেগে এভাবে পা নাড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুটি পা লম্বা করে লহরিকে বালিশে শুইয়ে নাড়াতে থাকে কান্তা। ঘুমে একটু চোখ লেগে এলেই থেমে যায় কান্তা। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় চিৎকার। কান্তা পা নাড়াতে শুরু করে আবার। ভোর পর্যন্ত লহরির এই চিৎকার আর কান্তার পা নাড়ানো চলতে থাকে। এরপর দু-চার ঘণ্টা একটা ঘুম দেয় মা-মেয়ে।
গত দেড় বছর ধরে এই চলছে। অবস্থার একটাই উন্নতি হয়েছে, এখন আরও একটি শক্ত অসুখ আবিষ্কার করা গেছে—সেরেব্রাল পালসি। মস্তিষ্কের অসুখ। লহরি সেরেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত। উইকি ঘাঁটলে আরও নানা কিছু জানা যায় এ রোগ সম্পর্কে। যেটা জানা যায় না, তা হলো এই অসুখের সত্যিই কোনো নিরাময় আছে কি না।
ছোট্ট একটা রুমে থাকি আমরা। আধো ঘুম আধো জাগরণে প্রতিটা রাত পার করতে হয় আমাদের। সকালবেলা অফিসে গিয়ে ঢুলতে ঢুলতে রাশিফল লিখি। পরদিন রাতে আবারও একই চিত্র।
রোজ রাতে ভাবি, মেয়েটাকে মেরে না ফেললে এই বিপদ থেকে উত্তরণ নেই! ঠিক কীভাবে মারলে পুলিশ সন্দেহ করবে না, সেটা ভেবে পাই না দেখে আরও রাগ লাগে।
কান্তার কথা
হাসপাতাল মানেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, একদম শেষ সময়ে ডাক। তারপর ঢোকার ঠিক এক মিনিটের মাথায় বের হয়ে আসা। আগে–পরে নতুন নতুন টেস্ট, নতুন ওষুধ।
আজ একটু ব্যতিক্রম ঘটল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল যুবক ডাক্তার। নতুন-পুরোনো সব রিপোর্ট, কাগজপত্র। তারপর চোখের ভারী চশমাটা পাশে খুলে রেখে আমার দিকে ফিরল। বলল, এক কাজ করুন। মেয়েকে ইন্ডিয়া নিয়ে যান। সত্যি কথা হলো, এখানে এলে দিনের পর দিন আপনাকে দৌড়াতেই হবে।
ওর মাথার পানির কী অবস্থা, স্যার? অপারেশন করলে কি অবস্থা স্বাভাবিক হবে কিছুটা?
ওর মাথায় আসলে পানি নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। এই অবস্থায় অপারেশন না করানোই ভালো। আমরা করতে চাই না।
হঠাৎ কেমন কান্না ঠেলে আসে আমার। কী করব? এভাবে আর কত দিন! রোজ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মেয়েটার গায়ে এলোপাতাড়ি হাত তোলে শোয়েব। ওকে দোষ দিয়েই লাভ কী! দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে অফিস করা যায় কীভাবে?
হাউমাউ করে আসা কান্না ভেতরে চেপে রাখতে পারি না আর। বিয়ের পর গত দশ বছরে একবারও কাঁদি নি আমি। এমন নয় যে কান্নার মতো কিছু ঘটেই নি। তবু কাঁদি নি। আজ কেন জানি না, রাজ্যের কান্না এসে ভর করল। কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারকে বললাম, স্যার, আমি আর পারছি না। রোজ মেয়েকে পায়ে নিয়ে বসে থাকতে হয়। পা ফুলে গেছে আমার। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয়। কবে তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়েছি, মনে করতে পারি না। তবু কোনো আপসোস করতাম না, যদি মেয়েটা সামান্যও সুস্থ হতো। কিন্তু কোনো আশাই দেখছি না আমি।
ডাক্তার বলল, কাঁদবেন না প্লিজ। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবেন। আপনার স্বামী কোথায় আছেন?
ও বাইরে বসে আছে। অনেক ডাক্তার একসাথে দুজন ঢুকলে বিরক্ত হন, তাই আমি একাই ঢুকি ওকে নিয়ে।
আপনার স্বামীকে ডাকুন।
শোয়েবের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার জানতে চাইল, আপনার অবস্থা কেমন?
সে ঠিক বুঝতে পারল না বোধ হয়। বলল, এমন একটা মেয়ে যার আছে, তার অবস্থা আর কেমন হবে, স্যার। জীবন তেজপাতার থেকেও খারাপ। তেজপাতা তো তাও কারও না কারও কাজে লাগে। আমার জীবন চোতরাপাতা। গায়ে লাগলেই চুলকায়, এমন অবস্থা। তবু যদি সামান্য সুস্থ হতো মেয়েটা!
ডাক্তার বলল, হতাশ হবেন না। অনেক সময় সিচুয়েশন মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না, ভাই। আচ্ছা শোনেন, আমি আপনার আর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আসলে। সেরেব্রাল পালসির চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। তার ওপরে রোগী পুরোপুরি কি, অর্ধেকও সুস্থ হবে কি না, তারও কোনো ঠিক নেই। ইন্ডিয়া গেলে কিছুটা ভালো হতেও পারে। যেতে পারবেন?
ডাক্তারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শোয়েব। অবশ্য কী জবাবই-বা সে দেবে আর! তার হাতের অবস্থা তো আমি জানি। তাই আমিই বললাম, স্যার, পারব। একবার হলেও ইন্ডিয়া নিতে চাই।
শোয়েব আমাকে বলল, কীভাবে নেবে?
আমি বললাম, সেটা বাসায় গিয়ে আলাপ করব।
ডাক্তার আমাকে বলল, আপনি অনেক শক্ত মহিলা। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে যে এখনো বেঁচে আছে, আমি বুঝতে পারছি যে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার একার।
শোয়েব ডাক্তারের দিকে কিছুটা হতভম্ব হয়ে তাকাল। সম্ভবত সে ভাবছে, তাকে অপমান করা হয়েছে। ডাক্তার সেদিকে তাকালও না। আমার দিকে ঘুরে বলল, শোনেন, মেয়েকে থেরাপি দিতে হবে নিয়মিত। যত দিন ইন্ডিয়া না নিতে পারেন, আমার কাছে আসবেন। এখানে না। চেম্বারে। আমি কার্ড দিচ্ছি, ঠিকানা লেখা আছে। আপনাদের ফ্রি দেখে দেব আমি। তবে আমি উত্তরা বসি। অত দূর আসতে পারবেন নিয়মিত?
মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, পারব।
ঠিক আছে। সামনের সপ্তাহ থেকে আসুন। শুক্রবার বিকেলে।
শোয়েবের কথা
ঢাকার রাস্তায় একলা হাঁটতে ভীষণ ভালো লাগত আমার। ‘লাগত’ বলছি, এর মানে এই নয় যে এখন আর লাগে না। কিন্তু লহরির জন্মের পর থেকে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। এখন আর একা হওয়ার সুযোগই পাই না আমি। আহা একাকিত্ব! আহা নিরুদ্দেশ!
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একা একা খুব হাঁটতাম। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যেত একসময়, তাও ভালো লাগত। ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে কারও কনুইয়ের খোঁচায় ঠোঁট কেটে ফেললেও মনে হতো, অপরিচিত কোনো রমণীর চুম্বন, ভালো লাগত। এমনকি সব খারাপলাগাদেরও ভালো লাগত সে সময়! মনে হতো, সব যাত্রাই কোনো এক প্রশান্তির পানে।
তখন এমনও হয়েছে, ক্যাম্পাসে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, এদিকে আমি ছাতা-টাতা ছাড়া হেঁটে বেড়াচ্ছি। ভার্সিটিতে সবাই জানে, আমার মাথায় সামান্য ছিট আছে। বিয়ের পরে শুনেছি, কান্তাও ভাবত যে আমার মাথায় ছিট আছে। সব জেনেশুনেই সে ভালোবেসেছিল আমায়। নাহ, অতীতকাল ব্যবহার করা যাবে না। এখনো সে আমায় ভীষণ ভালোবাসে। সেই প্রথম জীবনের মতো। বিয়ের দশ বছরেও স্ত্রীর এতটা ভালোবাসা পাওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি সৌভাগ্য মনে হয় নিরুদ্দেশে একা একা হাঁটা। নিষ্ঠুর শোনালেও এটা চিরন্তন সত্যি যে বাসায় যাওয়ার কথা ভাবলেই এখন একধরনের আতঙ্ক বোধ করি আমি।
অথচ বিয়ের পর এই বাসাতে ফেরার জন্যই কেমন চাপা একটা উত্তেজনা অনুভব করতাম। তিন রুমের বড় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতাম আমরা সে সময়। দুই রুমেই হয়ে যেত আমাদের, তবু তিন রুম নিলাম। সেই শৈশব থেকে কান্তার একটা পড়ার ঘরের খুব শখ, আমি জানি। ফলে তার জন্য বাড়তি পড়ার ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটটাই পছন্দ করলাম।
তিন রুমের ভাড়া একটু বেশি হলেও ভালোভাবেই চলে যেত আমাদের। খুব বেশি সঞ্চয় থাকত না, এই যা! কিন্তু সঞ্চয় দিয়ে কী করব? ছেলেমেয়েকে মানুষ করে বলব, এবার চড়ে খা। নিজের খরচ নিজে করবি। আমরা যেমন তোর ভবিষ্যতের জন্য কিছু রাখি নি, তোকেও আমাদের কিছু দিতে হবে না।
আমার বাবা ছিলেন একজন হজমিওয়ালা। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হজমি বিক্রি করতেন। ছোট একটি শিশিতে ভরা থাকত কালো দানাদার হজমি গুঁড়া। আরেকটি শিশিতে তরল কেমিক্যাল। ছোট কাগজের টুকরায় রেখে দেওয়া হজমিতে এক-দুই ফোঁটা কেমিক্যাল ফেললেই আগুন জ্বলে উঠত দপ করে।
আমার স্কুলের সামনেই হজমি বিক্রি করতেন বাবা। আমার ভবিষ্যতের জন্য তিনি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। রাখতে চানও নি। শুধু বর্তমানটি গড়ে দিয়েছিলেন। তাতেই চলে যাচ্ছিল দিব্যি।
এই দিব্যি চলে যাওয়াতেই ছেদ ঘটাল লহরি। যৎসামান্য সঞ্চয় ছিল, শুরুতে ডাক্তারের পেছনে সেটা যেতে লাগল। তারপর ধারদেনা করা শুরু করলাম। কান্তা চাকরি করতে চাইল। বললাম, তোমাকে চাকরি করতে দিতে সামান্যও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু তাহলে আমার চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে।
কান্তা ম্লান স্বরে জানতে চাইল, কেন?
বললাম, লহরির সঙ্গে সঙ্গে একজনকে যে থাকতেই হবে সব সময়। হয় তুমি, নইলে আমি।
শেষমেশ কান্তাই রাজি হলো ঘরে থাকতে। এখন চাকরি শুরু করলে তাকে তুলনামূলক কম বেতনে শুরু করতে হবে। কিন্তু আমাদের তো প্রচুর টাকা দরকার এখন।
আমার চাকরির বয়স বারো। একটা প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে সম্পাদনা সহকারীর কাজ করি। মোটামুটি ভালো বেতন আসে। এর বাইরে ওই পত্রিকায় রোজ যে রাশিফল প্রকাশিত হয়, সেটি আমি লিখি। লেখক হিসেবে অবশ্য ছাপা হয় অন্য নাম। সৈয়দ মইনুস সুলতান। সৈয়দ সাহেবের রাশিফল খুবই জনপ্রিয়। সম্পাদনা সহকারী পদে কাজ করা একজনের ঠিক রাশিফল লেখার ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এর পেছনে অদ্ভুত একটা ঘটনা আছে।
যা-ই হোক, নানাভাবে আয় বাড়াচ্ছিলাম, বিপরীতে ব্যয় কমাতে থাকলাম আমরা। শুরুতে মনে হয়েছিল, এত বড় বাসার ভাড়া টানার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে বাসা সাবলেট দিলাম। সমস্যা যেটা হলো, কেউই এক মাসের বেশি সাবলেট টিকল না। রাতে বাচ্চার তারস্বরে চিৎকার কেউই মেনে নিতে পারে না। পারার কথাও নয়।
তিন রুমের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে দুই রুমের ঘর নিয়েছিলাম একটা। পরে আরও কমে ছাদে এক রুমের একটা ঘর পেয়ে সেখানে উঠলাম। সবই ভালো। শুধু গরমে কষ্ট হয়। ইদানীং ম্যারাথন লোডশেডিং শুরু হয়ে পৃথিবীতেই জাহান্নাম দেখিয়ে দিচ্ছে।
কান্তার কথা
লহরি এখন হামাগুড়ি দিতে শিখে গেছে। খুব এলোমেলো হাস্যকর ভঙ্গিতে সে হামাগুড়ি দেয়। তবু এই যে হামাগুড়ি দেওয়া, এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। ডাক্তারকে এই খবর জানানোর পরই সে বলেছে দ্রুত ভারতে নিয়ে যেতে। তার ধারণা, চিকিৎসা করালে অন্তত চল্লিশ ভাগ ঠিক হয়ে যাবে আমার মেয়ে। সমস্যা হলো, এই চল্লিশ শতাংশ সম্ভাবনার জন্য শোয়েব লহরিকে অত টাকা খরচ করে ভারতে নিয়ে যেতে রাজি না। বহু জোরাজুরি করে তাকে রাজি করিয়েছি।
আমাদের বিয়ের পরপর আমার শাশুড়ি, মানে শোয়েবের মা, একদিন এসেছিলেন বাসায়। এসে লুকিয়ে-চুরিয়ে পুত্রবধূর হাতে একটা পোঁটলা দিয়ে যান। পোঁটলা খুলে দেখতে পাই, গলার হার, চুরি ইত্যাদি কতগুলো গয়না।
আমার দুহাত চেপে ধরে ফিসফিস করে আম্মা বললেন, শোয়েবের বাবাকে তো আমি হাড়ে হাড়ে চিনতাম। জানতাম যে সে ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখবে না। তাই ওর জন্মের পরদিন থেকে আমি তার পকেট থেকে কিছু কিছু করে টাকা সরিয়ে রাখা শুরু করলাম। তোমাদের বিয়ের আগে সব টাকা দিয়ে গয়নাগুলি বানালাম। খাঁটি সোনার। এটা রাখো। ভবিষ্যতে কাজে দেবে। শোয়েবের স্বভাবও ওর বাবার মতোই হয়েছে। তুমি ওকে জানিয়ো না এগুলোর কথা।
ভবিষ্যতে না, সেই সোনা বর্তমানেই কাজে দিচ্ছে। শোয়েবকে পাঠিয়েছি সেগুলোকে বিক্রি করতে। দশ বছর পরই কী দ্রুত আমাদের ভবিষ্যৎ চলে এল!
এখন একটু একটু করে বুঝতেও শিখেছে লহরি। কথা শুনতে পারে না, কানে শোনে না, কিন্তু ইশারা বোঝে। আনন্দ-বেদনা বোঝে। রাগ করলেও বুঝতে পারে। মাথা দুপাশে নাড়লেই বোঝে যে বারণ করছি, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সেই বারণ শুনতে চায় না।
আগে অল্পেই ক্লান্ত হয়ে যেত, এখন দীর্ঘ সময় ধরে হামাগুড়ি দিতে পারে। ছোট রুম, একটুতেই দেয়াল চলে আসে। তাই দেয়ালের চারপাশ ঘিরে চক্কর দিতে থকে সে।
কানে শোনে না জানি, তবু অভ্যাসবশত ডাক দিই আমি (ডাক্তারও বলেছে সব সময় কথা বলতে), লহরি, ওদিকে যায় না। সামনে মাল্টিপ্লাগে ইলেকট্রিসিটি আছে। লহরি।
লহরি তো শোনে না। সে ধীরে ধীরে মাল্টিপ্লাগের দিকে যেতে থাকে। আমি জানি, এখনই এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তবু দিতে পারি না। কে যেন ভেতর থেকে আমায় বলছে, যাক যাক। আর কত কষ্ট করবি?
আমি আবার চিৎকার করি, লহরি, ওদিকে যায় না। ওখানে কারেন্ট আছে। অ্যাই লহরি।
লহরি শোনে না। অতি ধীর ভঙ্গিতে সে এগোতে থাকে। ভেতর থেকে আবারও শুনতে পাই, কে যেন আমাকে বলছে, যাচ্ছে যাক। দিক না মাল্টিপ্লাগে হাত! তুই তাকাস না একদম।
লহরি।
কে বলে মাথার ভেতর থেকে, চুপ কর বোকা মেয়ে! তোর পেটে আরেকটি শিশু আসছে, তার কথা ভাবতে হবে না? তার ভবিষ্যতের ব্যাপার আছে। চোখ বন্ধ করে বসে থাক তুই। আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে তখনই কড়া নড়ে ওঠে, ঠক ঠক ঠক ঠক ঠক।
[গল্পটি অন্যদিন ‘ঈদুল আজহা সংখ্যা ২০২৩’-এ প্রকাশিত]
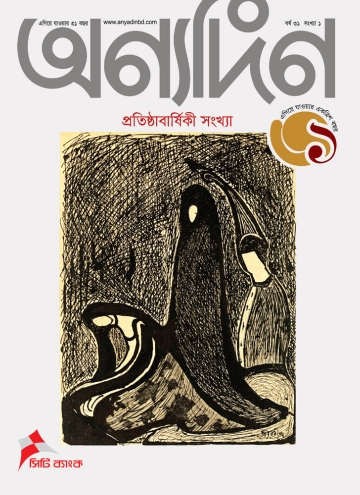





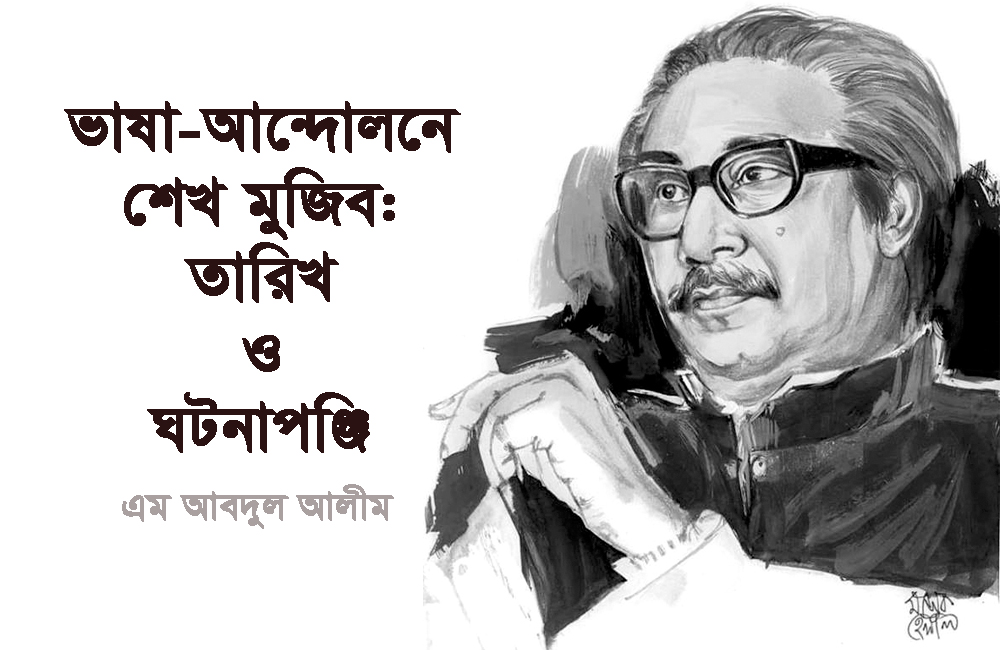


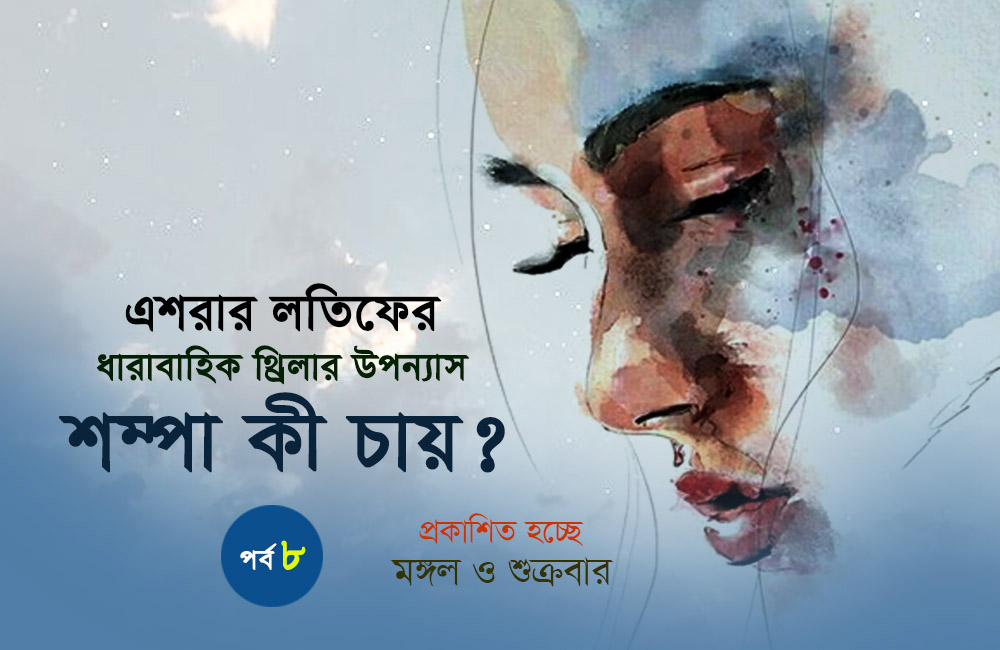





Leave a Reply
Your identity will not be published.