[বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ কাজী নজরুল ইসলাম। ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনন্যসাধারণ। বাংলা কাব্য-জগতে ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে খ্যাত। রবীন্দ্রযুগে যে-সব কবি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের পরেই কাজী নজরুল ইসলামের স্থান। ২৭ আগস্ট (১২ ভাদ্র) ছিল তাঁর ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ হলো।]
নজরুলের বিচিত্র জীবনের মতোই তাঁর সৃষ্টিকর্ম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচকেরা। তাদের অনুসরণ করে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই আর সেটি হলো, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের বৈপরীত্যের সহাবস্থান বা সমন্বয়ের বিষয়টি।
শুরুতে নজরুলের জীবনের প্রসঙ্গ। তাঁর জীবন ছিল দুঃখের। ‘দুখু মিয়া’ নামটি সত্যিই সার্থক। হাড়ভাঙা খাটুনি, সমালোচকদের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য, কুৎসা রটনায় ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি। আর ১৯৪২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত নির্বাক ও সংবিতহারা অবস্থায় কাটে তাঁর। সব জ্বালা-যন্ত্রণায় অবসান ঘটে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১২ ভাদ্র ১৩৮৩)। চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন তিনি। অথচ আমরা লক্ষ করি, হাসির রাজা ছিলেন নজরুল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন যখন-তখন। বলা যায়, অনেক সময় হাসির আড়ালে লুকাতে চাইতেন দুঃখকে। দুঃখ-বেদনার পাশাপাশি হাসির সহাবস্থান—বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য সমন্বয়। আর কী আশ্চর্য, দুঃখময় জীবনেই তাঁর সৃষ্টির উৎসধারা বেগবান হতো। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। নজরুলের প্রথম সন্তান, বুলবুল, যখন মারা যায় তখন ‘চন্দ্রবিন্দু’র মতো হাসির কাব্য রচনা করেন তিনি। দেখা গেছে একদিকে তিনি কাঁদছেন, অন্যদিকে তাঁর কলম ছুটে চলেছে কাগজের বুকে। ‘চন্দ্রবিন্দু’ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। ‘থাকতে চরণ মরণে কি ভয়/নিমেষে যোজন ফরসা।/মরণ-হরণ নিখিল-শরণ/জয় শ্রীচরণ ভরসা’। অথবা ‘দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,/রাজা আংরেজ হারামখোর/ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশি,/হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর’। অথবা ‘যদি শালের বন হ’ত শালার বোন/ আর কনে বৌ হ’ত ঐ গৃহের কোণ।/ছেড়ে যেতাম না গো,/আমি থাকিতাম পড়ে শুধু, খেতাম না গো’।
দুঃখ যেমন ছিল নজরুলের জীবনের সঙ্গী, তেমনি দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের উদ্দেশে যদিও তিনি বলেছেন—‘হে দারিদ্য, তুমি মোরে করেছে মহান/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান’, কিন্তু দারিদ্র্যের অনলে তিনি জ্বলেছেন চিরকাল। পাশাপাশি আবার এটাও লক্ষ করা গেছে যে, যখনই তিনি একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন তখনই অপরিণামদর্শিতা ভর করেছে তাঁকে। জলের মতো তখন অর্থ ব্যয় করেছেন। এটাও নজরুল-চরিত্রের আশ্চর্য একটি দিক। বৈপরীত্যের একটি উদাহরণ।
আমরা জানি, ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নজরুলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। ‘সাম্যবাদী’ ও ‘সর্বহারা’ কবিতাগুচ্ছ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুবাদ ‘জাগ অনশন বন্দি ওঠরে যত’ এবং ‘রেড ফ্লাগ’ অবলম্বনে রক্ত পতাকার গান এর প্রমাণ। অথচ সেই তিনিই, কী আশ্চর্য, লিখেছেন চরকার গান: ‘ঘোর—/ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর/ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর...।’ ‘সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন বনাম গান্ধীর অহিংস পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতায় নজরুল লিখেছেন: ‘এটা অহিংস বিপ্লবী ভাবে,/‘নয় চরকার গান গাবে?’ হ্যাঁ এমনি বৈপরীত্য ছিল নজরুলের জীবনে কিংবা অন্য কথায়, বৈপরীত্যের মাঝে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। যেমন, সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা লেখা, অন্যদিকে চরকার গান রচনা, ‘শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল’ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন, ১৯২৬ সালে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্যপদ লাভের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা— সবকিছুরই লক্ষ্য ছিল স্বরাজ অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি কোনো কিছু করেন নি।
১৯২৪ সালে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রমীলাকে বিয়ে করেন নজরুল। এটিও তাঁর জীবনে বৈপরীত্যের সমন্বয় বা মিলন।
এবার নজরুলের সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করা যাক। দেখা যাক বৈপরীত্যের সহাবস্থান বা সমন্বয়। সুবিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার নানা পঙ্ক্তি বৈপরীত্যের বিষয়টি বহন করছে নানাভাবে। যেমন, ‘আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান’, ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ-তুর্য, ‘আমি উত্থান, আমি পতন’, ‘কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-বন্যা’, ‘আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়’ ইত্যাদি।
‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ কবিতায় লক্ষ করি ‘আস্ল হাসি, আস্ল কাঁদন/মুক্তি এলো, আস্ল বাঁধন’, ‘আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,/মদন মারে খুন মাখা তুন—পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল’, ‘আজ জাগল সাগর, হাসল/ মরু’, ‘মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরার-মরা বাম পাশে।’
নারী সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় ‘পূজারিণী’ কবিতায়: ‘এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি।/ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমপর্ণ/ পূজা হেরি ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য ভীতি?/নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,/তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,/যাচে বহুজন’। অবশ্য নারী সম্পর্কে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে রয়েছে একটি কারণ আর তা হচ্ছে, ‘পূজারিণী’তে নজরুলের রোমান্টিক প্রেম-চেতনার বহুমাত্রিক স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।
অন্যদিকে ‘নারী’ কবিতায় রয়েছে নারীর যথার্থ মূল্যায়ন: ‘সাম্যের গান গাই—/আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।/বিশ্বে যা কিছু মহান চির কল্যাণকর,/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর/বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্র“বারি/, অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।’
নজরুলের গানে কী দেখি আমরা? আমরা দেখতে পাই যে, মানব মনের বৈপরীত্য এবং টানাপোড়েনের ব্যাপারটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রেমের গানে।
আমরা জানি যে, পুরুষের মন কখনোই পরাজয়কে মেনে নেয় না। যে নারী আমাকে আঘাত দিল, আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করল— সেই নারীকে সহজে আমি ভুলতে পারি না। শুধু তাই না, আমি চাই সেও যেন আমাকে ভুলে না যায়। কোনো এক অলস দুপুরে সেই নারীর স্মৃতিপটে আমার ছায়া যেন ধরা পড়ে। আমার স্মৃতি রোমন্থনে সেই নারী হৃদয় যেন কখনো বেদনায় টনটন করে ওঠে, কখনো আনন্দে আপ্লুত হয়। নজরুলের কবি মন এই মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকে নি। তাঁর গানেই আমরা প্রমাণ পাই। তিনি লিখেছেন, ‘আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।’
আবার যে নারী শুধু আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যানই করে নি, আমার ভালোবাসাকে অপমান করে হৃদয়ের নিভৃতে প্রদেশে এক দগদগে ঘা’য়ের সৃষ্টি করেছে—সেই নারীকে আমি ভুলতে চাই। সে নারী যদি পরবর্তী সময়ে আমার কাছে প্রেম পূজারিণীর বেশেও আবির্ভূত হয়, তবু ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগে না। এক্ষেত্রে সেই নারীকে আমিই শুধু ভুলতে প্রয়াসী হই না, আমি চাই সেই নারীও যেন আমাকে ভুলে যায়। নজরুল তাই নার্গিসের উদ্দেশে বলেছেন—‘যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, কেন মনে রাখো তারে/ভুলে যাও, মোরে ভুলে যাও একেবারে’।
আগের গানের সঙ্গে তুলনীয় আরেকটি গান উল্লেখযোগ্য: ‘যারে আঘাত দিয়ে ফেরায়েছ তুমি কেন ডাক তারে বারে বারে/যে ফুল হেলায় দলিয়াছ পায়, আজো রেখেছ অনাদরে, কেন পেতে চাওয়া তারে’।
আবার যে নাকি সর্বস্ব দিয়ে দয়িতকে ভালোবাসে—একেবারে নিবেদিত প্রাণ; যে নাকি নিজের ভেতরে নিজে নেই—প্রিয়জনই সর্বস্ব; শত আঘাতেও যে নাকি অবিচল, যে নাকি আঘাতকেই তার বলে মনে করে—প্রেমিকের কাছে যার পরিপূর্ণ সমর্পণ; —সে কিন্তু এই নির্দয় আঘাত, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য উপেক্ষা করে প্রিয়জনের পূজায় মগ্ন থাকে, পাষাণ গলিয়ে ভালোবাসার অঝোরধারা সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন থাকে। ভালোবাসার এই মনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে নজরুলের গানে— ‘যে পাষাণ হানি বারে বারে তুমি আঘাত করেছ স্বামী/সে পাষাণ দিয়ে তোমার পূজায় এ মিনতি রাখি আমি।’
প্রেমের জগতে দেখা যায়, যে নাকি আমাকে আঘাত দিয়ে আমার প্রেমকে একদা অপমান করেছিল তার প্রতি আমার তাচ্ছিল্য ঘৃণা। সে যদি কৃপা করে আমাকে আবার কাছে টানতে চায়, ভালোবাসতে চায়, তবু সেই করুণা ধারায় আমি ভেসে যেতে পারি না। প্রেম ধর্মের এই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের এই গানে— ‘ছেড়ে দাও মোরে আর হাত ধরিও না/প্রেম যারে দিতে পারিলে না—তারে আর কৃপা করিও না।’
আবার যে মানুষ আমার ভালোবাসাকে সম্মান করেছে, আমাকে একান্ত আপন করে নিয়েছে— যার মনের মাঝে আমি পেয়েছি ঠাঁই এবং যে হয়েছে করতলগত— তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম টান। তার বিরহে আমার দিন রজনী কাটতে চায় না। একটি মুহূর্তকে মনে হয় একটি যুগ। তাই মিলন ক্ষণে আমার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে, অনাগত বিরহের শঙ্কা জেগে ওঠে মনে। ভালোবাসার এই সুন্দর প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই গানে—‘ছাড়িয়া যেও না আর/বিরহের তরী মিলনের ঘাটে লাগিল যদি আবার’। এই গানের সঙ্গে তুলনীয় আরেকটি গান: ‘এসো প্রিয় আরো কাছে/পাইতে হৃদয়ে যে বিরহী মন যাচে।’
আবার বিরহ আমার ভালো লাগে। প্রিয়াকে আমি তাই কাছে টানতে চাই না। কেননা আমি জানি যে, ভালোবাসার পাখিকে সব সময় দূরের অজানা জঙ্গলের, অনামা গাছের অদৃশ্য ডালে বসেই ডাকতে দিতে হয়। সব পাখিকেই দেখতে নেই। আমি এটাও জানি যে, ভালোবাসার পাখি বনে অদেখা থাকলে, দূরে থাকলেই ভালোবাসা বেঁচে থাকে। আলোয় তাকে টেনে আনলে, বড় কাছ থেকে দেখতে গেলে সেই নরম অভিমানের পরম পাখি আর বাঁচে না। ভালোবাসার এই মনস্তত্ত্বের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে এই গানে—‘কাছে আমার নাইবা এলে/হে বিরহী দূর ভালো/নাই কহিলে কথা তুমি/বলো গানের সুর ভালো।’
আবার একদিকে নজরুল লিখেছেন ইসলামি গান অন্যদিকে শ্যামাসংগীত, এটাও কি বিপরীত্যের আশ্চর্য সহাবস্থান নয়? ‘ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’, ‘বক্ষে আমার কাবার ছবি, চক্ষে মোহাম্মদ রসুল’, ‘দিকে দিকে পুণঃ জ্বলিয়া উঠেছে/, দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল’, ‘মোহররমের চাঁদ এল ওই কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়,/ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়’—এইসব ইসলামি গানের পাশাপাশি যখন আমরা শুনি নজরুলের শ্যামাসংগীত ‘বল রে জবা বল/ কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল’, ‘মহাকালীর কোলে এসে/গৌরী হলো মহাকালী।/শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে/ম্লান হলো মার রূপের ডালি’, ‘মোরে আঘাত যত হানবি শ্যাম/ডাকব তত তোরে’, ‘কে বলে মোর মাকে কালো/মা যে আমার জ্যোতির্ময়ী’—তখন কী বিষয়ে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি না? কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা নজরুল জানতেন কী করছেন, কী লিখছেন তিনি। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ কাছে লেখা নজরুলের একটি পত্রের কিছু অংশ উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।
‘বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দু ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রিক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানেরা রাগ করা যেমন অন্যায় তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।’
‘পদ্মাগোখরা’ গল্পে বিষধর সাপের মাঝে আশ্চর্য মানবিকতা এবং মানুষের মাঝে বিষাক্ত কুটিলতা আর হিংস্রতা মূর্ত করে তুলেছেন নজরুল। অন্যদিকে ‘অগ্নিগিরি’ গল্পের নায়ক সবুর হচ্ছে গল্পকারের ভাষায়, ‘নামেও সবুর কাজেও সবুর, শান্তশিষ্ট গো-বেচারা মানুষটি।’ কিন্তু এই শান্তশিষ্ট গো-বেচারাটির ভেতর যে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিগিরি অবস্থান করছিল গল্পের শেষে তা ফুটে ওঠে।
এমনিভাবে গদ্যে-পদ্যে গানে, নজরুলের নানা লেখায় লক্ষ করা যায় বৈপরীত্যের আশ্চর্য সহাবস্থান বা সমন্বয়— যার সামান্যই উল্লেখ করা গেল এ রচনায়।
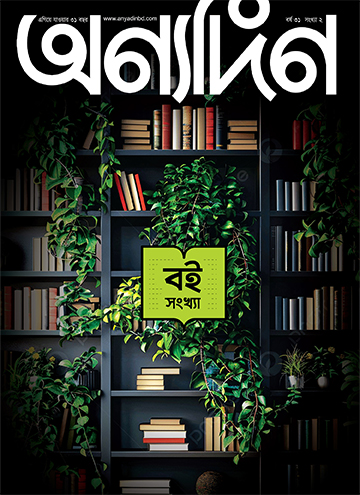





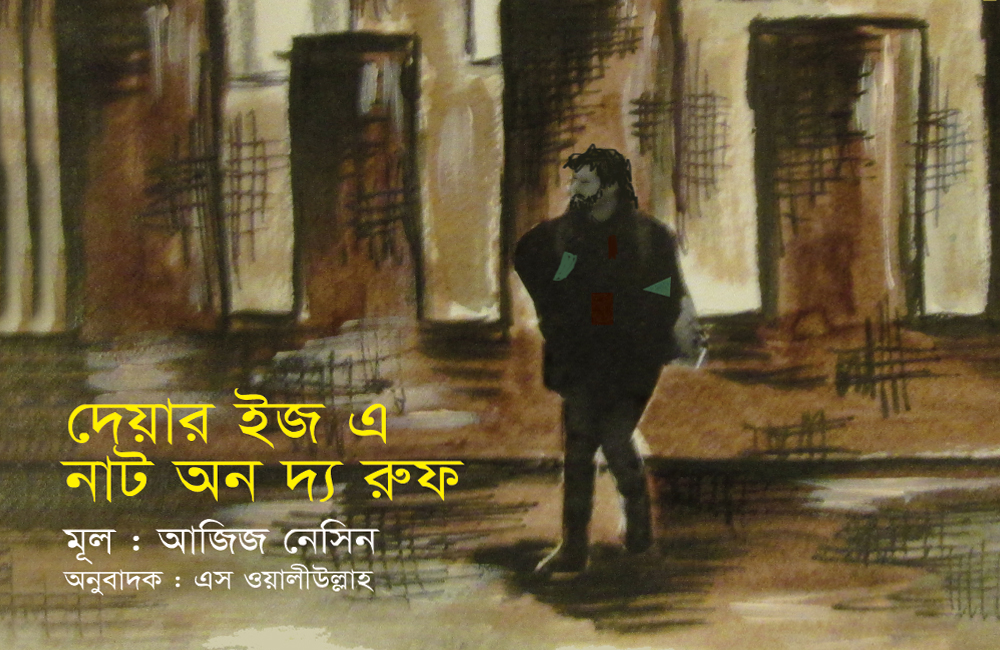

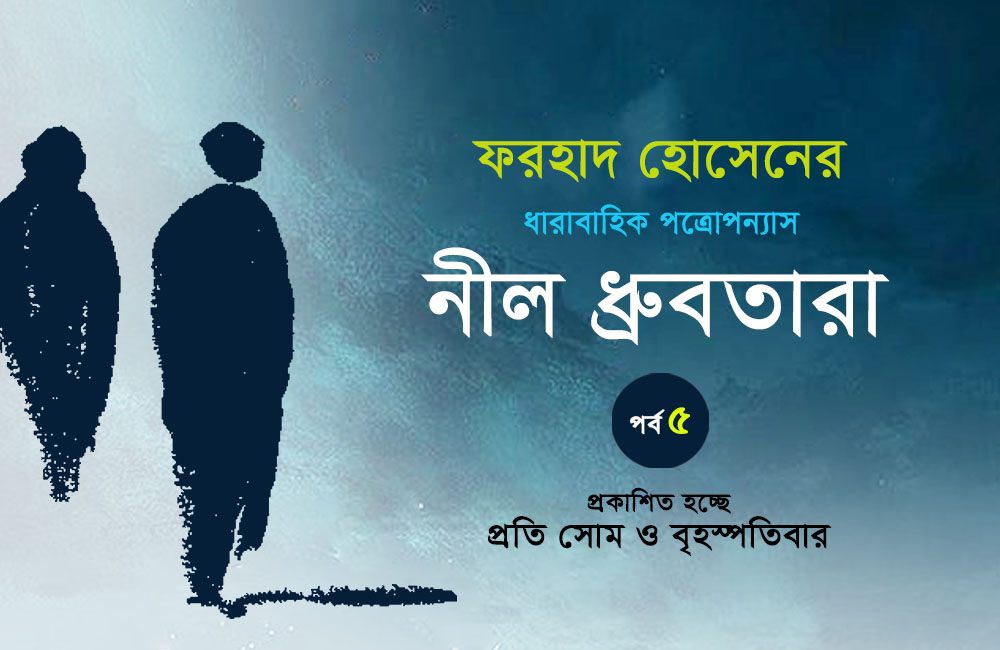






Leave a Reply
Your identity will not be published.