Ralph Waldo Emerson বলেছিলেন, "All life is an experiment. The more experiments you make the better”.
তিনি যখন এই বাণী দেন তখন আমার জন্মই হয় নি। ‘Experiment’’ বিষয়ক আমার এক্সপেরিয়েন্স শুনলে তিনি কথাগুলো হয়তো অন্যভাবে লিখতেন। এক্সপেরিয়েন্স মানুষকে ঋদ্ধ করে ঠিকই কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স লাভ করতে গিয়ে করা এক্সপেরিমেন্ট অনেককে বিদ্ধও করে। জন্মগতভাবেই মানুষ কৌতূহলী। তারা নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা করতে পছন্দ করে। কোনো লোক নতুন কিছু শিখলে বা জানলে সবার আগে পরিবারের সদস্যের উপরেই এক্সপেরিমেন্ট করে থাকে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।
১
টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে মেহেরজানের তখন রমরমা অবস্থা। মেয়েদের হেয়ার কাটিং আর বিউটি লুক দিয়ে তিনি ভালো নাম কামিয়েছেন। বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনেও তাকে দেখা যায়। সেইসব বিজ্ঞাপন বা প্রোগ্রামের নিয়মিত দর্শক হলেন মিমি আপু। প্রোগ্রাম দেখে দেখেই তার এরকম ধারণা জন্মেছে যে চুল কাটা কোনো ব্যাপারই না! চার আঙুলের চিপায় ধরে ঘ্যাচাং করে কাঁচির পোঁচ দিলেই হলো। এ এমন জাদুর কী ? আমাদের তথা এই উপমহাদেশের নাগরিকদের মাঝে এই প্রবণতাটাই প্রবলভাবে দেখা যায় যে তারা মলাট পড়েই বইয়ের সবটুকুই পড়ে ফেলেছেন এরকম ভাব দেখায়। মিমি আপুও এর বাইরে নয়। মেহেরজান হওয়ার প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় তিনি নিজ বাড়িতেই উতরাতে চান।
পরের দিন সকাল থেকেই হাত তার নিশপিশ করে। শুধু মেয়েদের চুলভর্তি মাথার দিকেই তার নজর। বাজারে বা রেলস্টেশনে বের হলেই খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই যে চটের ওপর বসে থাকা মুচি কোনো লোকের দিকে তাকায় না! তাদের চোখ প্রতিটি মানুষের পায়ের দিকে। চামড়ার জুতা বা স্যান্ডেল পরা কাউকে পেলেই হামলে পড়ে। মিমি আপু বাড়ির সব নারীদের চুলে হাত দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু কেউ রাজি হয় না। শেষে কাজের মেয়ে ছন্দার উপরেই প্রথম পরীক্ষা হয়ে গেল। রান্নাঘরের চিপায় বসে চিরুনি আর কাপড় কাটা কাঁচি দিয়েই কাজ সারেন তিনি। চুল কাটার পর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে নয় বছরের ছন্দা আসলে ছেলে না মেয়ে। এক সপ্তাহ পরেই ছন্দার মা তার বর যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছে বাহানা দিয়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ নাপিত বাড়িতে আর নয়!
মিমি আপার জিদ আরও চেপে যায়। বাইরের কাউকে না পেয়ে সে এবার ছোট বোন সিমিকেই রাজি করায় শনপাপড়ি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে।
শোন সিমি, কাল থেকেই তো তোর এক মাস স্কুল ছুটি। চল, তোকে সুন্দর একটা হেয়ার কাট দিই। আর তা ছাড়া তোর জন্য আমি শনপাপড়ি কিনে রেখেছি।
ঠোংগা খুলে শনপাপড়ি মেলে ধরে তার সামনে।
সিমি লোভ সামলাতে পারে না। জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে নেয়।
আচ্ছা দিদি, ঠিক আছে। তবে না লাগে যেন!
ধুর পাগলি, আমি তোর মায়ের পেটের বোন। তোর গায়ে ব্যথা লাগলে আমার বুকে ব্যথা হয় রে!
সিমি শনপাপড়ি খাচ্ছে। আর এদিকে মিমি আপু প্রাণভরে চুল কেটে যাচ্ছে। আজ তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নাই। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কাঁচি আর ছুরির চিরুনি অভিযান শেষ হলো। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে মিমি আপু বলেন, ‘যাহ, গোসল করে আয়। দেখবি আজ সবাই তোর দিকেই তাকিয়ে থাকবে।’
গোসলের পর যখন সিমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক তখনই চারদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। মাথায় জায়গায় যায়গায় চুল একেবারেই নাই, যেন কাঠঠোকরা তুলে নিয়ে গেছে। সেই দুঃখে সিমি দুইবেলা ভাত খায় নি। পরের দিন সেলুনে গিয়ে তাকে ন্যাড়া করিয়ে এনে তবে শান্তি। মিমি আপু সেদিন বুঝেছিল, শুধু টিভি দেখেই মেহেরজান হওয়া যায় না। এরজন্য লাগে যথাযথ ট্রেনিং আর পরিশ্রম।
২
দিপা ভাবি ভালোই রান্না করেন। অনেক বছরের সংসারে রান্না করতে করতে হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। তবে এই যাত্রায় তাকে যোগ্য সহায়তা দিয়েছেন মেজ ভাই আব্দুল জব্বার। ভাবি নতুন নতুন রেসিপি শিখেন আর রান্না বসান। আর এই রান্নার স্বাদ প্রথমবার অবধারিতভাবেই ভাইকে নিতে হয়। বিবিখানা, মমো, বাকরখানি, মাটন কষা, গাজরের হালুয়া, আরও কত যে বাহারি খাবারের এক্সপেরিমেন্ট হাউস হয়েছে ভাইয়ের পেট তার ইয়ত্তা নাই।
ভাবির স্টাইলটাও ইউনিক। তিনি নতুন খাবার বানাবেন অবশ্যই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। যেন অফিসের তাড়া ছিল এই অজুহাতে ভাই মানে শিকার পালাতে না পারে। জুম্মা পড়ে এসে বেচারির ভীষণ ক্ষুধা লাগলেও ঢাকনা তুলে করল্লা ভাজির একদলা মুখে দেওয়ার জো নাই। নতুন রান্না শেষ হলে তবে খাওয়া। ভাবি আয়েশ করে সবাইকে নিয়ে বসবেন।
কমলের আব্বু, এটার নাম বিবিখানা। খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে।
পাতে বিবিখানা তুলে দিয়ে তীক্ষè দৃষ্টি রাখেন ভাবি।
ভাই আমার সাগ্রহে প্রথমবার মুখে দিয়ে নীরব হয়ে যান। জিহ্বা নড়তে চায় না। মুখের মধ্যে বিবিখানা হাঁসফাঁস করতে থাকে।
সামনে বসে ভাবি মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝার চেষ্টা করেন।
ডান হাতের তর্জনী উপর-নিচ করে জানতে চান ভাবি। এটাই ভাবির স্টাইল।
বলো, কেমন হয়েছে বলো!
এই জানতে চাওয়ার টোনের মধ্যে পজিটিভ উত্তর পাওয়ার তাগিদের সাথে নিজের সৃষ্টির জন্ম ইতিহাস রচনার দ্যোতনা ছিল বেশি।
আমার মতোই দুনিয়ার তাবৎ গিনিপিগের একই উত্তর আবার উগরে দেন মেজ ভাই।
ভালো হয়েছে দিপা, খুব ভালো হয়েছে।
কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন তাহলে ?
আরে না, তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। তাই বিষম লেগেছে আর কী!
ইস, আজ আম্মা এখানে থাকলে কী খুশিই না হতেন বিবিখানা খেয়ে! আফসোস করেন রাঁধুনি। পাশ থেকে মেয়ে কলি খিক করে হেসে দেয়।
আম্মু, দাদির দইবড়া খাওয়ার কথা ভুলে গেলে ?
‘চুপ থাক! তোর খাল খিঁচে দেব এবার!’ মেয়ের ওপর এবার গর্জে উঠেন মা। ফ্লাসব্যাকে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই মজার ঘটনা।
সেদিনও এইরকম এক ছুটির বিকেল। মা অনেকদিন পর গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছেন মেজ ছেলের বাসায়। আসার পরের দিন থেকেই বাড়ি ফেরার তাগাদা। বাড়িতে তেমন কিছুই নেই, তারপরও তার মন টেকে না এই শহরে। দিপা ভাবি শাশুড়ির যত্ন-আত্তি কম করেন না। প্রতিদিনই আম্মাকে নতুন নতুন খাবার রেঁধে খাওয়াতেন। তো সেদিন নতুন খাবার দইবড়া বানানো হবে। সকাল থেকেই বাসায় হুলুস্থূল কাণ্ড। আমি রজনীগন্ধা মার্কেট থেকে টকদই থেকে শুরু করে সকল সদাই নিয়ে এসেছি। বিকালে দইবড়া প্রস্তুত। ডাইনিং টেবিলে আমরা গোল হয়ে বসেছি। সবার বাটিতে নতুন অতিথি দইবড়া হেলে বেড়াচ্ছে। ভাবির চোখ তার শাশুড়ির দিকে। পিন পতন নীরবতা।
‘মা মুরব্বি হিসেবে আগে খাবেন এবং রিভিউ দিবেন। কথা শেষ।’ ফাইনাল ভারডিক্ট দিয়ে দেন ভাবি।
কেন যেন মাকে উশখুশ করতে দেখছি। আসলে খাবারের চেহারা দেখেই মায়ের মন গলে নি। কালো রঙের এক গোল্লার ওপর দইয়ের আস্তরণ! তব্ওু মা মুখে দিলেন এবং চোখমুখ সিঁটিয়ে বসে রইলেন। আমাদের সবার চোখ এখন মায়ের মুখের দিকে। যেন থার্ড আম্পায়ার এখনই রান আউটের সিদ্ধান্ত জানাবেন। অবশেষে সেই সিদ্ধান্ত এল।
এমনিতেই মা তার সব বউকে ‘তুই’ করে বলেন। কিন্তু কোনো কারণে বিরাগভাজন হলে ‘তুমি’তে উঠে আসে। আজকেও মা সেই ‘তুমি’তেই উঠলেন। দইবড়া খেয়ে মায়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।
দেখো মা দিপা, আমি আর খাব না। আমার ভেতরে আর ঢুকছে না। আর আরেকটা অনুরোধ, আমার ছেলেদের বা তোমার বাচ্চাদের আজ আর কষ্ট দিয়ো না! কিন্তু তুমি যে খুব ভালো রান্না করো এটা আমি পল্টন ময়দানে গিয়ে মাইকেও বলে আসতে পারি।
সেদিনের পর থেকে আমাদের সামনে আর দইবড়া আসে নি। তবে দিপা ভাবি রান্নায় আরও সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। তাকে আমরা আদর করে সিদ্দিকা কবির'স রেসিপি নামেই ডাকি।
৩
নিজের এক্সপেরিমেন্টের কথা একটু মেপে বলাই ভালো। কাজেই শুরুতেই মারিয়া হিমোভিচের মানুষের আচরণ নিয়ে করা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে চাই। তিনি ১৯৭৪ সালে ‘রিদম জিরো’ নামের এক এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, যার মূল থিম ছিল মানুষকে কত দূরতক বিশ্বাস করা যায় তা দেখা। এই সার্বিয়ান তরুণী প্রায় ছয় ঘণ্টার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন জনগণের হাতে। তিনি এক ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাছেই রেখেছিলেন পাখির পালক, ফুল, রুটি, ছুরি, পিস্তলসহ প্রায় ৭২টি আইটেম। মানুষকে অভয় দেওয়া হয়, তারা এই উপাদান নিয়ে মারিয়ার ওপর যে-কোনো আচরণ করতে পারেন। সেখানে একটা নাদাবি নামাও লিখে তিনি সহি করে রেখেছিলেন। প্রথম প্রথম এসে মানুষ কেউ চুল আঁচড়িয়ে দেয়, কেউ গোলাপ ফুল দেয় বা মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে ভালোবেসে। কিন্তু শেষের দিকে লোকজন ভয়ংকর আর হিংস্র হয়ে ওঠে। কেউ তাকে চড় মারে তো কেউ জামা কাপড় খুলে নগ্ন করে দেয়। একজন তো সামনে রাখা পিস্তল দিয়ে গুলি করতেও চেষ্টা করে। মারিয়ার সেদিন দারুণ শিক্ষা হয়েছিল মানুষকে নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে।
এবার নিজের কথায় ফেরা যাক।
পোষা ছাই রঙের মুরগিটা কোনো অজ্ঞাত রোগে গতরাতেই গত হয়েছে। মায়ের মন খুবই খারাপ। আজ তিনি চুলার পাশে যাবেন না। মরা মুরগি নিয়েই তিনি বসে আছেন আর বিলাপ করছেন। স্কুল থেকে এসে এই অবস্থায় মাকে ভাত দেওয়ার কথা বলার সাহস হলো না। কিন্তু তিনি বাচ্চাদের ক্ষুধা ঠিকই টের পেয়েছেন। মেজ আপা, সেজ আপাদের ছুটি হতে হতে বেলা গড়িয়ে যাবে। বাড়িতে ভাত রান্নার আর কোনো অপশন হাতে নাই।
‘একদিন চারটে ভাত ফুটিয়ে খেতে পারিস না তোরা!’ কান্নাভরা কণ্ঠে মা আমাকে নির্দেশ করেন।
নিজে কখনো চুলাই ধরাই নি। তার উপর রান্নার ভার! কিছুটা ভীত হলেও নব সৃষ্টির অপার সুযোগ পেয়ে মনে মনে বিগলিত হই। আজকের আইটেম হবে সাদা ভাত আর ডিমভাজি। অনেক যুদ্ধ করে চুলা ধরিয়ে কোনোমতে ভাত সেদ্ধ করে পানি গড়িয়ে নিয়েছি। ডিমভাজি আর এমনকি!
পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ মাখিয়ে নিয়ে বসে আছি। কিন্তু তেল খুঁজে পাই না।
মা, তেল কোথায় ? চিৎকার করে রান্নাঘর থেকেই জানতে চাই।
খুঁজে দেখ, লাল শিশিতেই সরিষার তেল আছে!
প্রায় ৭/৮টা একই সাইজের লাল রঙা শিশির মাঝে কোনটা সরিষার তেলের তা বুঝতে যে কারোরই কষ্ট হবে।
ধুর ডিমভাজিতে সয়াবিন কী আর সরিষা কী! একটা দিলেই হয়।
তাই সামনে থাকা ছোট লাল শিশি থেকে ঢেলে দিলাম তেল গরম কড়াইতে।
আজকের ডিমভাজার ঘ্রাণ অন্যদিনের চাইতে একটু আলাদা মনে হচ্ছে না ? নিজের অবুঝ মন প্রশ্ন করে।
আরে নাহ, ডিমভাজির তলা একটু ধরে গেছিল বলেই এরকম। নিজেকে প্রবোধ দিই আমি।
বেলা পড়লে মেজ আপা আর সেজ আপা বাড়িতে ফিরে। বইপত্র রেখেই তারা খাবারের জন্য পাগল হয়ে যায়। আমার কাছে সকালের সমস্ত ঘটনা শুনে আর আমি রান্না করেছি জেনে যারপরনাই অবাক হয়।
ইতিমধ্যেই মা বিছানা নিয়েছেন। কন্যা শোকে যেন পাথর! আহারে ছাই রঙা মুরগি!
মা আগেই বলে দিয়েছিলেন, ‘ছাইমনের ডিম আমার পেটে ঢুকবে না। আমাকে তোরা কেউ ডাকবি না। তোরাই খা।’
অগত্যা তিন ভাইবোন গোল হয়ে বসেছি।
প্রথমবার ডিমভাজি মুখে দিয়েই মেজ তাকায় সেজর দিকে।
কিছু টের পাচ্ছিস নিরু ?
কেমন যেন তিতা তিতা লাগছে সুফি আপা।
তব্ওু ক্ষুধার তাড়নায় তারা পুরো ডিমসহ প্লেট শেষ করে উঠেন।
‘এবার বলতো লঠাই, কোন তেল দিয়ে ডিম ভেজেছিস!’ মেজ আপার সন্দেহভরা প্রশ্ন।
আমি ত্বরিত রান্নাঘর থেকে লাল শিশি এনে দেখাই।
হায় হায়, করেছিস কী ? এটা তো নিমের তেল! ছাগলের গায়ের উকুন মারার জন্য মা কিনে রেখেছে!
তারপরই দুই বোনে ওয়াক, ওয়াক, বমি শুরু হয়ে যায়।
প্রবল বমি। বিকেল নাগাদ আট-দশবার বমি করে দুইবোন কাহিল হয়ে বসে আছে আমাকে মারার জন্য।
রাত হতে হতেই তাদের পাতলা পায়খানা শুরু হলে আমি ভড়কে যাই। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, পাতলা পায়খানা হলে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হয়। স্কুলে গত মাসেই তো স্বাস্থ্যকর্মীরা শিখিয়ে গেলেন। আমিও নেমে পড়লাম। কিল থেকে বাঁচতে তো হবে নাকি!
আধা সের খাবার পানিতে একমুঠ গুড় আর এক চিমটি লবণ মিশিয়ে আধা ঘণ্টা পর পর দুইবোনের সামনে হাজির হই খাবার স্যালাইন নিয়ে। রাত বারোটা নাগাদ তাদের বাথরুম প্যারেড কমে এল। পরের দিন সকালে দুজন পুরোপুরি সুস্থ হলেও বেচারিদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। এক রাতের ধকলেই তারা যেন রোগী হয়ে গেছেন। আবার বমি বা পায়খানা হয় এই ভয়ে তারা খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। তিন দিন পরে তারা লক্ষ করলেন, স্যালাইন খাওয়ার কারণে তাদের বাথরুম যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আজ একটু একটু পেটও ব্যথা করছে। এর দায়ভারও আমাকেই নিতে হয়েছিল।
Henry Ford এর মতে, "Failure is only the opportunity to begin again, this time more intelligently." অত মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না বাপু! এই ফাঁদে আমি আর পা দিচ্ছি না। কাজেই নো ওমলেট, পনা গুবলেট তত্ত্বেই আছি আমি।
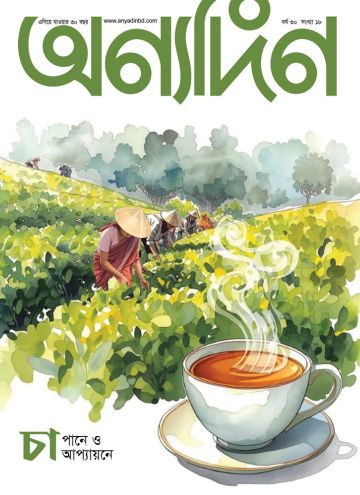





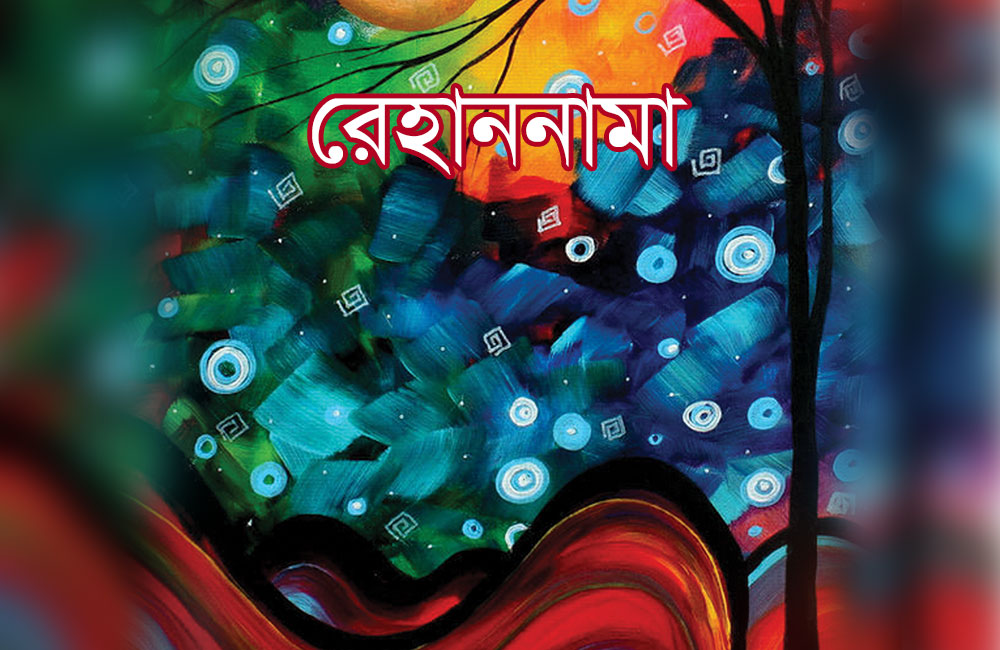
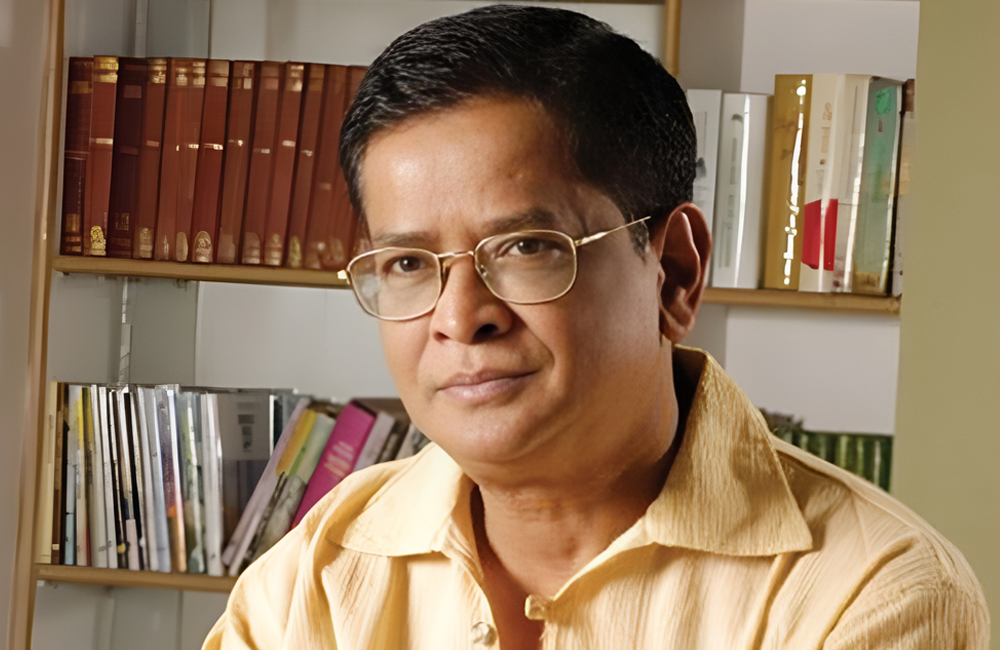



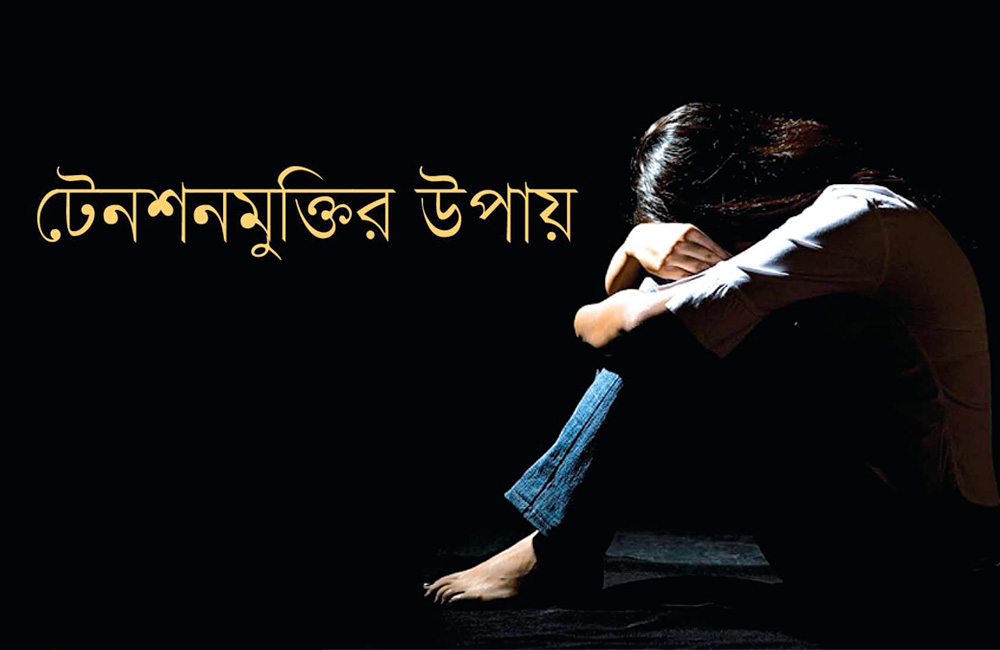



Leave a Reply
Your identity will not be published.