এখন যান্ত্রিক যুগ। প্রগতি ও আধুনিকতার যুগ। কর্মব্যস্ত মানুষের ব্যস্ততা যেমন বেড়েছে তেমনি যে-কোনো কাজ স্বল্প সময়ে স্বল্প শ্রমে দ্রুত সম্পন্ন করতে পারলেই মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ অতীতের ঐতিহ্যবাহী অনেক অনেক জিনিসপত্রের ব্যবহার বা কর্মকাণ্ড যা তাদের জীবনাচারের সাথে ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা পরিত্যাগ করেছে কিংবা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। বরং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং সময় বাঁচাতে অতীতের অনেক কিছুই পরিত্যাগ করতে হয় এবং নিত্য নতুন অনেক কিছু সেই জায়গা পূরণ করে নেওয়ায় অতীত হয়ে যায় ইতিহাসের অংশ। কিন্তু আমাদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের সেই হারানো ঐতিহ্যকে জানা এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও জানানো একান্ত প্রয়োজন। অতীতকে জেনেই ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে সুফল লাভ করা সহজ হয়ে যায়। আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি যাতে ভুলে না যাই সচেতন মহলের সেদিকে নজর দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। চিরায়ত বাংলার হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিহাস ঐতিহ্যেরই একটি অংশ হচ্ছে আমাদের অতীতের বহুল ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় সমাজ সংস্কৃতির অংশ ঢেঁকি ।
আগেকার যুগে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই ধান বানার জন্য ঢেঁকি থাকত এবং গাইল ছিয়াতো থাকতই। বর্তমানে নিতান্ত অজো পাড়াগাঁয়ের কোথাও কোথাও হয়তো ঢেঁকি থাকতেও পারে এবং গাইল ছিয়া এখনো প্রায় ঘরে থাকলেও এসবের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ঢেঁকিছাটা চালের কদর এখনো কমে নি কারণ এ চালের ভাতের মজাই আলাদা। ঢেঁকিছাটা চালের উপরের আবরণ বা খোসা অক্ষুণ্ন থাকে যাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে। যা ভাতের পুষ্টিগুণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই ঢাকা ও বিভিন্ন শহরের অভিজাত দোকানগুলোতে এখনো ঢেঁকিছাটা চাল পাওয়া যায় এবং এর দামও অন্যান্য চালের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি।
ঢেঁকি শিল্প গ্রামীণ ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ ছিল। একসময় গ্রামগঞ্জসহ সর্বত্র ধান ভানা চাল তৈরি, গুড়ি কোটা, চিড়া তৈরি, মসলাপাতি ভাঙানোসহ বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো চিরচেনা ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। তখন এটা গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত ছিল ওতপ্রোতভাবে। অনেকে কুটির শিল্প তথা পেশা হিসেবেও ঢেঁকিতে ধান বানতেন। ঢেঁকি চালাতে সাধারণত দুজন লোকের প্রয়োজন হয়। সাধারণত মহিলারাই চালাতেন তাদের সাধের ঢেঁকি। একজন ছিয়া সংযুক্ত যা বড় কাঠের সাথে লাগানো থাকে তার এক প্রান্তে উঠে যার পাশে হাত দিয়ে ধরার নির্দিষ্ট খুঁটি ও লটকন থাকে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পা দিয়ে চাপ দিতে হয় আবার ছাড়তে হয়। অপরজন নির্দিষ্ট গর্তে যেখানে ছিয়ার আঘাতে চাল থেকে ধান বের হয়। সেখানে সতর্কতার সাথে ধান দিতে হয়; আবার প্রতি আঘাতের পর পর ধান নড়াচড়া করে উল্টেপাল্টে দিতে হয়। যাতে সবগুলোতে আঘাত লাগে। শেষ হলে বা গর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেলে এগুলো তুলে আবার নতুন ধান দিতে হয়। মহিলারা ধান বানার ফাঁকে ফাঁকে আঞ্চলিক গীত পরিবেশন করতেন মনের আনন্দে একক বা যৌথ কণ্ঠে। যেমন ‘ও ধান বানরে...ঢেঁকিতে পাড় দিয়া, পিংকী নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া ও ধান বা... নরে, ধান বেচিয়া কিনমু শাড়ি পিন্দিয়া যাইমু বাপের বাড়ি, স্বামী যাইয়া লইয়া আইব গরুর গাড়ি দিয়া ও ধান বা... নরে’। আবার ধান ভাঙা ও চিড়াকুটার বিভিন্ন প্রবচনও বিভিন্ন জায়গায় শোনা যেত। যেমন ‘চিড়া কুটি, বারা বানি, হতিনে করইন কানাকানি, জামাই আইলে ধরইন বেশ, ঢেঁকি বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে জড়িত একটি প্রাচীন যন্ত্র। ঢেঁকির ইতিহাস মূলত বাংলা লোক সংস্কৃতির একটি অংশ। প্রাচীনকাল থেকেই ঢেঁকি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। ধান থেকে চাল তৈরি, চাল থেকে আটা বা পিঠার গুঁড়া তৈরি, মসলা গুঁড়া করাসহ বিভিন্ন কাজে ঢেঁকির ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে ঢেঁকির শব্দে মুখরিত থাকত প্রতিটি বাড়ি। আমরা বাঙালিরা বরাবরই উৎসব প্রিয় জাতি, বিশেষ করে, উৎসব-পার্বণে ঢেঁকির তৈরি পিঠা-পায়েসের প্রচলন ছিল ব্যাপক। ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত খাওয়ার মজাই ছিল আলাদা। তবে আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ চালিত ধান ভানা মেশিন সহজলভ্য হওয়ায় ঢেঁকির ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে। এখনকার প্রজন্ম ঢেঁকি সম্পর্কে খুব কমই জানে। তবে গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে এটি আজও অনেকের কাছে পরিচিত। একটা সময় ছিল যখন ঢেঁকি শুধু একটি যন্ত্র ছিল না, এটি ছিল গ্রামীণ নারীদের শ্রম, ভালোবাসা ও পারিবারিক জীবনের অংশ। পরিবারের মেয়ে-বউরা একসাথে বসে ঢেঁকি চালাতেন, গল্প করতেন, হাসতেন। যা তৈরি করতো এক সামাজিক মেলবন্ধন। খাঁটি চাল, ভাঙা ডাল, মসলা সবকিছুতেই ছিল এই ঢেঁকির ছোঁয়া।
আমার গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার ঘোনাপাড়া গ্রামে। আমার প্রয়াত পিতামহ প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। বড় গৃহস্থ বাড়ি হওয়ায় আমাদের বাড়িতে গ্রামের মহিলারা ঢেঁকিতে ধান ভানতে আসত। আমি ছোটবেলায় আগ্রহ করে মাঝেমধ্যে ঢেঁকির পাশে দাড়িয়ে ওদের ধান ভানা দেখতাম। ওরা গ্রামের ভাষায় ছন্দের তালেতালে গান গাইতো আর ঢেঁকিতে ধান ভানত কিংবা পিঠা তৈরির জন্য চালের গুঁড়া বানাত। ঢেঁকিতে কাজ করা আমার কাছে অনেক কষ্টসাধ্য ও ঝুকিপূর্ণ মনে হয়েছে। হিসাবের সামান্য একটু গড়মিল হলে সামনে বসা মহিলার হাত গুড়িয়ে যাবে, এই ধরনের ভয় আমার মনে সদা কাজ করতো। পরের বাড়িতে ঢেঁকি ভানার কাজ করে গ্রামের অনেক দুস্হ মহিলাদের জীবিকা নির্বাহ করতে দেখেছি। গ্রামের অনেক শ্রমজীবী মহিলাকে দেখেছি তারা নিজেরা ধান ভানিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফেরি করে ঢেঁকি ছাটা চাল বিক্রি করতে। এই পেশায় নিয়োজিত গ্রামের দুস্থ মহিলাদের অনেক কষ্ট করতে হতো। কিন্তু বিনিময়ে তাদের মজুরি কিংবা মুনাফা ছিল অতি সামান্য। বিষয়টি আমার কাছে সব সময়ই অমানবিক মনে হয়েছে। সত্তরের দশকে আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছের একটি ছোটো বাজারে প্রথম যন্ত্রচালিত রাইস মিল বসানোর পর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের বাড়িতে ঢেঁকি ব্যাবহারের কাজ কমে আসতে শুরু করে। বাড়ির রাখালরা মাথায় ধানের বস্তা বহন করে সেখান থেকে ধান ভানিয়ে আনত। যন্ত্রচালিত রাইস মিল সম্বন্ধে ধারণা নিতে আমি দুই-একবার বাড়ির রাখালদের সাথে ধান বানতে সেই রাইস মিলে গিয়েছিলাম। বাড়ির মুরব্বিরা মাঝেমধ্যে শখ করে ঢেঁকি ছাটা চাউলের ভাত খেতে বহুদিন সেই ঢেঁকিটি স্বযত্নে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই নিজেদের জমির ঢেঁকিছাটা চাউলের ভাত খেতে আমার খুব পছন্দের ছিল। এখন বাড়িতে ঢেঁকি নাই। সারা গ্রাম খুঁজলে একটি ঢেঁকিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান সময়ে খোলা বাজারে আর ঢেঁকি ছাটা চাল পাওয়া যায় না। ঢাকা শহরের বিভিন্ন সুপার সপগুলোতে অনেক উচ্চ মূল্যে বিলুপ্তপ্রায় অনেক দেশীয় জাতের ধানের ঢেঁকি ছাটা চাল মাঝেমধ্যে কিনতে পাওয়া যায়। তারা উচ্চমূল্যে অর্ডার দিয়ে এই চালগুলি গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। আমি অনেক শখ করে খাওয়ার জন্য এ-ই ধরনের চাল কিনে মাঝেমধ্যে বাসায় নিয়ে আসি এবং মজা করে যখন চ্যাপা শুঁটকি ভর্তা, ইলিশ মাছ ভাজি, বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীতলক্ষ্যা নদীর সুস্বাদু কেচকি মাছের চর্চরী ভুনা কিংবা আলু দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু গরুর মাংস দিয়ে খাই, কল্পনায় তখন হারিয়ে যাই সেই সত্তর দশকে আমার কৈশোরে। আমাদের দেশে ষাট থেকে সত্তরের দশকে নির্মিত কিছু বাংলা চলচ্চিত্রে ঢেঁকির ব্যাবহার চোখে পড়ে। আমি ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’ বাংলা চলচ্চিত্রে এদেশের গ্রামের মহিলাদের জীবনযাত্রা ও তাদের আয় রোজগারের সাথে যে ঢেঁকির এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল তা প্রত্যক্ষ করেছি।
ধানের খোসাকে তুষ বলা হয়। ঢেঁকি ছাটা চাল থেকে যে ধানের তুষ বের হতো সেই তুষ জ্বালানি হিসেবে গাছের শুকনো ডালপালা কিংবা পাটখড়ির সাথে মিশিয়ে রান্নার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এই তুষ মাটির ঘর নির্মাণ ও ঘর লেপার কাজেও ব্যবহার হতো। যন্ত্রচালিত রাইস মিল চালু হওয়ার পরে সেই তুষ আর গৃহস্থের বাড়িতে আসে না। বর্ষা মৌসুমে গ্রামের মহিলাদের শুকনো জ্বালানির অভাবে রান্নাবান্নার কাজ করতে বেশি রকম সমস্যায় পড়তে হয়। তুষের অভাবে সেই সমস্যা বড় করে দেখা দেয় এবং সেই সমস্যা এখনো রয়েছে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গসহ দেশের ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলাগুলোতে শতশত চাতাল মালিকরা অটোমেটিক রাইস মিল মালিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশের অধিকাংশ চাতাল বন্ধ করে ফেলেছে । বেকার হয়ে পড়েছে দেশের অসংখ্য চাতাল শ্রমিক। ফলে বিপাকে পড়েছে উত্তরবঙ্গসহ দেশের শীর্ষ ধান উৎপাদনকারী জেলাগুলোর শতশত চাতাল মালিকরা। ঠিক যেমনটি বিপাকে পড়েছিল ঢেঁকি বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার অসংখ্য দুস্থ মহিলারা-যারা ঢেঁকিতে ধান বেনে অতি কষ্টে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। এ-সবই আমার চোখে দেখা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তবে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ধানের তুষ থেকে ভোজ্যতেল তৈরি করছে আমাদের দেশের কতিপয় শিল্প উদ্যোক্তরা। বিষয়টি আমি অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। ধানের তুষ থেকে ব্যাপকভাবে যদি ভোজ্যতেল উৎপাদন করা যায়, তাহলে আমাদের ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে। ঢেঁকির সেই আগেকার দিন এখনো থাকলে ধানের তুষ থেকে যে ভোজ্যতেল উৎপাদন করা যায়, তা কখনোই আমাদের দেশে সম্ভব হতো না।
আমাদের দেশে সত্তরের দশক থেকে সর্বপ্রথম রাইসমিল বা যন্ত্রচালিত ধান ভানার মেশিনে প্রচলন শুরু হয়। মেশিনে ধান ভানার কাজটি ব্যায় ও সময় সাশ্রয়ী হওয়ায় তখন থেকেই ঢেঁকির প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। একসময় সারাদেশে বারো মাসে তের পার্বণ পালিত হতো। গ্রামগঞ্জে একটার পর একটা উৎসব লেগেই থাকত। হেমন্ত উৎসব, পৌষ পার্বণ, বসন্ত উৎসব, নববর্ষ, বিবাহ উৎসব, কনের বাড়িতে আম কাঠলী প্রদানের সময় হাতের তৈরি রুটি পিঠা তৈরির উৎসব, হিন্দুদের পূজা, মেলাসহ হরেক রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো বা এখনো হচ্ছে। এসব উৎসবে পিঠা পায়েস সন্দেশ ইত্যাদি তৈরির ধুম পড়ে যেত। আর এসব তৈরির মূল উপকরণ হচ্ছে চালের গুড়ি। চালের গুড়ি তৈরির জন্য অতীতে ঢেঁকি বা গাইল ছিয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। ঈদ বা উৎসবের সময় ঘনীভুত হয়ে এলে প্রত্যেক বাড়িতেই ঢেঁকি ও গাইল ছিয়ার ছন্দময় শব্দ শুনেই আন্দাজ করা যেত ঈদ বা উৎসব এসেছে। গ্রাম বাংলার শৌখিন মহিলারা চালের গুড়ি দিয়ে চই পিঠা, চিতল পিঠা, ঢুপি পিঠা, রুটি পিঠা, ঝুরি পিঠা, পানি পিঠা, চুঙ্গা পিঠা, তালের পিঠা, পাড়া পিঠা, পাটি বলা, হান্দেস, নুনগরা, নুনরডোবা, পব, সমছা সহ তৈরি করতেন হরেক রকমের পিঠা। কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ও যান্ত্রিক যুগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে আর অতীতের মতো জৌলুস নেই। উৎসবগুলো আজকাল একমাত্র প্রথা বা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একটা সময় ছিল যখন বড় গৃহস্থ বা কৃষকের ঘরে অবসর সময়ে বা রাতের অধিকাংশ সময়ই ঢেঁকিতে বা গাইল ছিয়ার মাধ্যমে ধান বানার কাজ হতো। ধান বানতে বানতে অনেক মহিলার হাতে ফুসকা পড়ে যেত। এভাবে ফুসকা পড়তে পড়তে হাতে কড় পড়েও যেত। গরিব মহিলারা বা গৃহ পরিচারিকারা এক আধসের চাল বা ধান পারিশ্রমিকের মাধ্যমে কেউবা শুধু পেটপুরে খাওয়ার বিনিময়ে ধনীদের ঘরে চাল কুটার কাজে নিয়োজিত থাকতো। যে গৃহস্থ যতো বেশি ধান বা চাল উৎপাদন করে বিক্রয় করতে পারতেন তিনিই এলাকায় ততো বড় ধনী হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করতেন। তাই বড় বড় গৃহস্থের বাড়িতে ঢেঁকিতে ধান বানার আওয়াজ তথা ঢেকুর ঢেকুর শব্দ শোনা যেত হরদম।
আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে যন্ত্রচালিত আধুনিক প্রযুক্তির ধান ভানার মেশিন আমদানি ও ব্যবহার শুরু হয় আশির দশক থেকে। এর ফলে দ্রুত হারিয়ে যেতে বসে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। আগের মতো এখন আর গ্রামের গৃহস্থ বাড়িগুলোতে চোখে পড়ে না ঢেঁকি। অথচ একসময় ঢেঁকি ছিল গ্রামীণ জনপদে চাল ও চালের গুঁড়া বা আটা তৈরি করার একমাত্র মাধ্যম। ঢেঁকির ধুপুর-ধাপুর শব্দে মুখরিত ছিল গ্রামীণ জনপদ। কিন্তু এখন ঢেঁকির সেই শব্দ আর শোনা যায় না। কাঠের ঢেঁকি এখন গ্রামীণ জনপদ থেকে অনেক আগেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ একসময় আমাদের দেশের গ্রামবাংলার প্রায় প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতে ঢেঁকি ছিল। ঢেঁকিছাঁটা চাল ও চালের গুঁড়ার পিঠার গন্ধে মন জুড়িয়ে যেত। কিন্তু এখন আর তা নেই।
ঢেঁকি তৈরি করা হতো বরই, বাবলা ও জামগাছের কাঠ দিয়ে। সাড়ে তিন থেকে চার হাত দৈর্ঘ্য, আর পৌনে এক হাত চওড়া। মাথার দিকে একটু পুরু এবং অগ্রভাগ সরু। মাথায় বসানো হতো এক হাত পরিমাণের কাঠের দস্তা। দস্তার মাথায় লাগানো থাকে লোহার গুলা। এর মুখ যে নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে সে স্থানকে গড় বলে। এই ঘড়ে ভেজানো চালে পাড় দিয়ে তৈরি করা হয় চালের গুঁড়া।
ঢেঁকি আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির অংশ। প্রাচীনকাল থেকেই ঢেঁকি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিল। আমাদের দেশে আশ্বিন-কার্তিক মাস এলে শুরু হয়ে যায় বাঙালি জীবনাচরণের আরেকটি বড় অংশ নবান্ন উৎসব। সেই সময় নতুন ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে নবান্ন উৎসব শুরু হয়। সেই উৎসবে পরিবারের শিশু-কিশোরেরা কত আমোদ-আহ্লাদে নাচত আর গাইত। বাঙালি জীবনের এই উৎসবটার সঙ্গেও ছিল ঢেঁকির নিবিড় সম্পর্ক। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে ঢেঁকির ছন্দময় শব্দ। এখন শুধু চাল নয় মসলাপাতিও মেশিনের মাধ্যমে কুটানো হয়। পাটা পুতাইলের (শিল-পাটা) ঘষায় যে মরিচ পিষা হতো তাও এখন বিলুপ্ত প্রায়। তাই তো ‘পাটাখান বিছাইয়া, মরিছও পিসাইলিগো সই, যেই পিসানি মোরে পিসাইলি’ এ ধরনের গানও তেমন একটা শোনা যায় না। মহিলাদের আরামের পরিধি বেড়েছে, বেড়েছে আধুনিকতা ও আধুনিক যান্ত্রিক জীবনযাপন। গ্রামের দু-এক বাড়িতে ঢেঁকি ও গাইল ছিয়ার অস্তিত্ব থাকলেও এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।
উপসংহারে বলব, ঢেঁকি বিলুপ্ত হলেও একে সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো জাদুঘরে গিয়ে জানতে হবে ঢেঁকি কী জিনিস এবং এর মাধ্যমে কোন ধরনের কাজ করা হতো। ঢেঁকির অবদানকে আমরা যেনো কখনোই ভুলে না যাই।








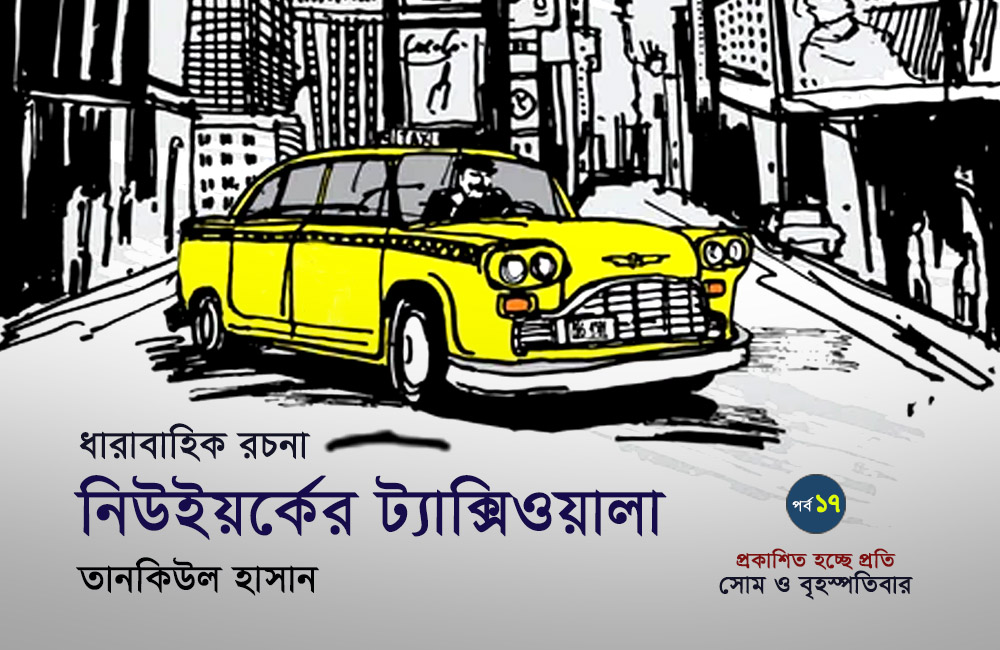
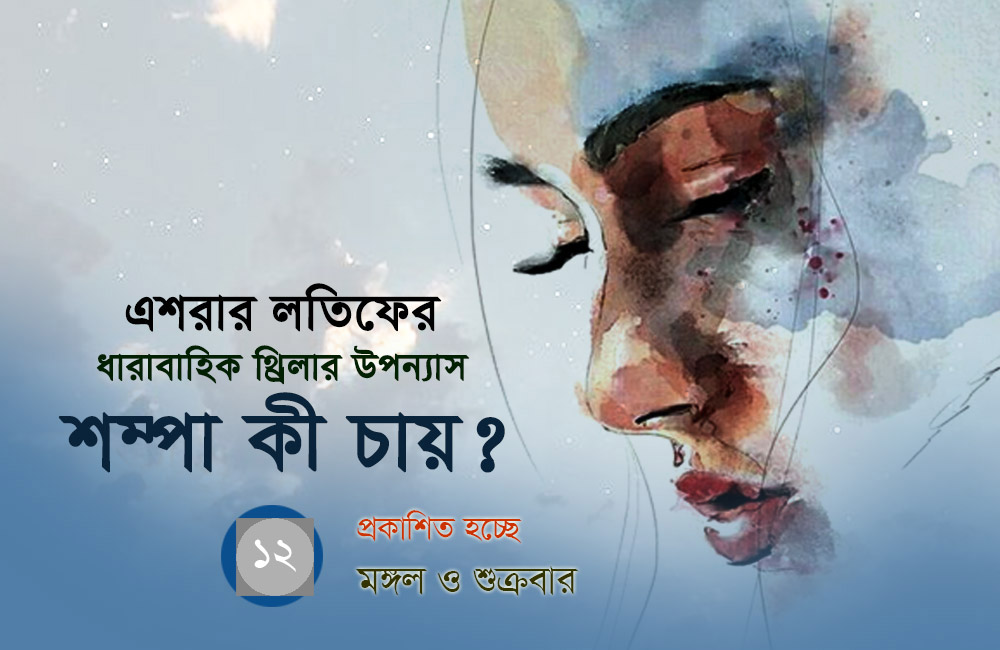



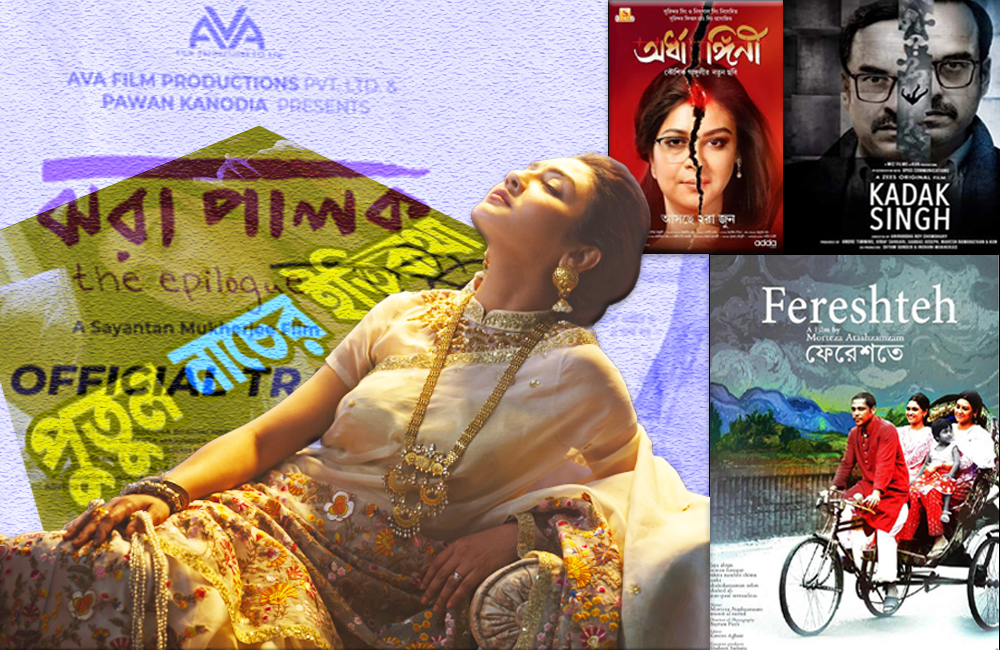

Leave a Reply
Your identity will not be published.