[১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় ইংরেজবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন নতুন রূপ পেতে থেকে। বাংলা এবং ভারতবর্ষের এই বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল জার্মানি এবং রাশিয়া। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব-প্রয়াসের প্রায় সমান্তরালে চলতে থাকল বাংলা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে রুশ বিপ্লবী এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি বিপ্লবীদের প্রেম এবং বিপ্লবের কাহিনি ও এই দুই ভূখণ্ডের বিপ্লবীদের আন্তঃসম্পর্ক। লেখাটির প্রথম খণ্ডের কাহিনি শেষ হয়েছে ১৯১৪-১৫ সালে এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে ‘অন্যদিন’-এ। এই খণ্ডের গল্প আরম্ভ হয়েছে ১৯১৪ সালের রাশিয়ায় আর শেষ হয়েছে ১৯২১-২২ সালে গিয়ে।]
১২
বার্কলে এখন ভারত-জার্মান অস্ত্র পাচার নীলনক্সার প্রাণকেন্দ্র। নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট আর বার্কলের আশপাশে অনেকগুলো অস্ত্র আর গোলাবারুদের ফ্যাক্টরি আছে। ওখান থেকে গোপনে অস্ত্র, গোলাবারুদ কিনে জাহাজে চালান দেওয়ার জন্য বাক্সে ভরে রেডি করা হয়। সান ফ্রান্সিসকোতে জার্মান ভাইস কন্সুল হলো ভন স্ক্যাক। ওয়েস্ট কোস্টের বিপ্লবীদের মাঝে টাকা বরাদ্দ করার দায়িত্ব ওকেই দেওয়া হয়েছে। অ্যাগনেস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে ভন স্ক্যাকের সঙ্গে কথা চালাচালি করে। এতে গোয়েন্দাদের নজর এড়ানো সহজ হয়।
অ্যাগনেসের স্বামী আর্নেস্ট আবার বে এরিয়া চলে এসেছে। আর্নেস্ট মনে মনে ভাবছে ওদের দুজনের সম্পর্ক আবার কিছুটা উন্নতি হবে। বেশ কদিন আবার ওরা একসাথে কাটিয়েছে। একসঙ্গে থাকলে যা হয়, শরীরের সম্পর্ক অ্যাগনেস চাইলেও এড়াতে পারে নি। অ্যাগনেস আবার গর্ভবতী হয়ে গেছে। আবারও প্রবল বিষণ্নতা অ্যাগনেসকে গ্রাস করেছে। অ্যাগনেস কোনোভাবেই সন্তান নেবে না। আর্নেস্ট জানে অ্যাগনেস মরিয়া হয়ে কী ঘটাতে পারে। ও তাড়াহুড়া করে আবার একটা অবৈধ ক্লিনিক খুঁজে বের করেছে। কিন্তু অ্যাগনেসের বাড়াবাড়িতে মনে মনে ও খুবই বিরক্ত।
গর্ভপাত আমেরিকায় আইনবিরুদ্ধ। গর্ভপাতের কথা জানাজানি হলে সমাজেও একঘরে হয়ে যেতে হয়। তার ওপর গর্ভপাত শারীরিকভাবে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। অবৈধ ক্লিনিকে এই ধকল সেরে ওরা জিটনি ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছিল। শারীরিক আর মানসিক ধকলে অ্যাগনেস প্রচণ্ড ঘামছে। বসে থাকতে না পেরে ও গাড়ির সিটে শুয়ে পড়েছে। একটু পরপর ও প্রবল ব্যথায় কাতরাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কী যেন বকছে। ও ডান হাত দিয়ে শক্ত করে আর্নেস্টের হাত ধরে রেখেছে। যেন আর্নেস্টের হাতটাই একমাত্র ভরসা। আর্নেস্টর হঠাৎ কী হলো কে জানে! ক্ষেপে গিয়ে বলল, এভাবে লোক দেখানো উঁহু আহা না করে ঠিকমতো সোজা হয়ে উঠে বসো তো, যত্তসব!
আর্নেস্টের কথা শুনে অ্যাগনেসের মুখ সাদা হয়ে গেল। কথাটা বলেই আর্নেস্ট বুঝল এমন নাজুক সময় এত নিষ্ঠুর ব্যবহার অন্যায় হয়েছে। আর্নেস্ট বলল, আমি খুবই স্যরি লক্ষ্মীটি। এভাবে বলা আমার একেবারেই উচিত হয় নি।
কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে, ধনুক থেকে ছুটে আসা তীর ফিরিয়ে নেওয়ার আর উপায় নেই। ।
অ্যাগনেস একটু সুস্থ হয়েই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কদিন বাদে অ্যাগনেস আর্নেস্টকে একটা চিঠিতে লিখল, আমি দুঃখিত আর্নেস্ট। তোমার আমার সম্পর্কটা আমি আর টেনে নিতে পারছি না। সম্পর্ক ছেদের সব দায়ভার আমি নিচ্ছি। আমিই ভুল করেছি। আমার মতো মেয়ের বিয়ে করাই উচিত হয় নি। তুমি হয়তো আমাকে অনেক ভালোবেসেছ কিন্তু আমি বোধহয় ভালোবাসা ব্যাপারটা তোমার মতো করে বুঝি না।
ট্যাক্সিতে ওই একটা ভুলের জন্য অ্যাগনেসের মন থেকে আর্নেস্ট চিরতরে হারিয়ে গেল।
১৩
জাপানি প্রমোদতরি ইয়োকোহোমা প্রশান্ত মহাসাগর বেয়ে চলছে। গন্তব্য আমেরিকা। জাহাজের বেশির ভাগ যাত্রী ইউরোপীয়। ইউরোপ এখন সারা পৃথিবী শাসন করছে। এ কারণে ইউরোপীয় সাধারণ যাত্রীদের মাঝেও একটা নাক উঁচু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব। এদের আশপাশে থাকতে নরেন মোটেও স্বস্তি বোধ করছে না। কিন্তু মাঝসমুদ্রে কী-বা করার আছে ? কিছুদিন চোখকান বুজে সাদাদের অবজ্ঞা, অপমানের অত্যাচার সয়ে যেতে হবে ।
গত কয়েক বছর নরেন অনেকবার অনেক জাহাজে চড়েছে। ইউরোপীয় কায়দায় পোশাক পরা, টেবিলে বসে কাটাচামচ দিয়ে এটা-ওটা তুলে খাওয়া, আরও কত কী ভংচং সে বাধ্য হয়ে রপ্ত করেছে। ওসব ট্রেনিংয়ের কারণেই এখন আর হুট করে কোথাও নাজুক পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। তবু প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে এই ভ্রমণটা অনেক বেশি লম্বা। ধর্মযাজকের ছদ্মবেশ ধরে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের মাঝে শত্রুদের সঙ্গ সে না চাইলেও সে একই জাহাজে আটকে আছে। জাহাজ তো নয়, এ যেন ভাসমান কারাগার। শত্রুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নরেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। নরেন জানে ও কাচের মতো পাতলা বরফের ওপর স্কেট করছে। কখন যে সব লুকোছাপার ভারে পায়ের নিচের বরফ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে কে জানে!
এই জাহাজের অফিসাররা জার্মান। এরা প্রথম শ্রেণিতে বসে, একসঙ্গে ডিনার খায়, গল্পগুজব করে। ইউরোপীয় ছাড়াও জাহাজের অনেক জাপানি যাত্রীও আছে। আর আছে কিছু আমেরিকান মিশনারি। এরা জাপান, কোরিয়া এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে আমেরিকা যাচ্ছে। এদের অনেকেই বহু বছর ভারতে থেকেছে। ভারতবর্ষের আদ্যপান্ত এরা জানে। পাদ্রি সেজে এদের সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে দার্শনিক আলাপ জমানো যে কী ভয়াবহ ঝুঁকির ব্যাপার সেটা নরেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওদের তুলনায় নরেন খ্রিষ্টান ধর্মের বলতে গেলে কিছুই জানে না।
তবে এসব ঝামেলার ঝুঁকি নরেন আগেই আঁচ করেছিল। সে কারণেই সে জাহাজে একটা সিঙ্গেল কেবিন ভাড়া নিয়েছে। দিনের বেলা ঝকঝকে রোদের আলোয় জাহাজের ডেকে নানান পদের মানুষ ভিড় করে গল্প জুড়ে দেয়। নরেন সহসা বের হয় না। ও কেবিনের ভেতর গুটিয়ে থাকে। বই পড়ে সময় কাটায়। চায়না সাগরে অস্ত্রের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে নরেনের শরীর এমন শক্তপোক্ত হয়ে গেছে যে ওর কোনোভাবেই সমুদ্ররোগ হয় না। এটা নিয়ে নরেনের ভেতর একটা মৃদু গরিমাভাব আছে। কিন্তু সি-সিকনেস না থাকলেও কেউ যদি সারাক্ষণ নিজের কেবিনে পড়ে থাকে, সেটা অন্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে।
এত দিন সমুদ্র শান্তশিষ্ট ছিল। কিন্তু ম্যানিলা থেকে নাগাসাকি যাওয়ার পথে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। এত বড় জাহাজটা ঝড়ো বাতাস আর প্রবল ঢেউয়ে টিনের তোরঙ্গের মতো দুলছে। দুদিন দুরাত ধরে ঝড়ের হুমকিধামকি আর শাসানি চলল। সবাই ভয়ে যার যার কম্পার্টমেন্টে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইল। একমাত্র নরেন মাঝে মাঝে ডেকে চলে যায়। একা একা দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ক্ষ্যাপামো উপভোগ করে। ধীরে ধীরে ঝড়ের দাপট কমে এল। সমুদ্র শান্ত। এখনো যদি নরেন সারাক্ষণ কেবিনে পড়ে থাকে, তাহলে লোকজন নানা কথা তো বলবেই। কে বিশ্বাস করবে যে লোক প্রবল ঝড়ে ডেকে দাঁড়িয়েছিল, তার সি সিকনেস হতে পারে ? এসব ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন ইদানীং ডেকে বেরিয়ে আসছে।
তা ছাড়া রাতে খাওয়ার সময় অন্য যাত্রীদের এড়ানো যায় না। ডিনারের জন্য ডাইনিং হলে যার যার সিট বরাদ্দ করা আছে। নরেনের ডানপাশের চেয়ারে বসে দক্ষিণ ভারত থেকে আসা একটা খ্রিস্টান মেয়ে। ও আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য যাচ্ছে। নরেনের বাঁ পাশে বসে হেনরি, সে একজন অ্যামেরিকান ইউনিটারিয়ান পাদ্রি। হেনরি টোকিও ইউনিভার্সিটিতে দর্শন পড়ায়। খাবার টেবিলে হেনরি বকরবকর করতেই থাকে। আর কেউ কিছু বলার সুযোগই পায় না। নরেনের এতে ভালো হয়েছে, ওকে অযথা মানুষের সঙ্গে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে হয় না। নরেন হেনরির কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে আর একটা দুটো প্রশ্ন করে ওকে আরও উস্কে দেয়। হেনরির কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগে। তবে ওর যুক্তিতর্কের কোনো আগামাথা নেই। একদিন হেনরি নরেনের গলায় ঝোলানো সোনার ক্রসটা ধরে জানতে চাইল, এটা কেন পরে আছ ?
নরেন অবাক হলো, একজন খ্রিস্টান পাদ্রি এটা কী বলে ? নরেন বলল, কেন, আমি মহান যিশুকে স্মরণ করে এটা পরি। যে-কোনো ধার্মিক খ্রিস্টানই ক্রস পরে।
কে বলেছে তোমাকে ? আমি কি পরি ?
নরেন খেয়াল করে দেখল কথা সত্য। হেনরির গলায় কোনো ক্রসের লকেট নেই। হেনরি বলল, আমি ইউনিটারিয়ান খ্রিস্টান। আমরা ট্রিনিটি কিংবা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরে যাওয়া বিশ্বাস করি না।
খ্রিস্টান ধর্মের ভেতরই যে নানা মতের নানা দল আছে, সেটা সম্পর্কে নরেন অতটা জানে না। কিন্তু সেই অজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেলে এখন নিজের মুখোশটাই খসে পড়বে। নরেন আহত হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, কী বলছো এটা ? তুমি হোলি ট্রিনিটি বিশ্বাস করো না ?
হেনরি নরেনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, তুমি কি সত্যি ভাবো যিশু খ্রিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ?
এবার নরেন আরও অবাক হয়ে গেল। নরেন নিজের যুক্তি সমর্থন করে বলল, আমি ক্রুশ পরি কারণ এই ক্রুশ সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক।
সেই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগটা কী ?
আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ।
এর পরই হেনরি আপনমনে কীসব বিড়বিড় করতে লাগল। মুখের ভাব দেখে মনে হলো, হেনরি কোনো সিরিয়াস চিন্তা করছে কিন্ত তার কথা মোটেও বোঝা যাচ্ছে না। নরেন ভাবল, এই লোক হয় একটু ক্ষ্যাপাটে নয় ব্রিটিশ এজেন্ট। ওর মতোই ভং ধরেছে।
সেদিন খাওয়ার সময় নরেনের অন্য পাশে বসা দক্ষিণ ভারতের মেয়েটি তামিল ভাষায় বলল, তুমি পন্ডিচেরি থেকে এসেছ শুনেছি। আমিও কিন্তু তামিল। আমার নাম অমরাবতী।
নরেন মনে মনে বলল, এই সেরেছে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ও তো তামিল ভাষা জানে না। নরেন ইংরজিতে বলল, আমি পন্ডিচেরিতে ধর্মশিক্ষার জন্য থেকেছি কিছুদিন। কিন্তু আমার জন্ম বাংলায়। আরও অনেক শহরেই থেকেছি। এ কারণে তামিল ভাষাটা না রপ্ত করতে পারি নি।
অমরাবতী ইংরেজিতে বলল, বাহ দারুণ কস্মোপলিটান জীবন আপনার! আসলে তামিল ভাষা না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই। ভাষা একটা প্রকাশের মাধ্যমমাত্র। আসল প্রকাশের মালিক তো মহান ঈশ্বর। তবে পন্ডিচেরিতে থেকে তুমি তামিল জানো না ভাবতেই অবাক লাগে।
আসলে আমি পন্ডিচেরিতে ছিলাম আরও একটা কারণে, ফরাসি ভাষাটা শেখার জন্য।
উপস, আমি আবার ফরাসির কিছুই জানি না। এখন তোমাকে একটি গোপন কথা বলব ?
কী সেটা ?
আমি নিজেও তামিল জানি না। কেবল একটা দুটো বাক্য বলতে পারি যেমন একটু আগে বললাম।
তাই ? তুমি কেন তামিল জানো না! আশ্চর্য কাণ্ড!
অমরাবতী এবার মুখ ম্লান করে বলল, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমার আব্বু-আম্মু মারা যায়। এক আমেরিকান মিশনারি যুগল আমাকে বড় করেছেন। আমি তাদের পালক সন্তানের মতো। ওরা আমাকে একটা খ্রিস্টান ইন্সটিটিউটে ভর্তি করে দিয়েছিল। ওখানে সবকিছু ইংরেজিতে হতো। আবার বাড়িতেও আমার পালক বাবা-মা ইংরজিতে কথা বলত। আমি নিজেও কয়েক বছর ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি।
কিন্তু তুমি তো চাইলেই তামিল ভাষা নিজে শিখে নিতে পারতে।
তা পারতাম। কিন্তু...।
কিন্তু কী ?
আমার পালক বাবা-মা কখনো চায় নি যে আমি দেশি যুবকদের সঙ্গে বেশি মাখমাখি করি। সে জন্য নিজের ভাষাটা শিখতে দেয় নি। মাঝখান থেকে আমি পড়েছি বিপদে। আমার গায়ের চামড়ার রং ঘন বাদামি। না পারছি দেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে। আবার বিদেশিরাও আমাকে সেভাবে আপন করে নিচ্ছে না। তোমার এ রকম অনুভূতি হয় না কখনো ?
হবে না কেন ? সাদাদের কথা বাদ দাও, ওদের অহংকারের শেষ নেই। কিন্তু এই জাহাজেই লক্ষ করবে হলুদ চামড়ার জাপানিরা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কীরকম উন্নাসিক ভাব ধরে।
অমরাবতীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নরেন ভাবল এই মেয়ের চেয়ে হেনরিই ভালো ছিল। এই মেয়েটি একটা ঝামেলার আকর। কথা বলে কম, প্রশ্ন করে বেশি। অন্য কোথাও অন্য কোনো পরিস্থিতিতে এই মেয়েটাকে হয়তো ভালো লাগত। মনে হতো, আহা কী উচ্ছ্বল প্রাণবন্ত একটা মেয়ে! কিন্তু এখন তো এর সামনে ছদ্মবেশ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে! খাওয়ার পর ডাইনিং হল থেকে বেরুবার সময় অমরাবতী হঠাৎ নরেনের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, আমাদের দুজনের কত মিল, তাই না ?
মিল! কোথায় ?
এই যে আমরা দুজনেই যিশুর প্রেমে নিজেদের ধর্ম ছেড়ে এসেছি। আবার দুজনেই খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আরও লেখাপড়ার জন্য বিদেশ যাচ্ছি।
নরেন সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে মনে মনে বলল, আমাদের একজন নকল পাদ্রি, আরেকজন আসল পাদ্রি। তাই তোমার কাছে থেকে আমি শত হাত দূরে থাকতে চাই।
নরেন যখন জাহাজের ডেকে আসে, তখনো বিশেষ সতর্ক থাকে। যাত্রীদের অযথা প্রশ্ন এড়ানোর জন্য সবার থেকে একটু দূরত্ব রেখে বসে। গম্ভীরভাবে বাইবেল পড়তে থাকে। আসলে ছদ্মবেশের সঙ্গে মিলিয়ে বাইবেলটা ঠিক ঠিক জানা দরকার, তা না হলে হঠাৎ উল্টোপাল্টা কিছু বলে ধরা খেলে খবর হয়ে যাবে। নরেন লক্ষ করেছে অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে, দেখেছো যুবকটাকে, ও নিশ্চয় প্যারিসে বড় কোনো ধর্মীয় পদে অভিষিক্ত হবে। নরেন মনে মনে জবাব দেয়, তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু।
দু সপ্তাহ প্রায় শেষ হতে চলল। প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে জাহাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে হনুলুলুর দিকে। জাপানিদের জাতীয়তাবোধ খুব প্রখর। জাহাজে সব সময় ওরা ওদের জাতীয় পোশাক কিমনো পরে থাকত। শুধু ডিনারের সময় জাহাজের জাপানি অফিসারেরা টাক্সিডো পরত। কিন্তু জাহাজ হনুলুলুর কাছাকাছি আসতেই সবার কিমনো হাওয়া হয়ে গেল। জাপানিরা সবাই এখন নিখুঁতভাবে স্যুট পরে আছে। অমরাবতী নরনের কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, জাপানিদের স্যুটে কেমন অদ্ভুত লাগছে না ? একদম কাকতাড়ুয়ার মতো।
হ্যাঁ।
বিরক্তিকর ব্যাপার। তাহলে এতদিন কিমনো পরল কেন ?
নরেনেরও জাপানিদের খুব একটা পছন্দ হলো না, কে জানে জাপানে ঠিকমতো সমাদর পায় নি বলেই হয়তো জাপানিদের প্রতি ওর অবচেতনে একটা বীতশ্রদ্ধা জেগে গেছে।
আমেরিকান সভ্যতার দ্বারপ্রান্ত হনুলুলু। জাপানি প্রমোদতরি ইয়োকোহোমা ওখানে ভিড়ল বিকেলবেলা। সবাই সেই আনন্দনগরে রাত কাটাবার জন্য জাহাজ থেকে নেমে গেল। হেনরি নরেনের কাছে এসে বলল, চলো সমুদ্রের তীর ধরে দুজন একটু হেঁটে আসি।
হ্যাঁ চলো, সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যাস্ত দেখতে ভালো লাগবে।
হেনরি অমরাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, অমরাবতী, আপনি যাবেন আমাদের সাথে ?
অমরাবতী মাথা নেড়ে সায় দিল। ওরা তিন জন সাগরের তীর ধরে ঘণ্টা খানেক ঘুরল। স্ট্রবেরির মতো টকটকে লাল সূর্যটা দিগন্ত ছুঁয়েছে। এমন রক্তিম সূর্যাস্ত নরেন বহুদিন দেখে নি। সেদিকে তাকিয়ে নরেনের মন হঠাৎ বিষাদে ভরে উঠল। এই যে দেশকে ভালোবেসে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে চলে এল, দেশের মানুষ কি সেই কথা কোনোদিন মনে রাখবে ?
সন্ধ্যা নামতেই ওরা তিন জন জাহাজে ফিরে এল। হনুলুলুর সৈকত থেকে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড দেখা যায়। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওরা তাকিয়ে রইল প্রবল পরাক্রমশালী পশ্চিমা সভ্যতার মুক্তোর মালার মতো আলোর বিন্দুর দিকে।
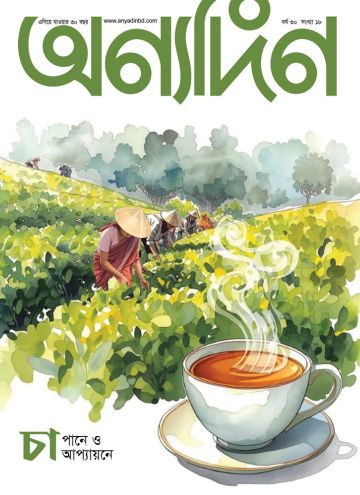





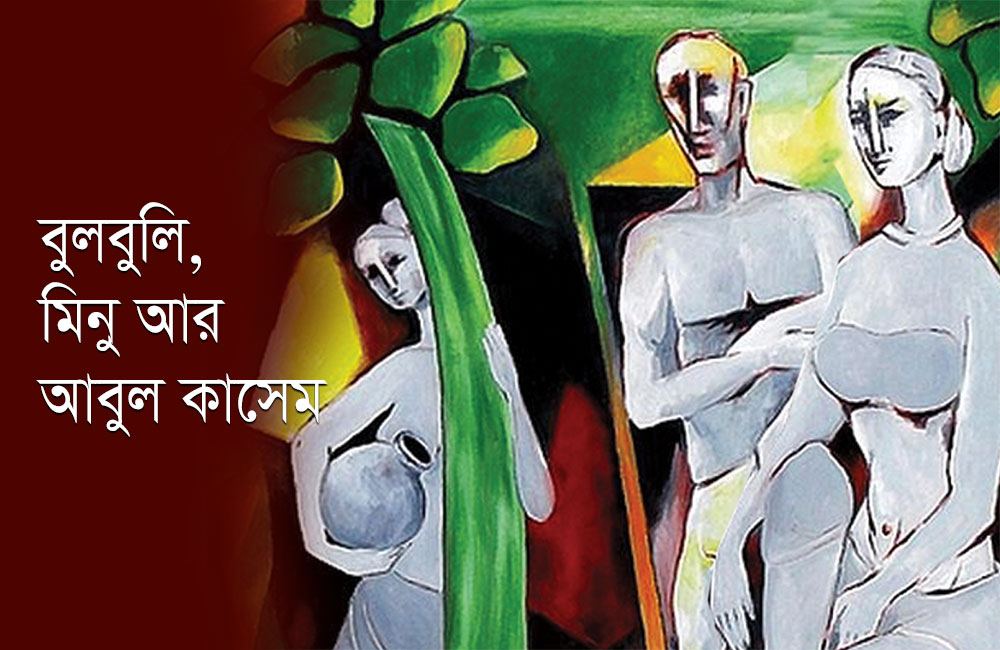
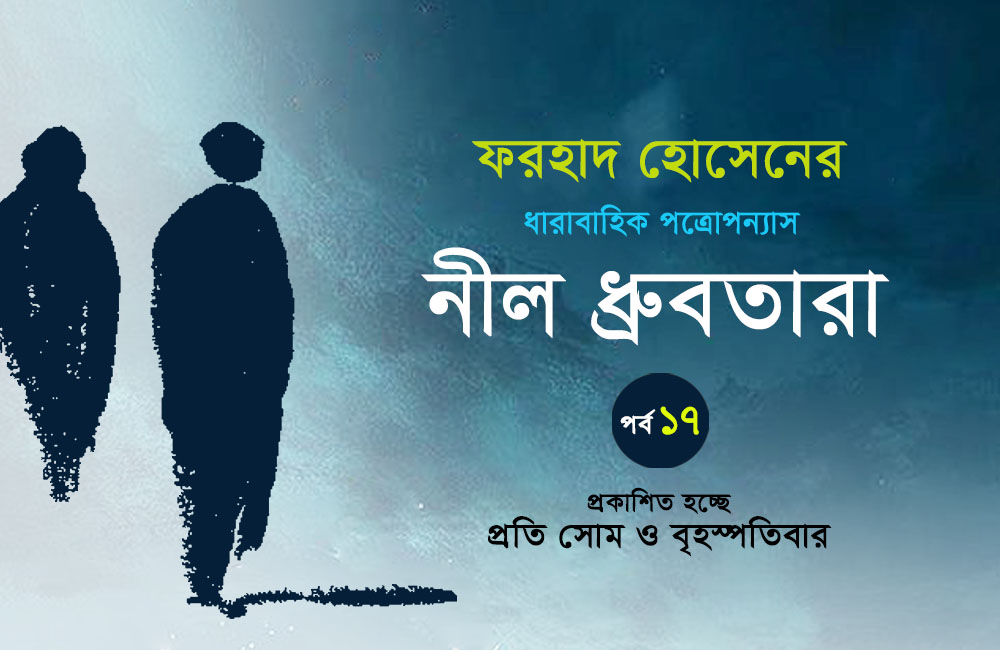
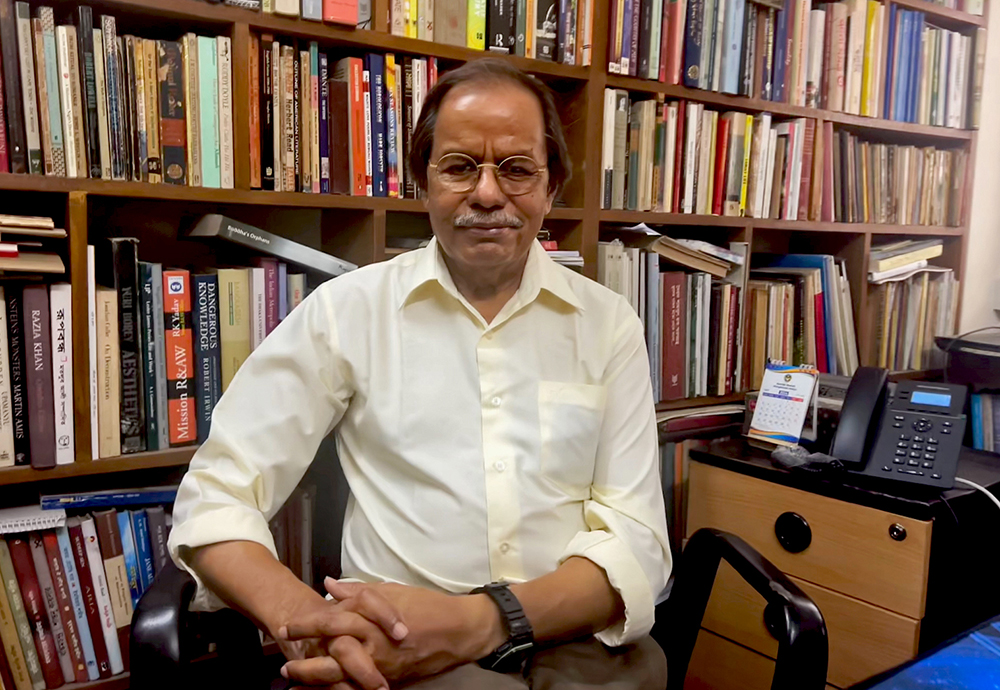


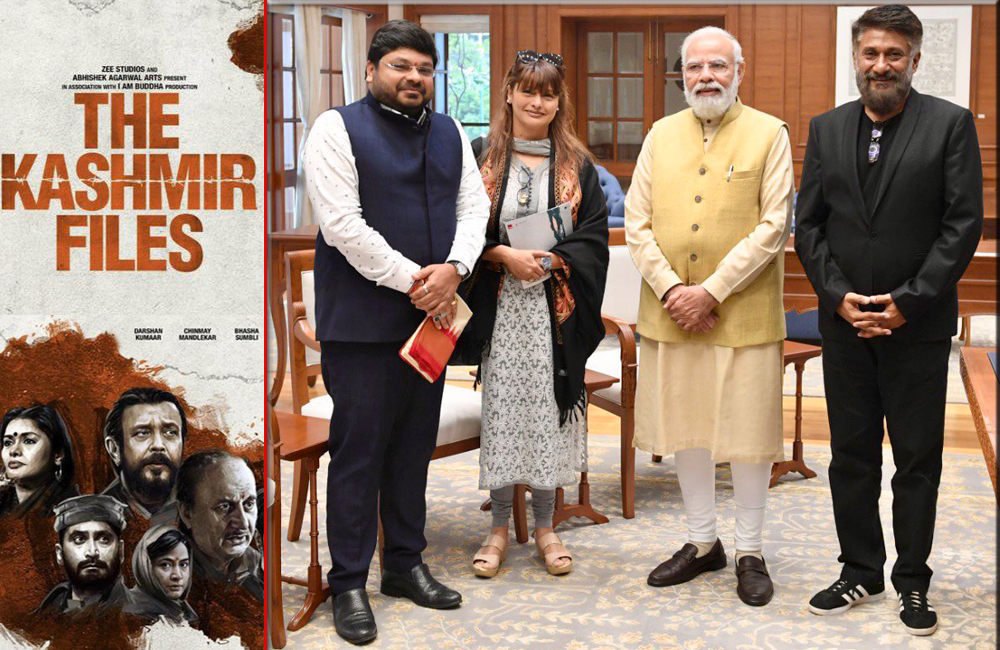



Leave a Reply
Your identity will not be published.