গোবিন্দচন্দ্র দাস। ‘স্বভাবকবি’ হিসেবে তিনি খ্যাত। তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে নারীভক্তি, পতি-পত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, গাহর্স্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি, পল্লিজীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেম।
ঢাকা থেকে গাজীপুর ইতিহাসখ্যাত ভাওয়াল রাজার বাড়ির কাছাকাছি স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ি। এখানে তাঁর সম্পর্কে ছোট্ট একটা গৌরবচন দিয়ে রাখি। স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস হচ্ছেন এমন ধারার কবি, যিনি ব্যক্তিত্ব বা কবির যেটি স্বকীয় মূল্যবোধ তাকে বিসর্জন দিলে জীবনে অনেক সুবিধা নিয়ে দুধে-ভাতে বাঁচতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তিনি কোনোদিন রাজন্যকুলের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে চান নি। ফলে গোবিন্দচন্দ্র দাসের গোটা জীবনটাই পাল্টাধারার একজন মানুষের জীবন।
পূর্ববাংলার এই মহৎ কবিপ্রতিভার শেকড় সংবাদের খোঁজে আমরা প্রথমে তাঁর বাস্তুভিটা, তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে জানতে চাই কবি তপন বাগচীর কাছে। তিনি গোবিন্দচন্দ্র দাস গবেষক খ্যাতনামা সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং গাজীপুর চৌরাস্তার মোড়ের দৈনিক গণমুখ পত্রিকার সম্পাদক ও গোবিন্দচন্দ্র দাস একাডেমীর সম্পাদক আমজাদ হোসেনের কথা বলে দেন।
সেই সূত্র ধরে সৈয়দ আবুল মকসুদের সাথে কথা বলে আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সরকারসহ একদিন সকালে আমরা রিকশা যোগে ফার্মগেট গিয়ে গাজীপুর চৌরাস্তার উদ্দেশে রাইডার-এ উঠে পড়ি। রাইডার আমাদের নামিয়ে দেয় দৈনিক গণমুখ অফিসের সামনেই। গণমুখ অফিসের উপরে গোবিন্দচন্দ্র দাস একাডেমী। ওই একাডেমীর কর্মকর্তা গোছের একজন লাকিব উদ্দিনকে পেলাম। তার আন্তরিক সহায়তার মধ্য দিয়ে পেলাম দুটো ব্রুশিয়ার এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ির একটা গাইড লাইন। সেই গাইডলাইন ধরে আমরা অগ্রসর হলাম ভাওয়াল রাজবাড়ির শ্মশানঘাটের দিকে। এখানে অনেককেই গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর দিতে পারে নি। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সাক্ষাৎ হলো এক ভদ্রলোকের সাথে। তিনি আমাদের সাহায্য করতে একজন রিকশাঅলাকে বুঝিয়ে দিয়ে পাঠালেন রাজপুকুর পাড়ের গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাস্তভিটায়।
যে বাস্তভিটায় গোবিন্দচন্দ্র দাসের মাটির ঘর ছিল, এখন সেখানে একতলা ভবন। ভবনটিতে চলছে গাজীপুর প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাইস্কুল। ওই বাড়ির বর্তমান মালিক এখন শেখ মোশাররফ হোসেন। তিনি ১৯৬০ সালে এই বাড়ি গোবিন্দচন্দ্র দাসের ওয়ারিশদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। ওয়ারিশের নাম জানতে চাইলে বললেন—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। গোবিন্দচন্দ্র দাসের ওয়ারিশ কীভাবে ‘দত্ত’ পদবির হলো এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কোনো কীর্তি এ অঞ্চলে নেই। কেউ চেনে না তাঁকে। তাঁর বাড়ির পাশের অনুন্নত সড়কটি ‘কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস’ সড়ক হিসেবে নামকরণকৃত হলেও একটিমাত্র বাড়ির ফোল্ডিং-এ দৃশ্যটি চোখে পড়েছে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ির অদূরেই এখনো সেই প্রাচীন ভিটা। অনেক গাছের সমাহার সেখানে। ১৮৮৫ সালের ২০ জানুয়ারি এখানেই জন্মেছিলেন পল্লিপ্রকৃতি ও গণমানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সহজিয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। কবির প্রথমা স্ত্রী সারদা সুন্দরী দেবী এই দেবপুরেই বাংলা ১২৯২ সালে মৃত্যুবরণ করলে চিলাই নদীর তীরে তাঁর শেষকৃত্য করা হয়। এ ব্যাপারে কবির কবিতাও রয়েছে।
গোবিন্দচন্দ্র দাসের বেশির ভাগ কবিতার বিষয়ই নৈসর্গিক ও আত্মজৈবনিক। দৈনন্দিন জীবনে কবি যা দেখেছেন যা অনুভব ও উপভোগ করেছেন, ঘৃণা করেছেন, তা-ই লিখেছেন। সমাজের অন্যায়-অসংগতিকে তিনি কখনোই চোখ বুজে মেনে নেন নি। তাঁর কাব্যের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে সমাজের কঠোর সমালোচনা।
বাংলা কাব্যের দুই প্রবল ও প্রতাপশালী স্রোতের মাঝামাঝি এক উজ্জ্বল পুরুষ গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর অব্যবহিত আগে প্রধান কবিদের মধ্যে ছিলেন রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখের এক ধারা এবং তাঁর প্রায় সমসাময়িক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখের এক স্রোত। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথসহ আর যেসব কবি উনিশ শতকে আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে প্রধান—অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র্র দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিন্দ্র মোহনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ।
উনিশ শতকের এই কবিসভার সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং নাগরিক কবি। তাঁরা কাব্য সাধনা করতেন কলকাতায় বসে এবং থাকতেন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস।
তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের দুর্জয় প্রতিপত্তির কারণে জীবদ্দশায় সংগ্রাম-কষ্ট, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে কেটেছে গোবিন্দচন্দ দাসের দিন।
গ্রন্থাবলির দিক থেকে হিসাব করলে প্রচুর লিখেছেন তিনি। ত্রিশ বছরের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মিলে ১১টি কাব্যগ্রন্থসহ তিনি প্রায় চার শ কবিতা লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুসুম (১২৯৮), মগের মুল্লুক (১২৯৯), কস্তরী (১২০২), চন্দন (১৩০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১২), শোক ও সান্ত্বনা (১৩১৬)। কিন্তু তাঁর লেখা কোথাও ওভাবে গুরুত্বের সাথে তখন গৃহীত হয় নি। তার জন্যে যথাযথ কারণও ছিল। তিনি ছিলেন নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি আর তখন সাহিত্যচর্চা উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সামাজিক গঞ্জনা ছাড়া কিছুই পান নি বাস্তব জীবনে। ‘স্বভাবকবি’ নামে সমধিক পরিচিত এই গণমানুষের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ভাওয়াল রাজার স্নেহেই ছিলেন। কিন্তু ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণের মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষের চক্রান্তে পড়ে কবি রাজার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। কালীপ্রসন্নের প্রতাপ ও প্রভুত্ব এত বেশি ছিল যে, সেখানে কবিকে অসম্মান করা হলেও প্রতিকারের কোনো পথ ছিল না। প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যদাসম্পন্ন কবি রাজন্যকুলের দ্বারা অপমানিত হয়ে ১২৮৭ সালে ময়মনসিংহ চলে আসেন। ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কবি ময়মনসিংহের জমিদার কেশবচন্দ্রের কাছে চাকরি করেন। ময়মনসিংহ ছেড়ে কিছুদিন পরে আবার জয়দেবপুরে নিজগৃহে চলে আসেন। তাঁর ‘বিদায়’ কবিতাটি এ সময়ই লেখা। জয়দেবপুর আসার অল্পদিন পরই তিনি প্রথমবার কলকাতা যাত্রা করেন। সেই সময় মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্র কিশোর কলকাতায় ছিলেন। দেবেন্দ্র কিশোরের বাসভবনে চার মাস থাকার পর ১২৮৯ সালের মাঘ মাসে কবি দেবেন্দ্র কিশোরের সাথে ময়মনসিংহ আসেন এবং সিটি স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিত পদ লাভ করেন। স্কুলটি দীর্ঘদিন টিকে না থাকার জন্যে উক্ত চাকরি ছেড়ে তিনি ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন।
১২৯৯ সালের ১ মাঘ কবি পুনরায় প্রমদা সুন্দরীকে বিয়ে করেন। এ সংসার সুখের হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী ১৩০০ সালের ১৪ কার্তিক কলকাতায় মারা যান। ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বগ্রাম থেকে পুনরায় নির্বাসিত হয়ে শেরপুর চলে যান। সেখান থেকে চলে যান কলকাতা। কলকাতায় ভাওয়াল রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সাথে দেখা হলে কবির ‘নবযুগ’ প্রবন্ধ নামে ভাওয়াল রাজাদের সমালোচনা করে লেখা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আসলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান।
রাজা নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলে কবি ক্ষুব্ধ হন। দেবী প্রসন্নের আনন্দ আশ্রমে বসে কবি ‘মগের মুলুক’ নামে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করেন। এতে ভাওয়াল রাজার নানা প্রকার অবিচার-অনাচারের কাহিনি হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশন করেন।
‘মগের মুলুক’ প্রকাশিত হওয়ার পর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মানহানির মামলা করে। মামলা নিষ্পত্তি হলেও ভূস্বামী এবং সামন্ত প্রভুদের অমানবিক দোর্দণ্ড প্রতাপের শিকার হন কবি। কবির জীবনের ওপর হামলা চালায় রাজন্যকুল। একাধিকবার এ ধরনের হামলা চালালেও প্রতিবারই অভাবনীয়রূপে কবির জীবন রক্ষা পায়।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ভাওয়াল এস্টেট থেকে চলে যাওয়ার পর রাজকুমাররা কবিকে চিঠি দিয়ে স্বগ্রামে ফিরিয়ে আনে। দীর্ঘ এগারো বছর পর স্বগ্রামে সর্বান্তকরণে কবি পুলকিত হয়েছিলেন। এই এলাকার নিসর্গের প্রতি কবির ভালোবাসা ছিল অপরিসীম।
কবির অকৃত্রিম দেশপ্রেমের পরিচয় বহু কবিতায়ই পাওয়া যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের স্তাবকতা করলে হয়তো তাঁর দারিদ্র্য মোচন হতো, এমনকি ব্রিটিশ সরকারের উপাধিও পেতে পারতেন। কিন্তু মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ কবি সেই কাজ করেন নি।
গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনসংগ্রাম ছিল খুবই দুরূহ ও অমানবিক। গোবিন্দচন্দ্র দাস সমালোচক প্রখ্যাত সাহিত্যিক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্বন্ধে লিখেছেন—জীবনের শেষ দশ বছর তিনি প্রায় জীবস্মৃত হয়েছিলেন। কাব্যলক্ষ্মীও এ সময় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পুরো জীবনটাই দারিদ্র্য আর অর্থকষ্টের ভেতর দিয়ে কেটেছে। তবে জীবনের শেষ দশ বছর আর্থিক অনটনের দরুন প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন কবি। অন্তিমকালের জীবনযাত্রায় বিপর্যস্ত কবি-জীবনের করুণচিত্র পাওয়া যায় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিঠিতে। ... “বাসায় আসিবার পথে কবির সহিত একত্রেই আসিতেছিলাম, পাটুয়াটুলীর হীরণ কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র প্লেটে তিনি নুনজল দিয়া চিড়া খাইতেছিলেন। পথে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, কি খাইব পূর্ণবাবু ? আজ ঠিক ত্রিশদিনের মধ্যে মাত্র ৮ বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। অর্থাভাবে হোটেলে নিত্য খাইতে পারি না। তাই তিনবেলা তিন পয়সার চিড়া খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।”
কবির দুঃখকর জীবনের অন্তিম পর্যায় সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তার মধ্যে সর্বাধিক তথ্য পাওয়া যায় অক্ষয় কুমার মৌলিক বিদ্যাভূষণের কাছ থেকে। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রথম পুত্র অরুণের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় পুত্র বরুণেরও পড়ালেখা বন্ধ করতে কবি বাধ্য হন। আর অন্যদিকে খাজনার টাকা বাকি পড়ায় কবির সামান্য ভূ-সম্পত্তিও ভাওয়াল এস্টেট কর্তৃক নিলামে উঠার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় কবির শরীর যেমন ভেঙে যায় তেমন অনাহারও প্রাত্যহিক হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন অসুখবিসুখ ভর করে এ সময় তাঁর শরীরে।
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন ব্যাপক সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য। মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম না নিলেও তাঁর জীবনমুখীনতা তাঁকে প্রথম সারির কবিদের কাতারে দাঁড় করে দেয় তাঁর কবিতা ও কর্ম দ্বারা।
রোগ, শোক, দারিদ্র্যের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের একজন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৩২৫ সালের ১৩ আশ্বিন শেষরাত্রিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত কবির প্রতি সম্মানার্থে কোনো লেখক, কবিকে শ্মশানে উপস্থিত থাকার কথা শোনা যায় নি। কবির একটি কবিতার নাম—‘আমার চিতায় দিবে মঠ’। কিন্তু না তাঁর চিতার কোনো নির্ধারিত স্থান নেই, মঠ তো নেইই নেই—আবক্ষ স্ট্যাচুও। এমনকি একটি তৈলচিত্রও এখানে নেই। জয়দেবপুর, ভাওয়ালে তাঁর নামে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে নি। গোবিন্দচন্দ্র দাসের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, তিনি নিতান্ত ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত ছিলেন। বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। থাকলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মারাত্মক রকমের দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। একদিকে তিনি সমাজের অবিচার-অনাচার ও উপেক্ষা মাথা পেতে নিয়েছেন, অপরদিকে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একমাত্র অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতাকে, সর্বৈব অন্যায় ও অসত্যের সামনে যার প্রভাব সামান্যই।
প্রচারের যুগে পিছিয়ে গোবিন্দচন্দ্র দাস। তবু এতটা পিছিয়ে থাকার কথা নয়। খুব কম লোক তাঁর নাম জানে, চেনে তারও কম। এভাবেই গোবিন্দচন্দ্র দাসকে যতদূর জানা যায়—তা জানতে জানতে জৈষ্ঠ্যের রোদ হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। গোবিন্দচন্দ্র দাস সড়কের পাশে রাজপুকুর। গ্রীষ্মের দাহে সেই পুকুরে স্নান করছে মানুষ। গোবিন্দচন্দ্র দাস সড়কের মোড়ে জিব বের করে হাঁপানো কুকুরের ক্লান্তি দেখতে দেখতে আমরা উঠে পড়ি রিকশায়। ইতিমধ্যে বিশ্বজিতের ক্যামেরা বহু ছবি সংগ্রহ করে নিয়েছে। রিকশা শিববাড়ি এসে থামলে আমরা ফার্মগেটের উদ্দেশে রাইডার-এ উঠে পড়ি। গাড়ি চলে, বেলা ডুবে আসে। পেছনে পড়ে থাকে ভাওয়াল রাজ্যের উপেক্ষিত এক কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিল ভিন্ন ইতিহাসের। এইভাবে অনাদরে-অবহেলায় এবং রাজন্যবর্গের কোপানলে পড়ে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকেন। এত বড় মাপের প্রতিভার এই ধরনের ক্ষয় সামলাতে কেউ এগিয়ে আসে নি। এটাই সবচেয়ে অবাক কাণ্ড। সবচেয়ে গর্ব করার বিষয় হচ্ছে, গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব। যা তাঁকে রাজন্যকুলের দিকে সামান্যও হেলাতে পারে নি। স্রোতের বিরুদ্ধে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো অপরাজেয় এই কবি আজীবন থেকেছেন আপসহীন। আর এই আপসহীনতার ফলে তাঁর জীবনের প্রতিটা সময়ই থেকেছে সংকটাপন্ন। জীবন থেকে অভাব কখনোই পিছু ছাড়ে নি। এই মেধাবী কবি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়েছেন আমাদের সাহিত্য থেকে। তিনি একটু শান্তিতে এবং অর্থনৈতিক চিন্তাশূন্য থাকতে পারলে হয়তো বাংলা সাহিত্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত নতুন ধারায়—নতুন মাত্রায়।
এখন বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের যে ফর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়, বিশেষত সাহিত্যের গতিশীলতার যে ধারার কথা বলা হয়, সেখানে আমাদের দেশজ ধারার কথাও বলা হতে পারত যদি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতো কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। এখনো আধুনিক বিশ্বের লেখক ও স্বভাব সাহিত্যিককে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে তাদের চিন্তাকে বোঝা ও জানার জন্যে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের আধুনিক হতে কত দেরি ?








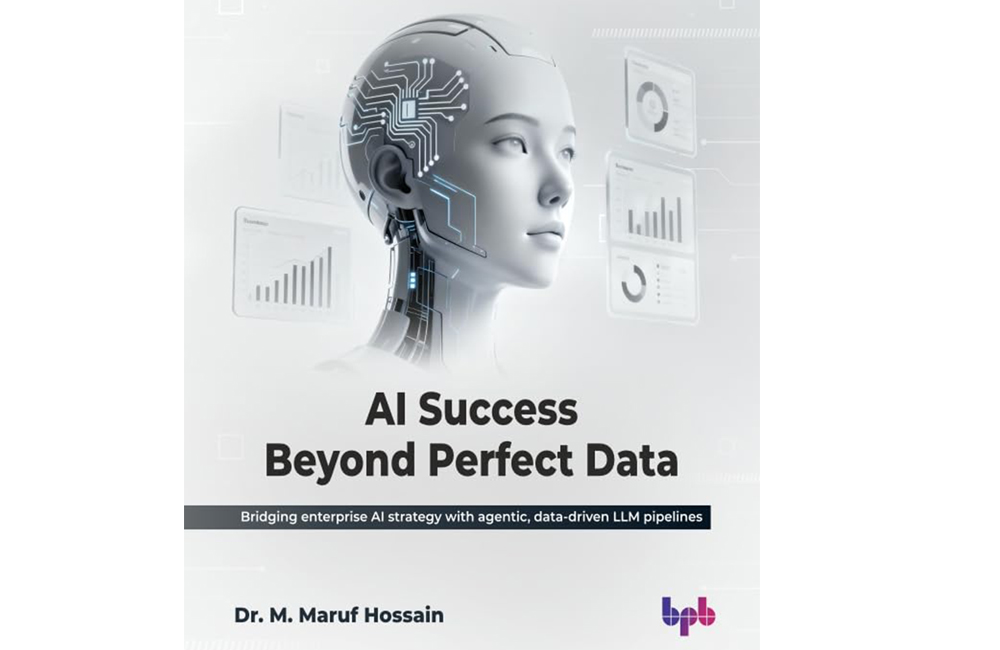



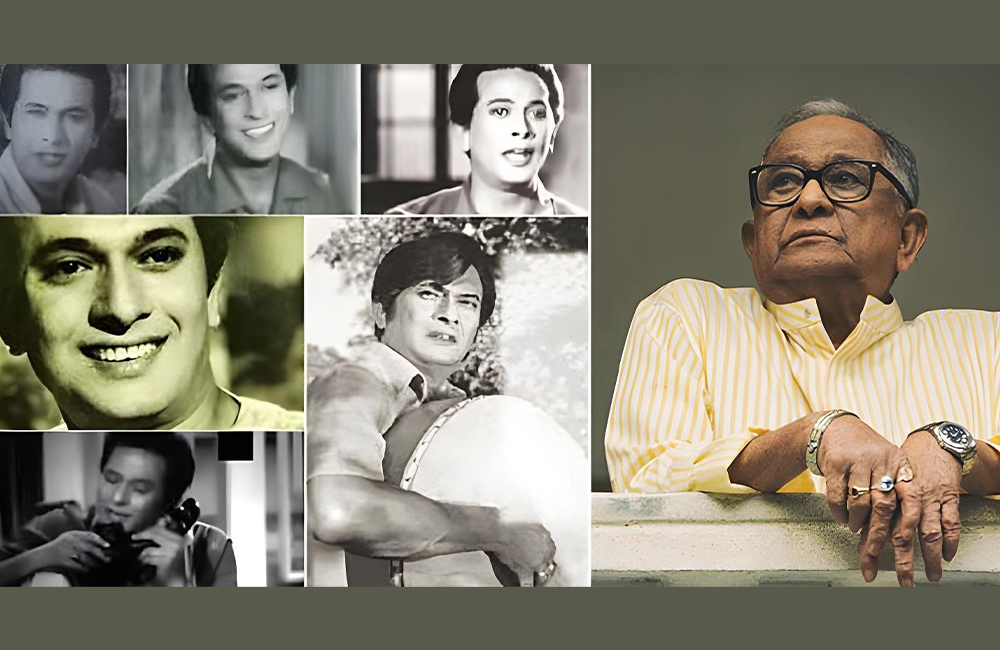


Leave a Reply
Your identity will not be published.