“সৌন্দর্যের দুটি ধরন আছে—একটি জন্মগত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত, আরেকটি অধ্যয়ন বা সাধনার ফল।
এই দুটির মিলন, এবং সেই মিলনের ফলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে, যা এক জটিল ও গভীর ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে—শিল্পসমালোচকের কর্তব্য হলো তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা।”
—পল গঁগ্যা
শুরুতেই একটা কথা বলে নেয়া ভালো। তিতা সত্য যত আগে মেনে নেব তত দ্রুত সমাধান কিংবা আরোগ্যের দিকে এগুনো যায়। তিতা সত্যটি হলো, শিল্প সমালোচনা ব্যাপারটা বাংলাদেশে সে অর্থে গড়ে ওঠে নি। সাহিত্য সমালোচক যে নেই, সেটা নিজের পঠন এবং চারপাশ থেকেই বারবার উপলব্ধি করেছি। আর শিল্পসমালোচক যে নেই তা একবাক্যে বলে দেওয়া যেত, যদি এ দেশে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম না-থাকতেন। এই একজন মানুষ তাঁর পঠনে, চর্চায়, লেখাতে প্রমাণ করে গেলেন, শিল্প সমালোচনার একটা বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার আজও খোলা আছে। অঙ্গুলিমেয় যে দুয়েকজন শিল্পসমালোচকের বইপত্র বাংলা ভাষায় পড়ি, তাদের জন্যও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন দিশারি। কারণ তাঁর তাত্ত্বিক প্রজ্ঞার পাশাপাশি, ভাষার দখল, গবেষকের গভীর নিষ্ঠা অন্যদের জন্য আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। তিনি শুধু শিল্পসমালোচক ছিলেন না ছিলেন নন্দনতাত্ত্বিক, শিক্ষক ও কথাসাহিত্যিক। এই সকল পরিচয় মিলে গঁগ্যা বর্ণিত ‘প্রবৃত্তি’, ‘অধ্যয়ন বা সাধনা’র সমন্বয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম হয়ে উঠেছিলেন ‘জটিল ও গভীর ঐশ্বর্য সৃষ্টি’ আবিষ্কার করার মতো দক্ষ শিল্পসমালোচক।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ’ গ্রন্থটি তাঁর শিল্প সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব চর্চার এক আদর্শ নমুনা। ২০১১ সালে প্রকাশিত হলেও বইটির যে সংস্করণ আমাদের হাতে আছে তা বেঙ্গল পাবলিকেশন্স থেকে ২০১৯ সালে প্রকাশিত। এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ তো আছেই, অন্যত্রও রবীন্দ্র শিল্পকলার কথা উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গেই। জয়নুল আবেদিনকে নিয়েও তিনটি প্রবন্ধ পাই। আরও পাই গগেনন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রাজা রবি বর্মার চিত্রকর্ম নিয়ে ভিন্ন প্রবন্ধ। এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, সার্ক চিত্রকলা প্রদর্শনীসহ একাধিক প্রদর্শনী ঘুরেও তিনি শিল্পকর্ম অধ্যয়ন করেছেন। তার দলিল-দস্তাবেজও এই বইতে বিদ্যমান। মূলত প্রাচ্য চিত্রকলার দিকেই এই বইয়ের টেক্সটগুলোর মনোযোগ। তিনি বারবারই চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে একটি মাইলস্টোন ধরে প্রাচ্য চিত্রকলার ঘরানাকে অনুসন্ধানের। সমান্তরালভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার একটা তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন। প্রসঙ্গতই ফ্রান্সিস বেকন, উইলিয়াম ব্লেইক, পিকাসো, ভ্যান গঘ প্রমুখের কথাও এসেছে। তবে এই বইয়ের দুটো লেখা নিয়ে আমি উল্লসিত, স্পর্ধিত বোধ করি। প্রথমত ‘উইলিয়াম ব্লেইক ও সুলতান’, দ্বিতীয়ত ‘চিত্রিত রিকশা : প্রান্তজনের শিল্প।’
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা এ দেশে সম্প্রতি শুরু হয়েছে একাডেমিকভাবেই। কিন্তু তুলনামূলক চিত্রচর্চার কথা আমরা শুনি নি। তুলনামূলক চিত্রচর্চা নিয়ে কথা বলার মতো ব্যক্তি যেমন দেখি নি, তেমন পরিবেশও তৈরি হয় নি। অথচ আরও এক যুগেরও অধিক কাল আগেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমাদের সুলতানের সঙ্গে উইলিয়াম ব্লেইকের মিল ও ফারাকগুলো তুলে ধরেন নিখুঁত শিল্পসমালোচকের দক্ষতায়। তাঁর বয়ান স্পষ্ট, “ব্লেইকের সঙ্গে সুলতানের আশ্চর্য কিছু সাদৃশ্য রয়েছে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে, যার গভীর তাৎপর্য এড়িয়ে যাবার মতো নয়। বরং চমৎকৃত হবার বিষয় ব্লেইক সম্বন্ধে রিড যা বলেছেন, তার অনেকটাই সুলতান সম্পর্কে সহজে বলা যায়। এই দুই শিল্পী কোথায় যেন অদৃশ্য কোনো সূত্রে গাঁথা—তাঁদের স্বপ্নে, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী ধূসর জগতে একই শরীরী ও অশরীরী কায়া ও ছায়ারা যেন ঘুরে বেড়ায়। উভয়েই তাঁরা ফিরে যান সৃষ্টির আদিতে, প্রথম পুরুষের কিংবদন্তির পৃথিবীতে, শক্তিশালী মানুষের গল্পে আর বর্তমানের জন্যে অতীত থেকে নিয়ে আসেন জীবন আর চঞ্চলতা, দ্রোহ আর গতিশীলতা, সৃষ্টি আর উল্লাসের বার্তা।” অবশ্য সাদা চোখে আমরাও খেয়াল করেছিলাম, উইলিয়াম ব্লেইক এবং সুলতানের মানুষের পেশিবহুল, শক্তিশালী কিন্তু তাদের ‘অশরীরী কায়া ও ছায়া’-র বিষয়টি সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের পক্ষেই আবিষ্কার করা সম্ভব। তেমনি সাদা চোখে আমরাও খেয়াল করেছিলাম, সচরাচর উইলিয়াম ব্লেইক এবং সুলতানের ক্যানভাস বিশাল আকৃতির কিন্তু তাদের ক্যানভাসে ‘সৃষ্টি ও উল্লাসের’ অনুসন্ধান করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এমনকি তিনি এমন সিদ্ধান্তও দিয়েছেন, “আমাদের শিল্পকলায় সবচেয়ে ধ্যানী, ারংরড়হধৎু চিত্রী এস এম সুলতান।” সুলতানকে ধ্যানী আর স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কীইবা বলতে পারি আমরা! আমি এই প্রবন্ধের সূত্র ধরেই বলতে চাই, আমাদের বাংলাদেশে তুলনামূলক চিত্রালোচনার জনক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। উদাহরণ দেই, “সুলতানের পুরুষেরা পেশিবহুল, নারীরা বিশাল স্তনের অধিকারী, শিশুরা বাড়ন্ত, ঘরবাড়ি গোছানো, ছিমছাম, গাছপালা সবুজ, আকাশ দিগন্তবিস্তারী। এই চিত্রায়ণে যে আদর্শবাদ কার্যকর তা অতীতবিহারী নয়, অনেক রোমান্টিক চিত্রীর মতো ভবিষ্যৎ নির্মাণকারী। ব্লেইকের ছবিতেও অতীত যত বেশি সাড়ম্বরে উপস্থিত, যত কিংবদন্তির পর্যায়ে বিলীয়মান সময় তত বেশি আশাবাদ সঞ্চারিত; কারণ অতীতের অখণ্ডতা আর পূর্ণতা, অনন্ত-সন্ধানী দৃষ্টি বর্তমানকে তুচ্ছ করে দেয়, বর্তমানের সীমাকে ভেঙে ভবিষ্যকে ঘটমান করে তোলে।” এটুকু পাঠের পড়ে সুলতান আর ব্লেইক সম্পর্কে পাঠককে নতুন করে ভাবতে হবে এবং বিস্ময়কর হলো, তারা দুজনই অতীতের যে ছবি এঁকেছেন, পুরাণ কিংবা কিংবদন্তির যে চিত্র রূপায়িত করেছেন তা যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেটুকু একজন সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের চোখ দিয়ে, বোধ দিয়ে আমরা অনুভব করি। আমার মুহূর্তে মনে পড়ে যায়, ১৭৯৫ সালে আঁকা ব্লেইকের ‘করুণা’ (Pity) আর সুলতানের আঁকা ১৯৭৫ সালের ‘প্রথম বীজ বপন’ (First Plantation) ছবি দুটোর কথা। প্রায় দুই শতাব্দীর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দুটো ছবির বিস্ময়ক ‘অনন্ত-সন্ধানী দৃষ্টি’ আমাকে তাড়িত করে। আমার এমনও মনে হয়, আরও দুই শতাব্দী পেরিয়ে সুলতান ও ব্লেইক আধুনিক থাকবেন, সমকালীন থাকবেন। সুলতানকে ব্লেইকের মতো দ্রষ্টা আর স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অথচ ২০১০ সালে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী’ শিরোনামের গ্রন্থে রফিক হোসেন নামের একজন সমালোচক বলছেন, “এদেশের মানুষ সুলতানকে প্রায় সাধু সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন। এর কারণ হলো একদিকে শিল্প সম্বন্ধে তাদের অস্পষ্ট ধারণা এবং অন্যদিকে সুলতানের ব্যক্তিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য। বস্তুত তার ভবঘুরে জীবন, অস্থিরতা, খামখেয়ালি মেজাজ, অন্যদিকে চিত্রকর্মের মধ্যে প্রায়ই হেঁয়ালিপনা সৃষ্টির চেষ্টা। এসব কিছু মিলিতভাবে তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, কেবল জনপ্রিয়তা, বাহ্যিক রূপ ও আচরণের উপর নির্ভর করে তার কাজের মূল্যায়ন করলে অবশ্যই ভুল করা হবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার কাজের চেয়ে সুখ্যাতি অধিক এবং বাস্তবতার চেয়ে ভান বেশি।” বাংলাদেশের চিত্রকলা সমালোচনার ভয়াবহ দৈন্য ধরা পড়ে কথিত সমালোচকের এই বক্তব্যে। শুধু এই মতামত দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি সরাসরি সুলতানকে সিজনোফ্রেনিক বলেছেন। চিত্র সমালোচনা, নন্দনচর্চা যে গভীর প্রাজ্ঞতার বিষয় তা আমরা যত দ্রুত বুঝতে পারব, তত সৃষ্টিমুখর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখতে পারব। এই প্রবন্ধটিতেই আমাদের চিত্রকলার একটা গভীর সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তাঁর বয়ানেই পাঠ করা যাক, “ব্লেইকের ছবিতেও চরিত্ররা—এবং ব্লেইক বাইবেল, খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, সৃষ্টিতত্ত্ব এসব থেকে চরিত্র ধার করেছেন—প্রতীকী অর্থে পুনর্নির্মিত হয়, এক একটি চিন্তাকে বিভিন্ন তল থেকে বিকশিত হবার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তবে ব্লেইকের যে স্বাধীনতা ছিল, সুলতানের তা নেই; আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে চিন্তাকে চিত্রাশ্রয়ী করার বিধান নেই।” চিত্রশিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে আজকের দিনে কথা বলার স্বাধীনতাও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে উঠছে। চিত্রশিল্প না-থাকলে কিংবা সংকুচিত হতে থাকলে, শিল্প সমালোচনা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।
মার্শাল দ্যুশাম্প একটা ইউরিনালকে বিশ্বসেরা শিল্পকর্মের তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিলেন, এন্ডি ওয়ারহল স্যুপের বোতলের ডিজাইন কিংবা মেরিলিন মনোরোর প্রিন্টকে বিশ্ব দরবারে হাজির করেছিলেন পপ আর্টের নিদর্শন হিসেবে। ফাউন্ড আর্ট, ফোক আর্ট, পপ আর্টের দিকগুলোকে এখনো যেন আমাদের মূলধারার শিল্প সমালোচনায় আনা হয় না। আমাদের চোখের সামনে একটা জীবন্তু শিল্পকলা হিসেবে ঘুরপাক খায়, প্রতিনিয়ত রিকশা নামের বাহন। এই বাহন শিল্পকলা বা ট্রান্সপোর্ট আর্ট ফর্ম তো আসলে একটা চলমান শিল্প। কিন্তু আমাদের ব্রাত্য শিল্প সমালোচকরা রিকশাচিত্র নিয়ে একটা সময়ের আগে কথাই বলেন নি। এনজিওর ফান্ড, বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণের আগে এ নিয়ে কথা বলা খুব একটা ফায়দার ছিল না। কিন্তু একজন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম দায়িত্বশীল শিল্পসমালোচক হিসেবেই লিখেছিলেন ‘চিত্রিত রিকশা প্রান্তজনের শিল্প’ প্রবন্ধটি। রিকশা আর্টের সূচনা থেকে শুরু করে একটা সম্ভাব্য জরিপের হিসাব তো দিয়েছেনই তারচেয়েও বড় কথা তাঁর অপূর্ব বর্ণনাশৈলীতে তিনি এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, “শরীরে আর্ট না থাকলে রিকশার পরিচিতিটা তৈরি হয় না। আরও বলা যায়, শিল্পের শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে অসম্ভব শৃঙ্খলাহীন রাস্তাঘাটের তুলকালাম রাজ্যে তারা একটি নান্দনিক শিল্প পাঠাচ্ছেন, যেমন মানুষ সবচেয়ে ঘিঞ্জি বস্তিতে তাদের ছাপরা ঘরের গায়ে মাধবীলতা জড়িয়ে দেয়। এ হচ্ছে শিল্পের অনিবার্যতার প্রতি আদিম সাড়া, আর আস্থা জ্ঞাপন।” এ তো শুধু শিল্প সমালোচনা নয়, এ কথা যেন জীবন দর্শন। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনেও শিল্পকে দেখার নয়া কৌশল বাতলে দিয়েছেন একজন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। একজন এণ্ডি ওয়ারহল কিংবা মার্শাল দ্যুশাম্পের দেশে জন্মালে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম হয়তো একজন দেনিস দিদেরো কিংবা জিওর্জিও ভাসারির সম্মান পেতেন।
এত এত কীর্তি আর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরও সম্মান এ দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পান নি বলা যায়। আমাদের ক’জন শিক্ষিত মানুষ জানেন যে বিপুল সাহিত্য ভান্ডারের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবি এঁকেছেন অন্তত আড়াই হাজার ? ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি’, ‘রবীন্দ্রনাথের রেখা ও রং’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি’ শিরোনামের লেখা তিনটিতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি পূর্বোল্লেখিত ‘উইলিয়াম ব্লেইক ও সুলতান’ প্রবন্ধেও তিনি লিখছেন, “সত্য যে, কবি ব্লেইক অনেক বেশি শক্তিশালী চিত্রী ব্লেইকের চাইতে, কিন্তু তাঁর বিশাল কল্পনাপ্রতিভার কতটুকু পরিচয়ই-বা তাঁর কবিতা দিতে পারে! রবীন্দ্রনাথের মতো অত্যাশ্চর্য তাঁর চিত্রকলা, এক সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ নির্মাণকারী, যে জগতে প্রবেশের শর্ত সম্পূর্ণভাবে তারাই আরোপ করে।”
‘অত্যাশ্চর্য’ চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখছেন, “ফ্রয়েড-উত্তর বিশ্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যার যে বিস্তৃতি, তা মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তমুক্তির একটি আয়োজন যে তাঁর চিত্রকলায় হয়েছিল এক ভিন্ন পরিবেশে, পরিমণ্ডলে, সেটুকু বলা যায়।” রবীন্দ্র চিত্রকলা যে তাঁর বহুল পরিচিত সাহিত্যকর্মের পরিমণ্ডল থেকে একেবারেই আলাদা সেটা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে মৃত্যুর মহা সমারোহ দেখেছিলেন। তার লেখাতেই পাই, ‘মরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান’। অন্য লেখায় বলছেন,
‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে—
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।”
কিন্তু রবীন্দ্র চিত্রকলায় মৃত্যু এসেছে অন্য ভঙ্গিমায়। ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি’ প্রবন্ধে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখছেন, “মৃত্যুর অনিশ্চয়তা, রহস্য, মৃত্যুর পরপারে শূন্যতা অথবা পূর্ণতর জীবন—এইসব ভাবনার একটি হদিস তিনি চিত্রকলায় চেয়েছেন। সাহিত্য তাঁকে মায়া থেকে আরও অধিক মায়াতে নিয়ে গেছে, মৃত্যুর কোনো সমাধান তিনি করতে চান নি সাহিত্যে, কিন্তু চিত্রকলার অবচেতনের দরজাগুলি খুলে দিয়ে তিনি মৃত্যুকে যেন আহ্বান জানান; সে এলে তার রূপটি তিনি নিকট থেকে দেখতে পাবেন, সে আশায়।” এই আলোচনায়, শুধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন নয়, বরং সাহিত্য ও চিত্রকলার মাধ্যমগত প্রকাশভঙ্গির একটা তুলনামূলক ইশারাও পাই। কবি ও চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেইকের মতোই চিত্রকর ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে একটা তুলনামূলক মানদণ্ডে ফেলে শিল্প-সাহিত্যের দিগন্তটাকে পরখ করে নিতে চান সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। একই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, “রবীন্দ্রনাথের ছবিতে নারীমূর্তিগুলি এক আশ্চর্য সহজ স্বাধীনতায় বিচরণ করে, যা তাঁর সাহিত্যের নারীরা করতে অপারগ। এই মুক্ত এবং অবাধ বিচরণ আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিলাষের প্রকাশ। এ বিচরণ তাঁর ইচ্ছার, তাঁর নিজের চিন্তার প্রতিকল্পের। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার নারীরা সুশ্রী নয়, কুশ্রীই বটে, প্রায়শই। চিত্রাঙ্গদার সুরূপা-কুরূপা দ্বন্দ্বের কথা আমরা জানি, কিন্তু চিত্রকলার নারীরা আরও গভীরতাপ্রয়াসী।”
‘রবীন্দ্রনাথের রেখা ও রং’ প্রবন্ধে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, তাঁর কবিতা থেকেও, অনেক বেশি ব্যাখ্যার স্বাধীনতা দেয় আমাদের; তাদের প্রতীকী জগতটি অনেক বেশি প্রসারিত, অনেক বেশি অস্বচ্ছ। চিত্রসমালোচকদের পরিশ্রম বেড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিচিত্র সব ফর্ম ও ফিগারের বাহুল্যে, তাদের অন্ধকার, নিষ্কৃতিহীন উপস্থিতির কারণে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আছে অশুভ, আছে অমঙ্গলের আভাস, আছে স্বস্তিহীন নানা বিষয়-আশয়। এসব পড়তে হয় অভ্যাসের বাইরের কোনো পঠন-ব্যাকরণ থেকে।” লিখিত ভাষার মতো, মৌখিক ভাষার মতো রং ও রেখার যে ভাষা চিত্রকলার নিজস্ব বয়ান তৈরি করে তা পাঠ করতে আমাদের উৎসাহী করেন একজন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। শুধু তাই নয়, তিনি শিল্প সমালোচনার যে মানদণ্ড ‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ’ গ্রন্থে তৈরি করেছেন তাতে করে আমি বলব, নিশ্চয়ই অন্য ‘চিত্রসমালোচকদের পরিশ্রম বেড়ে গেছে’।
‘রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি’ শিরোনামের প্রবন্ধে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অনেকটা আক্ষেপ করেই লিখেছেন, “তাঁর কবিখ্যাতির জন্য চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা ঔদাসীন্যই লক্ষ করা গেছে।” আমিও এই লেখার শেষে এসে বলতে চাই, বিখ্যাত অধ্যাপক, গল্পকার সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিল্পচিন্তার প্রতি যেন আমরা কখনো ঔদাসীন্য না-দেখাই।
সূত্র : রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ, সৈয়দ মনজরুল ইসলাম, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৯।
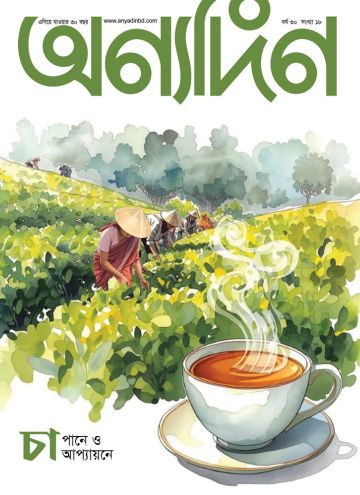





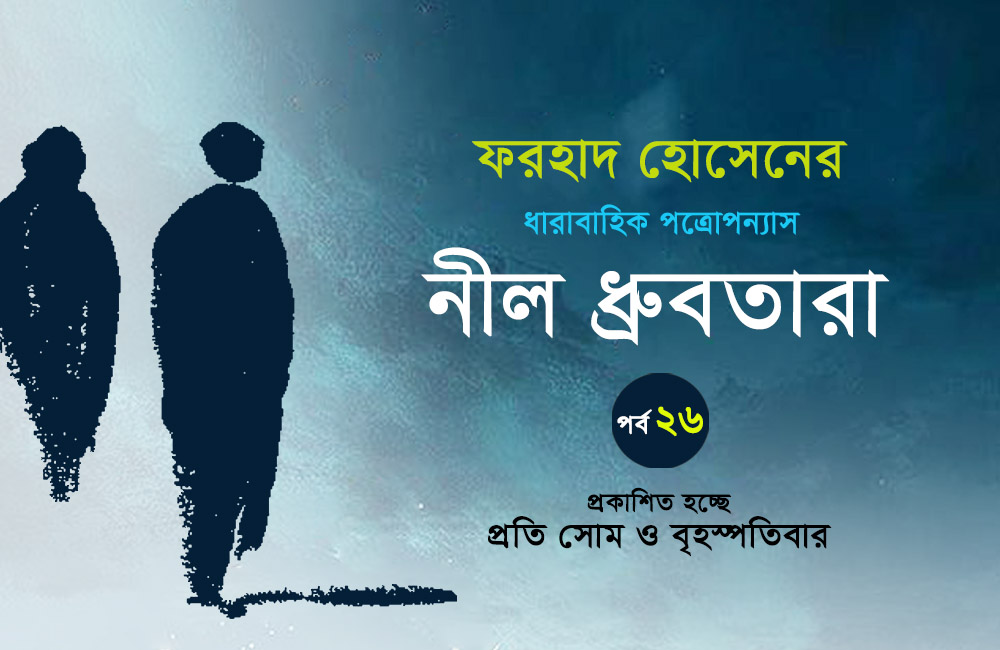








Leave a Reply
Your identity will not be published.