স্বনামধন্য ভ্রমণলেখক, গল্পকার, অনুবাদক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক ফারুক মঈনউদ্দীন। তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণগদ্য ‘মরু গুহা ও দ্বীপের গল্প’-এর তৃতীয় পর্ব প্রকাশ হলো আজ।
প্রথম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন
দ্বিতীয় পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন
ছাত্রাবস্থায় লোকাল ট্রেন বা বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা হয় নি, এমন মধ্যবিত্ত সন্তান বিরল। কলেজের হোস্টেলে সিট পাওয়ার আগপর্যন্ত কিছুদিন সকালবেলায় ডেলি প্যাসেঞ্জার আর ভিক্ষুক বোঝাই করে ফেনী শাটল নামের যে ট্রেনটি চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেত, সেই ট্রেনে চড়ে কলেজে হাজিরা দিয়েছি বহুদিন। স্থানীয় লোকজন মজা করে এই ট্রেনের নাম দিয়েছিল ‘ফইন্নির ট্রেন’ অর্থাৎ ফকিরনিদের ট্রেন। ফেরার সময় প্রায়ই আসতে হতো শুভপুরের লোকাল বাসে। কারণ, চট্টগ্রাম থেকে ফেনী বা নোয়াখালীর লংরুটের বাসে আমরা লোকালরা ছিলাম অন্ত্যজ শ্রেণির যাত্রী। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর হলে সিট পাওয়ার আগে কয়েক মাস শ্যামলী থেকে গাবতলী-গুলিস্তান রুটের লোকাল বাসে চড়ে নীলক্ষেত নেমে তারপর ক্লাস ধরতে হতো।

এইসব অভিজ্ঞতা প্রায় যখন ভুলতে বসেছি, তখন এ রকম লোকাল সার্ভিসের দেখা পাওয়া গেল আকাশপথে। আমাদের গন্তব্য উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ। এক কাকভোরে ঢাকা থেকে উড়ান দিই বাংলাদেশ বিমানে, সেটি প্রথমে চলে যায় চট্টগ্রাম, এটি ছিল আমাদের জন্য এক ‘বিপন্ন বিস্ময়’, কারণ, ফ্লাইটটি প্রথমে চট্টগ্রাম যাবে জানার পর আমাদের কিছুই করার ছিল না। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের রানওয়েতে আমরা প্লেনের পেটের মধ্যে বসে থাকতেই সেখান থেকে যাত্রীরা ওঠে। বলা বাহুল্য, সব সময়ের মতো কয়েকজন পরিচিত যাত্রীর দেখা মিলে যায় এখানে। তাঁরা কলকাতাগামী এই ফ্লাইটে আমাদের অপেক্ষমাণ দেখে অবাক হলেও কিছু বলেন না। অবশেষে ঠিক সময়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে যাত্রা করে বিমান নির্ধারিত সময়েই কলকাতা নামিয়ে দেয় আমাদের। বিমানও যে কাঁটায় কাঁটায় শিডিউল রক্ষা করতে পারে, তার প্রমাণ পেয়ে অবাক হই।
কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা যাত্রাবিরতির পর ধরতে হয় দিল্লিগামী ফ্লাইট। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছাই তখন শেষ বিকেলের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। হোটেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সে রাত দিল্লিতে পার করে পরদিন দুপুরের পর দিল্লি থেকে আবার চড়তে হয় তাসখন্দগামী ফ্লাইটে। অবশেষে তাসখন্দ পৌঁছা গেল সেদিন সন্ধ্যার পর। ছত্রিশ ঘণ্টার এই দীর্ঘ ও ভাঙা ভাঙা যাত্রাপথের বর্ণনা এত সহজে লিখে ফেলতে পারি, কারণ, সিল্ক রুটের একটি অংশে প্রথমবারের মতো পা রাখার উত্তেজনা দীর্ঘ এই যাত্রার ক্লান্তিকে মুছে দিয়েছিল। উল্লেখ করা দরকার, তাসখন্দ নামের অর্থ ‘পাথর নগরী’, এই নামটি প্রথম ব্যবহার করে তুর্কিরা। বিখ্যাত সিল্ক রুটের সংযোগস্থল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এক নগরী হিসেবে উঠে আসে তাসখন্দ এবং পরিণত হয় মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী নগরীতে।

তাসখন্দ এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে আসে স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্টের দুই প্রতিনিধি মোহাম্মদ ও আলিশের বাইসভ। উল্লেখ্য, নায়কোচিত চেহারার যুবক আলিশের নিজেই এই এজেন্সির মালিক। স্বয়ং মালিক এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে এসেছেন দেখে আমরা যারপরনাই অবাক। আমাদের গন্তব্য আমির তিমুর স্ট্রিটের ওপর দাঁড়ানো সিটি প্যালেস হোটেল। হোটেলের লবিতে ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়। লবির দুপাশ দিয়ে তিনতলা সমান উঁচু দুই থাম, তার একটিকে লতার মতো পেঁচিয়ে ধরে সিঁড়ি উঠে গেছে মেজনাইন ফ্লোর পর্যন্ত। আরেকটি নিঃসঙ্গ থাম ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। দুটো থামের গায়েই টাইলসের ওপর জ্যামিতিক নকশা আর ফুলের কারুকাজ। লবির অন্য দেয়ালগুলোতেও ময়ূরকণ্ঠী নীলপ্রধান একই ধরনের নকশা। পরে ঠিক এ রকম নকশার কারুকাজ দেখতে পাই বুখারা ও সমরকন্দের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্যে। ভবনটির আধুনিক স্থাপত্যের ভেতর এ রকম প্রাচীন অন্তঃসাজ প্রত্যাশার অতীত।
হোটেলে চেক ইন করার আনুষ্ঠানিকতা সারার পর আমাদের রাতের খাবার খেতে নিয়ে যায় আলিশের। হোটেল থেকে বড় রাস্তায় নামার পর মাথার ওপর ছোট ছোট বাতির সাজসজ্জা দেখে মনে হয় কোনো বিশেষ উপলক্ষে এই আলোকসজ্জা। আলিশেরকে মজা করে জিজ্ঞেস করি, এই আয়োজন কি আমাদের সম্মানে? ও জবাবে বলে, সেটা আমরা ভাবলেও ভাবতে পারি, কারণ, কোনো বিশেষ উপলক্ষ নয়, এই আলোকসজ্জা নগরীর নৈশশোভা বর্ধনের জন্যই। কাছাকাছি যে রেস্তোরাঁয় আমাদের খেতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটিতে রাতের এই প্রহরেও জনসমাগম দেখে বোঝা যায় খুব মশহুর ওটা। ওসব দেশে ডিনার সারা হয় সন্ধ্যার পরপরই। খাওয়া শেষে যখন আমরা বের হয়ে আসি, তখন প্রায় সব টেবিলই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আমাদের দেশের রেস্তোঁরাগুলোর মতো টেবিলের ওপর উল্টো করে তুলে রাখা হয়েছে চেয়ারগুলো। বাইরের ৪ ডিগ্রি ঠান্ডায় সামনের চত্বরটায় কিছুক্ষণ যে চড়ে বেড়াব, সে উপায় নেই।
তাসখন্দে যাওয়ার আগেই ভেবে রেখেছিলাম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিখ্যাত তাসখন্দ চুক্তিটি যেখানে হয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখতে যাব। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধটি ১৭ দিনের বেশি চলে নি, এর মধ্যে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে। অথচ এই যুদ্ধের প্রায় তিরিশ বছর আগে মুসোলিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়া (বর্তমানের ইথিওপিয়া) দখল করে নিলেও বর্তমান জাতিসংঘের মতো ঠুঁটো জগন্নাথ তখনকার লিগ অভ নেশনস কিছুই করতে পারে নি। যা-ই হোক, পাক ভারতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও পরবর্তী সময়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই কোসিগিনের উদ্যোগে তাসখন্দ শহরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরের রাতেই শাস্ত্রীকে হোটেলের রুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আকস্মিক এই মৃত্যুকে অনেকেই স্বাভাবিক মনে না করলেও এটি অপমৃত্যু ছিল কি না, তার সুরাহা হয় নি আর। যে সোভিয়েত নেতা কোসিগিন এই চুক্তির উদ্যোক্তা ও সাক্ষী ছিলেন, পরদিন তাঁকে ভারতীয় দূতাবাসের শোকবইতে স্বাক্ষর করতে হয় এবং শবানুগমন করে যেতে হয় বিমানবন্দর পর্যন্ত।
কিশোর বয়সের দেখা সেই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের জায়গাটি নিয়ে আমাদের চার ভ্রমণসঙ্গীরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। গুগলে অনেক খুঁজেও জায়গাটার হদিস পাই নি, আলিশেরকে জিজ্ঞেস করলে ও মাথা চুলকে সেখানেই জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করে। বুঝতে পারি জন্ম ষাটের দশকের পরে বলে দুই বিদেশি যুদ্ধবাজ নেতার চুক্তির খবর এদের জানা নেই। আমরা ওকে বলি বয়স্ক কাউকে জিজ্ঞেস করে যাতে আমাদের জানায়। আমাদের উজবেকিস্তানে থাকা অবধি বয়স্ক কোনো লোককে ও খুঁজে পায় নি বলেই মনে হয়।

তাসখন্দ চুক্তির ঐতিহাসিক জায়গাটা বের করতে না পারলেও আরও প্রাচীন একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখানোর ব্যবস্থা ছিল আমাদের ভ্রমণসূচিতে। ঝকঝকে রোদের মধ্যে আমরা যেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নামি, সেটি এক চমৎকার স্থাপত্যমণ্ডিত মসজিদ চত্বর। বরফশুভ্র দেয়ালের গায়ে পরিমিত নীল লতাপাতার নকশা, তার পাশে দীর্ঘ মিনার, ফিরোজা রঙের গম্বুজ—সবকিছু এতটাই পরিচ্ছন্ন, যেন মনে হয় মাত্র গতকাল শেষ হয়েছে মিনর মসজিদ নামে পরিচিত এই স্থাপনার কাজ। প্রকৃতপক্ষেই মসজিদটি একেবারেই আনকোরা নতুন, মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ২০১৪ সালে এটির উদ্বোধন করা হয়। সে কারণে এর সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিংবদন্তির গল্প জড়িত নেই। প্রাচীন স্থাপত্যের মসজিদগুলোর সঙ্গে এটির কোনো মিলও নেই। এর শ্বেতপাথরের দেয়াল পুরো আবহে ছড়িয়ে দিয়েছে এক পবিত্রতার আমেজ। প্রখর সূর্যালোকে এই শুভ্রতা আরও বেশি ঝকঝক করে যেন। দুপাশে দুটো দীর্ঘ মিনার মেঘমুক্ত নীলাকাশের দিকে তর্জনী তুলে দাঁড়ানো, মূল মসজিদের ওপর একটা আকাশি নীল গম্বুজকে দূর থেকে ওলটানো এক বিশাল গামলার মতো দেখায়। উঁচু তোরণের গায়ে শ্বেতপাথরের ওপর লতাপাতার কাজ। মেহরাবের মতো ভেতর দিকে অবতল অংশের শীর্ষে প্রাচীন যুগের সাংকেতিক চিহ্নের মতো নানান নকশা আঁকা। তার ওপরের চাঁদওয়ারিতে কোরানের দীর্ঘ আয়াত উৎকীর্ণ। তোরণের পায়ের কাছের বেমানান কাঠের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রশস্ত চাতাল, তার দুপাশে টানা বারান্দার মতো করিডর। বিপরীত প্রান্তে মসজিদে ঢোকার প্রায় একই ধরনের নকশাশোভিত একই উচ্চতার আরেকটি তোরণ। সেটির মাঝখানের মূল কাঠের দরজাটি কেবল মহিলা নামাজি ও দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষিত, দুপাশে দুটো করে আরও চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা, সেগুলো পুরুষদের জন্য। প্রায় আড়াই হাজার মানুষ একসাথে নামাজ পড়তে পারে এই মসজিদে। ভেতরে গম্বুজের বিশাল ঘেরের নিচে প্রশস্ত হলরুম, হলরুমের দেয়ালজুড়ে মেঝে থেকে উঠে যাওয়া দরজার দ্বিগুণ উচ্চতার বিশাল সব জানালা গলে ঢুকছে দিনের আলো। গম্বুজের ঘেরজুড়ে নকশার সুষম কাজ, তার ওপরের অংশে বাঁকানো খিলানের গবাক্ষের বৃত্তাকার সারি, সেখান থেকেও ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ দিবালোক। গম্বুজের ছাদের তলার কেন্দ্রটি সূক্ষ্ম নকশায় পরিপূর্ণ। কেবলামুখী মেহরাব সোনার গিল্টিকরা নকশা আর আরবি ক্যালিগ্রাফিতে পরিমিতভাবে সাজানো।
মসজিদটির নাম মিনর মসজিদ হলেও এটি ‘শ্বেত মসজিদ’ নামেও পরিচিত। হোটেল থেকে রওনা হওয়ার সময় গাইড মোহাম্মদ যখন জানায় আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্স, ভেবেছিলাম তুষারশুভ্র এই মসজিদটিই খাস্ত ইমাম। অবশ্য এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্সে পৌঁছার পর সে ভুল ভাঙে। কমপ্লেক্সটির পোশাকি নাম খাজরাতি ইমাম। এখানে আছে বারাক খান মাদ্রাসা, তিল্লা শেখ মসজিদ, মুয়ি মুবারক মাদ্রাসা, কাফফাল শাশির মাজার ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এই কাফফাল শাশির পুরো নাম আবু বাকার আল-কাফফাল আল-কাবির আশ-শাশি। তাঁর ছিল কোরান, হাদিস ও ইসলামি আইন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। তিনি কবি ও গীতিকার এবং ব্যতিক্রমীভাবে ছিলেন এক দক্ষ তালার কারিগর (কাফফাল), তাই তাঁর নামের সঙ্গে আল-কাফফালও যুক্ত হয়েছে। ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর প্রায় সাত শ বছর পর তাঁর কবরের ওপর তৈরি দরগা পরিণত হয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তীর্থভূমিতে।
খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্সের তিল্লা শেখ মসজিদের সামনে দিয়ে বেশ কিছুদূর হেঁটে গেলে মুয়ি মুবারক মাদ্রাসা ও কুতুবখানা, যেখানে রক্ষিত আছে হজরত উসমান (রা.)-এর সময়ে তাঁর হাতে লেখা কুফি কোরানের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির একটি। কুফি হচ্ছে আরবি হরফের প্রাচীনতম রূপ, যা সপ্তম শতাব্দীতে কুফা নগরে প্রবর্তিত হয়। এটি যখন উজবেকিস্তানে আসে, তখন ধারণা ছিল যে এটিই কোরানের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি। কিন্তু গবেষকদের মতে এটি লেখা হয়েছিল অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে। কিন্তু হজরত উসমান (রা.) নিহত হয়েছিলেন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে, সুতরাং গবেষকদের ধারণা যদি সঠিক হয়, এটি তাঁর হাতে লেখা, এমনকি তাঁর আমলের হওয়াও সম্ভব নয়। কিংবা যদি সত্যিই তা-ই হয়, তাহলে গবেষকদের ধারণা ভুল। তবে এই বিতর্ক বা বিভ্রান্তির সুরাহা করা এখানে সম্ভব নয়।
ইস্তাম্বুলের তোপ কাপি প্রাসাদের জাদুঘরেও এ রকম প্রাচীন কোরানের একটা পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটির ছবি তুলতে গেলেই প্রহরীরা ‘রে রে’ করে ছুটে আসে। এটিকেও প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি বলে দাবি করা হয়, গবেষকেরা এখানেও বাগড়া দিয়ে বলেছেন, এটি প্রাচীনতম না হলেও উসমানিয়া কোরানের চেয়ে অন্তত এক শতাব্দী আগের।

কোরানের প্রাচীনতম সংস্করণ নিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সে হিসেবে ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির দুটি পাতাই এযাবৎ পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন সংস্করণ বলে মনে করা হয়। কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা করা হয়, চামড়ার তৈরি পাতায় এটি লেখা হয়েছে ৫৬৮ থেকে ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে। কালের হিসাবে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় পাওয়া চামড়ার তৈরি কাগজে দুই পাতার পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয় প্রাচীনতম বলে গবেষকদের মত। মনে করা হয়, এটি লেখা হয়েছে ৬৪৬ থেকে ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। গবেষকদের হিসাবে তোপ কাপি প্রাসাদে রক্ষিত কোরানের পাণ্ডুলিপিটি ৭৬৫ থেকে ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছে। এটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি হলেও দুটো পৃষ্ঠা নেই। সে হিসেবে তাসখন্দে আমাদের দেখা পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ প্রাচীনতম কোরান।
পরবর্তী পাণ্ডুলিপিটা একসময় রক্ষিত ছিল মিসরের আমর ইবনে আস মসজিদে। নেপোলিয়নের মিসর জয়ের পর এটি দুই অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্যারিসে চলে আসে। একাংশ নিয়ে আসেন নেপোলিয়নের সঙ্গে যাওয়া শিল্পবিশারদ জাঁ জোসেফ মার্শেল। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছিলেন সে সময় কায়রোতে ফরাসি ভাইস কনসাল হিসেবে কর্মরত জোঁ লুই শেরভিল। এই দুই অংশ এঁদের উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন সময়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছড়িয়ে আছে ফ্রান্সের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ভ্যাটিকান লাইব্রেরি এবং লন্ডনের খলিলি কালেকশনে। পরবর্তী সংস্করণের পাণ্ডুলিপিগুলোও যথাক্রমে রক্ষিত আছে তিউনিসের বারদো জাতীয় জাদুঘর, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে চেস্টার বেটি লাইব্রেরি এবং জার্মানির মিউনিকের ব্যাভারিয়ান স্টেট লাইব্রেরিতে।
মুয়ি মুবারক কুতুবখানায় ঢোকার সময় টিকিট কিনতে হয়, তবে সেসব গাইড মোহাম্মদের মাথাব্যথা। মূল দরজার মুখে জুতা খুলে রেখে ঢুকতে হয়। বড় হলরুমের মাঝখানে উঁচু বেদির ওপর কাচের বড় কাসকেডের ভেতর মেলে রাখা বিশাল পাতাজুড়ে ভারী হরফে লেখা বারো শ বছরের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থটি দেখে যে অনুভূতি হয়, সেটি ছাপিয়ে অনুভব করি এটি কেবল প্রাচীন একটি পাণ্ডুলিপিই নয়, বিশ্বাসী মানুষের কাছে পরম আবেগ ও সম্মানের। হরিণের চামড়ার কাগজে লেখা ৩৫৩ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপির পাতার ওপর রয়েছে রক্তের দাগ, প্রচলিত ধারণা ছিল, এই কোরান পাঠরত অবস্থায় হজরত উসমানকে (রা.) হত্যা করা হয়। কিন্তু গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী এটির যে বয়স, তাতে বোঝা যায় এটি লেখা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। সুতরাং রক্তের দাগের উৎসটিও অমীমাংসিত। গাইড মোহাম্মদ আমাদের জানায়, এই পাণ্ডুলিপি থেকে অনেকগুলো পাতা খোয়া গেছে।
এযাবৎ পাওয়া তথ্যমতে উসমানিয়া কোরানটি রক্ষিত ছিল বাগদাদে। সেখান থেকে সমরকন্দে আসার বিষয়টি অস্পষ্ট। হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ (১২৫৮), পাইকারি হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাটের সময় মঙ্গোল সৈন্যরা মসজিদ, প্রাসাদ, হাসপাতাল লাইব্রেরি—কিছ্ইু বাদ দেয় নি। বাগদাদের ছত্রিশটি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অমূল্য বইগুলো ছিঁড়ে সেগুলোর চামড়ার মলাট দিয়ে তারা চপ্পল বানায়। বাগদাদের গ্র্যান্ড লাইব্রেরিতে ছিল অগণিত ঐতিহাসিক দলিল এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থরাজি। সেসব ধ্বংস করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে জানায় টাইগ্রিস নদীর পানি ফেলে দেওয়া বইয়ের কালিতে কালো এবং হত্যা করা বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের রক্তে ছিল লাল। সেই ডামাডোলে পাণ্ডুলিপিটি ইরাকের কোনো নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান রক্ষা করেছিলেন হয়তো। তা না হলে তৈমুর লং পাণ্ডুলিপিটি ইরাক থেকে সমরকন্দ নিয়ে এসেছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তার কোনো ভিত্তি থাকে না। এটি সমরকন্দের মসজিদেই রক্ষিত ছিল প্রায় চার শ বছর। ১৮৬৮ সালে সমরকন্দ রাশিয়ান সাম্রাজ্যের করতলগত হয়। এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটির কথা জানতে পেরে জেফারশানের জেলা প্রশাসক জেনারেল আব্রামভ মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে এটিকে তাসখন্দ পাঠিয়ে দেন। পরের বছর গভর্নর জেনারেল ভন কাউফম্যান এটি পাঠিয়ে দেন সেন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন পাণ্ডুলিপিটি রাশিয়ার বাশকর্তোস্তানের মুসলমানদের দান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে এটির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হয় উজবেকিস্তানকে ।

মুয়ি মুবারক কুতুবখানার ভাবগম্ভীর পরিবেশে অতি সন্তর্পণে কাচের বাক্সটির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। নিজেদের মধ্যে কথাও বলি ফিসফিস করে, এটা কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু এমন জায়গায় গেলে আপনা থেকেই গলা নিচু হয়ে আসে, হাঁটা হয় পা টিপে টিপে। কাসকেডের ভেতর বিশাল গ্রন্থটির পাতায় পাতায় হাতে লেখা ঐশী বাণী দেখে নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করা লেখকের নিষ্ঠার প্রতি নিজের অজান্তে মাথা নুয়ে আসে। ঘরটির এক কোণে চেয়ারে বসে সতর্ক চোখে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে এক নিরাপত্তাকর্মী। আমরা কিছু সময় কাচের বিশাল বাক্সটির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সরে আসি। লোকটির দৃষ্টি এড়িয়ে একখানা ছবি তোলার সাহস করি না। তুলতে পারলেও কাচের বাধার কারণে ভালো ছবি আসবে না জানি। গুগলে গেলে বরং এই পাণ্ডুলিপির অনেক ছবি পাওয়া যাবে। পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট রুমে ঢুকলে দেখা যায় কাচের শোকেসের ভেতর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কোরান সাজানো আছে দর্শনার্থীদের জন্য। বাংলা একটা কোরানও সেখানে থাকার কথা, কিন্তু চোখে পড়ে নি।
মুয়ি মুবারক কুতুবখানার পেছনে খাস্ত ইমাম মসজিদের সুদৃশ্য ভবন, তার দুপাশে দুটো উঁচু মিনার, ভেতরের পাশে দুটো ফিরোজা রঙের গম্বুজ। এই মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে, ২০০৭ সালে। ভেতরের স্তম্ভগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে ভারত থেকে আনা চন্দন কাঠ, তুরস্কের সবুজ মার্বেল পাথর, ইরানের নীল টাইলস।
সামনের খোলা বাঁধানো চত্বরের উল্টো পাশে ষোড়শ শতাব্দীর বারাক খান মাদ্রাসা ও মসজিদ। মূল প্রবেশদ্বারটি বুখারা সমরকন্দের বিভিন্ন মাদ্রাসার মতো বিশাল উঁচু পোড়া ইটের তৈরি, তার ওপর বর্ণিল জ্যামিতিক নকশা, চাঁদওয়ারিতে গাঢ় নীল পটভূমিতে লতানো ফুলের কারুকাজ। ভেতরের অবতল প্রকোষ্ঠে ইসলামি স্থাপত্যের নিদর্শন বাঁকানো খিলানের দুইতলা কুলঙ্গি। মাঝখানের মূল দরজার ওপর জাফরি কাটা গবাক্ষ। ফটকের দুপাশে দুটো নীল রঙের গম্বুজ। ভেতরে ঢুকলে আরেক প্রস্ত চাতাল পার হয়ে কেন্দ্রের মূল প্রশস্ত ঘরটিতে নানান স্যুভেনিরে ঠাসা দোকান। ঢোকার মুখেও সাজিয়ে রাখা উজবেকিস্তানের ট্র্যাডিশনাল হস্তশিল্পের নানান পণ্য, পেইন্টিং, পোশাক। ভেতরের বিভিন্ন পণ্য দেখে আমরা যখন ওদের সঙ্গে দর-কষাকষি করি, তখন গাইড মোহাম্মদ আমাদের কানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে যায়, এখান থেকে কিছু না কেনাই ভালো, অনেক দাম নেবে। আপনাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাব, সেখান থেকে কিনতে পারবেন। মোহাম্মদের এই উপদেশের পর থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস পছন্দ হওয়ায় কিনতে মনস্থ করার পরও সেগুলোর দাম অহেতুক রকম বেশি মনে হতে থাকে। তাই দর কষাকষি করে নামিয়ে আনা দামেও সেসব আর কেনা হয় না।
বারাক খান মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে প্রশস্ত চত্বর পেরিয়ে খাস্ত ইমাম মসজিদের পাশ দিয়ে আসার সময় এক স্বর্ণকেশী দীর্ঘাঙ্গী তরুণী আমাকে পাকড়াও করে। তার সঙ্গে এক যুবক ট্রাইপডের ওপর ভিডিও ক্যামেরা তাক করে ছবি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তরুণী আমার সঙ্গে কিছু কথা বলার অনুমতি চাইলে ওর রূপ দেখে সাগ্রহে রাজি হয়ে যাই। জানা যায় মেয়েটি প্যালেস্টাইনি কোনো টেলিভিশনের জন্য উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক জায়গাগুলোর ওপর একটা ডকুমেন্টারি বানানোর কাজ করছে। এই ঐতিহাসিক জায়গায় আমরা কী কারণে এসেছি, সেটাই দেখানোর চেষ্টা করবে ও এই ডকু দিয়ে। উজবেকিস্তান ভ্রমণের ওপর আমি ভ্রমণকাহিনি লিখব জানার পর ওর উৎসাহ বেড়ে যায়। সঙ্গী ক্যামেরাম্যানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেই লোকটি নানান কসরত করে আমাকে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে দাঁড় করায়। আমি একটু অসহিষ্ণুতা দেখালে মেয়েটি ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলে, জাস্ট ফিউ মিনিটস। তারপর আমাকে ভ্রমণসংক্রান্ত নানান প্রশ্ন করে একটা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেলে। আমার সফরসঙ্গীরা দূরে অপেক্ষায় থেকে উশখুশ করলেও কিছু করার ছিল না। সেই সাক্ষাৎকারটি অদৌ প্রচার করা হয়েছিল কি না, জানি না। ডকু ফিল্ম প্রস্তুতকারী সেই আরব সুন্দরীর নামধাম, ঠিকানা কিছুই জেনে নিই নি বলে কিছুটা আফসোস রয়ে গেছে। সাক্ষাৎকার পর্ব থেকে উদ্ধার পেয়ে এগিয়ে গেলে মুসলিম বোর্ড অভ উজবেকিস্তানের সুদৃশ্য আধুনিক ভবনের সামনের বাগিচায় এক উজবেক সুন্দরীকে তিনটে ছানাপোনা নিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখি। আমাদের সঙ্গের মহিলারা ওদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য হামলে পড়লে বেচারি কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও সম্মতি দেয়।

দুপুরে যেখানে খেতে যাই, তার সামনের খোলা জায়গায় তৈরি হচ্ছে কাঠের কাঠামো, সামনে শীত আসছে, তারই প্রস্তুতি হিসেবে এখানে চালাঘর তৈরি করে বসবে বাজার, অস্থায়ী রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। এখান থেকে দুই পা এগিয়ে গেলে একটা আটতলা ভবন, সেটার বহির্ভাগের সজ্জা ও নকশাগুলো বিজাতীয় ঠেকে। ওটা দেখিয়ে মোহাম্মদ বলে, এটা রুশ আমলে তৈরি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। এবারে এটির ভিনদেশি চেহারার রহস্য পরিষ্কার হয়। ভবনটির নিচতলায় রুশ ধাঁচের হরফে লেখা একাধিক সাইনবোর্ড দেখে বোঝা যায় এগুলো বিভিন্ন কোম্পানির অফিস বা দোকান। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দে যে ভূমিকম্প হয়, তাতে শ দুয়েকের মতো প্রাণহানি ঘটলেও, নগরীর বেশির ভাগ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে গৃহহীন হয়েছিল তিন লক্ষাধিক মানুষ। সেসব ভবনের শূন্যতা পূরণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী মানুষের চাপ সামলাতে তৈরি হয় সোভিয়েত ধাঁচের বহু আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। এটিও সেই সব ভবনের একটি।
ডলার ভাঙানোর জন্য লোটে সিটি হোটেল তাসকেন্ত প্যালেস নামের এক অভিজাত হোটেলের ভেতরে ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ বুথে গিয়ে ওটার নাম দেখে আমার আক্কেলগুড়ুম, ব্যাংকটির নাম ট্রাস্ট ব্যাংক, তবে ট্রাস্ট বানান দুই জায়গায় দুরকম, এক জায়গায় Trust, আরেক জায়গায় Trast। তবে ব্যাংকটির লোগো দেখে বুঝতে পারি না, এটি কোন ধরনের ব্যাংক। লোগোতে একটা ডলফিনের ছবি, ব্যাংকের সাথে ডলফিনের মতো একটা নিরীহ প্রাণির কী সম্পর্ক, ধরতে পারি না। ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে এক ডলার ভাঙালে পাওয়া যাবে ৮২৩০ সোম। ২০০ ডলারে ১৬ লাখ ৪৬ হাজার সোম পেয়ে নিজের মধ্যে বেশ বড়লোকি ভাব আসে। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর একটা আলাদা মজা আছে। উল্লেখ্য, সোম হচ্ছে উজবেক মুদ্রার নাম। ঠিক এ রকম ঘটনা ঘটেছিল ভিয়েতনামে গিয়ে। সেখানে প্রতি মার্কিন ডলার ভাঙিয়ে পাওয়া গিয়েছিল ১৫ হাজার ৮৬০ দং। অর্থাৎ দুই শ ডলার ভাঙিয়ে পেয়েছিলাম ৩১ লাখ ৭২ হাজার দং। ভাগ্যিস, ওদের কাগজের মুদ্রায় এক ও দুই লাখ দং আছে, তা না হলে এতগুলো টাকা বহন করতে ট্রাংক নিয়ে ঘুরতে হতো। ভিয়েতনামে গিয়েও হ্যানয়ের হোয়াম কিয়েম লেকের কাছে একটা ব্যাংক দেখে চমকে উঠেছিলাম, এবি ব্যাংক। এই দুই ভিনদেশি শহরে দেশি দুইটা ব্যাংকের সমিল নামের ব্যাংক দেখে চমকে উঠতে হয় বৈকি।
চওড়া ছিমছাম উজবেকিস্তান অ্যাভিনিউ থেকে বাঁয়ে মোড় নিলে হোটেলের সামনের বুয়ুক তুরন স্ট্রিট। ওপারে দীর্ঘাঙ্গ বৃক্ষের ঘন সমাবেশ, কিন্তু পাতাঝরার মৌসুম শুরু হয়েছে বলে পার্কের মতো জায়গাটি ছায়াঘন নয়। গাছগুলো তাদের একমাত্র পায়ের নিচের অংশে সাদা রং নিয়ে যেন সাদা মোজা পরে সটান দাঁড়ানো। সেই পায়ের আশপাশে সবুজ ঘাসের বিছানাজুড়ে ঝরাপাতার নকশা। রাস্তার পাশের চিনার গাছগুলোর ঝরাপাতা ঝাড়ু দিয়ে জড়ো করছে দুই নারী কর্মী। তাদের নাকমুখ ঢাকা মুখোশ আর মাথার হ্যাটের কারণে বয়স বা চেহারা কোনোটাই ভালোভাবে বোঝা যায় না। সেই গাছের নিচে ফাইবার গ্লাসের কিওস্কের ভেতর বসে দুপুরের ভাতঘুম বাদ দিয়ে কী যেন লেখালেখি করছে তাসখন্দ সিটি পুলিশের এক অফিসার। পুলিশের গুমটি ঘরটি পেরিয়ে গেলে চারপাশ বাঁধানো একটা বড়সড় কৃত্রিম পুকুর, তার মাঝে ফোয়ারা। পুকুরটির বিপরীত পাশে প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যের ছিমছাম একটা ভবন। তার দুপাশে চেস্টনাট গাছেরা এই পাতাঝরার মৌসুমে কিঞ্চিৎ ছায়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। সামনের পুকুরের শান্ত জলে প্রতিবিম্বিত ভবনটির নাম, আলিশের নাভাই অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার। উল্লেখ্য, আলিশের নাভাই (১৪৪১-১৫০১) ছিলেন মধ্যযুগের মরমি কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ, ভাষাবিদ ও চিত্রশিল্পী। চাগাতাই ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সমর্থক আলিশের মনে করতেন, চাগাতাই ও অন্য তুর্কি ভাষাগুলো সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে ফারসির চেয়ে অনেক উন্নত মানের। চাগাতাই হচ্ছে বিলুপ্ত এক তুর্কি ভাষা, যা একসময় মধ্য এশিয়াতে চালু ছিল। এই ভাষা থেকে উৎপত্তি হয় উজবেক ও উইঘুর ভাষা। থিয়েটার হলের মূল প্রবেশপথে তিনতলার সমান উচ্চতার তিনটি বিশাল ধনুকাকৃতি তোরণের পোর্টিকো। তার ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান ছোট দরজার সারি, ওপরের তলায় সারিবদ্ধ জানালা। সেই উঁচু খিলানের ওপর স্টেলেকটাইটের মতো ছোট ছোট ঝুলন্ত কার্নিশ, তার ওপর অনুচ্চ ছোট কয়েকটা মিনার। বুখারা সমরকন্দের পরিচিত স্থাপত্যের একই ঘরানার হলেও এটির মধ্যে রয়েছে একধরনের পরিমিত ধ্রুপদি মেজাজ। থিয়েটার হলের জন্য মানানসই ক্রিম আর সাদা রঙের মিশ্রণে শালীন স্নিগ্ধ আভা।
এই ভবনটির নকশা করে দিয়েছিলেন রুশ স্থপতি আলেক্সেই সুশেভ (১৮৭৩-১৯৪৯)। এটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৪২ সালে। পরবর্তী বছরগুলোতে জাপানি যুদ্ধবন্দীদের এই নির্মাণকাজে লাগানো হয়েছিল। সুশেভের নামটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি একটি কারণে যে রুশ সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের পড়া কিছু নামের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। যেমন, মস্কোর কমসোমোলস্কায়া স্টেশনের নকশা কিংবা নাৎসি আক্রমণে বিধ্বস্ত নভগরদ শহরের পুনর্গঠন পরিকল্পনা তাঁরই করা। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁকে একটি সমাধির নকশা করতে বলা হলে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রাচীন কয়েকটি সমাধিমন্দিরের মিলিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি নকশা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে পরে কানাঘুষা থেকে অভিযোগ উঠে আসে যে লেনিনের সমাধির নকশার কাজটি মূলত করেছিলেন ফ্রানৎসুজ নামের সুশেভের অধীনস্ত একজন আর্কিটেক্ট। এই বিষয়টি প্রমাণ করে দেওয়ার জন্য সেলিম খান ম্যাগোমেদভ নামের এক স্থাপত্যশিল্প সমালোচককে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রায় বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছিল। আসলে ঘটনার মূল কারণ ছিল স্থাপত্য নকশাটির মূল ব্যক্তি ইসিদর ফ্রানৎসুজ ছিলেন ইহুদি। জাতীয়তার প্রশ্নে পার্টির বক্তব্য ছিল যে রেড স্কোয়ারের মতো সোভিয়েত জাতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসের সঙ্গে এসব ইহুদি নাম জড়ানো উচিত নয়। সে কারণেই লেনিনের সমাধির স্থপতি হিসেবে সুশেভের নামই সরকারিভাবে স্বীকৃত। যা-ই হোক, ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু রুশ সাহিত্যের রসে সিঞ্চিত আমাদের গড়ে ওঠা পাঠাভ্যাসের কারণেই প্রসঙ্গটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও এখানে ঢুকে পড়ল।

বিকেলের দীর্ঘায়িত ছায়ায় নাভাই থিয়েটারের সামনের পুকুরের ধারের বাঁধানো রকের ওপর বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা হই আমরা। দুপাশে চিনার গাছের সারির মধ্যিখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মতো ফুটপাত, সেখানেও ঝরাপাতার নিঃশব্দ পতনের চিহ্ন আলপনার মতো আঁকা। সেই আলপনা মাড়িয়ে যেতে যেতে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের কথা গাইডকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না, ট্যুরিস্টদের জন্য সব অদেখা গন্তব্যই একেকটি অজানা উদ্দিষ্ট।
তাসখন্দে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন দেখতে চাইলে কিছুটা হতাশ হতে হয়। অন্তত বুখারা বা সমরকন্দের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ উজবেকিস্তানের রাজধানী শহরটিকে হতশ্রদ্ধা করলেও করতে পারে। যেসব শতাব্দীপ্রাচীন ভবনের জন্য তাসখন্দের সহোদরা দুই নগরীর বিশেষ আকর্ষণ, তাসখন্দ সেসব হারিয়েছে ১৯৬৬ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে। তারও আগে ১৯৪১ সালে জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন যুদ্ধ থেকে দূরে থেকেও উজবেকিস্তানকে যুদ্ধসরঞ্জাম শিল্পের বহু কারখানাকে স্থান দিতে হয়েছিল। এসব শিল্পের সঙ্গে এখানে আসে হাজার হাজার রাশিয়ান কর্মী। আরও একটি কারণে জনমিতির এই প্রবণতা বেগবান হয়েছিল। যুদ্ধকালে রাশিয়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আনুগত্যের বিষয়ে সন্দেহের কারণে সোভিয়েত সরকার কোরীয়, তাতার, চেচেনদের মতো ক্ষুদ্রতর জাতির মানুষকে বলপূর্বক উজবেকিস্তানে স্থানান্তর করে। ফলে বিশাল এই অভিবাসী জনসংখ্যার কারণে তাসখন্দ রূপান্তরিত হয় এক বহুজাতিক নগরে। ভূমিকম্পে গৃহহীন উজবেক এবং অভিবাসী রুশদের জন্য দ্রুত অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক এবং সোভিয়েত ঘরানার আজদাহা সাইজের বহু আধুনিক ভবন তৈরি হলেও তাসখন্দ ফিরে পায় নি ইতিহাসমণ্ডিত একটি প্রাচীন নগরীর সম্মান।
তাসখন্দের প্রাচীনতম স্থাপনা খাস্ত ইমাম স্কোয়ারে ইতিহাসের কিছুটা দেখা মেলে। তবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর স্বাধীন রাষ্ট্র উজবেকিস্তান তাসখন্দকে একটি আধুনিক নগরীতে পরিণত করার সকল প্রয়াস বাস্তবায়ন করে। সেসবের নজির দেখতে দেখতে অনতিপ্রাচীন আলিশের নাভাই থিয়েটারের পাশের পাতাঝরা ছায়াময় প্রায় নির্জন বুখারা স্ট্রিট ছাড়িয়ে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক স্ট্রিটে পড়লে দৃশ্যপট বদলে যায়। এখানে দেখা মেলে অভিজাত দোকানপাট, বার, রেস্তোরাঁ, প্যাস্ট্রি শপ, নামিদামি ব্র্যান্ড স্টোরের। কোনো কোনো ভবনের গায়ে আধুনিক ঘরানার ম্যুরাল থেকে উঁকি দিচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নারীমূর্তি। হেঁটে গেলে এসব খুঁটিনাটি দৃশ্য চোখে পড়ে। পশ্চিমি ট্যুরিস্টদের দেখি পিঠে ঝোলাব্যাগ নিয়ে এটা-ওটা দেখতে দেখতে রোদ বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে রাস্তা ধরে হেঁটে যায়। আমরা নিজ দেশে প্রতি পদে বিভিন্ন ধরনের নাগরিক যন্ত্রণা ভোগ করি বলেই বোধ হয় বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য বিলাসী হয়ে পড়ি। অথচ রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে এটা-ওটা দেখে নেওয়া যায়, কুকুর নিয়ে রাস্তায় নামা বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খুনসুটি করা যায়, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের সঙ্গে ‘হাই’ বিনিময় করা যায়, এমনকি নারী পথচারীদের প্রতি স্মিত হেসে আরেকটু আগবাড়িয়ে ‘গুড আফটারনুন’ও বলা যায়। এসবই সম্ভব বিদেশের মাটিতে। আমাদের দেশে এসবের কোনো কিছু করার জো নেই। রাস্তায় পথচলতি কারও দিকে হেসে তাকিয়ে সম্ভাষণ জানালে প্রতিপক্ষ এমন অবাক সন্দেহের চোখে তাকাবে যে অজান্তেই নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকবে। কোনো বাচ্চার সঙ্গে মজা করতে গেলে ছেলেধরা মনে করে হেনস্তার শিকার হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।
মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক স্ট্রিটের এক জায়গায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করা। এখানেও নাইট ক্লাব, পাব, শপিং মল, বুটিক শপ, বড়লোকদের জন্য গলাকাটা ফ্যাশন স্টোর, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে—এসবের ছড়াছড়ি। গাড়িহীন প্রশস্ত সড়কটিতে জনসমাগম দেখে কোনো মেলার মতো মনে হয়। সন্ধ্যার পরের প্রস্তুতি হিসেবে মাথার ওপর জালের মতো বিছানো হয়েছে মিটমিটে তারাবাতির সজ্জা, সেখান থেকে ঝালরের মতো ঝুলছে তারাবাতির মালা। সেই মালা দিয়ে তৈরি বড়সড় একটা ঝাড়বাতিও তৈরি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে বসেছে এক অন্য রকমের মেলা। তবে কোনো দোকান বা স্টলের স্থায়ী কাঠামো নেই, নেই কোনো টেবিল বা কাউন্টার, স্রেফ রাস্তার ওপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে হরেক রকমের পসরা। মেলা না বলে এটিকে স্ট্রিট মার্কেট বলাই শ্রেয়। মোস্তফা কামাল স্ট্রিটের এই অংশটা সোজা বেরিয়ে গেছে সেইলগখ স্ট্রিটকে ক্রস করে। রাস্তাটির পাশে বড় গাছে ঢাকা বিস্তৃত পার্ক। মেলাটির নাম সেইলগখ স্ট্রিট ব্রডওয়ে আর্ট বাজার। ব্রডওয়ে নামের মাহাত্ম্যটা বুঝতে পারি না। নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে নাটকপাড়া ব্রডওয়ে আছে বটে, যার নাম এসেছে ওলন্দাজ ‘ব্রিড ওয়েখ’ থেকে, যার অর্থ প্রশস্ত রাস্তা। প্রথমবার যখন নিউইয়র্ক যাই, আমার ধারণা ছিল ব্রডওয়ে হচ্ছে আমাদের মহিলা সমিতি মঞ্চের মতো কোনো নাট্যশালার নাম। বিভিন্ন স্ট্রিট ও অ্যাভিনিউ পার হয়ে একটা বড় রাস্তায় পৌঁছে পথচারী এক বয়স্কা মহিলাকে জিজ্ঞেস করি, ব্রডওয়েটা কোথায়? ওসব দেশে বয়স্ক মানুষের কথা বলার মতো লোকের অভাব, তাই মহিলা আমার দিকে একটু স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, বাছা, এই রাস্তাটার পুরোটাই ব্রডওয়ে। পরে বুঝতে পারি ব্রডওয়েও অন্যান্য অ্যাভিনিউর মতো একটা চওড়া রাজপথ।
তাসখন্দের এই সড়কটিকে স্থানীয়রা হয়তো আদর করেই এ নামে ডাকে। তবে আর্ট বাজার বলাটা ভুল নয়। সাজিয়ে রাখা পসরার একটা বড় অংশজুড়ে আছে পেইন্টিং। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু পথশিল্পী, ওদের সামনে বসলে স্বল্পতম সময়ে এঁকে দেবে একটা পোর্ট্রটে। রাস্তায় সাজিয়ে রাখা পেইন্টিংগুলো অবশ্য তেমন আহামরি কিছু নয়, সাধারণ কিংবা শিক্ষানবিশ শিল্পীদের আঁকা সস্তা ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল লাইফ, কিছু সাদাকালো পুরোনো পোর্ট্রটে। অনেক ঘেঁটেও কেনার মতো কিছু পাওয়া যায় না। এসবের পাশাপাশি আছে পুরোনো বইয়ের স্তূপ। তবে বেশির ভাগই কীটদষ্ট, সেসবের প্রায় সব রাশিয়ান কিংবা উজবেক ভাষায়। ইংরেজিতে দু-চারখানা পাওয়া গেলেও কেনার মতো নয়। এক জায়গায় বইয়ের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে রংচটা নড়বড়ে ফ্রেমে স্তালিনের বাঁধানো পুরোনো সাদাকালো ছবি, ঝাপসা হয়ে আসা পোকায় খাওয়া পত্রহীন গাছের ফটোগ্রাফ। বই আর ছবি ছাড়া বিভিন্ন তরফে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা আছে নানান ধরনের পুরোনো স্যুভেনির, অ্যান্টিকস। বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ফুলদানি, মোমদানি, লম্বা নলওয়ালা গড়গড়া, কেরোসিন স্টোভ, সামোভার, পিতলের ঘণ্টা, মূর্তি, বর্শা হাতে ঘোড়সওয়ার, টেবিলঘড়ি, চেইন লাগানো পকেটঘড়ি, নানান ধরনের ঝরনা কলম, কাফলিংক, টাই ক্লিপ, পিতলের ছাইদানি—কী নেই সেখানে?

এক জায়গায় কালো আর খয়েরি কেসে রাশিয়ান জেনিথ ক্যামেরা রাখা আছে বেশ কয়েকটা। এই জেনিথ ক্যামেরা দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। ছাত্রাবস্থায় যখন আমাদের ক্যামেরার দৌড় ইয়াশিকা মিনিস্টার থ্রি থেকে ইয়াশিকা ইলেকট্রো থার্টি ফাইভ পর্যন্ত, তখন ঢাকায় দু চারজনের কাছে দেখেছিলাম এই জেনিথ ক্যামেরা। দেখতে ঢাউস এবং কাঠখোট্টা চেহারার ক্যামেরাটির আকৃতি মোটেই পছন্দ হতো না। সোভিয়েত সাহিত্যের অপূর্ব স্বাদে ডুবে থাকলেও রাশিয়ান যন্ত্রপাতির এই ঢাউস ভাবটা পছন্দ হয় নি কখনো। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে যায়। রাশিয়ায় তৈরি ট্রাক্টরের এক বড় ক্রেতা ছিল জাপান। কিছুদিন পর দেখা গেল জাপান রাশিয়ান ট্রাক্টর কিনছে, আবার নিজেদের তৈরি ট্রাক্টর রপ্তানিও করছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ও রহস্যজনকই বটে। তবে বহু কসরতের পর সেই রহস্য ভেদ করে জানা যায়, জাপান রাশিয়া থেকে ট্রাক্টর কিনে তার প্রতিটা থেকে দুটো ট্রাক্টর তৈরি করতে পারে। কাঁচামালসাশ্রয়ী হওয়ার কারণে দেশের চাহিদা মিটিয়ে কম দামে বিদেশে রপ্তানিও করতে পারছে। অর্থনীতির ছাত্রদের জন্য হালকা চালে এটিই বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের একটা উদাহরণ হতে পারে। তবে বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক নয় বলে আর না এগোনোই ভালো।
এই আর্ট বাজারে সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছবিও তুলি। এক জায়গায় এক দিদিমা একটা চৌকিপিঁড়ির মতো উঁচু আসনে বসে নিজের জিনিসপত্রের ওপর সতর্ক নজর রাখছেন। ছবি তুলতে গেলেই কড়া ধমক দিয়ে নিষেধ করেন যাতে কোনো ছবি না তুলি। তারপর গজগজ করে কী সব বলতে বলতে সামনের সাজানো পসরা বিনা কারণে এদিক-ওদিক সরিয়ে নতুন করে সাজান। নিশ্চয়ই বলছেন, ‘কিছু কেনার মুরোদ নেই, আবার ছবি তুলতে এসেছে হতভাগা বিদেশি ট্যুরিস্ট।’ সেখান থেকে সরে এসে এ পাশের পথশিল্পীদের ডিসপ্লে করা নিখুঁত স্কেচ দেখতে থাকলে একজন ছবি এঁকে দেওয়ার আহ্বান জানায়, ‘হ্যালো মিস্তার, পোত্রেত?’ আগ্রহী শিল্পীকে ‘নো থ্যাংকস’ বলে নিবৃত্ত করি। প্রায় জীবন্ত সেসব আঁকা পোর্ট্রটে দেখে কিছুটা লোভও হয়, কিন্ত আমাদের হাতে অত সময় নেই।
ব্রডওয়ে আর সেইলগখ স্ট্রিটের কোনায় সাজিয়ে রাখা আছে একটা আস্ত ইয়ুর্ট। এটা হচ্ছে স্তেপ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তাঁবু, গোলাকার এই তাঁবু তৈরি হয় মেষের চামড়া, ফেল্ট—এসব দিয়ে, যাতে ঠান্ডা ঢুকতে না পারে। এগুলোর কোনোটির ছাদ শামিয়ানার মতো মাঝবরাবর খুঁটির ঠেকনা দিয়ে ওপর দিকে ওঠানো, শীর্ষে থাকে ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যাযাবর মানুষেরা এ রকম অস্থায়ী তাঁবুতেই থাকে। মঙ্গোলিয়াতে ঠিক এ রকম তাঁবুতেই থাকে যাযাবর মানুষ। সে দেশে এটির নাম ‘গের’। এই ইয়ুর্টটি নিজেই এক দর্শনীয় স্যুভেনির, তবে এর গায়ে বড় ব্যানারে লেখা দেখে বোঝা যায় এখানে এটি স্যুভেনিরের দোকান। ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় দরজা ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বুঝতে পারি কোনো কারণে বন্ধ আছে দোকানটি। মঙ্গোলিয়ায় একাধিক গেরের ভেতর ঢোকার সুযোগ হয়েছে আমার, তাই সফরসঙ্গীদের দেখাতে চেয়েছিলাম ইয়ুর্টের ভেতরটা কেমন। কিন্তু ওদের ভাগ্য খারাপ, কী করা?
যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস দেখার পর ব্রডওয়ে লাউঞ্জ বারের বারান্দায় বসে পয়সাওয়ালা ট্যুরিস্টদের মতো আয়েশি ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা দেখি। তরুণ-তরুণী, বাচ্চাকাচ্চাসহ গোটা পরিবার এবং আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের ঘোরাফেরায় জায়গাটা সরগরম। এখানে কেবল পসরা সাজিয়ে বসা নয়, পেইন্টিং শিল্পীদের মতো অন্য বিদ্যায় পারদর্শী লোকজনও এখানে দেখায় নানান কসরত, পথগায়কেরা শোনাতে পারে লোকগীতি। তাসখন্দের এই ঘরোয়া, নিরাভরণ ও আন্তরিক আদি বিনোদনের জায়গাটাকে খুব ভালো লেগে যায়। কিন্তু ভালো লাগলেই যে কোথাও বসে থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। অগত্যা আমাদের উঠতে হয়।
সেইলগখ স্ট্রিটের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাতের ডান পাশে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া একটা বাঁধানো পুকুরকে পাশ কাটিয়ে ছিমছাম রাস্তায় উঠে এলে বুঝতে পারি এটা সেই বুয়ুক তুরন স্ট্রিট, এই রাস্তার পাশেই দেখে এসেছিলাম আলিশের নাভাই থিয়েটার। রাস্তাটা পার হয়ে কয়েক পা এগোলেই গ্রিলের ঘেরার ভেতর প্রাচীন স্থাপত্য ঘরানার একটা বাড়ি দেখে দাঁড়াতে হয়। বাড়ি না বলে ছোটখাটো প্রাসাদ বলাই উচিত। দেয়ালভর্তি অজস্র খাঁজ আর নাতিদীর্ঘ স্তম্ভের বহুরৈখিক দেহরেখা, বাঁকানো খিলানযুক্ত জানালার বিচিত্র আকৃতি, ওপরে ব্যতিক্রমী মিনার ও গম্বুজ, পোর্চের ছাদের দুকোণে দুটো কুকুর, আর দরজার দুপাশে বসে থাকা দুটো হরিণের মূর্তি—সব মিলিয়ে এটি ঠিক কোন ঘরানার কাজ বোঝা যায় না। গাইড আবদুল্লা জানায় এটি হচ্ছে প্রিন্স রোমানভের প্রাসাদ। রাজপুত্র নিকোলাই কনস্টান্টিনোভিচ রোমানভ (১৮৫০-১৯১৭) ছিলেন জার প্রথম নিকোলাসের দৌহিত্র এবং দ্বিতীয় নিকোলাসের খুড়তুতো ভাই। ছোটবেলা থেকে অতি আদরে বেড়ে উঠে বখে যাওয়া মেয়েবাজ রোমানভের সঙ্গে ফ্যানি লিয়ার নামের এক কুখ্যাত মার্কিন নারীর আশনাই ছিল। তার জের ধরে রোমানভ মায়ের গয়না থেকে তিনটে দামি হীরা চুরি করে ধরা পড়ার পর পরিবারের মান রাখতে তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত করে রাশিয়া থেকে বহু দূরে নির্বাসন দেওয়া হয়। তাসখন্দের বিভিন্ন এলাকায় কঠোর নজরদারিতে থাকাকালে তিনি এখানে সাবান কারখানা, ফটো স্টুডিও, বিলিয়ার্ড সরঞ্জাম তৈরি, চাল, তুলা—এসব ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তাঁর আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় হতো বিভিন্ন শিল্পকর্ম সংগ্রহে। এই প্রাসাদটি তিনি নির্মাণ করান যাতে সংগৃহীত শিল্পকর্মের বিশাল সম্ভার সাজিয়ে রাখা যায়। রোমানভের মৃত্যু হয় ১৯১৭ সালে, তবে সে মৃত্যু রহস্যাবৃত। তিনি নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন বলা হলেও বলশেভিকদের হাতে খুন হওয়ার গুজবও বেশ জোরালো। রোমানভের অনেক কীর্তির মধ্যে তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, দুই পুত্র এবং গোটা ছয়েক বিবাহবহির্ভূত সন্তান।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রাসাদটি উজবেকিস্তানের শিল্প জাদুঘর, পুরাকীর্তি ও জহরতের জাদুঘর, সোভিয়েত আমলে পাইওনিয়ার নামে পরিচিত তরুণ স্কাউটদের আবাস হয়ে শেষাবধি উজবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিসেপশন হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়িটার ভেতরের চত্বরের বিশাল চিনার গাছগুলোর বয়স কমপক্ষে এক শ ত্রিশ বছর। সেগুলোর নিচে ঝরাপাতার রাশি দেখে জনহীন বাড়িটাতে প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না।
রোমানভের বাড়ি থেকে বের হয়ে বিশাল চওড়া রাস্তা সরাফ রশিদভ অ্যাভিনিউ, তার উল্টো পাশে একটা উঁচু আরেকটা খাটো ঝাঁ-চকচকে বিল্ডিং দেখিয়ে আবদুল্লা বলে, ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি বিল্ডিং। ও জানায়, বেঁটে ভবনটা এটুকু তোলার পর বরাদ্দের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে আর উঁচু করা হয় নি। ওর কথার সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। পেশাদার গাইডেরা অনেক সময় ট্যুরিস্টদের মজা দেওয়ার জন্য এ জাতীয় কিছু আজগুবি তথ্য দেয়, এটা সে রকম কিছু হতে পারে।
অ্যাভিনিউর তলা দিয়ে আন্ডারপাস ধরে ওপারে গেলেই মুসতাকিলিক মায়দোনি, অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ার। এখানে রয়েছে উবেকিস্তানের মন্ত্রণালয়, অর্থাৎ মন্ত্রীদের দপ্তর এবং উজবেক পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ, অলি মজলিশ। জারের আমলে এটার নাম ছিল ক্যাথেড্রাল স্কোয়ার। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই স্কোয়ারের নাম হয় রেড স্কোয়ার, তারপর লেনিন স্কোয়ার। উজবেকিস্তানের স্বাধীনতার (১৯৯১) পর এই বিশাল চত্বরের নামকরণ করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ার। মূল স্কোয়ারটি রাস্তা থেকে ভেতরে, একটা হালফ্যাশনের গেটের ওপর তিনটা উড়ন্ত পরস্পরসংলগ্ন সারস পাখির ভাস্কর্য, এই গেটের নাম ইজগুলিক আর্চ। ভেতরের মূল স্কোয়ারে শিশু কোলে চিরন্তন মায়ের ভাস্কর্য নিয়ে স্বাধীনতা স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় বিশাল ভূগোলক। আমরা সময় বাঁচাবার জন্য ভেতরে না ঢুকে ইজগুলিক আর্চের সামনে দিয়ে দুপাশে বিশাল চিনার গাছের সুড়ঙ্গের মাঝপথ দিয়ে হেঁটে যাই। সূর্য তখন বড় বড় গাছের পেছন দিয়ে নেমে পড়ার আগে নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে দেখছিল পেছন দিকে। দূরের অল্পবয়সী গাছগুলোর পাতা আশ্চর্য পাটকিলে রঙে নেয়ে উঠেছে যেন। পাশের লম্বা কৃত্রিম লেকের শান্ত জলের আয়না সেই পাতার বিম্বিত বর্ণে রঙিন।
লেকের অংশটুকু পার হয়ে আবার ঢুকে পড়ি বিশাল বৃক্ষের ছায়া ঢাকা পার্কের গভীরে। এই অংশটুকু পার হয়ে এগিয়ে গেলেই আচমকা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক বিশাল ভাস্কর্য। এক মাথা সমান উচ্চতার বেদির ওপর বসা এক বয়স্কা নারীমূর্তি, মাথায় ঘোমটা পরে হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে আছে নতমুখে। তার সামনে গোলাকার চৌবাচ্চার মতো নিচু বাঁধানো বৃত্তের কেন্দ্রে লাফিয়ে উঠছে আগুনের অনুচ্চ শিখা। তার বিষাদভারাক্রান্ত দৃষ্টি যেন আগুনের শিখার স্তিমিত দহনে জ্বলে যাচ্ছে অহর্নিশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিখোঁজ কিংবা নিহত পুত্রের প্রতীক্ষায় ক্লান্তিহীন বসে থাকা এই শোকাতুরা মা যেন জগতের সকল প্রতীক্ষারত মায়ের প্রতিরূপ। এই যুদ্ধের বিভীষিকা নানাভাবে স্পর্শ করেছিল উজবেকিস্তানের প্রতিটি পরিবারকে। যুদ্ধে নিহত ও নিখোঁজ প্রায় চার লাখ উজবেক সৈনিকের মা কিংবা স্ত্রী এভাবেই দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন দুঃসহ প্রহর। এখানে উল্লেখ করা যায় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ১৪ লাখ উজবেক সৈনিক রেড আর্মির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল জার্মানির বিপক্ষে। এদের মধ্যে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২ লাখ ৬৩ হাজার নিহত আর ১ লাখ ৩২ হাজার নিখোঁজ হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। উজবেকিস্তানের মানুষ যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য যোগান দিয়েছিল ৬৫ কোটি রুবল, ৫৪ কেজি সোনা ও রূপা, ২০ লাখ জোড়া জুতো এবং লাখ লাখ শীতবস্ত্র। হাজার হাজার এতিম শিশুকে দত্তক নিয়েছিল উজবেক পরিবারের লোকজন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে বহু দূরে থাকলেও বইপত্র আর সিনেমার কল্যাণে সেই বীভৎস সময়ের বিপন্ন মানবতার স্বরূপ কিছুমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারি। ভাস্কর্যটির নির্মাণশৈলীর চেয়ে বেশি অকৃত্রিম যেন এই রমণীর বসার ভঙ্গি—ক্লান্ত, অসহায় ও হতাশ। নাতিপ্রশস্ত এই কমপ্লেক্সের অন্য পাশে টানা করিডরে পিতলের পাতায় উৎকীর্ণ আছে যুদ্ধ থেকে না-ফেরা সৈনিকদের নামের মিছিল। যুদ্ধে নিহত ও নিখোঁজ সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রতিবছর ৯ মে তারিখে উজবেকিস্তানে পালিত হয় ‘স্মৃতি ও সম্মাননা দিবস’, সেদিন এই শোকাতুরা মায়ের পদতল ভরে ওঠে ফুলে, সেনাদল জানায় আনুষ্ঠানিক সামরিক অভিবাদন। বেদির ওপর বসা মায়ের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে কি পড়ে না। আমরা বসে থাকতে থাকতে চারপাশের গাছের মাথায় বিদায়ী সূর্যের ম্লান আলো সৃষ্টি করে এক অপার্থিব আভা। খানিক পরই এখানে নামবে অন্ধকার, কেবল প্রজ্জ্বলিত শিখাটি ঠেকিয়ে রাখবে তার আগ্রাসন।
কিছুটা ভারী মন নিয়ে ফিরতি পথ ধরে আমরা আবার পৌঁছে যাই স্বাধীনতা স্কোয়ারে। ইজগুলিক আর্চের সামনে থেকে পাতালপথে নেমে যে একটা মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে যাব, আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তাসখন্দের প্রায় সব মেট্রো স্টেশনে ঢোকার পথ এমনই সাদামাটা, অথচ ভেতরে রয়েছে চোখধাঁধানো স্থাপত্যের নিদর্শন, বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই।
তাসখন্দের দ্রুত নগরায়ণ ও বাড়তি জনসংখ্যার সাশ্রয়ী পরিবহন চাহিদা মেটানোর জন্য এখানে মেট্রোরেলের কাজ শুরু করা হয় ১৯৬৬ সালের ভূমিকম্পের দুবছর পর। রুশ বিপ্লবের ষাটতম বার্ষিকী উদ্যাপনের প্রাক্কালে তাসখন্দ মেট্রোর প্রথম ধাপ চালু করা হয় ১৯৭৭ সালে। এখন মোট ৩৭ কিলোমিটার লাইনে চালু রয়েছে ২৯টি স্টেশন। উল্লেখ্য, তাসখন্দ মেট্রো হচ্ছে মধ্য এশিয়ার দুটি মাত্র মেট্রোর একটি, আরেকটি রয়েছে কাজাখস্তানের আলমাতিতে।
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র যে ঢাক ঢাক গুড় গুড় অবস্থা ছিল, মেট্রো স্টেশনগুলোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এগুলো যে কেবল স্টেশন, তা নয়, সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবেও মেট্রো স্টেশনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। পরমাণু বোমা হামলার সময় এগুলো যাতে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তার জন্য রাখা হয়েছিল পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এমনকি কিছু স্টেশনে ব্যাংকের ভল্টের দরজার মতো ভারী দরজার দেখা মেলে, যাতে পরমাণু হামলার সময় এই সব ভারী দরজা লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে আশ্রয় নেওয়া সাধারণ নাগরিক ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের রক্ষা করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫ টুকরো হয়েছে ২৮ বছর, বিদায় হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, অথচ মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত এখানকার মেট্রো স্টেশনের ভেতরের বা বাইরের ছবি তোলা ছিল রীতিমতো নিষিদ্ধ।
গাইড আমাদের নিয়ে পাতালে নেমে টিকিট কিনে নেয়। টিকিটের দাম ১ হাজার ২০০ সোম, অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় ১২ টাকার মতো। এটা নাকি সাবেক সোভিয়েত যুগের সবচেয়ে সস্তা সাবওয়ে ভাড়া। মেট্রোতে ঢোকার পথটা যত নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল, প্ল্যাটফর্মে নেমে নকশাদার স্তম্ভের সারি, ছাদ থেকে ঝুলে থাকা জেল্লাদার ঝাড়বাতির সমারোহ দেখে উপলব্ধি করি প্রচ্ছদ দিয়ে সব সময় বই চেনা যায় না। আমাদের মেট্রোযাত্রা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি স্টেশন, মুসতাকিলিক মায়দোনি থেকে পরের স্টেশন আমির তিমুর খিয়োবোনি, অর্থাৎ আমির তিমুর স্কোয়ার স্টেশন। সোভিয়েত আমলে এই স্টেশনের নাম ছিল অক্টোবর রেভল্যুশন স্কোয়ার।
স্টেশন থেকে বের হয়ে এগোতেই পথে পড়ে জয়েন্ট স্টক কমার্শিয়াল ব্যাংকের মির্জা উলুগবেগ শাখা। পেশায় ব্যাংকার বলেই বোধ করি আমার নজর কাড়ে ওটার পাশে ডিসপ্লে বোর্ডে লেখা তাসখন্দের স্টেট ব্যাংকের ইতিহাস। জার শাসনামলে রাশিয়া তাসখন্দ দখল করে ১৮৬৫ সালে, তার পর বলশেভিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত তাসখন্দে বেশ কয়েকটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংকে রাশিয়ান পুঁজির সঙ্গে ছিল বিদেশি পুঁজিও। তেমনি একটা ব্যাংক ছিল স্টেট ইম্পেরিয়াল ব্যাংক। এটির তাসখন্দ শাখাটি ছিল ব্যাংকের শাখার তুলনায় অনুপযোগী একটা ভাড়াটে বাড়িতে। প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ব্যাংকের ভল্টে ঢোকার এক ব্যর্থ চেষ্টার ঘটনা ধরা পড়ে ১৮৯২ সালে। এই ঘটনার পর কনস্টানটিনোভস্কায়া স্কোয়ারে (বর্তমানের আমির তিমুর স্কোয়ার) স্টেট ইম্পেরিয়াল ব্যাংকের একটা নতুন ভবন নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়। বোর্ডটিতে আরও দীর্ঘ বয়ান আছে কীভাবে এই ব্যাংক বেড়ে ওঠে, কীভাবে এটিতে আরও কয়েকটা চুরির ঘটনা ঘটে। সেসব এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা বরং আমির তিমুর স্কোয়ারের দিকে নজর ফেরাতে পারি। জারশাসিত রাশিয়ান আমলে বিশাল এই স্কোয়ার এখনকার মতো এমন সাজানো-গোছানো ছিল না। খানাখন্দে ভরা গ্রীষ্মে ধুলা আর বর্ষার কাদায় সয়লাব এই মাঠটিকে চার ফালি করে মাঝবরাবর পরস্পরকে ছেদ করে বের হয়ে গিয়েছিল দুটো সড়ক, কাউফম্যান সড়ক আর মস্কো সড়ক। দ্বিতীয়টি ছিল সিল্ক রোডের অংশ, যেটি ধরে চীন অবধি যাওয়া যেত। ফলে এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশে যে স্টেট ব্যাংকের শাখা চালু করা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। পরবর্তী সময়ে এখানে রাশিয়া শাসিত তুর্কিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কনস্টানটিন পেত্রোভিচ ভন কাউফম্যানকে সমাহিত করা হয়েছিল বলে এটির নাম হয় কাউফম্যান স্কোয়ার। তার পর থেকে নামবদলের পালা শুরু হয়। বলশেভিক বিপ্লবের পর মস্কো স্ট্রিটের নামকরণ করা হয় এঙ্গেলস স্ট্রিট, কাউফম্যান স্ট্রিটের নাম দেওয়া হয় কার্ল মার্ক্স স্ট্রিট।
অবশেষে উজবেকিস্তান যখন (১৯৯১) স্বাধীন হয়, তখন এটির নাম চূড়ান্তভাবে বদলে রাখা হয় আমির তিমুর স্কোয়ার। স্কোয়ারের ঠিক মাঝবিন্দুতে বসানো হয় তৈমুর লংয়ের অশ্বাসীন ব্রোঞ্জমূর্তি। এই কেন্দ্র থেকে সবুজ ঘাসের লন পেরিয়ে বাঁধানো পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। পরিকল্পিত প্যাটার্নে সাজানো বিভিন্ন বৃক্ষসারি, ফুলের বেড, ফোয়ারা ছড়িয়ে রয়েছে পুরো স্কোয়ারজুড়ে। গাছের মধ্যে এল্ম, পপলার আর চিনারই চোখে পড়ে বেশি। এসবের মধ্যে কিছুদূর পরপর বসানো আছে বসার জন্য বেঞ্চ। এখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে হোটেল উজবেকিস্তানের বিশাল বহুতল ভবন, চেহারায় সোভিয়েত স্থাপত্যের কাঠখোট্টা ভাব স্পষ্ট। তার অন্য পাশে ডম ফোরামের আধুনিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভবন। এটি উজবেকিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদার এই ভবনটি তৈরির সঙ্গে নাকি প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী জড়িত ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন স্থপতি, প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং দক্ষ কারিগরদের এক বিশাল বাহিনী। দুর্জনেরা বলে, ২০১০ সালে এই স্কোয়ারের ছায়াময় শতবর্ষী চিনার গাছগুলো কেটে ফেলা হয় সাবেক স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভের নির্দেশে, যাতে এই ভবনটি গাছের আড়ালে ঢাকা না পড়ে।
অতি সম্প্রতি এই ভবনটি ভিন্ন আরেক কারণে আলোচনায় উঠে এসেছে। ভবনটি উজবেকিস্তানের শিল্প ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সঙ্গে জড়িত, আর এই ফোরাম হচ্ছে প্রেসিডেন্টের মেয়ে গুলনারা কারিমোভার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। গুলনারার বিরুদ্ধে অবৈধ প্রভাব খাটানোর বহু অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা হচ্ছে টেলিকম কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য প্রায় ৮৬ কোটি ডলার উৎকোচ গ্রহণ, যা বর্তমান আইনে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ। এসব অভিযোগ এমনই অকাট্য ছিল যে প্রেসিডেন্ট কারিমভ বাধ্য হয়েছিলেন নিজের মেয়েকে গৃহবন্দী করে পরবর্তী সময়ে সেটিকে কারাদণ্ডে পরিণত করতে। আসলে ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত ব্যবসায়ী, কূটনীতিবিদ, ফ্যাশন ডিজাইনার ও পপশিল্পী গুলনারা ছিলেন তাসখন্দের ওপরের মহলের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী। তাঁর ফ্যাশন শোতে উপস্থিত থাকতেন পশ্চিমি দুনিয়ার বাঘা বাঘা সেলিব্রিটিরা। তারপর আচমকা জনসমক্ষ থেকে উধাও হয়ে যান এই নারী। পরে জানা যায়, তিনি তাঁর লন্ডনে পড়ুয়া মেয়ে ও দুই পরিচারিকাসহ গৃহবন্দী আছেন। পিতা ইসলাম কারিমভের জীবদ্দশাতেই তাঁরা যে বাড়িতে বন্দী, সে বাড়িতেই এক অস্থায়ী আদালত বসিয়ে কয়েক ঘণ্টার বিচারসভার শেষে তাঁকে ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আরও জানা যায়, গৃহবন্দিত্বের সময় গুলনারার পরিচারিকাদের একজন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা সইতে না পেরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। প্রেসিডেন্ট ইসলাম কারিমভের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৫ বছরের স্বৈরশাসন, নিষ্ঠুর দুঃশাসন, ২০০৫ সালে আন্দিজান নগরীতে নিরস্ত্র প্রতিবাদকারীদের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞসহ অগণিত অভিযোগ থাকলেও তিনি যে তাঁর নিজ মেয়েকে শাস্তি দিতে পিছপা হন নি, সেটা এক বিস্ময়। বিভিন্ন বাণিজ্যে রাষ্ট্রপতির কন্যার অবৈধ প্রভাব, একটি বিশেষ ভবনের নাম তাঁর সঙ্গে জড়িত হওয়া, মালকিনের সঙ্গে পরিচারিকার বন্দিত্ব—এসব কিছুর সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু ঘটনার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।
এ রকম কাহিনি জানার পর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগমুহূর্তে ডম ফোরামের সুদৃশ্য ভবনটিকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। জানা যায়, গুলনারার সাংস্কৃতিক ফোরামের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এই ভবনটি সত্যিই এখন কিছুটা কোণঠাসা, কালেভদ্রে ব্যবহার করা হয়। ওটার ছাদের মৃদু উত্তল গম্বুজের ওপর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দুটো সারসের সিল্যুয়েট মূর্তিকেও যেন বিষণ্ণ দেখায়। ঠিক সে সময় একদল মেয়ে কলকল করতে করতে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দলটিকে দেখে ওরা কৌতূহলভরে এগিয়ে এসে আলাপ করে। আলাপে জানা যায়, ওরা সবাই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। কিছুক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়ে এবং নানান প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাদের দলের মহিলাদের সঙ্গে ফটোসেশনের পর কলকল করতে করতে নির্জন স্কোয়ারের প্রশান্তিতে টোল ফেলে চলে যায় ওরা।
কোনো নগর ভ্রমণে গেলে সেখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রা বোঝার জন্য স্থানীয় বাজার দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই তাসখন্দে আমাদের ভ্রমণসূচিতে চরসু বাজার দেখে অবাক হই নি। প্রাচ্যদেশীয় সমাজজীবনে হাট বা বাজার ছিল একটা জনপদের মূল কেন্দ্র। এগুলো যে কেবল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বেচাকেনার জায়গা তা নয়, এসব ছিল মানুষের সম্মিলন ও সামাজিক মেলামেশার জায়গাও। আমরা যে হোটেলে ছিলাম, সেখান থেকে বের হয়ে নাভাই অ্যাভিনিউ ধরে কয়েক কিলোমিটার পথ গেলে পৌঁছে যাওয়া যায় জমজমাট চরসু বাজারে। এক সকালে আমাদের তুলে নিয়ে সেই বাজারে ছেড়ে দিয়েও সঙ্গ ছাড়ে না আবদুল্লা। বাজারের চৌহদ্দিতে ঢুকতেই নজর কাড়ে ফিরোজা, নীল আর সাদা রঙের মিলিত নকশার বিশাল গম্বুজ। মূল বড় গম্বুজটি ছাড়াও আরও কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ দেখা যায়। গম্বুজের নিচে বাজার বুখারাতেও একাধিক দেখে এসেছি, মেটে রঙের সেসব গম্বুজের কোনোটিই চরসুর বর্ণিল গম্বুজগুলোর ধারে কাছেও লাগে না। রোদ, বৃষ্টি আর ধুলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাণিজ্যপথের ওপর স্থাপিত এসব বাজারে বিকিকিনির পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হতো নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।
মূল বাজারে ঢোকার আগে আবদুল্লা আমাদের নিয়ে ঢোকে নানান হস্তশিল্প পণ্যে ঠাসা বড় এক দোকানে। সেটি এমনই ঠাসা যে নড়াচড়া করতেও ভয় লাগে, পাছে কোনো মৃৎপাত্র কি মহার্ঘ ফুলদানি গায়ের সঙ্গে লেগে পড়ে ভেঙে যায়। সেদিন খাস্ত ইমাম স্কোয়ারের স্যুভেনির শপ থেকে কোনো কিছু কিনতে দেয় নি বলেই আবদুল্লা প্রথমেই আমাদের এখানে ঢুকিয়ে দেয়। দলে চারজন মহিলা থাকলে যা হয়, ওদের সামলাতে দোকানের দু তিনজন বিক্রয়কর্মীর দিশেহারা অবস্থা। দরকষাকষির জন্য আবদুল্লা তো মজুত আছেই, নিজে থেকেই এখানে নিয়ে এসেছে বলে দাম নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ার দায়িত্বটা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তে দোকানের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ জিনিসকে ছেনে ফেলতে থাকেন।
দোকানটির বাইরের চাতালের ওপারে অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েকটা দোকান, কোনোটিতে কার্পেট, কোনোটিতে লেপ-কম্বল, চাদর, বালিশ, কুশন ইত্যাদি, কোনোটিতে হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্রের লোভনীয় সম্ভার। উজবেকিস্তানের ট্র্যাডিশনাল পোশাকের দোকানে ঝুলছে বাহারি কুর্তা, কোট, শাল। দোকানের বাইরে রাস্তার পাশে সাজিয়ে রাখা জাতীয় পোশাক পরানো ছোট ছোট মূর্তি, বড় বড় মাটির ফুলদানি। ঢাকা নিউমার্কেটের মতো বাইরের খোলা চাতালেও পণ্য সাজিয়ে বসা কিছু ভাসমান দোকান। সে কারণেই বাজারের এই অংশটির চেহারা বেশ পরিচিত ঠেকে।
রাশিয়ানরা আসার আগে তাসখন্দ ছিল চারটি উপশহরের একটা নগর। এসব উপশহর শাসন করতেন চারজন হাকিম, যাঁদের বলা যায় মেয়র। এঁরা নির্দিষ্ট বিরতিতে কিংবা কখনো জরুরি ভিত্তিতে সভায় বসতেন, যাকে বলা হতো ‘চরহাকিম’, অর্থাৎ চার মেয়র। চার উপশহরের বাসিন্দারা কখনো কখনো সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ত। তখন বাইরে থেকে কাজাখ বা উজবেকদের সাহায্যের জন্য ডেকে আনা হতো। চার মেয়রের আধিপত্য শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নতুন নেতৃত্বে হাকিমদের নিয়োগ দেওয়া হয় উপদেষ্টা হিসেবে।
ফারসি ‘চরসু’র বাংলা করলে দাঁড়াবে ‘চার নহর’, বা চার নহরের সংগমস্থল। অর্থাৎ এখানে বাণিজ্য এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য মিলিত হতো চারটি উপশহরের মানুষ। যে বিশাল বর্ণিল গম্বুজটি এখন দৃশ্যমান, সেটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ভূমিকম্পের পর। তবে গম্বুজঢাকা বাজারের পরম্পরাটা এখানে টিকিয়ে রাখা হয়, সোভিয়েত রাশিয়ার স্থাপত্যের আদলে আজদাহা সাইজের কংক্রিটের ঢাউস কিছু বানানো হয় নি। সে কারণেই বোধ করি তাসখন্দের অল্প কয়েকটা আকর্ষণের মধ্যে চরসু বাজারও একটা দ্রষ্টব্য। রাশিয়ানরা তাসখন্দ দখল করার পর ব্যাপক নির্মাণকাজ শুরু হলে নগরীর পুরোনো এবং নতুন অংশের মধ্যে পরিবর্তনটা জোরালো হয়। পুরোনো অংশে থেকে যায় মুসলমানপ্রধান মধ্য এশীয় নাগরিকেরা, অন্যদিকে বেড়ে ওঠে জনসংখ্যার ইউরোপীয় ও রাশিয়ান অংশটি। হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে পুরোনো অংশটিতে রয়ে গিয়েছিল মধ্য এশিয়ার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপত্যগুলো। সেসবের বেশির ভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ভূমিকম্পে। ফলে পুরোনো অংশের অনেক কিছু নতুন করে তৈরি করলেও প্রাচ্যের আদলে রেখে দেওয়া হয়েছিল মূল বাজারটি, যেটি দেখতে এসে আমাদের এক বেলা কাটে। এটির পাশেই একসময় স্থানীয় কারিগরেরা বিক্রি করত কাঠের আসবাব, বাদ্যযন্ত্র ও নানান গৃহস্থালি সরঞ্জাম। সিল্ক রুটের পাশের এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারটিতে বাণিজ্যের পাশাপাশি লোকজন কাছের-দূরের মানুষের সঙ্গে খবরাখবর বিনিময় করত, উপভোগ করত গান-বাজনা, বাজিকরদের কসরত, মোরগ লড়াই কিংবা চাইখানায় বসে মশগুল হতো আড্ডায়।
স্যুভেনিরের দোকানের বাইরে রাস্তার পাশে পসরা বিছিয়ে দুই অসমবয়সী মহিলা পাশাপাশি বসে, একজনের কাছে চকলেটের প্যাকেট, নেসকাফে কফির বয়াম, কয়েক ব্র্যান্ডের চায়ের বাক্স, আচার ইত্যাদি। বয়স্কজনের সামনে ছড়ানো রয়েছে চিরুনি, চুলের ব্রাশ, ক্লিপ, রিবন ইত্যাদি মেয়েদের জিনিস। এখান থেকে একপাতা ক্লিপ আর কী যেন কিনে মিনা আমাকে দাম দিয়ে দিতে বলে। দাম কত জিজ্ঞেস করলে মহিলা হাতের তিন আঙুল তুলে দেখায়। আমি খুব মনোযোগ না দিয়ে তিনখানা দশ হাজার সোমের নোট ধরিয়ে দিলে কম বয়সী মহিলা বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে কী যেন বলে ওঠে, আমি ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটতে শুরু করলে মহিলা আমাকে দুখানা নোট ফিরিয়ে দিয়ে আরও সাত হাজার সোম ফেরত দেয়। এবার বুঝতে পারি, ওরা চেয়েছিল তিন হাজার, আমি উজবেক সোমের দুর্বলতা বিবেচনা করে দিয়েছিলাম ত্রিশ হাজার। এরা হয়তোবা মা-মেয়ে কিংবা শাশুড়ি-বউ। ওদের সরলতা ও সততায় স্তম্ভিত হয়ে বারবার ‘থ্যাংক ইউ’ বললে ওরাও কেবল ‘থ্যাংকু থ্যাংকু’ করতে থাকে, আর অবোধগম্য ভাষায় আমার বোকামির কথা বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। প্রতিদান হিসেবে ওদের ছবি তুলতে চাইলে প্রথমে কিছুটা আপত্তি করেও শেষে দুজনেই দোকান ছেড়ে উঠে এসে সহজ ভঙ্গিতে পোজ দেয়। ভাষার কারণে ওদের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপের সুযোগ হয় না।
এখান থেকে এগিয়ে গেলে চরসুর মূল আকর্ষণ বিশাল গম্বুজঘেরা বাজার। এটার ঘের কত বড় ধারণা করতে পারি না, আড়াই শ-তিন শ মিটারের কম হবে না। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ঢোকার পথ, সেখান থেকে আবার একপ্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। এই ফ্লোর যেন বিশাল চওড়া বৃত্তাকার ব্যালকনি, মধ্যিখানটা পুরোটা খোলা। সেখান থেকে নিচে তাকালে নিচতলার পুরো ফ্লোরজুড়ে দেখতে পাওয়া যায় মাছ-মাংসের দোকান। আমাদের কাঁচাবাজারের মতো গরু বা খাসির রান ও সিনা ঝোলানো, সাজিয়ে রাখা চামড়া ছাড়ানো মুরগি। আবার ফ্রিজের মধ্যে হিমায়িত মাংসের দোকানও কম নেই। তবে এই বাজারে হিমযন্ত্রটিকে বেমানান লাগে। দোতলার এই ফ্লোরটির যেদিকে তাকাই কেবল শুকনো ফল, বাদাম ইত্যাদির দোকান। বাজারের গমগম শব্দ না থাকলেও মানুষের সমাগম, কেনাকাটা—কোনোটারই কমতি নেই। এ রকম বাজারে ট্যুরিস্টদের কেনার মতো একমাত্র জিনিস শুকনো ফল আর বাদাম ইত্যাদি। সে কারণেই আবদুল্লা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে বুঝতে পারি। দোকানিদের সামনে থরে থরে সাজানো কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম, চিনা বাদাম, আখরোট, আলুবোখারা, শুকনো ডুমুর, কিশমিশ, খেজুর, নাম না জানা ফলের বীজ। সব দোকানেই একই জিনিস। সেখান থেকে ইচ্ছেমতো খেয়ে স্বাদ পরখ করে অর্ডার দেওয়া যায়, দোকানির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। দামে সস্তা কিংবা খদ্দেরের এই স্যাম্পল খাওয়ার খরচও দামের মধ্যে ঢোকানো থাকে বলে কেউ আপত্তি করে না। এমনকি এটা-ওটা খেয়ে না কিনে চলে গেলেও সমস্যা নেই। ফলে যে দোকান থেকে আমাদের দলটি পুরো সদাই করে, সেখান থেকে বিরামহীন খেয়ে আমাদের সবার বাদামে অরুচি ধরে যায়।
বড় গম্বুজের ভেতর থেকে নেমে এলে পাশের বাজারটির এক পাশে কাঁচা ফল, পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ মসলাপাতির দোকান। মসলার পরিচিত মিষ্টি ঝাঁজালো গন্ধে চারপাশ ভরে আছে। অন্য পাশে তাকালে চূড়া করে রাখা জাফরানের উজ্জ্বল আভায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বাজারের এই অংশটিকে আমাদের খুব পরিচিত মনে হয়। একসময় বড় মুদিদোকানে গেলে এ রকম বাজারের ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা যেত। আজকাল প্যাকেট করা বিপণনব্যবস্থায় সেই স্মৃতিময় ঘ্রাণ কেবলই অতীত। বাজারের এই অংশের বাইরে পথের পাশে দেখা যায় তাজা ফল, শাকসবজি সাজিয়ে বসা দরিদ্র চেহারার মহিলাদের। খোবানি, খেজুর, কিশমিশের মতো শুকনো ফল নিয়ে বসেছে কেউ কেউ, নানান রঙে প্রক্রিয়াজাত একই ফল তৈরি করেছে বহুবর্ণ কোলাজ। তাজা ফলের মধ্যে আপেল আর কমলাই চোখে পড়ে বেশি। কমলা আর জাফরানের মিলিত রঙে বাজারের একাংশ পায় বাড়তি উজ্জ্বলতা। বাজারে তরমুজ বিক্রির ওপর মেয়রের আচমকা নিষেধাজ্ঞার কারণে কিংবা মৌসুম নয় বলেই হয়তো চোখে পড়েনি তরমুজ। এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টা সত্যিই মজার। ২০১১ সালে তাসখন্দের মেয়রের এক ফরমানবলে নগরীর সব বাজারে রসাল এই ফলটির বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। কারও মতে, এটিতে মাত্রাতিরিক্ত কেমিক্যাল মেশানোর কারণে, আবার কারও মতে হাসপাতালগুলোতে তরমুজ খেয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় এমন অনেক আজগুবি নিষেধাজ্ঞা জারির ঘটনা আছে। ২০০২ সালে সারা দেশে নিষিদ্ধ করা হয় বিলিয়ার্ড হলগুলো। কারণ হিসেবে খোলাখুলিভাবেই বলা হয় যে এসব জায়গায় মদ-সিগারেটের মারাত্মক দৌরাত্ম্য মানুষকে বখে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর স্বাধীন উজবেকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইসলাম কারিমভের নির্দেশে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে উজবেকিস্তানের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি থেকে সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয় রাজনীতিবিজ্ঞান বিষয়টি। তাঁর নিজের কিংবা উপদেষ্টাদের মতে পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মডেলের জায়গায় উজবেক মডেল প্রতিস্থাপন করার জন্যই এই পদক্ষেপ।
কোলাহলময় নানান জাতির বিচিত্র জটলা, দেশি-বিদেশি ফলের বিপুল সম্ভার, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণিল পোশাক, দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা এশীয় পসরার রঙিন আভা, দূরদূরান্তের উদ্দেশে হেঁটে চলা ঘোড়ার ওপর আসীন সফেদ দাড়ির নুরানি চেহারার মানুষ, খচ্চর আর উট—সব যেন গলিত তেলের ওপর ভাসতে ভাসতে দক্ষিণায়নের রোদে চকচক করছে—বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ রকমই ছিল তাসখন্দের কোনো বাজারের বর্ণনা। এখন আর এই দৃশ্য কল্পনা করা যায় না, যদিও একটা জমজমাট বাজারের অতি পরিচিত দৃশ্য এটা। এই চরসু বাজারেই একসময় পথগায়ক, দড়াবাজ, ভেলকিবাজ, সার্কাসের ভাঁড়েরা জনসমক্ষে উপস্থাপন করত নিজেদের কসরত। আমাদের গ্রামের সাপ্তাহিক হাটগুলোতে হুবহু না হলেও প্রায় এ রকমই দেখা যায়। হাটের পথে অনেক দূর থেকে শোনা মৃদু গুঞ্জন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়, কাছাকাছি হলে অনুভূত হয় জীবনের অস্তিত্ব, টের পাওয়া যায় মানুষের অনিঃশেষ কর্মচাঞ্চল্য। আজকাল কাঁচাবাজারে সেকালের মতো কেউ শখ করে যায় না, কিন্তু ঝানু ট্যুরিস্টের মতো আমরা মশহুর বাজারটি আলগোছে দেখে বুঝতে পারি, মানুষের অকৃত্রিম জীবনযাত্রা বোঝার জন্য এ রকম বাজারই আসল জায়গা। চরসু বাজারের প্রাচ্যদেশীয় চরিত্র ও ঘ্রাণ, কৃত্রিমতাবর্জিত পরিবেশই ভিনদেশি মানুষদের এখানে টেনে আনে। ট্যুরিস্টদের বিরামহীন আনাগোনার কারণে সাধারণ বাজারের চেয়ে এটি বহুগুণ বেশি সাফসুতরোও বটে। শতাব্দীপ্রাচীন বাজারটি থেকে যখন বের হয়ে আসি, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। অদূরে মাথা তুলে রোদ পোহাচ্ছে কুকেলদাশ মাদ্রাসার ফিরোজা গম্বুজ।
চলবে...
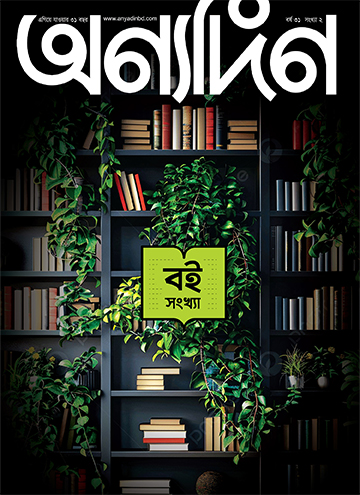














Leave a Reply
Your identity will not be published.